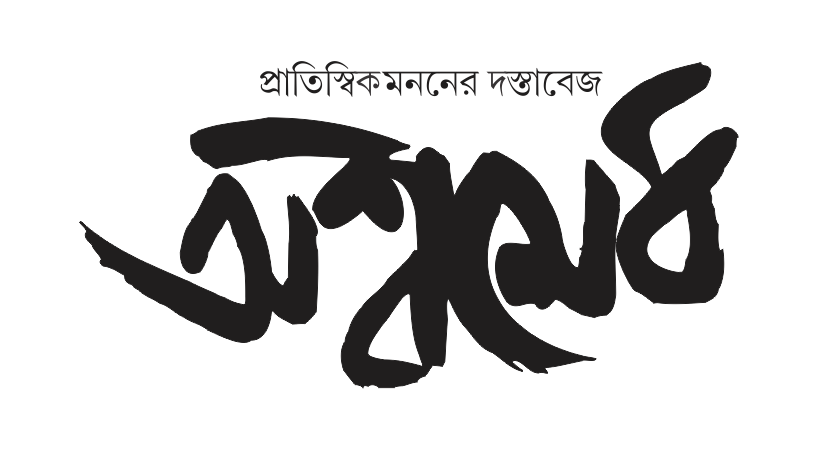মল্লিকা মুখ শুকনো করে ক্লাসে ঢুকে বললো,—’আমাদের পাড়ার লোকগুলোর সব মাথা খারাপ হয়ে গেছে ম্যাম।’ ওর কথার ধরনে হেসে ফেলি,—কেন রে? কী হলোটা কী!—শুনলাম, সারা পাড়ার গাছগুলো সব মুড়িয়ে দিয়ে গেছে, গাছ কাটার লোকজন। পাড়ার লোকের মত হলো—গাছ হলে মশা হয়, মশা হলে ডেঙ্গি, ম্যালেরিয়া। তাই কেটে ফেলো সব।—মল্লিকা অবাক হয়ে বলে,—কী অদ্ভুত কথা বলুন ম্যাম, এদিকে পোস্টারে লেখা হচ্ছে—‘একটি গাছ একটি প্রাণ; গাছ লাগান প্রাণ বাঁচান’—আর প্রতি বছর এরকম করে গাছ কেটে ফেলা হচ্ছে!
আমি বা আমার মতো অনেক দিদিমণিই মল্লিকাদের মতো সচেতন ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে রাস্তায় অনেক হেঁটেছি, ‘গাছ লাগাও’ স্লোগান বলে বলে। বর্ষার সময় স্কুলের ছেলেমেয়েরা গাছ লাগিয়েছে এদিক সেদিক। অথচ স্কুল-পাঠ্য বইয়ের সঙ্গে বাস্তবের অসঙ্গতি এতটাই, যে, বাস্তবের মুখোমুখি হয়ে কিশোর-মনের এই কষ্ট, অসহায় অনুভব, বোধের কোনও সদুত্তর দিতে পারি না আমি। কী করেই বা পারবো! সে-ই ১৯৭৪ সাল থেকে ‘বিশ্ব পরিবেশ দিবস’ পালন করা শুরু হয়েছে। ১৪৩টি দেশ এতে অংশ নেয়। চল্লিশ বছর পার করেও তবু কেন গ্রেটা থুনবার্গদের পথে নামতে হবে?
কোনও বাড়ির ছাদে বা ব্যালকনিতে সাজানো ফুলবাগান দেখে, সে বাড়ির মানুষদের ‘বৃক্ষপ্রেমী’ ভেবে নিয়ে বার বার ভুল করেছি, যখন দেখেছি, প্রয়োজনের ছুতোনাতায় কাটা পড়ছে ঘর-লাগোয়া বৃদ্ধ জামগাছ, নিমগাছ। কারণগুলো তর্কের বিষয়: কখনও প্রতিবেশী, কখনও বাড়ির ছাদে পাতা পড়া, কখনও পোকামাকড়, আবার শুধুই বিক্রি বাবদ প্রাপ্য অর্থের কারণও রয়েছে। এমন মানুষও দেখেছি, উম্পুনের ঝড়ে ঘর লাগোয়া শিশু গাছের বেঁকে যাওয়া আর তাতে সদরের ঢাল উলটে যাওয়া নিয়েও দিব্যি হাসছেন, বাস করছেন। অতএব ‘গাছ লাগাও প্রাণ বাঁচাও’ যে এক অসম্পূর্ণ স্লোগান—এ নিয়ে কোনও সংশয় নেই। পরিবেশ সংরক্ষণের বিষয়ে কাজ করেন যেসব সংগঠনগুলি, তারা ইদানীং তাই গাছ লাগানোর পাশাপাশি বলছেন, গাছ প্রতিস্থাপনের কথা, বড় গাছ বাঁচানোর কথা। যদিও প্রক্রিয়াটি যথেষ্টই ব্যয়সাপেক্ষ। ১৫ জুন, ২০২০ আনন্দবাজার পত্রিকার অনলাইন সংস্করণের একটি সংবাদ-সূত্রে জানা যাচ্ছে, হলদিয়া বন্দর কর্তৃপক্ষ উম্পুন ঝড়ে পড়ে যাওয়া গাছগুলি বাঁচিয়ে তোলার চেষ্টা করেছে। বন্দরের ডেপুটি ম্যানেজার জানিয়েছেন, একটি বকুল গাছ প্রতিস্থাপন করা সম্ভব হয়েছে কিন্তু নয়াচরে উপড়ে যাওয়া লক্ষাধিক গাছকে বাঁচানো সম্ভব হয়নি। পূর্ব-মেদিনীপুরে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের কর্মীরা বন দফতরে যোগাযোগ করলে, ডিএফও জানান,—“গাছ প্রতিস্থাপনের পরিকাঠামো কোনও জেলাতেই নেই। কলকাতায় রয়েছে। হিডকো এই কাজ করে। কিন্তু ওরা আসতে রাজি নয়। কলকাতায় গাছ প্রতিস্থাপন করা হয়। হরমোন ব্যবহার করা হয়। যেহেতু যন্ত্রপাতি খুব দামি তাই কলকাতা থেকে এসে খরচে পোষাবে না জানিয়েছে তারা।”
বছর ঘুরতে না ঘুরতে আরও একটি ঝড়ে বেহাল অবস্থায় দেখতে পাওয়া গেল, ভ্রমণকারীদের পরিচিত এ রাজ্যের, ওড়িশার সমুদ্র সৈকতকে। উন্নয়ন আর সৌন্দর্যায়নের ভাবনায় পরিবেশের ভারসাম্যের, বাস্তুতন্ত্রের কথা যে বিশেষ ভাবা হয় না—পরিবেশবিদরা সে-কথাই বলছেন।
পৌরাণিক আমল থেকেই অরণ্য আর অরণ্যচরেরা কোণঠাসা হয়ে এসেছে শাসক-শক্তির হাতে। সভ্য-সমাজ মানে রাজনীতির চাল। ব্যক্তি আর রাষ্ট্র এ-দুই হলো জীবনযাপনের দুই অভিমুখ। সে-ই পরিপ্রেক্ষিতে উন্নয়ন ও পরিবেশ ধ্বংস ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। উন্নয়নের প্রশ্নে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই সারা পৃথিবী জুড়ে বনাঞ্চল এক বিপদ-সংকেতের মধ্যে দিয়েই চলেছে। ১৯৭২ সালে স্টকহোমে রাষ্ট্রসংঘ আয়োজিত আলোচনাচক্রে পরিবেশ বিষয়ক আলোচনায় অংশগ্রহণকারী দরিদ্র দেশগুলির ধারণা ছিল, পরিবেশ সমস্যা আসলে শিল্পোন্নত দেশগুলিরই সমস্যা। ভারতের মতো দরিদ্র দেশগুলির মূল সমস্যা হলো শিল্পোন্নতির মাধ্যমে দারিদ্র্য দূর করা। অতএব এমনটা অনেকেই ভেবেছেন যে, পরিবেশ সমস্যা বা দূষণ সমস্যার কথা বলে আন্তর্জাতিক স্তরে ধনী আর দরিদ্র দেশগুলির ভেতর পার্থক্য বজায় রাখার চেষ্টা করা হচ্ছে। সে-ই পার্থক্য দূর করতে এবং দেশের নাগরিকের জীবনযাত্রার মানের উন্নয়ন করতে ‘উন্নয়ন’-এর যে মডেলকে অনুসরণ করা হলো, তাতে দেশের ভেতর এক শ্রেণির মানুষ ধনী থেকে আরও ধনী এবং দরিদ্র আরও দরিদ্র হলো। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অবশ্য তৃতীয় বিশ্বের রাষ্ট্র হিসাবে ভারত পরিচিত হলো—উন্নয়নশীল হিসাবে।
পরিবেশ বাঁচিয়ে শিল্পের কথা হয়তো বলা হয়, কিন্ত কাজের কাজ কতদূর হয় তা কে খতিয়ে দেখছে! সম্প্রতি মুক্তি পাওয়া সিনেমা ‘শেরনি’ (২০২১)-তে পরিচালক অমিত মাসুরকর দেখিয়েছেন, জঙ্গলের বাফার জোনে কীভাবে এক খনি খনন করায় সে পথ বাঘিনির কাছে অগম্য হয়ে উঠেছে। তাহলে সে যায় কোন পথে, আর খায়ই বা কী? বন কেটে আবাদের পদ্ধতি যদিও প্রাচীন। ভারতে, পুরাকালে মোট স্থলভাগের শতকরা আশি ভাগই ছিল এক সময় অরণ্যে আচ্ছাদিত। ইন্দিরা গান্ধীর আমলে, জাতীয় কৃষি কমিশনের হিসাবে ১৯৫১ থেকে ১৯৭২ পর্যন্ত মোট ৩৪ লক্ষ হেক্টর বনভূমি উন্নয়নের প্রয়োজনে উচ্ছেদ হয়েছে। অর্থাৎ বছরে ১৫,৫০০ হেক্টর জমি গড়ে। শতাংশের হিসাবে এর মধ্যে কৃষিকাজে ৭১ ভাগ, নদী প্রকল্পে ১২ ভাগ, শিল্পের প্রয়োজনে ৩. ৫ ভাগ, রাস্তাঘাটের জন্য ১. ৫ ভাগ ও অন্যান্য প্রয়োজনে বাকি জমি ব্যবহৃত হয়েছে বলে জানা যায়। এ বোধহয় সময়ের এক বিচিত্র খামখেয়াল, যে, সলিল চৌধুরীর কথা ও সুরে মান্না দে ‘মর্জিনা আবদুল্লা’ ছবির জন্য গাইলেন, এই বাহাত্তরেই, কাঠুরিয়াদের গান। যে গান আজও বাঙালি সংগীত-প্রেমীর মনে অনুরণন তোলে। এক লেখক বন্ধুর বই (‘মহাভারত’, শুদ্ধসত্ত্ব ঘোষ) পড়েছিলাম। তিনি লিখছেন,—“কুরুরাজ্য শক্তিশালী হতে গেলে তার প্রয়োজন সম্পদের। অরণ্যের সম্পদের চাইতে অনেক বেশি সম্পদ কৃষিতে সে পেতে পারবে। তাই দেখা যাচ্ছে অরণ্যের প্রান্তে প্রথম বাস করতে শুরু করেছে কৃষিজীবীরা। ক্রমশ প্রশাসনের সমর্থনে তারাই গ্রাস করতে শুরু করছে অরণ্য।”—লেখক পর্যালোচনা করে লিখছেন,—“পরের প্রজন্ম কোনদিকে যাবে সে-কথা পরের। আভ্যন্তরীণ রাজস্ব বৃদ্ধি না হলে কোনওভাবেই সম্ভব নয় ব্যয়বহুলতা চালিয়ে যাওয়া। অতএব প্রচলিতর পাশাপাশি অপ্রচলিত সূত্র থেকেও কর আদায়ের ব্যবস্থা চলছে। অরণ্যকে কৃষিজমিতে পরিবর্তন সে কার্যক্রমের অন্যতম।”—সব সমস্যার মূলে আসলে মানুষ, জনসংখ্যার বৃদ্ধি। চাই অন্নসংস্থান। খেতে পেতে হবে তো আগে। আগে বাঁচা, পরে পরিবেশ সামলানো। এ এক ভিশাস সার্কেল। মানুষ নিজেই নিজের হন্তারক হয়ে উঠল। আজকের পৃথিবীর দিকে তাকালেই এ জিনিস অত্যন্ত স্পষ্ট। শিল্প এসে শিকড় গেড়েছে শাসকের মনে। এই ষড়যন্ত্র থেকে অব্যাহতি পায়নি পৃথিবীর ফুসফুস আমাজন অরণ্যও। অরণ্যচরেরা আদালতে জিতলেও প্রাণের ঋণেও বাঁচাতে পারছেন না অরণ্য। আবার ঠিক এর পাশাপাশিই রয়েছে, অপরিকল্পিত বনায়ন। যেনতেনপ্রকারেণ গাছ লাগিয়ে মান বাঁচানোর চেষ্টা। বন সৃজন-প্রক্রিয়ার গলদ বুঝতেই কেটে যাচ্ছে এক-দুই দশক। ততক্ষণে যা ক্ষতি হবার তা হয়ে বসেছে।
“এমন সময় আসিবে হয়তো দেশে, যখন মানুষ অরণ্য দেখিতে পাইবে না। শুধুই চাষের ক্ষেত আর পাটের কল, কাপড়ের কলের চিমনি চোখে পড়িবে, তখন তাহারা আসিবে এই নিভৃত অরণ্যপ্রদেশে, যেমন লোকে তীর্থে আসে।”—পথের কবি বিভূতিভূষণের ভবিষ্যৎ-দৃষ্টি কতদূর সত্যি হয়েছে, সে কারোর অজানা নয়। মানুষ গাছেদের কোণঠাসা করতে করতে এমন পরিস্থিতি করে তুলেছে, যে, আজ দিকে দিকে অক্সিজেন পার্লার খুলেছে। হাঁটার জন্যে কৃত্রিম বাগান তৈরি হচ্ছে। সবুজকে পাওয়ার, ছোঁয়ার জন্যে পয়সা খরচ করে লোকেশান বাছাই করতে হচ্ছে আমাদের। আচার্য জগদীশচন্দ্রের দেশের মানুষ আন্তর্জালের খবরে জানছেন, গাছকে জড়িয়ে ধরে কেমন করে প্রাণের উজ্জীবন হয়, খালি পায়ে ঘাসে বা সবুজ জঙ্গলের মধ্যে গাছের ছায়া ধরে হাঁটলে ফিরে পাওয়া যায় হারানো জীবনীশক্তি। জঙ্গলে গাছেরা কেমন নিবিড়ভাবে একে অপরের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে, একে অপরের প্রাণ বাঁচায়, সংকেত দেয়। র্যাচেল কারসন, বিভূতিভূষণের থেকে বয়সে অনেকটাই ছোট। র্যাচেল যখন তাঁর ‘সাইলেন্ট স্প্রিং’ বইয়ের মাধ্যমে কৃষিকাজে রাসায়নিক দূষণের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, তখনও সে বিষয়কে কেউ সেভাবে আমল দেয়নি। জাপানি কৃষিবিদ ফুকুয়োকা, কারসনের মন্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় ‘কর্ষণহীন’ চাষাবাদের কথা বললেন। কিন্তু পুঁজির পৃথিবীতে, বিপুল সংখ্যক জনগণের জীবনধারণের চাহিদার অনুপাতে এই পদ্ধতি কতটা কার্যকরী, কতটাই বা জৈব-চাষ—সে প্রশ্নের সদুত্তর বিগত কয়েক দশকে মেলেনি। বর্তমানেও, জৈব-চাষে উৎপন্ন পণ্যে স্বাস্থ্যসচেতন, ক্রয়-সামর্থ্যে এগিয়ে থাকা নাগরিকের অধিকার বেশি আর সামর্থ্যহীনের জন্য রয়েছে—‘সবুজ বিপ্লব’।
সত্যিই তো, গাছ না কেটে উপায়ই বা কী আমাদের? অর্থনীতির, জীবনযাপনের মানের উন্নয়ন থমকিয়ে যাবে না? ‘আরণ্যক’-এর লেখকের মুখে সে-কথাই তো আমরা শুনেছি, —“কি অবর্ণনীয় শোভা দেখিলাম এই বনভূমির সেই নিস্তব্ধ অন্ধকার রাত্রে! কিন্তু মন খারাপ হইয়া গেল যখন বেশ বুঝিলাম নাঢ়া-বইহারের এ বন আর বেশি দিন নয়। এত ভালবাসি ইহাকে অথচ আমার হাতেই ইহা বিনষ্ট হইল। দু-বৎসরের মধ্যেই সমগ্র মহালটি প্রজাবিলি হইয়া কুশ্রী টোলা ও নোংরা বস্তিতে ছাইয়া ফেলিল বলিয়া।”—শুধু আমরা মানুষেরা ভালো থাকব বলেই এই ধ্বংসের আয়োজন। মানব-সভ্যতার ইতিহাস কী তাহলে দূষণের ইতিহাস? ক্ষমতায় যে যখন আছি, নিয়ম বদলে, কানুনের দোহাই দিয়ে শুধু ‘সবুজ নিধন’ চালাচ্ছি নির্বিচারে। আর তার বদলে কী পাচ্ছি! ‘আরণ্যক’-এর লেখক লিখছেন—“কতকগুলি খোলার চালের বিশ্রী ঘর, গোয়াল, মকাই জনারের ক্ষেত, শোনের গাদা, দড়ির চারপাই, হনুমানজীর ধ্বজা, ফনিমনসার গাছ, যথেষ্ট দোক্তা, যথেষ্ট খৈনী, যথেষ্ট কলেরা ও বসন্তের মড়ক। হে অরণ্য, হে সুপ্রাচীন, আমায় ক্ষমা করিও।”—তিনি ক্ষমা চেয়ে গেছেন অরণ্যদেবতার কাছেই। আমরা তো হুকুমের চাকর, আমাদের সাধ্য কী একে বাঁচানোর। মনের ভেতর ক্রমশ ক্ষতবিক্ষত হওয়া ছাড়া আমাদের গতি নেই। অথচ স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়ার জন্য পাঠ্য-বিষয় হিসাবে রয়েছে—ইকোলজি। জীববিদ্যার শাখা হিসাবে সে-ও তো দেখতে দেখতে দেড়শো বছর পেরোলো।
কেওনঝড়-সিংভূমের গহিন জঙ্গলে যন্ত্রপাতি মালমশলার হিসাবরক্ষকের চাকরি নিয়ে গিয়েছিলেন শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ, পরে হয়ে উঠেছিলেন—‘অল পার্পাস ম্যান’। বিজু পট্টনায়কের আমলে, ওড়িশা মাইনিং কর্পোরেশনের চেয়ারম্যানের মতো উচ্চপদ থেকে অবসর নেন। শুরুতে ইজারা নেওয়া পাহাড়গুলো ছিল সে-ই এলাকার ম্যাঙ্গানিজ লোহা চুনাপাথরের আকর। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে ভারতীয় শিল্পের অগ্রগতির দিকে নজর দেওয়া হয়েছিল। সে-ই সময় কত পাহাড়-জঙ্গল-প্রাণীকুল যে ধ্বংস হয়েছিল তার ইয়ত্তা নেই। কিন্ত উন্নয়ন ও অগ্রগতির সঙ্গে তাল রাখতে এসব অপরিহার্য। লেখক বার্ড কোম্পানির উচ্চপদের দ্বায়িত্বে ছিলেন। কিন্ত তাঁর মতো মনের মানুষ আজ বিরল। তাঁর এই কর্মময়-আত্মজীবনীমূলক বইতে (‘জঙ্গলে জঙ্গলে’) এক জায়গায় তাঁর আক্ষেপ ছিল এরকম—“নিজের প্রতি নজর পড়লে বুঝতে পারি আমার সহৃদয়তার মূলে আছে পৃষ্ঠপোষকতার অহঙ্কার ছাড়া আর কিছু নয়। আমি তো এই বড়ো ক্যাম্পে এলে ভিআইপি শ্রেণীভুক্ত অতিমানুষ হয়ে যাই। এখানকার গাছপালার প্রতি আমার মমতা নেই। এই বাংলোর সামনেকার গাছপালা নির্মমভাবে কাটিয়ে ধাপে ধাপে নাকা পর্যন্ত কটি তৃণখচিত লন ও ফুলের কেয়ারি বানানো হয়েছে আমারি নির্দেশে।”—এই ক’টি লাইনের মধ্যে ‘ভিআইপি শ্রেণীভুক্ত অতিমানুষ’ কথাটি লক্ষণীয়। এই মানুষটি এক সময়ে জনমানবহীন উলিবুরুর গভীর অরণ্যে কাজের সূত্রে গিয়ে জড়িয়ে পড়েছিলেন জঙ্গলের মায়াবী রহস্যময়তায়, পরবর্তীকালে সে-ই মানুষ যখন অনেক উচ্চপদস্থ তখন বোধ আর বুদ্ধির লড়াই লেগেছে মনে, এবং তিনি তাঁর কর্তব্যে বাধ্য। ফলে যা সত্যি তা হলো, ‘কেউ কথা রাখেনি, কেউ কথা রাখে না’। সাহেবরা আমাদের দেশে জঙ্গল বাঁচানোর আইন বানায় প্রথম। কিন্তু ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমলে একশো বছর ধরে সাহেবরাই ভারতীয় জঙ্গল তছনছ করেছে। শাল, চন্দন, মেহগনি, আবলুশ কাঠ জাহাজ জাহাজ রপ্তানি হয়ে বিদেশে চলে গেছে। ব্রিটিশ কলোনির দেশগুলোয় আমাদের দেশের কাঠ নিয়ে গিয়ে পাতা হয়েছে রেল লাইন। ১৯৩৯ থেকে ১৯৪৫-এর মধ্যে চরম ক্ষতি হয়ে গেছে ভারতের বনসম্পদের। তবে সব সাহেব আর জিম করবেট তো এক নন। ছয় বছর ধরে জিম করবেট পায়ে হেঁটে দেখে বানিয়েছিলেন—‘হেইলি ন্যাশনাল পার্ক’। আর সে-ই পার্কই দ্বিতীয় বিশ্বযদ্ধের সময় কেটে মাঠে পরিণত করে ব্রিটিশরা। এই হলো প্রহসন!
জঙ্গলে ফিরে যাওয়ার পথ আমরাই বন্ধ করেছি। ভারতবর্ষের যে দুটি প্রধান বায়োস্ফিয়ার হটস্পট আছে, তা হলো হিমালয় আর পশ্চিমঘাট। কুর্গের মাইলের পর মাইল কফির বাগানের আকর্ষণ ভ্রমণপিয়াসীদের চিরকালের। কিন্ত এই সবুজ কি আমাদের আদি সবুজ? ভারতবর্ষে ‘প্লান্টেশন’ শুরু হওয়ার পর থেকেই ক্ষয়ক্ষতির মুখে পড়েছে পশ্চিমঘাটের বাস্তুতন্ত্র। ঠিক একইভাবে দার্জিলিং-এর হ্যাপি ভ্যালি বেড়াতে গিয়ে আমরা যা কিছু দেখে আপ্লুত হই, বিভিন্ন ভঙ্গিমায় ছবি তুলে আনি, তা-ও কিন্ত আমাদের আদি সবুজ (স্বাভাবিক উদ্ভিদ) নয়। ওই চা বাগান, ওই ছায়া দেওয়া গাছ সবই বিদেশ থেকে এনে বসানো হয়েছিল। তাহলে, আসলে কী ছিল সেখানে? স্বাভাবিক উদ্ভিদ বলতে যা বোঝায় তা হলো—যা একান্তভাবেই স্থানীয় আবহাওয়া-জল-মাটি-খনিজ ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। আমাদের দেশে দক্ষিণ ভারতে ও দার্জিলিং-এর অন্তর্গত পূর্ব-হিমালয় অঞ্চলে যথাক্রমে কফি ও চা প্লান্টেশনের কারণে অরণ্য ধ্বংসের সূচনা হয়। এছাড়াও ছিল, কাগজ ও আসবাবপত্রের প্রয়োজন। তার ফলে প্রাকৃতিক শাল গাছেরা উজাড় হয়ে গিয়ে এসেছে বিদেশী সেগুন, ইউক্যালিপটাস, ওয়াটেল। পশ্চিমঘাটের ১৬০০ মিটার উচ্চতায় যে প্রাকৃতিক শোলা বন ছিল সে সবই নির্মূল হয়েছে কফি বাগান ও আসবাবের কাঠের জোগান দিতে। আর সে-ই ক্ষতির কারণে বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য নড়বড়ে হয়ে যাওয়ায় যখন প্রশাসনের টনক নড়েছে ততদিনে কেটে গেছে বহু বছর। হারিয়ে যাওয়া শাল, চন্দন, শিরিষ, তেজপাতা, তেঁতোকুঙ্গা, হরেকরকম বাঁশ, ছাতিম, নাগকেশর আর শোলা বন-কে ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ শুরু হয়েছে এত বছর পর। কোনও কোনও মানুষের খবর আন্তর্জালে উঠে আসছে, যাঁরা একক চেষ্টায় শোলা বন তৈরি করেছেন। কিন্ত ক্ষতিপূরণ কতদূর সম্ভব?
গাছ কেটে যে গাছ লাগানো হয়নি তাও তো নয়। শোলা বন কেটে ফেলা অঞ্চল সবুজ করার জন্যে সেগুন আর সিলভার ওক আনা হয়, যা তাড়াতাড়ি বাড়বে। ‘গাছ লাগাও প্রাণ বাঁচাও’ কার্যক্রম চটপট সফলও হয়েছিল এভাবে। কিন্ত বাস্তুতন্ত্রের ক্ষতিপূরণ হয়নি। ক্রমশ ধরা পড়তে লাগল পশুপাখির হারিয়ে যাওয়া। কারণ জঙ্গল তো শুধু গাছেদের নয়, একটা বড় প্রাণী বা ক্ষুদ্র কীটের উপস্থিতির ওপরে বিশাল বাস্তুতন্ত্র ও খাদ্যশৃঙ্খল দাঁড়িয়ে থাকে। বড় বড় গাছের নীচে যেসব ঘাস-গুল্ম জন্মায় তারা একে অন্যের সঙ্গে নিবিড়ভাবে পারস্পরিক নিবিড় বন্ধনে বাঁধা থাকে। পশুরা যেসব ঘাস-পারা-কন্দমূল খায় তার বদলে জোগান দেয় সার আর জল। শোলা বন উজাড় করার পর যে সিলভার ওক আর সেগুন এসেছিল, তার সঙ্গে আন্ডারগ্রোথ হিসেবে আনা হয় ল্যান্টানা আর পার্থেনিয়াম, যা খুব তাড়াতাড়ি ঝোপ বানিয়ে ফেলে। কিন্তু এরা আসায় আমাদের দিশি ঝোপগুলো নষ্ট হয়ে যায়, ফলে পশুপাখির খাবারের অভাব হয়ে পড়ে। আমরা বাহারি বুনো ঝোপ দেখে, তার ফুল দেখে খুশি হলাম—কিন্ত আমাদের অজানা রয়ে গেল, বাস্তুতন্ত্রের সমস্যার দিকটা। ১৯৪০ থেকে এইসব সমস্যার সূত্রপাত। ১৮৮২ সালে সিলভার ওয়াটেল প্লান্টেশনের ফলে বন সবুজ হলো, কিন্তু ১৯৭০ সালে পশুপাখির সংখ্যা সংকটজনক ভাবে কমে যাচ্ছে ধরা পড়ার পর টনক নড়ল সরকারের। কতকগুলো গাছের নাম বলি: আদিন, ধ্ব, বিষতেন্দু, অঞ্জন, গজারি, ফাঁপা বাঁশ, ভরায় বাঁশ—এসব গাছপালা কিন্তু আমাদের দেশের আসল গাছ (স্বাভাবিক উদ্ভিদ)। কিন্ত আমরা ক’জন তাদের নাম জানি! তাই সরকারি (এমনকি বেসরকারি) ‘গাছ লাগাও প্রাণ বাঁচাও’ অনুষ্ঠানকে প্রহসন ছাড়া আর কীই-বা বলা যায়! গাছ লাগালেই হলো? কোথায় কী লাগাবো, কেন লাগাবো—তার আগামুড়ো না ভেবেই গাছ লাগিয়ে ফেললাম! আর পরিবেশের ওপর তার প্রভাবের ভালোমন্দ বুঝতে লেগে গেল শয়ে শয়ে বছর— কী লাভ?
চিপকোর বহু আগে, রাজস্থানের ‘বিষনোই’ সম্প্রদায়ের গাছ বাঁচানোর কাহিনি শোনা গেছে। আড়াই হাজার বছর আগে বুদ্ধদেব বলে গিয়েছিলেন, প্রতিটি মানুষ যেন পাঁচ বছরে অন্তত একটি বৃক্ষ রোপণ করে। যুগ যুগ ধরে যাঁরা বলার, যেভাবে বলার, বলেই এসেছেন—কেউ শোনে কি?
ছবি সৌজন্য: www.indianexpress.com www.timesofindia.com www.theculturetrip.com