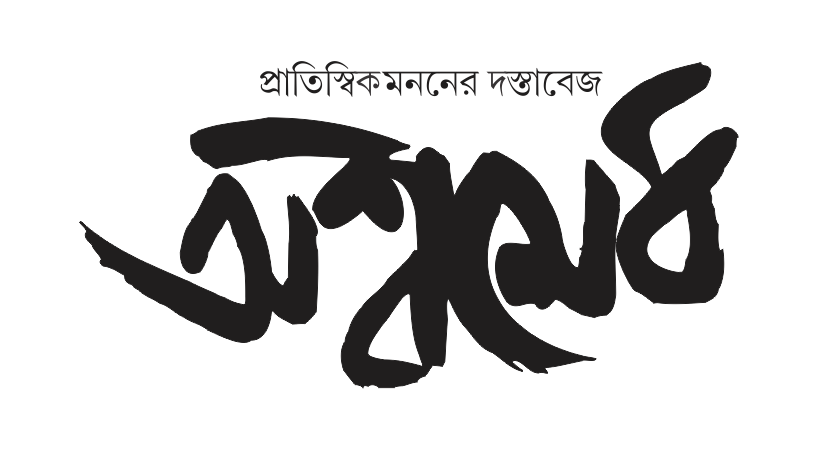‘মাগো আমি তোমার আমার প্রতি করুণার কথা প্রকাশিব!’
নিষিদ্ধের প্রতি কী অসহ্য টান আমার, আজন্ম! আমি ঘরের কোণের চিরকালীন ডার্টি ফেলো। কেননা, আমার মনে অবয়সোচিত প্রশ্নের ক্লেদ… অন্ধকার। যৌনাঙ্গ যে আদৌ ‘যৌনাঙ্গ’, তা আমি গুহামানুষের একাকী অন্বয়ে ধীরে ধীরে বুঝেছি একদিন। তা যে কত স্বভাব-সুন্দর আত্মকামনা, নিন্দুকে যাকে মাস্টারবেশন বলে রটিয়েছে পাড়ায়, তা কথ্য ভাষায় জেনে উঠতে কত যে জল খসে গড়িয়ে বয়ে গেছে… গঙ্গায়, তার কোনও লেখাজোখা নেই।
জামসেদপুরে জন্মেছিলাম। কিন্তু, কলকাতা সে-ই জন্মরহস্য জানার দুর্বার আগ্রহ দিয়েছিল আমায়। উত্তর যে আমার শরীরেই লুকানো, লালন করছি, সে-কথা তখনও কী জানি? শরীরের সঙ্গে আমার নিঃশব্দ কমিউনিকেশন প্রথম বুঝলাম, সেদিন, যেদিন হঠাৎ টের পেলাম আমার যৌনাঙ্গের উপরকার পরিচ্ছন্ন ত্রিকোণ, তেল মাখার সময়ে, অযুত বন্য আড়ষ্ট চুলের জঙ্গলের আড়ালে অদৃশ্য: আমি যেন আর ঠিক ‘আমি’ নেই আর… মারা গেছি বা যাব… কী এক ভয়াবহ বদল, রোগ, দেহান্তর যেন ঘটেছে আমার… আমার রূপ যেন নিজের অদৃশ্য হাতে নিজেকেই নির্মম রূপান্তর করে। ওই কর্কশ চুল আমার নয়… আমার বাকি দেহটা যেন উচ্ছেদ করে এনে জুড়ে দিয়েছে কেউ: সে তখন পৌগণ্ডেয় সীমা অতিক্রমিয়াছে… বহুবছর পর ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে কমলকুমারের ‘খেলার প্রতিভা’ পড়ান লেখক-আঁকিয়ে-চিন্তক বন্ধু কৌশিক সরকার; যেখানে মুহূর্তের ফেরে আমি কমলবাবুর বাক্যের ভেতর অন্তর্হিত বালক মাত্র… যে আপন পৌগণ্ডেয় সীমা পার ক’রে সে-ই কোমল দাগহীন শিশু-ত্রিকোণটির ইনোসেন্স বড় মিস করে: সে যেন আরও উদ্ধারহীনভাবে অসহায় ততদিনে: না সে জেনেছে জন্মরহস্য… না আছে তার আগের মতো ‘এটা কী? ওটা কী?’ বলার বেলাগাম ছুট… শুধু একরাশ সংকোচের ভেতর সে বাঁচে, কেননা চারপাশের সকলে সবকিছু জানে… শুধু, সে জানে না… কখন জানলো এরা… সে কী ঘুমিয়ে পড়েছিল তখন… ইশ্! আজও সে নির্বোধের মতো প্রশ্ন করে… আজও সে ম্যাচিওর হতে পারলো না!
দেরিদায় একটা ইশারা আছে, দেশের সীমা পার ক’রলে মৃত্যুর ধারণা বদলে যায়। সে দেশ বোধহয় শুধুমাত্র বাইরের নয়, ভেতরেরও বটে। আমি যৌবনের সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক সীমা অতিক্রম ক’রে এখন বুঝতে পারি, কথাটার জোর কতখানি; ফলত জীবনের ধারণাও বদলে গেছে, চারপাশে দিনে দিনে আগের চেয়ে আরও কত মৃত্যুমুখর হয়েছে জীবন… আরও কতখানি চুপিসারে সাড়হীন হয়ে পড়েছি আমরা… অবশ্যই মৃত্যু প্রসঙ্গে। দু-দুটো বিশ্বযুদ্ধ পেরিয়ে একটা খুব নিখুঁত গ্রাফিক উত্তেজক বর্ণনা ছাড়া, যাতে শরীরের আরামের ন্যারেটিভ বা বোধটুকু সাময়িক ভায়োলেট হয় মাত্র; আমরা কিছুতেই রিলেটিবিলিটির ভেতর ছুঁতে পারি না, মৃত্যুকে। আমাদের অবচেতনা তা-ই অপৌগণ্ডেয় প্রান্তে থাকা শিশুটির মতো আপন অন্ধকারে আজও প্রশ্ন করে চলেছে: ‘মা, মরে গেলে কেমন লাগে?’ আর তার উত্তরের সন্ধানে নিজের আত্মকামনার মুক্তি-যুদ্ধে কেবলই বীর্য হারিয়ে যেতে থাকে… এক অবলিভিয়ন থেকে আরেক অবলিভিয়নে।
প্রশ্ন জাগে আবার: আমার হস্তমৈথুন-হেতু এই যে আত্মবিলি-ব্যবস্থা… এটা কী সুপরিকল্পিত জেনোসাইডের এক প্রাক্-ধারণা নয়? বিশেষত, পৃথিবীময় জীবনের ধারণা যখন এতখানি টালমাটাল; এই আছি এই নেই… অথচ কী যায়-আসে তাতে? তখন আমি কী আগামী প্রজন্মকে আগাম অতিবাহিত ক’রে মৃত্যুর ধারণাকেই কিছুটা বদলে দিচ্ছি না? চানঘরে একেকবারের স্খলনে কতজন মানুষের আগাম জীবনরোধ হয়, কতগুলো অবোধ প্রশ্নের গণহত্যা হয়, কতগুলো নতুন জন্ম আর মৃত্যুর কল্পদৃশ্যের সোকল্ড পারভারশনের মুখ দেখতে হয় না এই মহাপৃথিবীকে? একই পথে ঠিক কতগুলো আগামী মহাযুদ্ধ, বন হরণ, দুর্ভিক্ষ আর দেশ দখল ঠেকানো যায়? তবুও চলতে হবেই… তা সে জীবনই হোক বা মৃত্যু… কী করব… কোথায় যাব… যাব কতদূর… এই প্রশ্নগুলোও সঙ্গে সঙ্গে চলতে থাকবে। আমি তো আমার এহেন স্যাকরিফাইসের জের টানার জন্য বরাবর রয়ে গেছি… আমার মুক্তি নেই। এই কারণেই তো গল্পের চির-সূত্রপাত আজও ঘটে পৃথিবীতে। আর প্রতিবার বীর্যপাত হলে দেখি, বীর্যের রং ঠাকুরঘরের শিশিতে রাখা গঙ্গাজলের মতো মেঘাচ্ছন্ন।
আমার প্রশ্নের উত্তরের আশায় এখন গঙ্গার দিকে তাকাই। সে-ই জন্মরহস্যই যেন ঠাওর হয় আজ এই মৃত্যু-উপত্যকায়। আমার জন্মের কথা বলছে গঙ্গা-বীর্যের স্রোত। ভাগীরথী ‘আমি’ কোথা হইতে আসিয়াছি? আজও খুঁড়ে চলেছি এই নার্সিসীয় জিজ্ঞাসা… আমার অস্তিত্ব… অস্তিত্বের অন্ধকার… আর এভাবেই ক্রমশ বেড়ে চলেছে কৃষ্ণবিবর। আমি সে-ই অন্ধকার নিয়ে গঙ্গার দিকে তাকিয়ে দেখি: সেখানে বয়ে যাওয়া বীর্য, তার জল… আর রয়ে যাওয়া অস্তিত্ব, যতদূর খনন করি শুধু মাটি আর মাটি।
‘…এইরূপ এ কাঙালের বিশ্বাস’
আমি তাকে চিনতাম। তার সঙ্গে প্রায়ই দেখা হতো মধ্য-কলকাতার কোনও আধা-খ্রিস্টান পাড়ার চা-কচুরির দোকানে, অথবা বইপাড়া লাগোয়া প্রায় দেড়শো বছরের পুরোনো কোনও মেস বাড়িতে, না-হলে বজবজের কিছুটা আগে মোড় ঘুরলেই চড়িয়ালের খালের মোহনায়। সে এইসব জায়গার হদিশ পেয়েছিল তার পালক-পিতার কাছ থেকে, লেগাসি। সে আসলে বাবা বলেই জানতো পনেরো-ষোল বছর পর্যন্ত, কিন্তু তারপর একদিন জারজ-সন্তান জাতীয় এক অদ্ভুত আনভেরিফায়াব্ল উন্মোচনের জেরে তিনি নিজেকে আলাদা করে নেন। সে-ই থেকে সে তাঁকে মনে মনে পালক-পিতা বলেই মানে। তার জারজত্বের বিশুদ্ধতা যাচাই করার সামর্থ্য বা ইচ্ছা কোনওটাই তার ছিল না। তার নিত্যকার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার লড়াইয়ে সে-ই প্রশ্নটা খুব একটা জোরালো ছায়াও কিছু ফেলেছিল বলে তো মনে হয় না। সে যাক, পালক-পিতার দেওয়া সে-ই কয়েকটি সময়-কাটানোর জায়গার হদিশ ছাড়া আর কিছুই তার হাতে এলো না; না টাকাকড়ি, না একটা চাকরির যোগাযোগ, না নিদেনপক্ষে মাথা-গোঁজার মতো একটা ঠাঁই। সে যখন বাড়ি ছাড়ে, বা তাকে বে-রোজগেরে ব’লে যখন তাড়িয়ে দেওয়া হয় বাড়ি থেকে; তখন তার কাছে তা তেমন একটা উদ্বেগের কিছু ব’লে মনে হয়নি, কোনও আক্ষেপও ছিল না। কারণ আনুষ্ঠানিকভাবে তাড়িয়ে দেওয়ার অনেক আগেই সে নিজেকে রাস্তার মানুষ হিসাবেই খুঁজে পেয়েছিল। গ্রাস এবং আচ্ছাদন নিয়ে তার কোনওদিন কোনও অতিকায় স্বপ্ন ছিল না, শুধু দৈব বিশ্বাস ছিল—কিছু না কিছু নিশ্চয়ই জুটবে, আর তাতেই কাজ চালিয়ে নেওয়া যাবে। ঘরের দরজার চৌকাঠ যখন শেষবারের মতো পার হয়ে এসেছে সে, তখন ফুটপাথ থেকে সিংহদ্বার সবেতেই সে এক্সপোজ্ড—তার কোনও অধিকার নেই একটার চেয়ে আরেকটাকে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করার… যুগ যুগ ধ’রে চলে আসা এই সামাজিক-মানসিক হিপোক্রেসির অবসান হতে দেখেছি তার ভেতর।
আগে অস্বাভাবিক মনে হতো, কিন্তু যত দিন গেছে আমাদের বন্ধুত্বের, তত বুঝেছি, আক্ষেপ বা উদ্বেগ ছিল না বলেই হয়তো সে চূড়ান্ত বিপর্যয়ের দিনেও আকাশের দিকে তাকাতে ভোলেনি, জলের দিকে তাকাতে ভোলেনি, মাটির দিকে তাকাতে ভোলেনি; এমনকি নিজের কীটদষ্ট ভগ্ন শরীরের দিকেও তাকাতে ভোলেনি। নিজের শারীরিক-মানসিক আওতার ভেতর সকলকে ফিল করার, ধারণ করার, সর্বময় এক নার্সিসিজ্ম তাকে আচ্ছন্ন করেছিল। একদিন বলেছিল, তুমি যখন তন্ময় হয়ে গিটার বাজাও তখন তোমার হাত আর আঙুলগুলো আমার ভেতর নড়তে-চড়তে থাকে, কেন জানি আমার ভেতরেও একটা গিটারের অস্তিত্ব টের পাই, আমি যাকে বাজাতে পারি না; অথচ তোমার মতো কেউ নির্ঘাত একদিন এসে তারগুলো বাজিয়ে দিয়ে যাবে। সে-ই অপেক্ষায় কোনও ক্লান্তি নেই আমার।
ভেবে অবাক হয়েছি পরে, যে এও কী এক প্রকাণ্ড ‘ধারণ’-এর প্রোজেক্ট নয়? এত কিছু ধারণ করতে কী ব্যথা লাগেনি কখনও তার? অথচ কোনওদিন ঘুণাক্ষরেও তাকে নিজের ব্যথার কথা বলতে শুনিনি। বরং, স্মিতহাস্যে নীরবে এক-দুটো শিষ্ট বা বিশিষ্ট তামাকের ধোঁয়ার ঘেরাটোপের ভেতর, এক-দুটো বাউলানা সুর ভাঁজতে ভাঁজতে, চলমান লোকালের দরজায় দাঁড়িয়ে, দক্ষিণ-শহরতলি থেকে শিয়ালদার দিকের ফ্লাডলাইটে ধোয়া আন্ডারপাসের শেষ বিচূর্ণীকৃত থামটার চ’লে যাওয়া দেখতে দেখতে, আমরা রোজকার মতো আবার একটা আড়ষ্ট কাঠখোদাইয়ের রুক্ষ দুপুর পেরিয়ে আরও একটা জলরঙে-তরল চুইয়ে পড়া বিকেল-সন্ধ্যের ভেতর ঢুকে পড়তাম। সে সময় যে চাকরি করতে করতে তার দিনরাতগুলো কেটে গেছে, তাকে ‘আকাশবৃত্তি’ বললে কিছু ভুল বলা হয় না। কিন্তু সেটা কোনও ধীরমন্ত ধূসর সময় নয়, বরং একবিংশ শতাব্দীতে তৃতীয়-পৃথিবীর একটা রুথলেস ইঁদুর-দৌড়ের শহরে, সে আপন জীবন পণ ক’রে সে-ই জিনিস প্র্যাকটিস করেছে!
আমার ভয় হতো, নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে যাচ্ছে সে; অনেক তর্ক ঝগড়া ক’রে আমার সন্দেহ নিয়ে বিব্রত করেছি তাকে, কিন্তু সামান্যতম একটা স্মিতহাস্যময় উত্তর ছাড়া আর কিছুই পাইনি কোনওদিন—‘হলে হবে… তাছাড়া আমার মতো আরও কি বন্ধু হবে না তোর? যদি-র ভয় নদী-তে।’ যে-কোনো সময় ভেসে যেতে পারে, জলে প’ড়ে যেতে পারে, জীবনের এহেন অনিশ্চয়তায় জলময় সে-ই অদৃশ্য নদীটির তটরেখা ধ’রে এগিয়ে গিয়েছে আমাদের টালমাটাল বন্ধুত্ব। আমাদের রোজকার এই চেনাশোনার ভেতর শুধু এক নিরবচ্ছিন্ন নির্বিকার ভ্রাম্যমাণতাই ছিল, যা তথাকথিত ভালোমন্দের দিকে ঠেক খেতে দেয়নি আমাদের। সবাই চারপাশ থেকে ঠারেঠোরে বুঝিয়ে দিত—সময় বয়ে চলে যাচ্ছে হাতের বাইরে… আর ফিরে আসবে না এই অপচিত জীবন। সে হেসে উঠত, কলঘরে, আচমকা প্রতিধ্বনি ক’রে। ‘…কে চায় ফিরিয়ে আনতে? সময় ছাড়া আর কীবা নষ্ট করার আছে এই শহরটাতে… এই দেশে… পৃথিবীতে… মানচিত্রে?’ সবাই তো যে যার উদ্দেশ্য, প্রতিভা সম্বল ক’রে আসলে নষ্টই করছে সময়! পুরো আস্ত একটা পৃথিবীর মানচিত্র তার সাক্ষ্য বয়ে বেড়াচ্ছে। সৃষ্টি-বৈভব থেকে শুরু করে ধ্বংস-তাণ্ডব পর্যন্ত, কিছুই তো কোনও স্থায়িত্ব ক্লেইম করতে পারেনি, পারবেও না। তাহলে এত সিরিয়সনেসের ভান কেন? প্রকৃতির চেয়ে বিষণ্ণ, একা আর কেউ আছে নাকি? সে-ই তো একা, যে থেকে যায়…শেষের পরেও যে শেষ এগিয়ে আসছে, তাকে বাঁচার জন্য। আর বাকি সবাই তো কোনো-না-কোনো সংস্রবের স্বপ্নে বিভোর… ‘অন্ধকারে হেমন্তের অবিরল পাতার মতো’।
‘…তাহলে?’ সপ্রশ্ন চোখে আমার দিকে তাকাতো সে, আমার চেনা সে-ই কাঙাল বন্ধুটি। মনের ভাবখানা এমন… যে, কী প্রমাণ হবে একটা বাঁধা মাইনের তাঁবেদারি করলে, বা দুটো আকাশ-ছোঁয়ানো বাড়ি বানিয়ে, জীবনে সাফল্যের একটা মিথ্যে মিথ্যে হাতযশ চাড়িয়ে তুলে? প্রতিদিন সকালের একচামচ ঝুঠা-সফলতার প্লাসিবো-এফেক্ট সারাদিন আচ্ছন্ন রাখে। নিজের আদত অস্তিত্বের কথা ভুলে থাকার স্লো-পয়জন ড্রাগ… আরও একটা দিন শুধু ক্ষণিকের আনন্দ বই তো আর কিছু না? কীসের আনন্দ… না নিজেকে প্রমাণ করার উত্তেজক প্রবণতার! লেখাপড়া থেকে কর্মজীবন… কাউন্সেলিং থেকে আড্ডা, সবটারই মূল সুর হল… ‘আমি জানি কিন্তু তুমি জানো না… আমরা পারি কিন্তু তোমরা পারো না… সমাজই কিন্তু বাঁচাবে তোমায়… নইলে তুমি একা, ইনসিকিওর, দুর্বল, ভবিষ্যৎহীন, নির্বিকল্প খতম।’ এটুকুই তো আমার অধিকার… এরই জন্যে তো জীবন দেবো, আর মনে মনে নিজেকে একটা ঘোরের ভেতর প্রতিপালন করব: ‘আমারও একদিন হবে’ অথবা ‘আমার হলো না তো কী, আমার সন্তানের হবে…’ বা ‘আমার সন্তানের হয়নি তো কী হলো… তোমার নিশ্চয়ই হবে…’ তোমাদের হলো না তো হলো না… পরের প্রজন্মটা যদি পারে… সেখানেও যখন ফাঁকি, তাহলে মানুষের কিচ্ছুটি হবার নয়… মানুষ উচ্ছন্নে যাক… আমাকে বৈতরণী পার করাও।
এরকমই কিছু একটা মনে পড়ায় একদিন সে ঘুমের মধ্যে অট্টহাস্য করেছিল। জানতে চাইলে বলেছিল: সোসাইটি কোনওদিন মানবে না যে, তা আসলে খুব বড় একটা ফেলিওর, অথচ সব সময়ে ইন্ডিভিজুয়ালকে ফেলিওর হিসাবে প্রতিপন্ন করতে তৎপর। এতেই তার কী যে স্যাডিস্ট আনন্দ! তাহলে, সে-আনন্দ বাকি সব ফেলিওর, অবাধ্য মানুষেরা যদি অন্যভাবে, আপন সহজাত নিষ্ক্রিয়তার ভেতর পেতে চায়, তাতে সোসাইটির এত অস্বস্তির আছেটা কী? খানিকক্ষণ চুপ করে শেষে উত্তরটা সে নিজেই দিত…কারণ, সোসাইটি হিস্টেরিক… নিজের মেকবিলিফের বাইরে যেতে তার মন কাঁদে… হাতে-পায়ে আতঙ্ক দেখা দেয়…তাই আত্মতুষ্ট মানুষকে তার ম্যাসোচিস্ট বলে মনে হয়… সোসাইটির স্যাডিজ্মের চূড়ান্ত প্রকাশ হলো এইসব তথাকথিত ফেলিওরদের পৃথিবী-মানচিত্রের মার্জিনের দিকে ঠেলে দেওয়া। সোসাইটির যুক্তির স্রোত বড় প্রবল, একা অবাধ্য কাঙাল পারবে কেন? তাই সে-ই কাঙালকে বরাবর, সবচেয়ে প্রান্তিক অবস্থানে খুঁজে পাওয়া যায়। সে সেইখানে একলা-হাতে নিজের ছাউনিটুকু ফেলেছে, যেখানে সভ্যতার কোনও বাজার বসেনি এখনও, যেখানে কোনও ধর্মগুরু তার অন্ত্যেষ্টির জলের ঘটি হাতে দাঁড়িয়ে নেই, যেখানে কোনও সৌম্যকান্তি এনজিও ত্রাণ-প্রহসন মঞ্চস্থ করার জন্য মরিয়া নয়। আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, এত নির্জন একাকীত্বে কীভাবে বাঁচবে খ্যাপা? সে বলতো, অন্যের ত্রাণের দিকে তাকালে হবে না, আসলে মরে যাবার মতো ডিট্যাচমেন্ট ফিল করলে তবে মানুষ নিজেকে স্পষ্ট দেখতে পায়… বুঝতে পারে, সে কী নিয়ে জন্মেছে… কী করতে জন্মেছে। তখন বাঁচতে পারে। বাঁচতে পারা মানে তো একটা মিনিমাম পা রেখে চলার মতো পাকদণ্ডী মাত্র… নয় কী? তারপর চলা নিজেই নিজের চলার পথ তৈরি ক’রে নেয়।
সে বলতো, বিশ্বাসে ভর করে চলতে জানলে, সে পথের হদিশ সর্বত্র: সবচেয়ে সুদূরতম নৈকট্যে সে-পথ তো আমার ভেতরেই বড় একা নির্জন হয়ে শুয়ে আছে! আমাদের একে অন্যের সান্নিধ্যে দিনাতিপাতের যে ভ্রাম্যমাণতা ছিল, সেটা প্রায় পায়ে হেঁটে শহরের এ দরজা থেকে সে দরজায় ঘুরে বেড়ানোর স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে আছে। কেন দিনলিপির মতো করে লিখে রাখিনি সেইসব ঘুরে বেড়ানোর কথা—সেটা ভেবে আমার কতবার যে আক্ষেপ হয়েছে, তা আর কী বলবো! পরে মনে হতো, সেটা তো একটা নেশায় ঘোর লাগানো সময় ছিল, ভালোই হয়েছে লিখিনি। ঝাপসা চোখে নেশার ঘোরে কী লিখতে কী লিখে রাখতাম কে জানে! এখন, যত দিন যায় ততই দূরদৃষ্টি স্বচ্ছ হয়। আমাদের এই ভ্রাম্যমাণতার একটা বড় প্রাপ্তি ছিল, আমার চাকরি খোঁজার অজুহাতে আপিস পাড়ার ভিড় ঘুরে দেখা। অজস্র মানুষ, সে-ই একই লক্ষ্যে প্রতিদিন… শহরতলির পেটের ভেতর থেকে শহরে…
আমাদের স্বতঃপ্রণোদিত ঘুরে বেড়ানোর বিপরীতে অফিস বাড়িগুলোর দিকে বয়ে যাওয়া মানুষের স্রোত কী ভীষণ অজ্ঞেয় অনুকরণ… এমনটা মনে হতো তার। আমি বলেছিলাম, কীসের অনুকরণ? সে বললো, দশটায় জোয়ার আসে আর পাঁচটায় ‘হৃদয়ে আমার চড়া’… তাহলে কীসের অনুকরণ হচ্ছে ভেবে দেখো। অথচ, সে-ই অনুকরণের আড়ালে একটা খুব জেনুইন প্রাণশক্তির আনাগোনা আছে। প্রাণ কী জিনিস! কাউকে রেয়াত করে না। জন্ম অবধি তার মায়ার অধীন। এইসব আধো-আলোকিত মানুষেরা সারাজীবন তাকে প্রতিপালনের জন্য স্বার্থের সংকীর্ণতায় দেশের দশের চাকাটাকে ঘোরায়, কিন্তু নিজেরা, বোবা অলিন্দে মাথা নীচু করে হেঁটে যাওয়া ঘোরলাগা মানুষের মতো, বয়ে যায়। আমি সে-ই স্যাডিজ্মের অংশী নাকি ম্যাসোচিজ্মের? জিজ্ঞেস করলে বলি, ‘আমি কী জানি!’ সে বলে, কাল আপিস পাড়ায় হঠাৎ একটা উল্কাপিণ্ড আছড়ে পড়লে, এদের জন্যই টনটন করবে বুকের ভেতরটা। আমি বলি, সে কী! কাঙালেরও এইসব হেলদোল আছে নাকি? তুমি তো নির্লিপ্ত গুরু! তোমার আবার টনটন করবে কেন?
আমার কথার কোনও উত্তর না দিয়ে সে তাকিয়ে থাকে, সে-ই আদি অকৃত্রিম জনস্রোতের দিকে। আকাশে হালকা মেঘ করেছে, বিকেলের গুমোট বাতাসে থেকে থেকে ঠান্ডার মিশেল। জানিস তো, বলে সে, আমরা সবাই অন্যলোকের জীবন বাঁচতে চাই… নিজের জীবনের অধিকারে সবাই বঞ্চিত। নিজের জীবনের থেকে সাদামাটা, আনইন্টারেস্টিং আর কীবা আছে! নিজের প্রাণকে রেকগ্নিশন-হীনতার ভেতর বছরের পর বছর বাঁচিয়ে রেখেছি শুধু, স্বীকৃতি দিইনি। দিলে, আমরা সবাই নিরঙ্কুশ ভাবে বুঝতে পারতাম, যে, আমরা সবাই আসলে জারজ। আমাদের জন্ম-পিতা যদি সামাজিক স্যাডিজ্ম হয়, তো আমাদের পালক-পিতা ব্যক্তিগত ম্যাসোচিজ্ম। দুই স্রোতের মিশ্র-অভিব্যক্তি আমরা। এমনকি আমাদের হাতে-গড়া সমস্ত কিছুর গায়েও এই দ্বিচারী আইডেন্টিটির রং। আমাদের এক হাতে শক্তি তো অন্য হাতে অপার সংশয়। আমি জানতে চাই, মধ্যিখানে? সে বললে, ভয়… যে-কোনো একটা স্রোতের ভেতর পড়ে যাবার ভয়। কিন্তু কীসের ভালো কীসের মন্দ… এসবের কী কোনও ভ্যালু-জাজমেন্ট হয়? সে-ই স্রোতই আমাদের গঙ্গা…যেন ভক্তের আকুলতা নিয়ে গঙ্গাস্নানে এসে দেখি… গঙ্গা এক নয়, দুই, আমাদের ভেতরেই গঙ্গা দ্বিধাদীর্ণ হয়ে পড়ে আছে। যুগ যুগ ধরে এই রহস্যের কিনারা হয়নি, তাই মানুষ তার কাঙ্ক্ষিত গঙ্গা পায়নি আজও: শুধু ঠাওর করেছে মাত্র। আর তাতেই তার আনন্দ আর হতাশা, অথবা হতাশ হতে হতে একসময় মুখ ফিরিয়ে নেওয়া, ভুলে থাকার অভিমান।
এত বলার কওয়ার ভেতর সে যে কখন থামল, বুঝতে পারিনি। কিন্তু কাঙাল জানে, তার কোনওদিক থেকেই মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার অধিকার নেই… না মাটির থেকে… না জলের থেকে… না স্যাডিজ্মের সংঘাতে… না ম্যাসোচিজ্মের শ্বাসরুদ্ধ বেদনায়। তাই সে এক তৃতীয় ধারার অন্বেষণে আকাশে চোখ মেলে বসে আছে। বাইরের আকাশটাতে কতটা জানি না, তবে অন্তরের মেঘাচ্ছন্ন আকাশে নির্ঘাত, অপলক। কবে যে একটা পারাপারের ফেরি আসবে, আর সে যাবে সে-ই তৃতীয় গঙ্গায় গা ভাসাতে। তন-গঙ্গা, মন-গঙ্গার পর কী জানি কী নামে ডাকবে সে তাকে? আমাকে সে দেখাতো, বহু দূরে জলের রেখার ভেতর একটা চড়া জেগে আছে… যেখানে স্বেচ্ছা নির্বাসনে যাবার মন হয় তার… আমি কী দেখতে পাচ্ছি সেটা… আমি কী যেতে চাই সেখানে… আমার প্রকৃত ‘আমি’ সন্ধানে? কী বলব আমি: হ্যাঁ… না… না? হয়তো, আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসতো—জানি না… ঠিক বলতে পারবো না। ফেরিতে চ’ড়ে শেষবারের মতো সে বলেছিল: হয়তো এখন পারবি না… তবে একদিন না একদিন নিশ্চয়ই পারবি… তুই নয়তো অন্য কেউ পারবে… তোরই মতো আমার অন্য কোনও বন্ধু… অন্য কোনও প্রজন্মের মানুষ… আর সেদিন আমার ভেতর সে-ই গিটারটা হঠাৎ ঝমঝমিয়ে বেজে উঠবে… সে আমি যেখানেই থাকি না কেন… এ আমার মতো কাঙালের স্থির বিশ্বাস।
‘…এইরূপ আমার জাগা ঘর, যে, গঙ্গার জল পান করিলে আমার ভিতর শুদ্ধ হয়।’
কলকাতায় থাকতে থাকতে, হাঁপিয়ে উঠলে, একেকদিন বিনা নোটিসে কোনও দূর গ্রামে পালিয়ে যেতে ইচ্ছে করত। এমন কত যে গ্রামের ছবি আজও আমার চোখে ভাসে, তা বর্ণনায় কুলাবে না। দূরান্তের গ্রামে, সমতলে শুয়ে থাকা জনহীন বৈকালিক একটা রেল-স্টেশন। বিকেলটা গড়িয়ে যাচ্ছে রেললাইন ধ’রে, নীচু তারে শ্বাস নিতে নিতে, দিনের শেষতম মিথকথক রেলগাড়িটার মতো, আমাকে একলা ফেলে রেখে। হাত কয়েক দূরে একটি অতি পুরাতন জলের কল। ইংরেজ আমলে লাগানো এরকম কল এখনও খুঁজলে পাওয়া যাবে সম্ভবত কলকাতায়। কিন্তু এই অজ গ্রামে সেটা কোথা থেকে এলো, কে জানে! কাছে গিয়ে দেখি, একটা মরচে ধরা বিষণ্ণ সিংহের মুখ থেকে তিরতিরে গতিতে অবিরাম জল প’ড়ে যাচ্ছে। আমি জানি কেমন স্বাদ সে-ই জলের। ছোটবেলায়, এ-ধরনের কলের জলে লোহার স্বাদ পেলে, মনে প্রশ্ন জাগতো, পুরোনো কলের লোহা কি ধীরে ধীরে জলে গুলে যাচ্ছে? তাহলে একসময় তো কলের সিংহটাও জলে গুলে নিঃশেষ হয়ে যাবে! পুরোনো কলকাতার সে-ই একদা ঔপনিবেশিক, বিষণ্ণ সিংহটা তাহলে এই গ্রাম্য-প্রান্তর পর্যন্তও নিজের থাবা বসিয়েছিল কোনও একদিন। এই জলে-জমিতে ছড়িয়ে দিয়েছিল কিছু বেমানান স্বাদ, গন্ধ, কর্কশ স্পর্শ। নির্ঘাত কোনও ধ্বংসপ্রাপ্ত কারখানারও অবশেষ দেখা যাবে, গ্রামের অন্যপ্রান্তে এগিয়ে গেলে… অথবা কোনও একটা বর্জিত খাল বা দীঘির কালো বিষাক্ত জল… মৃত মাছ… খেত ভরা নষ্ট কালো ধানের গল্প… একটা বহতা স্রোতের থেমে যাওয়ার নস্ট্যালজিক বৃদ্ধ ক্রন্দনরত ইতিহাস। খানিকটা জল আঁজলা ভরে খেতেই টের পেলাম, যা ভেবেছিলাম তা নয়; জলের স্বাদ লোহাটে নয়, তবে মাটি মাটি। কীসের মাটি? লোকাল লোকেরা বলেছিল—গঙ্গার। তারই জল এই বহু প্রাচীন ব্রিটিশ ভারতের স্মৃতিধন্য, লোহার কলের সিংহের নির্গমন-মুখ মারফত এই জনমানবহীন স্টেশনের কিনার পর্যন্ত প্রবাহিত। কোনওদিন এই গঙ্গাজলে খ’য়ে খ’য়ে নিঃশেষ হয়ে যাবে কি এই মদগর্বী সিংহের মুখ? সে-দিন যে বহতা স্রোতের শরীরে মিশেছিল লোহার কটু স্বাদ, সে কী এখন ধীরে ধীরে সে-ই লোহাকেই মেনে নিয়ে নিজের বিষ-নিয়তিকে পালটা স্রোতে ঠেলে দিল আমাদের দিকে… নাকি যে জল আর সবকিছুর চেয়েও অপার ক্ষমাশীল… নিজের বিষকে সে নিজেরই শরীরে যুগ যুগ ধরে সইয়ে রাজী করিয়ে কলমা পড়িয়েছে কোনও গাঙ্গেয় পরম্পরায়: বিষের ভেতর থেকেও জলের ঘুরে ঘুরে কথা কওয়ার প্রজ্ঞা… ইটার্নাল রিটার্ন?
সে ঘটনার আজ প্রায় কুড়ি-বাইশ বছর পর, এই প্রশ্নের উত্তর চাক্ষুষ করি। মহামারীর দিনকাল এখন। কাতারে কাতারে অরক্ষিত-আতঙ্কিত মানুষ হেঁটে চলেছে ভারতের ছোট-বড় শহর, মহানগর থেকে দেশের নানা অজানা প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা গ্রামগুলোর দিকে। এই গতিটা শুধুই একটা মূক গতিমাত্র নয়; এর আড়ালে একটা বিরাট সত্য প্রবাহিত। এই লক্ষ লক্ষ শ্রমিকের একটা খুব বড় অংশ আসলে কলকারখানাগত শ্রমজীবীতায় কনভারটেড। কাফকার মেটামরফোসিসের এক ইন্ডাস্ট্রিয়াল উৎপাদিত সত্য। আসলে আমরা নাইভের মতো ভাবি, যে ওরা চলেছে সব ছেড়ে উন্নত জীবনের টানে… অথচ গ্রামের ছোট ছোট স্টেশনগুলোতে প্রথম ট্রেন ধরার সময়, অর্থাৎ প্রথমবার পরম্পরা থেকে বিচ্যুত হওয়ার সময় ওদের পেছনে ক্যাপিটালিজ্মের চোরা বিশাল হাত সি-অফ করতে এসে পিঠ ছুঁয়ে থাকে। সে-ই সুবিশাল অদৃশ্য হাত ওদের ছোট ছোট অজস্র হাতে প্রেতযোনি সচল করে। ফলে, কাল অবধি যে হাতে তারা গ্রাম-ভিটের কাছে জলে-জমিতে ভাইটালিটির প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেছে… শস্যকে সন্তান বলে জেনেছে… মীনকে চন্দ্রালোকের রাত্রে ঘুম পাড়িয়েছে… আজ সে-ই হাতেই তারা শিল্পাঞ্চলের বিষোদ্গার টেনে এনে ফেলছে অন্য কোনও জলে, অন্য কোনও জমিতে। জমি-জলের আবার এখান আর ওখান! মাঝারি থেকে ভারী শিল্পের দত্তক নেওয়া সেইসব জেলে আর কৃষক সন্তানের দল, খুব আইরনিকালি এখন এই মহামারী পরিস্থিতিতে, দেশের নানা প্রান্তে একটা অ্যান্টি-ইন্ডাস্ট্রিয়াল স্রোত তৈরি করছে। এটা ওদের ঘরে ফেরার স্রোত… অযান্ত্রিকতার ধারা। কী কোনও ইটার্নাল রিটার্ন… নাকি আমাদের আকছার জীবনের ভ্রম…কী নাম এর? কিন্তু এই স্রোত, এই ধারা শিল্পায়নোত্তর চেতনার থেকে প্রাক্-শিল্পায়ন চেতনার দিকে এক ঊর্ধ্বগতি, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। শুধু কী মানুষেরই গতি? না তা নয়। বিশেষত, সমগ্র প্রকৃতির দিকে তাকালে বোঝা যায়, শুধুমাত্র শিল্পায়ন স্তব্ধ ব’লে আকাশ, বায়ু, জল, মাটি ধীরে ধীরে শ্রমিকদের পায়ে পা মিলিয়ে ফিরে যাচ্ছে আবার তাদের পরিচ্ছন্ন চেহারায়… সে-ই তাদের সহন প্রজ্ঞায়… তাদের ইটার্নাল রিটার্ন। বিষ থিতিয়ে যাচ্ছে সর্বত্র আর ধীরে ধীরে পুনরুদ্ধার হচ্ছে অবলুপ্ত প্রকৃতি আর ‘প্রকৃতিসঞ্জাত মানুষ’-এর সে-ই অবলুপ্ত ধারণা। হয়তো সেখান থেকেই আবার মুখ তুলে চাইবে, প্রাকৃত জনগোষ্ঠীর ধারণা অথবা প্রাকৃতিক জীবনযাপনের অবদমিত কামনা। একদা শিল্পাঞ্চলের লৌহ-ফ্যালাস (লৌহ-শিশ্ন) যে সুচারু কামনায় আচমকা আহত বলাৎকারের মতো নেমে এসেছিল একদিন ধরিত্রীশয্যায়। হতে পারে এই পুনরুদ্ধার সাময়িক, হতে পারে দীর্ঘমেয়াদি। মানুষের মতিচ্ছন্নতার কোনও গ্যারান্টি আছে কী? কিন্তু জীবনের এতখানি ঝুঁকি, এই অজানা মারণ ভাইরাস, অসহ্য পথকষ্ট, অনাহার, দুর্ঘটনা, সহযাত্রীদের অপমৃত্যু… আরও কী কী অসম্ভাব্যতার নাম করবো… এই সাফারিং বোধহয় মহাভারতের মহাপ্রস্থানকে নতুন আলোয় (বা অন্ধকারে) মনে পড়ায় আমাদের।
সারা ভারত জুড়ে এই মহাভারতীয় প্রত্যাবর্তন, এই হোম কামিং, আসলে শিল্পায়নের সূত্রে উন্নয়নের ঐকিক নিয়মের দুনিয়া থেকে এই আজন্ম ব্যবহৃত মানুষগুলোর সবচেয়ে কাঙ্ক্ষিত মহাপ্রস্থান। কিন্তু কেন? কী সে-ই কারণ যার জের এই সর্বব্যাপী মৃত্যুযাপনের দিনেও এতদূর টেনে আনতে পারে, এত লক্ষ মানুষের ঢল? মাত্র একটা মহাজাগতিক শব্দে এর উত্তর দেওয়া যায়—ঘর। গাস্তঁ বাশেলারের কথায়, এ সে-ই ঘর যা স্মৃতির-মায়ার নিরালা কোণে না-জানি কত দীর্ঘ বছরের পর বছর একা পড়ে আছে… যাকে সে-ই মায়া আড়াল করে, আর সে-ও আড়াল করে সে-ই মায়াকে… পৈতৃক জন্মভিটের উষ্ণ ছোঁয়া—‘প্রোটেকটেড ইন্টিমেসি’। আমার মতো প্রবাসী মানুষমাত্রেই জানে, জন্মভিটে শেষ পর্যন্ত জন্মভিটেই… যেখানে মানুষ নিজের নাড়িকাটা রক্তের দাগ ফেলে রেখে এসেছে… আর সে-ই দাগের চরম কাছটিতেই নিজেকে সে ছোঁয়াতে চায়, ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চায়, আপন ঐকান্তিক মৃত্যুতে। প্রবাসে সে-ই টান, সে-ই আম্বিলিকাল নাভিক্ষত কোথায়; কোথায় সে-ই আঁতুড়ঘর? প্রবাস তো ছিন্নতার যাপন… এক ছিন্ন মানুষ আরও অনেক ছিন্ন মানুষের দুখোবন্ধু সেখানে।
তাই আঁতুড়ঘরে যদি শেষসজ্জা পাতা যায়, তো কোথাও যেন একটা পরিক্রমা সম্পূর্ণ হয়। তাই অদম্য বিশ্বাসে বুক বেঁধে, অদৃশ্য মায়ের অদৃশ্য গর্ভের দিকে মৃত্যু-অন্বেষী লক্ষ লক্ষ হ্যামলেটের এই স্রোত কী সত্যিই তার কাঙ্ক্ষিত ‘গঙ্গা’ পেয়ে যাবে শেষ পর্যন্ত? এর বিপরীতে এ কথাও ঠিক যে, এদের সবাইকে তো মৃত্যু নিজের হাতে হাত রাখতে দেবে না। মৃত্যুও তো বঞ্চনাবিলাসী। সে-ই মৃত্যু-প্রবঞ্চিত মানুষগুলোকে তাদের ঘর, তবে কোন অবগতির দিকে টানবে?
আচ্ছা, যদি এমন হয়, যে, তারা আর ফিরছে না শিল্পাঞ্চলে অথবা মহানগরের অন্ধকার বস্তিগুলোয়। এই মাঝারি থেকে ভারী শিল্পের বন্ধ চাকার বিপরীতে, প্রকৃতির নিঃশব্দ ডাকের দিকে সাড়া দিয়ে, আদ্যন্ত অনিশ্চিত সাফারিং-এর এই চৈতন্য-গঙ্গার ভেতর দিয়ে যে অন্তরশুদ্ধির ঘটনা ও বোধ; তা যদি সত্যিই স্থায়ী হয় জনমানসে; তাহলে পৃথিবীকে যারা ভালোবাসে… প্রকৃতির দুঃখে যারা আজও কাঁদে, তারা কি চাইবে… যে ওরা ফিরে আসুক… আবার মহানগরে… আবার এই সপ্রশংস উৎপাদনকামী রক্তপাতের ভেতর… শিল্প-কারখানার পঙ্কিলতায়? বরং তারা চাইবে পৃথিবীর সমস্ত প্রান্তে আবার গজিয়ে উঠুক লবটুলিয়া বইহারের জঙ্গল… ভানুমতি আর সত্যচরণ-এর দেখা হোক আবার হে শালিখঠাকুর… রাজা দোবরু পান্না সে-ই জঙ্গলাকীর্ণ অরণ্যের আদিম অধীশ্বর হয়ে বেঁচে থাকুক… প্রকৃতির ক্লান্ত-ঘর…আমাদের-ওদের মনে… ভেতর জাগা-ঘরের রূপ নিক। অভ্যেসের দাস সমস্ত ‘সু-সভ্য’ অথচ মানসিক পক্ষাঘাতগ্রস্ত মহানগরগুলো, এতে শুধুমাত্র তাদের শিল্পাঞ্চলগুলো বন্ধ করে দিক। ‘রক্তকরবী’ থেকে ‘সুবর্ণরেখা’ পর্যন্ত… আধুনিকতার উন্নয়নের নামে, প্রাকৃতজনের যে স্খলন-বঞ্চনা আর জাগা-ঘরের জন্য যে আর্তি; তার নিবৃত্তির জন্য জীবনকে গাছের ছায়ায় একটু মাটিতে বসতে দিক। এত শতাব্দীর উন্মত্ত ব্যস্ততার পর একটু জিরিয়ে নেবার সুযোগ দিক। মানুষ টের পাক…এই সত্য, যে শিল্পায়নের ব্ল্যাকহোলের সে-ই সুবিমলীয় ‘ঠান্ডা নীল হাঁ’… তার পৃথিবীবাসের ইতিহাসের সবচেয়ে বড় ব্লান্ডারের ক্ষমাহীন নিষিদ্ধ ফলাফল!
কীসব আকাশকুসুম ভাবছি, তাই না? এসব হয়তো হবে না কিছুই। কিন্তু ভাবনাহীনতার তোহমৎ বড় ক্ষতের মতো জ্বলছে যে গায়ে, কী করি। আমরা কার্যত ম’রে গেছি ভাবনার বিহনে… এই ভাবনাটুকু তাই এখন স্তব্ধ পাথর হয়ে আসা আমাদের সকলের ভেতর ব’সে…সেখানে একা একা ফাঁকা তাঁত চালিয়ে যাওয়া মদন তাঁতির মতো—শব্দ আসে খটখট খটখট… অন্ধকারে… ঝড়ের আগের অস্বস্তিকর গুমোট নৈঃশব্দ্যের ভেতর শুধু ফাঁকা শব্দটুকু আসে এখন। এইটুকু ‘অসম্ভাব্যতার’ ভাবনা-প্রতিরোধ, আগুন, ভক্তির সবুজ-প্রাণকণা, বুকের ভেতর নিয়ে, মানুষের সামান্যতম একটা কাণ্ডজ্ঞানহীন অংশও যদি আসন্ন মহাবিলয়ের দিকে এগিয়ে যায়, তাহলেও এই পৃথিবী জানবে… এই আকাশ জানবে… আর সর্বোপরি এই বহতা জল মনে রাখবে; যে কিছু দায় সত্যিই রয়ে গেছে প্রকৃতিরও মনে… হয়তো প্রকৃতি, মানুষের শেষ বিলয়ের পরও, কণামাত্র থেকে যাওয়া ‘মানবের’ অস্তিত্ব টের পাবে তার অবচেতনায়… গ্রহব্যাপ্ত আসমুদ্র সাইলেন্সের ভেতর! ফলত আবার কোনও এক অনির্দেশ্য কালবেলায় প্রলয়ের জল নেমে গেলে, একটা চারাগাছ গজাবে কোথাও… আর তাকে আশ্রয় অথবা পীড়ন করতে একটা কীটও কী ঘর বাঁধবে না সে-ই আদিবৃক্ষের শরীরে… অথবা কিছুটা দূরে?
‘গঙ্গায় আমার ভক্তি পাঁচ আনা পাঁচ সিকে, এইরূপ এ দাসের হয় মতি যে যখনই ঐ অলৌকিক স্নেহময়ী ধারায় ডুব কাটিল সে তন্মুহূর্তে ঠাকুরঘরে যাইবার শতেক বাধা উজাইল…’
বাংলায় ‘ভ’ শব্দটি আদতে ‘হয়’ বা ‘হওয়া’-র দ্যোতক। একধাপ এগোলে আরেকটা শব্দ আসে: ‘ভজ’। একটু জটিলতা এড়িয়ে বললে শব্দটি, ‘হয়’ বা ‘হওয়া’-র বা ‘ভ’-এর থেকে জাত কিছুকে ইঙ্গিত করে। অর্থাৎ, যা ‘ভ’ থেকে জাত তা-ই ‘ভজ’। আরও একটি নানার্থ শব্দাভাস হলো ‘ত’। কারণ বা হেতু অর্থে একে চিহ্নিত করলে দেখা যায়: ‘ভজ’ যার কারণ স্বরূপ, তা-ই ‘ভজ’+‘ত’= ভক্ত। অর্থাৎ ‘হওয়া’ বা অস্তিত্বসঞ্জাত সমস্ত গুণের জন্যই যাঁর উপস্থিতি, তিনিই ‘ভক্ত’। ভক্ত তাই অস্তিত্বসঞ্জাত সমস্ত গুণের আধার। তাহলে ভক্তি কী? এই বিশ্বচরাচরকে যদি সমগ্র অস্তিত্বময়তার সাপেক্ষে দেখা যায়, তাহলে অস্তিত্বসঞ্জাত সমস্ত কিছুর সঙ্গেই অস্তিত্ব রেসিপ্রোকেট করে চলেছে অবিরাম। আপন অস্তিত্বের সঙ্গে এই অবিরাম রেসিপ্রোকেশনের যে উৎকেন্দ্রিক তন্ময়তা, তাই আসলে ভক্তি। ব্যাপারটা আত্মগত নৈঃশব্দ্যের কাছাকাছি। কাঁসর-ঘণ্টা বাজিয়ে পাঁঠাবলি দেবার চেয়ে অনেক ওপরতলাকার ‘দৈব-হল্লা’।
অগত্যা এই অবস্থায় নিজের দিকে তাকালে একটা কথাই বেজে ওঠে: ‘আমি’ সঞ্জাত এই বিশ্বজৈবনিকতায় এই ‘আমি’-র সংলগ্নতা, কথোপকথন, সমর্পণ ও পুনরুদ্ধার ‘আমি’ নিজেই বড় একটা টের পাই না। অর্থাৎ কিনা আমার ভেতরেই চুপিসারে অনর্গল পরম্পরায় তা ‘হয় হয়’…, শুধু আমিই জ়ানতি পারি না, এইমাত্র। ‘আমি’ এখানে শুধু আমি নই। এই ‘আমি’, প্রকৃত প্রস্তাবে, কলকাতার অন্যমনস্ক গাঙ্গেয় বাঙালি। গঙ্গায় রোজ রোজ স্নানরত এক বিশাল জনসমষ্টি। গঙ্গায় গা ভাসানো মূলত—বিলয় সাধনা। কাঙ্ক্ষিত জীবন পেরিয়ে গিয়ে মুহূর্তের কাম্য বিলয়। গঙ্গার জল সর্বাঙ্গে লেগে এদের শরীর সিক্ত মাটির মতো ভারী সংলগ্ন আঁট প্রত্যয়ী। গঙ্গার এই এক মজা। এখানে বিগ্রহের শক্ত মাটি ভাসানের জলে পড়ে আলগা জীর্ণত্বে বিলীন হয়… আবার সে-ই আলগা মাটি একই জলে বছর ঘুরলে চর্মস্থ-মাংসল রকমের এঁটেল ও প্রাণ-প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যাকুল হয়ে ফিরে ফিরে ধরা দেয়। ঠিক যেমন মর-মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু হয়ে আবার জন্মের ভেতর ইটার্নাল রেকারেন্স। আমাদেরও নিজের নিজের ব্যক্তি-বিগ্রহের (বা ইমেজ বা যাকে সাদা কথায় ‘মতি’ বলে) বিসর্জন আর আবাহন সিদ্ধ হয়, প্রতিদিনের স্নানের জেরে; কেননা গঙ্গা কখনও আমাকে নিরাশ করে না। গঙ্গায় কোনও দারিদ্র্য নেই। যেখানে একদিন নিজেকেই নিজে সবটুকু নিঃশেষে খরচ করে দিতে হবে অকাতরে, ইহলৌকিক সঞ্চয়ের পাঁচ আনা পাঁচ সিকে পর্যন্ত; সেখানে দারিদ্র্যের আর্থসামাজিক বোকা মানেগুলো সব পাড়েই দাঁড়িয়ে থাকবে। কিন্তু আমাদের প্রাত্যহিক স্নানমৃত্যুর আগের দিন পর্যন্ত বড় হিসেবি: সে-ই আদি অকৃত্রিম রেসিপ্রোকেশনের ব্যাপারে। হাত ভেজাবার জলে তাই নিত্যকর্মের কাকস্নান সেরে, ঘড়ি ধ’রে বাঙালি আবার শহরটার অলিতে গলিতে হারিয়ে যায়। সারাদিনের পঙ্কিলতায় মজে ওঠে আরও একটা দিনের মতো বড় তার জীবন প্রবাহ। হয়তো আবার পরদিন ক্লেদাক্ত চেহারায় একের পর এক মৃত্যু ডিঙিয়ে, অবরুদ্ধ কণ্ঠে সে গঙ্গায় ফিরে আসবে ব’লে। এভাবেই গঙ্গায় তটস্থ বাঙালি দিন আনে দিন খায়, আমৃত্যু। তবু তার হিসাব কষার ভানটুকু নস্যাৎ হয় না।
চৈতন্যদেব বলতেন, সঞ্চয়ের চেয়ে সঞ্চয়ের ইচ্ছে আমাদের ভাগবত দারিদ্র্যের প্রতি সবচেয়ে বড় বাধা… অস্তিত্বের প্রতি মন আরোপে সর্বাত্মক অন্তরায়। সে-ই ভক্তের রেসিপ্রোকেশনের বিচ্ছেদের প্রশ্নটি এখানেও। মাটিকে ছুঁয়েও ‘আকাশবৃত্তি’ করতে চায় যে ভক্তের মন, তাকে মন্দির মসজিদ কলকারখানা টাকাকড়ি প্রেম-অপ্রেমে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকতে হয় আমরণ। ভক্তের প্রত্যাশাময় সংলগ্নতা থেকে আপন অন্তরের ঠাকুরঘরের অন্ধকারে ‘বিভক্ত’ হয়ে নিজেকে দেখাশোনার কপাল বড় দূরস্থান। বিভক্ত এখানে বিচ্ছিন্ন শব্দের বিপরীত। ভক্ত থেকে বিশেষভাবে ভক্তে উত্তরণের ইশারা আছে শব্দটিতে। জাগতিক বাঙালির, মৃত্যুর এই চাকরিতে, কাফকার ওভারটাইমের দুঃস্বপ্নের থেকে নির্ভার সমাধির ভেতর অবসরযাপনের বাস্তবতা তার ইহজীবনে হলো না, বোধহয়। নিত্যকার এত গঙ্গাস্নান সত্ত্বেও হলো না! ভাবলে অবাক লাগে। তাহলে তো বস্তুনিষ্ঠ ‘বামাচারী’ নাস্তিকতাই আমাদের একমাত্র সম্যক পথ, একদা তো সে সবও ভেবেছিলাম আমরা…ভাবিনি? গঙ্গার বুকে প্রমোদরঙ্গী বিস্তীর্ণ আলোকিত মাতাল তরণীটিতে চড়ে ক্রমে নোয়ার নৌকার মতো অজ্ঞাতবাসে হারিয়ে যেতে থাকি আমরা… পৃথিবীর এই চরমতম নৈঃশব্দ্য-প্রলয়ের দিনে-রাতে… আমাদের ‘রণ-রক্ত-সফলতা’-র অবলেপনে চৌখশ হয়ে উঠুক মর্ষকামী জীবনবোধের আঙিনা। ‘আমি’ শব্দের প্রবহমানতার বিপরীতে এক আন্ডারগ্রাউণ্ডকামী গ্রস্ত ‘আমি’-র মনোলগে অন্ধকার হোক আকাশ।
অথচ নিজের দিকে শেষপর্যন্ত তাকিয়ে থাকতে পারিনি আমরা। তামাম ইউরোপ বলেছে, অন্ধকারের কথা… ঈশ্বরের পুনরাবির্ভাব ও পুনঃপুন মৃত্যুর কথা… অথচ গঙ্গা কেবল গঙ্গাতেই সীমাবদ্ধ থেকে গেছে… নিজের অতলেই জেগেছে আর ঘুমিয়েছে। এই সীমাবদ্ধতার জেরে তার আলোর থেকে একটা গোটা জনসমষ্টি বঞ্চিত থেকে গেছে, অন্য কিছুতে নয়, স্রেফ টের পাওয়ায়… বাঙালির ইউরোসেন্ট্রিজ্মের দেড় শতকেরও বেশি সময় পার ক’রে, আঠারশো সাতান্নর মিউটিনির মডেলকে সূত্রপাত ধরে নিলে: কলকাতার তথা বাঙালির আপন অন্তরে বহমান গঙ্গাকে ঠাওর করতে খুব সম্ভব ‘ডুব’ শব্দটাকে তার বাহ্যিকতা থেকে তামাম অন্তর্মুখীন পসিবিলিটির শেষ সীমান্ত পর্যন্ত বয়ে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব আজ এই বাঙালিরই উপর বর্তাচ্ছে, একেবারে সমষ্টিগতভাবে। অর্থাৎ আপন মরজীবনের ভেতরেও ডুব দিয়ে বাঁচা বাকি আমাদের… এই আমরা যারা ‘গঙ্গার স্বরে কথা বলি’। তবেই না তার একান্ত আপন ব্র্যান্ড-গঙ্গার আদ্যন্ত অনটোলজিকাল বিনির্মাণ সম্ভব হবে। সেদিন কলকাতার মুখ ঢেকে যাবে একটাই বিজ্ঞাপনে: ‘আমিই স্যামসাং মোবাইল’-এর অ্যান্টিথিসিস সে-ই মারণ স্বীকারোক্তি: ‘কলকাতার গঙ্গাই আমি… আমিই কলকাতার গঙ্গা’।
কমলকুমার মজুমদারের ‘কলকাতার গঙ্গা’ অবলম্বনে একটি অন্তর্বীক্ষণ।
প্রচ্ছদ ও অন্যান্য ছবি সৌজন্য: শুভেন্দু চৌধুরী।