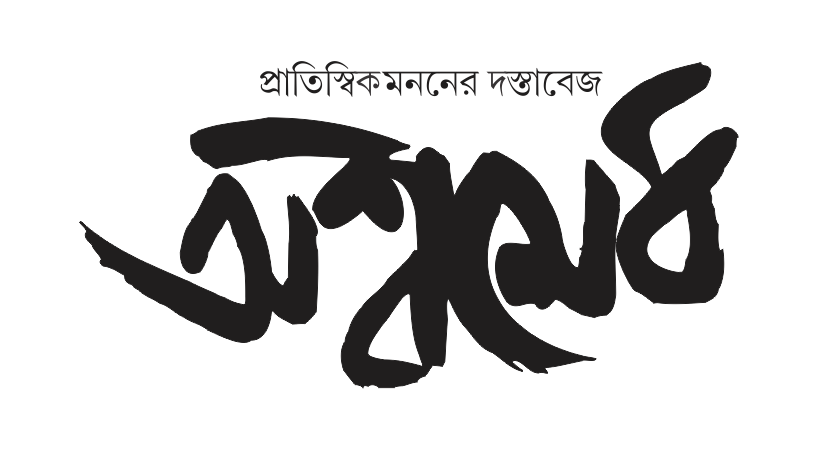“…প্রশ্ন হইতে পারে, সাহিত্য-ক্ষেত্রে কি বিজ্ঞানসেবকের স্থান আছে?”
বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতি হিসাবে বিজ্ঞানাচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর ভাষণে উঠে এসেছিল এই প্রশ্ন। পরে অবশ্য ‘বিজ্ঞানে সাহিত্য’ নামক প্রবন্ধ হিসাবে এই লেখার ঠাঁই হয় তাঁর ‘অব্যক্ত’ গদ্যগ্রন্থে (১৯২১)। সে বই পড়ে কবিগুরু তাঁর চিঠিতে বিজ্ঞানসাধককে লেখেন—’…যদিও বিজ্ঞানবাণীকেই তুমি তোমার সুয়োরাণী করিয়াছ, তবু সাহিত্যসরস্বতী সে পদের দাবী করিতে পারিত—…’
এই পর্যন্ত কোনও সমস্যা নেই, বরঞ্চ বাঙালি হওয়ার গর্বে বেশ খানিকটা বুক ফুলিয়ে রোব্বারের মধ্যাহ্নভোজ সেরে গা এলিয়ে গোঁফে তা দিতেই পারি আমরা। এমনকি এই বক্তব্যের শেষের দিকে বিজ্ঞানীকে বলতে শুনি—’…জ্ঞান অন্বেষণে আমরা এক সর্বব্যাপী একতার দিকে অগ্রসর হইতেছি।’ অর্থাৎ পাশ্চাত্যে যেভাবে বিজ্ঞান ও সাহিত্যকে ভেঙে টুকরো করে অ্যালিয়েনেট করা হয়েছে আমরা সে পথে বিশেষ না হেঁটে প্রাচ্যের একান্নবর্তী সাধনায় ব্রতী হয়েছি। শুধু তাই বা কেন? বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও তো পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, গণিত ইত্যাদি নানান স্তরের বিভাজন পাশ্চাত্যেরই অবদান। তবে ‘অব্যক্ত’ পড়তে পড়তে সর্বত্রই জগদীশচন্দ্রকে ‘অ্যান আইডিয়াল অপটিমিস্ট’ মনে হতেই পারে আপনার, সে আপনার মহানুভবতা (কিংবা তাঁর)। এই ধরনের কথা তাঁর নিজের সময়ে জগদীশচন্দ্র যেমন বলেছেন, তেমনই বলেছিলেন ১৩১৫ ও ১৩১৯ বঙ্গাব্দের সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতির আসন আলোকিত করা আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ও। তবে একটা পার্থক্য রয়েছে। প্রফুল্লচন্দ্র বা তাঁর অনুজ রাজশেখর বসুর লেখা সাহিত্য ও বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধগুলোয় কিন্তু এই ‘আইডিয়াল অপটিমিজ্ম’-এর প্রভাব তেমন নেই। বঙ্গবাসী এবং বঙ্গভাষী বিজ্ঞানসাধক হিসাবে এক প্রচ্ছন্ন গর্ব লেখা ও বক্তব্যগুলির ইতিউতি অবশ্যই ছড়িয়ে রয়েছে, তবে তা মোটেই অন্ধ নয়। সে গর্বে যেমন সহকর্মী ও সহনাগরিকদের জন্য স্নেহ ও ভালোবাসা স্থান পেয়েছে, তেমনই জায়গা পেয়েছে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চা কেন্দ্রিক অনীহার উপর তীব্র শ্লেষ ও বিরক্তি। প্রফুল্লচন্দ্রের লেখায় যেমন অক্ষয়কুমার ও রাজেন্দ্রলাল কর্তৃক ‘তত্ত্ববোধিনী’ পত্রিকায় নিয়মিত প্রকাশিত বৈজ্ঞানিক সন্দর্ভের প্রভূত প্রশংসা বারবার উঠে আসে, তেমনই কেবল মাত্র ইংরেজি ভাষায় চাকরি-ভিত্তিক বিজ্ঞান শিক্ষা প্রবর্তনের উপর একরাশ তীর্যক মন্তব্যেরও দেখা মেলে।
কাজেই যে সমস্যা নিয়ে এই নিবন্ধের এত মাথা ব্যথা, তা যত না বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চা কেন্দ্রিক, তার থেকে ঢের বেশি তা আমাদের মাতৃভাষায় সাহিত্য ও বিজ্ঞানের দূরত্বকে কেন্দ্র করে। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চা কখনও স্বল্প আবার কখনও বা দীর্ঘ পরিসরে চিরকালই ভারতবর্ষে তথা পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গে হয়েই এসেছে। কিন্তু তার পরিমাণ গল্প, উপন্যাস, কবিতা, নাটক ইত্যাদির (রাজশেখর যার নাম দেন ‘ললিত সাহিত্য’) তুলনায় নিমিত্ত বললে বুঝি খুব ভুল বলা হবে না। অর্থাৎ আধুনিক ও উত্তরাধুনিক বাঙালি লেখক ও পাঠক হিসাবে আমরা যে সাহিত্য ও বিজ্ঞানকে একেবারে দূরদেশীয় বানিয়ে তুলেছি, এ নিবন্ধের উদ্দেশ্য সে সমস্যায় খানিক আলোকপাত করা, এবং যদি সম্ভবপর হয় তবে অগ্রজ বিজ্ঞান তথা সাহিত্যসাধকদের আজ্ঞায় তাঁদেরই দেখানো পথ আবারও খানিকটা প্রশস্ত করায় প্রবৃত্ত হওয়া।
“…সাহিত্যের সীমা নির্ণয় করিয়া তাহার অধিকারের দ্বারা সংকীর্ণ করিতে মনেও করি নাই।”
যে সমস্যা নিয়ে এত কথা অর্থাৎ এই যে সাহিত্য ও বিজ্ঞানকে আলাদা করে দেখার অভ্যেস, সে রোগের মূলে যেতে হলে প্রথমেই সাহিত্যের ধরণ ও বিভাজন সম্পর্কে গুটিকয়েক কথা বলা প্রয়োজন। এই বিতণ্ডার বিষয়বস্তু মূলত যেহেতু গদ্য সাহিত্য তাই ‘গদ্যরাজ’ রাজশেখর বসুর স্মরণাপন্ন না হয়ে উপায় নেই। নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী মহাশয় অবধি যাঁকে বাংলা গদ্য রচনার কুলপুরোহিত ঠাউরেছেন তো এই নিমিত্ত কোন ছাড়? নিজেদের বোঝার সুবিধার্থে বিষয়ভিত্তিক ভাবে বিভক্ত করলে সাহিত্য তিন প্রকার। প্রথমটি তথ্যমূলক অর্থাৎ মৌলিক গবেষণা পত্র, জীবনচরিত, জিনিসপত্রের বিবরণ ইত্যাদি। দ্বিতীয়টি প্রচারমূলক অর্থাৎ ধর্মগ্রন্থ, রাজনৈতিক ম্যানিফেস্টো ইত্যাদি। এবং তৃতীয়টি ভাবমূলক, যার মধ্যে পড়ে: গল্প, কবিতা, নাটক, উপন্যাস, প্রবন্ধ ইত্যাদি। আমাদের আলোচনার প্রধান উপজীব্য প্রথম এবং তৃতীয় শ্রেণির সাহিত্য, এবং অবশ্যই সে-ই দুইয়ের মধ্যে প্রায় জবরদস্তি তুলে দেওয়া দেওয়ালের কথা। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস যদি উপর উপর মোটামুটি ঘাঁটা যায় তাহলে দেখা যাবে যে, অনেক দিন অবধি আমাদের সাহিত্য মূলত পদ্য নির্ভর ছিল। এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটতে শুরু করে রামমোহন রায় ও তাঁর সমসাময়িকদের হাত ধরে। একই সময়ে রামমোহন বাংলায় ইংরেজি শিক্ষার বিস্তারে বিরাট অবদানও রাখেন। ১৮১৭ থেকে ১৮৩০ সাল অবধি একনাগাড়ে চলা শিক্ষা আন্দোলনে ইংরেজি ভাষার হাত ধরেই পাশ্চাত্য আধুনিক বিজ্ঞান আমাদের অখণ্ড বঙ্গদেশে উপনীত হয়। একজন কট্টর দেশভক্ত স্বদেশীও বলবেন—এ কাজে আমাদের বিশেষ ক্ষতি হয়নি। এর পরের আরও প্রায় ১০০ বছর ইংরেজ কেবলমাত্র ইংরেজি ভাষাতেই শিক্ষাদানের উপর জোর দেয় এবং গদ্য সাহিত্যের ক্ষেত্রে গোলটা বাঁধে এখানেই। পাশ্চাত্য যেখানে প্রথম থেকেই বিজ্ঞান ও সাহিত্যকে আলাদা করেই দেখে, গদ্য সাহিত্যের ক্ষেত্রে তার প্রভাব যে আমাদের উপর পড়বে এতে আর আশ্চর্য কী? আমাদের গদ্য সাহিত্যের শুরু মূলত ইংরেজি সাহিত্যেরই অনুপ্রেরণায়। তাই ললিত গদ্য এবং বিজ্ঞান ভিত্তিক গদ্যের এই যে অ্যালিয়েনেশান তার ঐতিহাসিক শিকড় যে রামমোহন সমসাময়িক এ কথা বললে খুব ভুল বলা হবে না।
সমস্যা আরও অন্য জায়গায়। ইংরেজি, জার্মান, ফরাসি ইত্যাদি ভাষায় এই বিভাজন সত্ত্বেও বৈজ্ঞানিক গ্রন্থের কমতি কিন্তু চোখে পড়ে না। তবে আমরা পিছিয়ে পড়লাম কেন? অক্ষয়কুমার, ব্রজেন্দ্রলাল যে কাজে নিজেকে উজাড় করে দিয়েছিলেন সে কাজ এত তাড়াতাড়ি থিতিয়ে পড়ল কেন? এ সমস্যার জন্য কিন্তু ব্রিটিশরাজের বৈষম্যনীতিই অধিকাংশে দায়ী। এ প্রসঙ্গে ব্যালান্টাইনের সে-ই বিতর্কিত মন্তব্য স্মরণীয়: ইংরাজি ভাষায় জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চা করলে সংস্কৃত ক্লাসের ছাত্ররা স্কিজোফ্রেনিয়ার রোগী হয়ে পড়বে। ইংরেজের হাত ধরে এদেশে রামমোহন কর্তৃক ইংরেজি ভাষার আগমন হলেও সাধারণ গ্রামবাসী বাঙালি অবধি সে ভাষাকে পৌঁছে দেওয়া সহজ কাজ ছিল না। ব্রিটিশদের সময়ে স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটিতে যেহেতু ইংরেজিতেই মূলত বিজ্ঞান শিক্ষা হতো তাই ভারতবর্ষের তৎকালীন জনসংখ্যার পরিমাপে ইংরাজি ভাষায় বিজ্ঞান-শিক্ষার্থীর সংখ্যা শতকরার হিসাবেও আসে না। সরকার কর্তৃক তৈরি হওয়া বিজ্ঞান শিক্ষা মন্দিরে বেশিরভাগ নাগরিকই ঠাঁই পাননি। কাজেই হাতে গোনা যে ক’জন ইংরেজি ভাষায় বিজ্ঞান শিক্ষার সুযোগ পেলেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই পরিশিষ্টে হয় আইনি বিশ্ববিদ্যালয়ে অথবা সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে জীবনধারণ ও সংসারধর্ম পালনে ব্রতী হন। বিজ্ঞান গবেষণা ভিত্তিক শিক্ষাকে ব্যবহার করে কলকারখানা স্থাপন হলে যে কর্মক্ষেত্রের শ্রীবৃদ্ধি হওয়া সম্ভব—তা হয়নি। রবীন্দ্রনাথ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র, রাজশেখর বসু, জগদীশচন্দ্র ইত্যাদিরা ও পরবর্তী সময়ে সত্যেন্দ্রনাথ বোস ও মেঘনাদ সাহার মতো গুটিকয়েক মহাত্মা স্বল্প পরিসরে নিজেদের চেষ্টায় বিজ্ঞানের জগতকে বঙ্গ সাহিত্যের আঙিনায় নিয়ে আসার চেষ্টা করেছিলেন। সে কারণেই বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের মতো গৌরবময় পরিসরে সভাপতিত্ব ও সহসভাপতিত্বের দায়িত্ব বর্তায় এই ‘সাহিত্য’ আচার্যদের উপর। তৈরি হয় বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদও।
কিন্তু সে-ই অবধি! মেইনস্ট্রিম বাংলা সাহিত্য-আঙিনায় কিন্তু আজও ‘ললিত সাহিত্য’ ও ‘বৈজ্ঞানিক সাহিত্য’ দুজন দুই-মেরুরই বাসিন্দা। তবে ললিত সাহিত্যের ক্ষেত্রে ব্যাপার একেবারেই আলাদা। বাংলা মাতৃভাষা হওয়ার কারণে সে সাহিত্য বঙ্গদেশের সর্বপ্রান্তে অনায়াসেই পাড়ি দিতে পেরেছিল, পৌঁছে যেতে পেরেছিল সাধারণ বাঙালির হৃদয়ের কাছাকাছি। উল্লেখ্য, শেকসপিয়রের চর্চা বাঙালি শিক্ষিত-মহলে ব্যাপক হয়ে উঠলেও বিজ্ঞান-দর্শন নিয়ে চর্চার পথ তাঁরা সযত্নে পরিহার করতে চাইল। একবার ভেবে দেখুন, প্রথম থেকেই যদি বাংলা ভাষাতেই বিজ্ঞান চর্চার সুযোগ থাকত তবে কত বিজ্ঞান ভিত্তিক বই ও লেখায় উর্বর হতো আমাদের সাহিত্যের আঙিনা? এই যে ‘ললিত সাহিত্য’ ও ‘বিজ্ঞান সাহিত্য’র পাশ্চাত্য আরোপিত বিভাজন তার থেকে মুক্ত হতাম আমরা, বাঙালিরা। ভয়-ভীতিহীন এক বৈজ্ঞানিক মনন আমাদের উপহার দিতে পারতেন বিজ্ঞান-সাহিত্যের কৃতী অগ্রজরা। রাজশেখর বসুরও তবে আর ‘বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি’ প্রবন্ধটি রচনার দরকার পড়ত না।
১৩১৯ সালের চট্টগ্রাম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতি হিসাবে তাঁর বক্তব্যে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র যেমন স্পষ্ট করেই বলেন—“…বিজ্ঞানের শিক্ষা স্বয়ং প্রকৃতির হইতেই শিক্ষালাভ। উহা মাতৃভাষাতেই হওয়া উচিত। একটা বিদেশীয় ভাষার কবলে উহাকে আবদ্ধ রাখা উচিত নয়।… আমাদের দেশ ত ভীষণ অজ্ঞানতিমিরে আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে।… তোমরা ইংরাজিতে বিজ্ঞান আলোচনা করিবে, প্রথমে ভাব দেখি তোমার দেশবাসীর মধ্যে কজন ইংরাজি বুঝিবে।”
“…বহুর মধ্যে এক যাহাতে হারাইয়া না যায়, ভারতবর্ষ সেইদিকে সর্বদা লক্ষ্য রাখিয়াছে।”
তবে? এই এত শতাব্দীর বিভাজন বা অ্যালিয়েনেশান থেকে বেরিয়ে আসার উপায় কী? কেবলমাত্র বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান রচনা বা বিজ্ঞানসাধনা আমাদের নিশ্চয়ই কয়েক ধাপ এগিয়ে দিতে পারে—তবে তারও আগে প্রয়োজন সাহিত্যে বিজ্ঞানমনস্ক মূল্যবোধের প্রবর্তন ও বিবর্তন।
পদার্থবিদরা এবং মূলত হাই এনার্জি ফিজিক্সের বিজ্ঞানীরা তাঁদের আলোচনায় এক তত্ত্বের কথা মাঝেমধ্যেই টেনে আনেন, যার নাম—’গ্র্যান্ড ইউনিফায়েড থিয়োরি’। সাদা বাংলায় বলতে হলে আমাদের আশপাশের জীব ও জড় জগতকে যে সমস্ত শক্তি বা বল নিয়ন্ত্রণ করে, উচ্চ থেকে উচ্চতর এনার্জিতে পৌঁছলে তাদের আর কোনও নিজস্ব একক অস্তিত্ব থাকে না, সবটা মিলে একটিমাত্র বল হিসাবেই তাদের একান্নবর্তী অস্তিত্ব। অর্থাৎ পাশ্চাত্য বিজ্ঞান-সাধনা যে সর্বগ্রাসী বিভাজনকে ঘিরে বিবর্তিত হয়েছিল তাও একসময় আমাদের একান্নবর্তী অস্তিত্বে একত্রিত হলো। বিজ্ঞান ও সাহিত্যের ক্ষেত্রেও তা শত শতাংশ সত্যি। পরম সৃজনশীলতার আবর্তে সৃষ্টির কোনও ভগ্নাংশ নেই। বাংলা গদ্য সাহিত্যের বিবর্তন ইতিহাসে লক্ষ্যণীয়—রামমোহন রায় ও বঙ্গীয় মিশনারিদের আঁতুড় ঘরে জন্মলগ্নের সময় থেকে শুরু করে বিদ্যাসাগর, মধুসূদন, বঙ্কিমের কলমে কৈশোর উত্তীর্ণা; পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র, জগদীশচন্দ্র, রাজশেখর; আরও পরে অবশ্যই সত্যেন্দ্রনাথ বসু, মেঘনাদ সাহা ইত্যাদিদের মনন প্রাপ্তিতে যৌবন-মদে নেশাতুর বাংলা গদ্যে কিন্তু কখনোই সাহিত্য-বিজ্ঞান বিভাজন লক্ষ করা যায়নি। একদিকে আমরা যেমন কবিগুরুর বিজ্ঞান বিষয়ক ‘সরস’ প্রবন্ধ পড়েছি, তেমনি পড়েছি সুকুমার রায়কেও। কাজেই বিজ্ঞান ভিত্তিক লেখায় সাহিত্যরস বঙ্গ-লেখনীতে দুর্লভ নয়, কখনোই ছিল না। এই একই পরিপ্রেক্ষিতে রাজশেখর বসুর কথা বারবার উঠে আসে। পরশুরামের ছোটগল্প বাঙালি মননের আকাশের যেমন এক উজ্জ্বল নক্ষত্র; বারংবার পঠিত, অন্য দিকে রাজশেখর রচিত বঙ্গরসে টইটুম্বুর বিজ্ঞান ও সমাজ-বিজ্ঞান সম্পর্কিত একের পর এক প্রবন্ধ কীভাবে ও কেন হাতের নাগালে থাকা সত্ত্বেও আমরা এড়িয়ে চলেছি সেটা বুঝতে চাওয়ার নিতান্ত চেষ্টাটাও আমাদের এ সমস্যার গোড়ায় পৌঁছতে সাহায্য করতে পারে।
রাজশেখরের কৌতুক প্রীতির নজির ছড়িয়ে রয়েছে তাঁর বিজ্ঞান-সম্বন্ধীয় প্রবন্ধের পরতে পরতে। যেমন, ‘তিমি’ প্রবন্ধের শুরুর দিকে বড় তিমির ছোট মাছ ভক্ষণের জীববিজ্ঞান ভিত্তিক তত্ত্ব কখন যে পাঠকের অজান্তেই সমাজবিজ্ঞান ছুঁয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের রাষ্ট্রবিজ্ঞানে পৌঁছে যায় তা ভেবে কুলীন পাঠক নিজেই মনে মনে হাসেন। কেবল বাংলা ভাষায় কেন, যে-কোনো ভাষার গদ্য সাহিত্যে এমন ‘ফ্লুইডিটি’ বড়ই দুর্লভ; সমকালীন ইংরেজিতে বার্টান্ড রাসেলের ‘মর্টাল অ্যান্ড আদার্স” বইয়ে সংকলিত নিউ ইয়র্ক টাইম্স-এর প্রবন্ধগুলির সঙ্গে হয়তো সে লেখার তুলনা চলতে পারে। রাজশেখর নিজেই আমাদের পথ দেখিয়ে বলছেন—“… আমদের প্রথম কর্তব্য—বড় বড় লেখকগণ যা লিখিয়া ফেলিয়াছেন তার একটা গতি করা। দ্বিতীয় কর্তব্য—ভবিষ্যতে যাঁরা লিখিবেন তাঁদের জন্য একটি আদর্শ নির্দেশ।”
একই লেখকের মনন যেমন একদিকে গল্প, কবিতা, কৌতুক, উপন্যাস, নাটকের জন্মভিটে; অন্যদিকে সে মনে ছিল বিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ভিত্তিক উজ্জ্বল প্রবন্ধের সমান আনাগোনা। তবে আজ বাংলা সাহিত্যের উত্তর-আধুনিকতার দিনে এই অ্যালিয়েনেশান কেন? আমরা কি তবে অনুজ হিসাবে অগ্রজদের অনাধুনিক ভেবে ব্রাত্য করলাম? বুঝতে কোথাও কী ভুল হলো যে, বিজ্ঞান সর্বদাই আধুনিক, শিল্প ও কলা উভয় যেভাবে একে অপরের পরিপূরক। চর্চার ক্ষেত্রে সাহিত্য ও বিজ্ঞান দুইই সমান প্রয়োজনীয়। বিজ্ঞান-সাহিত্য মেলবন্ধনের আরেকটি গুরুতর কাজের জায়গা অবশ্যই কল্পবিজ্ঞান। আমাদের দুর্ভাগ্য, বাংলা সাহিত্যে কল্পবিজ্ঞান এখনও শিশুতোষ হয়েই রইল, সে ডিসকোর্সে মৌলিক লেখার থেকে অনুবাদের সংখ্যা এখনও ঢের বেশি। এমনকি সত্যজিৎ রায়ের লেখাতেও বিদেশী লেখার প্রভাব স্পষ্টত বিদ্যমান।
‘সুবুদ্ধিবিলাস’ রাজশেখর বসু ১৯৫১ সালে ‘সাহিত্য-সংস্কার’ প্রবন্ধে যখন লেখেন—“সর্বভুক্ পাঠক হাঁ করিয়া আছে। ওস্তাদ রসস্রষ্টা কাহাকেও বঞ্চিত করিতে, কিছুই বাদ দিতে পারেন না।”—এ কথা তখন যেমন জরুরি ছিল আজও ততটাই আধুনিক, এবং মূলত এই শপিং-মল-সাহিত্যের দিনে আরও অনেক বেশি করে প্রাসঙ্গিক। এ আমাদের দুর্ভাগ্য বটে, তবে ‘সায়েন্টিফিক মেকানিকাল ব্রেইন’ যে আমাদের মাতৃভাষায় এ কথা লিখে রেখে গেছেন, সে-ও তো কম সৌভাগ্য নয়!
রাজশেখরের এ কথাটি প্রণিধানযোগ্য—’সর্বভুক্ পাঠক হাঁ করিয়া আছে।’ হাঁ করে থাকার পরেও বাঙালি-পাঠক বিজ্ঞান বিষয়ক লেখালেখির থেকে সাধারণত একটু দূরেই সরে থাকে—এর কারণ কি আমাদের উপনিষদীয় মানসিকতা! এ জগৎ মায়া, এ জগৎ মিথ্যা—এই অধ্যাত্মসর্বস্বতা? “ইংরেজী Science ও Arts (বা humanities) জ্ঞানবিজ্ঞানের কাটছাঁট পার্থক্য ঊনবিংশ শতাব্দের মধ্যভাগেও সর্বস্বীকৃত হয়েছিল বলে মনে হয় না। সেইজন্য বাংলায় ‘বিজ্ঞান’ শব্দটি ব্যুৎপত্তিগত ব্যাপক অর্থে ঊনবিংশ শতাব্দের ষষ্ঠ দশক অবধি চলে এসেছিল এমনকি কবিতার বইয়ের নামেও ‘বিজ্ঞান’ অচল ছিল না! ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিশিষ্য রসিকচন্দ্র রায় ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দে ‘বিজ্ঞানসাধুরঞ্জন’ বার করেছিলেন। আধুনিক অর্থে ‘বিজ্ঞান’ শব্দটি বংলায় পাকাপাকিভাবে চালু করে দেন বঙ্কিমচন্দ্র—১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে তাঁর ‘বিজ্ঞানরহস্য’ বার করে।”—এ কথা সুকুমার সেন বলছেন। সুকুমার সেন বর্ণিত এই অবস্থাটির প্রায় হুবহু সমান্তরাল আমরা দেখতে পাই ব্রিটেনে। সেখানেও উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় অবধি ‘Science’ কথাটি কেবল বিজ্ঞানকে বোঝাবার জন্যই ব্যবহৃত হতো না। কথাটা ব্যাপক অর্থে জ্ঞান বা প্রজ্ঞার প্রতিশব্দ হিসাবে ব্যবহৃত হতো। সময় যত আধুনিক হলো ভাবনাচিন্তা পালটাল। সূত্রপাত হলো একটার থেকে আরেকটাকে আলাদা করে দেখার রীতি রেওয়াজ। ইউরোপীয় শিক্ষাব্যবস্থায় যেভাবে ইদানীংকালে ‘মাল্টি-ডিসিপ্লিনারি’ শব্দের বহুল প্রয়োগ, সেখানে দাঁড়িয়ে আমাদের মনে পড়তে বাধ্য এ কথা : ‘…জ্ঞান অন্বেষণে আমরা এক সর্বব্যাপী একতার দিকে অগ্রসর হইতেছি।’ প্রাবন্ধিক আশীষ লাহিড়ী তাঁর ‘ঔপনিবেশিক বাংলায় বিজ্ঞান ও অধিবদ্যার সংঘাত’-এ লিখছেন: “সুকুমার সেন পুরোনো পুথির বাজে পাতায় একসময়ে কিছু মশাল তুবড়ি হাউই ইত্যাদি আতশবাজির কিছু ফর্মুলা পেয়েছিলেন। সেটুকুই বাংলাদেশে ফলিত রসায়ন চর্চার একমাত্র সাক্ষ্য। কিন্তু সে-তো বিজ্ঞান চর্চা নয়।” এদেশে ইংরাজি শিক্ষা প্রবর্তনের আগে প্রকৃত অর্থে বিজ্ঞান চর্চা সম্ভব ছিল না। কিন্তু, ইওরোপীয় বৈজ্ঞানিক সংস্কৃতি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র একটি অংশ ব্যতিরেকে বাঙালি সমাজে কোনও বিশেষ প্রভাব ফেলতে পারেনি। তার কারণ হয়তো এই যে, ইউরোপে বৈজ্ঞানিক বিপ্লবটা বাস্তবে ঘটেছিল। এখানে ঘটেনি। কেবল জ্ঞান চর্চার বা শিক্ষার একটা ক্ষেত্র উন্মুক্ত হয়েছিল।
“…উচ্ছৃঙ্খল ধূমকেতুকেও একদিন সূর্যের দিকে ছুটিতে হয়।”
তবে আসুন আমরা সকলে মিলে একসাথে সমস্ত প্রকার সাহিত্য রচনায় মনোনিবেশ করি—না, এই নিবন্ধ মোটেই তেমন অমূলক দাবি করে না। শেষের সেদিন এখনও অথই দূরে। শূন্য থেকে শুরুর দিন আজ। আমাদের অগ্রজ সাধকরা বাংলা সাহিত্যের একান্নবর্তী সমন্বয় তথা আধুনিকতার যে সমুদ্র উজাড় করে গেছেন—আসুন আমরা বরং আপাতত সে-ই সাগরে নিমজ্জিত হই। সে ডুব সাঁতারে এতই মজা যে পাড়ে ওঠার ইচ্ছা হয় না, মনে হয় জলেই থাকি, না-হয় হাবুডুবুই খাই খানিক। এই তো বেশ! এই তো দিব্যি! সৃজনশীলতার পরমে পৌঁছে সাহিত্য-বিজ্ঞানের গ্র্যান্ড ইউনিফিকেশান হোক। বর্তমান সার্বিক অ্যালিয়েনেশানের যুগে জগদীশচন্দ্রের মতো ‘আইডিয়াল অপটিমিস্ট’-এর বুঝি প্রভূত প্রয়োজন। এই ‘খেলা হবে’র দিনে না-হয় খানিক পড়াশোনাই হোক বরং!
পরিচ্ছেদগুলির শুরুর ‘কোটেশন’ বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতি হিসাবে বিজ্ঞানাচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর ভাষণ থেকে নেওয়া হয়েছে। পরে অবশ্য ‘বিজ্ঞানে সাহিত্য’ নামক প্রবন্ধ হিসাবে সে-ই বক্তব্য তাঁর ‘অব্যক্ত’ গদ্যগ্রন্থে প্রকাশিত হয় (১৯২১)।