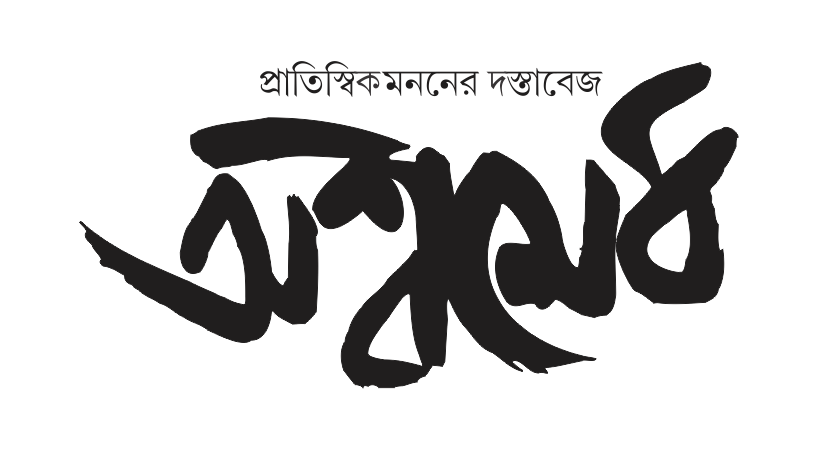ঈশ্বরসৃষ্ট মানুষ ও বিবর্তিত মানুষের দ্বন্দ্ব
মানুষের উৎপত্তির ইতিহাস মনে রাখলে দেখা যাবে, পশু জগতের ‘নিয়মনীতি’ উত্তরাধিকার সূত্রে মানুষের মধ্যে বর্তেছে। এবং মানুষের সমাজ-সংস্কৃতিতে তার প্রকাশ। এই ‘সাইবার’ যুগেও ভীষণ দৃষ্টিকটুভাবে তার প্রকাশ ঘটে চলেছে। ‘মানবিক’ হয়ে-ওঠার গতিপথে মনুষ্যজগৎ যে ‘নীতি-নৈতিকতা’র জন্ম দিয়েছে তাও পাশবিকতায় আক্রান্ত হয়ে আছে তার জন্মলগ্ন থেকেই। হয়তো এ কারণে ‘মানবসভ্যতা’র বিকাশ ঘটেছে যুদ্ধ-রক্তপাতের মাধ্যমে। ‘জীবশ্রেষ্ঠ’ মানুষ ‘পাশবিক পথে’ই এক অমানবিক সভ্যতার বিকাশ ঘটিয়ে চলেছে। কোনও নির্দিষ্ট উদাহরণ না রেখে মানুষের প্রতি মানুষের শোষণ-নিপীড়ন-বঞ্চনার যে সামাজিক ইতিহাস, তা ফিরে দেখা যেতে পারে, এবং সুবিধামতো আমাদের স্মৃতি-সত্তা থেকে দৃষ্টান্ত চয়ন করাও সম্ভব। এই আলোচনায় আমরা এই পদ্ধতি-ই অনুসরণ করব এবং মনে রাখব, ‘অমানবিক’ যদি তত্ত্ববিশেষণ হয় তা হলে সভ্যতার বিকাশপথে ‘মানবিক’ও তত্ত্ববিশেষণ হয়ে আছে। আমাদের উদ্দেশ্য হবে তার বিকাশ ঘটানোর পথ খোঁজা।
সামাজিক ইতিহাসের সমৃদ্ধ উপাদান হলো, আমরা সকলেই জানি, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক নিদর্শন। আমাদের দেশে বেদ-উপনিষদ, রামায়ণ-মহাভারত (কালক্রমে এগুলি হিন্দু-ধর্মপুস্তক নামে খ্যাত হয়েছে) থেকে সমাজের যে ইতিহাস পাওয়া যায়, তা ইহুদি (>) খ্রিস্টান (>) ইসলাম ধর্মপুস্তকের সঙ্গে এক বেসিক জায়গায়, বিশ্ব সৃষ্টির গল্পে, পার্থক্য রয়েছে। গল্প দুটির তাৎপর্য যথাক্রমে এই যে, আমাদের দেশে মানুষের সৃষ্টি হয়েছে কর্ম-বিভাগসহ।
ব্রহ্মা (= ঈশ্বর) স্বদেহের চারটি কর্মেন্দ্রিয়কে খণ্ড খণ্ড করে তা থেকে এক-একটি কর্মী-মানুষের সম্প্রদায় সৃষ্টি করেছেন। এর অর্থ, মানুষের মর্যাদা কর্ম (= ধর্ম) সাপেক্ষে বিশেষ। আর উক্ত ধর্মগুলিতে, ঈশ্বর মাটি থেকে নিজের সাদৃশ্যে মানুষ (পুরুষ ও নারী) সৃষ্টি করেছেন এবং অনুমান করা যায় যে, বেঁচে থাকার রসদ সংগ্রহ/উৎপাদন-কর্ম অনুসারে মানুষের কর্মী-পরিচয় তৈরি করেছে সমাজ। প্রসঙ্গত আমাদের দেশে ‘আদিবাসী’ জেনেসিসেও ‘ঈশ্বর’ মাটি থেকে সবকিছু সৃষ্টি করেছেন বলে জানা যায়।
কোনও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ না করে এটা সহজে অনুমান করা যায় যে, দেশে-দেশে মানুষের মর্যাদা নির্বিশেষ নয়, আমাদের দেশে, হিন্দুধর্মে তা শ্রেণি-সম্প্রদায়ে বিভক্ত (= সাম্প্রদায়িক) কিন্তু উক্ত ধর্মপ্রধান দেশগুলিতে মানুষের মর্যাদা নির্বিশেষ হলেও কর্মী-পরিচয়ে তা শ্রেণিবিভক্ত। অর্থাৎ দেশে-দেশে মানুষ, বিশেষ করে আমাদের দেশে, মানুষ একই সঙ্গে সম্প্রদায়গত ও শ্রেণিগতভাবে বেঁচে থাকার লড়াই চালাচ্ছে—এই অনুষঙ্গে আমাদের ডারউইনের তত্ত্ব মনে পড়তে পারে। অনেকেই মানুষের ক্ষেত্রে ‘সারভাইভাল অব দ্য ফিটেস্ট’-তত্ত্বটি ব্যবহার করতে চান না। তাঁদের যুক্তি: মানুষ ভয়কে যেমন জয় করতে শিখেছে, তেমনই ভয়ের ব্যবহারও শিখে নিয়েছে এবং মানুষ তার ‘যৌনতা’কে কেনা-বেচার জিনিস করে তুলেছে। আবার এরকম মতও শোনা গেছে যে, কীটপতঙ্গ সহ পশুজগতে যেমন নানা প্রজাতি আছে এবং তাদের মধ্যে প্রত্যক্ষ-পরোক্ষে রয়েছে ‘খাদ্য-খাদক’ সম্পর্ক—তেমনই, অর্থনৈতিক জীব হিসাবে মানুষেরও নানা ‘প্রজাতি’ তৈরি হয়েছে এবং… পশুজগতের ‘শিকার-কৌশল’ প্রায় সবই মানুষ ‘অর্থ শিকারে’র ক্ষেত্রে ব্যবহার করে থাকে—খুব পরিচিত বিষয় ফাঁদ ও টোপ, ক্যামোফ্লেজ… কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে যেটা অভিনব তা হলো, ‘শিকার করা’ (= বিজিত) মানুষকে পশুর মতো উৎপাদনের (পণ্য-পরিষেবা) কাজে ব্যবহার করতে শেখা, শেখানো!
ধর্ম ও জিরাফে থাকা মানুষের রাজনৈতিক হয়ে ওঠা
আমাদের দেশে এই বিজিত মানুষকে (প্রাচীন সিন্ধু সভ্যতার মানুষ) বিজেতা সম্প্রদায় (= ঋগ্বেদের মানুষ) শূদ্র-শ্রেণি রূপে চিহ্নিত কোরে, সমাজের প্রান্তে তাদের জায়গা দিয়েছে। গড়ে উঠেছে নতুন সিন্ধু সভ্যতা [= (কালক্রমে) হিন্দু (<সিন্ধু) সভ্যতা] আর যারা বনজঙ্গলে পালিয়ে বেঁচেছে, তারা গড়ে তুলেছে এক-একটি ‘বনসভ্যতা’, যেমন রামায়ণে উল্লেখিত ‘কিষ্কিন্ধ্যা সভ্যতা’।
সে-ই যে ঋগ্বেদ-বিবৃত সময় (খ্রিঃ পূঃ ২০০০ অব্দ) থেকে উপনিষদের কাল ছুঁয়ে (রচনা খ্রিঃ পূঃ ৭ম শতক) বুদ্ধের সময়ের আগ-পর্যন্ত অব্যাহত থেকেছে—নব্য সিন্ধু সভ্যতার বিস্তার, যুদ্ধের নিয়মে বিভিন্ন গণরাজ্যের গড়ে ওঠা (অশ্বমেধ যজ্ঞ স্মরণ করা যেতে পারে)। যত যুদ্ধ তত বিজিত মানুষ (=জাতি)। তাদের অধিকাংশই শূদ্র জাতি। কর্ম অনুসারে তারা নানা উপজাতে (সাব কাস্ট) বিভক্ত। বংশ পরম্পরায় তাদের কাজ নির্দিষ্টই (কর্মই ধর্ম, স্বধর্মে নিধনও শ্রেয়) থেকেছে।
‘বুদ্ধ যুগ’ (আনুমানিক খ্রিঃ পূঃ ৫৬৩-৪৮৩ অব্দ) থেকে এই অবস্থার এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন শুরু হয়—অন্তরবস্তুতে বৌদ্ধ মতাদর্শ মানুষের মধ্যে যে পাশবিকতা রয়েছে, তা থেকে মানুষকে মুক্তির পথ দেখানোর প্রস্তাবনা। যে কেউ তাঁর নির্দেশিত পথে হাঁটতে পারে। এই সময় থেকে বৌদ্ধ-পথে চলা চার বর্ণের মানুষের বর্ণত্ব লোপ পাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়। অন্য তিন বর্ণের মানুষের সঙ্গে সমমর্যাদা অনুভব করে শূদ্র-বর্ণ।
কিন্তু প্রায় দেড় হাজার বছরের বেশি সময় ধরে গড়ে ওঠা বর্ণ-পরিচয় বিভিন্ন বর্ণের মানুষ ভুলতে পারেনি—সে-ই সময়কার কোনও তথ্য হাতের কাছে নেই, কেবল সাম্প্রতিক সময়ের (সে-ই সময়ের কমবেশি সোয়া দু-হাজার বছর পরের) একটি তথ্য উল্লেখ করা যেতে পারে, ব্রাহ্মণ্যত্ব না থাকা কোনও ‘ব্রাহ্মণ সন্তান’ যেমন উপবীত ত্যাগ করতে দ্বিধা করেন, তেমন একজন নাপিত-ঘরে জন্মানো তথাকথিত শিক্ষিত-সন্তান তাঁর পরিচয়-জ্ঞাপক পদবি পরিবর্তন করতে চান। হয়তো এর থেকে সামান্য হলেও তৎকালের পরিচয় ভুলতে না পারার বিষয়টির তীব্রতা অনুমান করা সম্ভব হবে। কিন্তু তখন নব্য সিন্ধু সভ্যতার ধর্মের পরিচয় ছিল ‘বৈদিক’। আর বুদ্ধের অনুগামীদের পরিচয় ‘বৌদ্ধ’। অন্তত পাঠ্য ইতিহাস বই থেকে আমরা এরকমই জেনেছি—‘বৈদিক ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির আধিপত্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-আন্দোলন’ থেকে এই ধর্মমতের উদ্ভব। এবং তার জন্মলগ্ন থেকেই এই ‘ধর্ম’ রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা পায়। বলা বাহুল্য তবু উল্লেখ প্রয়োজন যে, রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা ধর্মপরিচয়কে বিপন্ন করেছিল, বিশেষ করে বৈদিক ধর্মকে। এই উল্লেখ এ কারণে যে, বৈদিক ধর্ম পুনঃজাগরণ ঘটাতে চাইবে—এই ঘটনার জন্য প্রস্তুত থাকা।
সামরিক অভিযান: অনুপ্রবেশ অথবা রক্তাক্ত রাজনীতি
আর-একটি বিষয় উল্লেখ করতে হবে, বুদ্ধের সময়কালে সিন্ধু-উপত্যকা ও গান্ধার (বর্তমান রাওয়ালপিণ্ডি ও পেশোয়ার অঞ্চল) পারস্য (বর্তমান ইরান) সম্রাট দারায়ুসের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল—এই উল্লেখ এ কারণে যে, আর্য-অনুপ্রবেশের পর, এই প্রথম নব্য সিন্ধু সভ্যতার ভূমি আক্রান্ত ও বেদখল হলো। আরও মনে রাখবার বিষয় তখন ইতিহাস আখ্যাত ‘ষোড়শ মহাজনপদ’ গড়ে উঠেছে, বৈদিক ধর্ম-অনুসারে রাজ্য শাসন চলছে, সমাজ চার বর্ণে বিভক্ত থেকেই চলমান। কিন্তু রাজনৈতিক সম্প্রীতি রাজ্যগুলির মধ্যে ছিল না, অতএব, প্রতিবেশীর সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহ চলছিল এবং বিদেশী শক্তিকে বাধা দেওয়ার মতো ঐক্য মহাজনপদগুলির মধ্যে গড়ে ওঠেনি। এই সময়ের প্রেক্ষিতে একটি প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক: কেন গড়ে ওঠেনি? কিন্তু এই প্রশ্নের উত্তর আমরা এখন খুঁজব না। তাতে আমাদের আলোচনার অভিমুখ বদলে যাবে, তবে আমাদের আলোচনায় তার আভাস পাওয়া যেতে পারে।
যাই হোক, বুদ্ধ-দারায়ুসের সময় থেকে বৃহৎ আর্যাবর্তে শুরু হয় ভাষা-সংস্কৃতির বদল। একটি প্রাসঙ্গিক দৃষ্টান্ত: দারায়ুসের শিলালিপিতে সংস্কৃত শব্দ ‘সিন্ধু’ হয়েছে ‘হিন্দু’— এটি পারসি শব্দ। শাসকের ভাষা-যে বিজিত জাতি গ্রহণ করতে বাধ্য হয়, আমাদের দেশে তার আদি দৃষ্টান্ত এই— ‘সিন্ধু’র ‘হিন্দু’ হওয়া। এবং অনুমান করা সম্ভব যে, কালক্রমে ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও বৌদ্ধধর্মের মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য সূচিত করবার জন্য, এমনকি ‘ব্রাহ্মণ্য’ শব্দে নিহিত ‘নেতি’কে আড়াল দেওয়ার জন্য ও ধর্মের উৎসভূমি নির্দেশ করবার জন্যও বটে—‘হিন্দু’ শব্দটি তৎকালীন বুদ্ধিজীবীরা গ্রহণ করেছিলেন।
বৌদ্ধযুগের আগে ও পরে শূদ্র-শ্রেণির অবস্থা কেমন ছিল—সে বিষয়ে ইতিহাস নীরব। সাহিত্যে যেসব দৃষ্টান্ত আছে—একইসঙ্গে তা ভয়ংকর, মর্মান্তিক ও বিতর্কের বিষয়—যেমন, রামায়ণে শম্বুক হত্যা, মহাভারতে একলব্যর উপাখ্যান-কী আজকের ভাষায় বারানাবত হত্যাকাণ্ড… বৌদ্ধ সাহিত্য ‘নির্বাণ’ তত্ত্ব অনুসারী হওয়ায়, সেখানে জাত-পাতের মর্মান্তিক ঘটনা নেই, কিন্তু জাত-পরিচয় ছিল এবং তার রাজনৈতিক প্রকাশের সাক্ষ্য ইতিহাস বহন করছে, অশোকের রাজত্বকালের ইতিহাস—জাত-ধর্ম নিরপেক্ষভাবে ‘সব মানুষই আমার সন্তান’—এরকম কথা আর কোনও রাজা বলেছেন কি-না আমাদের জানা নেই।
শত্রুর শত্রু আমার মিত্র…
কিন্তু বর্ণ-সংস্কৃতির চোরা স্রোত (বিদ্বেষ) যে ধর্ম-বিদ্বেষে রূপ পেয়েছিল—এটা অনুমান করা যায়, যা ভারতের ইতিহাসে ‘আরবদের সিন্ধু বিজয়’ (অষ্টম শতকের শুরুর দিকে) পর্বে অনুমানের সত্যতা প্রকাশ পেয়েছে। হিন্দু ও বৌদ্ধের রাজনৈতিক শত্রুতা বৃদ্ধির—(সম্ভবত) ‘সিন্ধুর পরাজয়’ প্রথম সামরিক দৃষ্টান্ত। কিন্তু মনে রাখতে হবে ব্রাহ্মণ-বংশীয় সিন্ধুর রাজা (>হিন্দু রাজা) দাহির সেন-এর সঙ্গে মহম্মদ-বিন-কাশিমের যুদ্ধে কাশিমকে ওই অঞ্চলের আদিবাসীরাও (আধুনিক ভারতে উপজাতি) সহায়তা দিয়েছিল। এবং এক্ষেত্রে আমাদের মনে পড়তে পারে, মহারাষ্ট্রের ভীমা নদীর তীরে কোরেগাঁও-এর ইতিহাস—উনিশ শতকের আগে-পরে ওই অঞ্চলে ইংরেজরা তাদের ক্ষমতা বিস্তারের কাজ চালিয়ে যাচ্ছিল এবং মাহার জাতি (শূদ্র/তপশিলি) তাদের উপর পেশোয়াদের (=বর্ণহিন্দু) নিপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ তৈরি করতে চাইছিল—এই চাওয়াকে কাজে লাগিয়েছিল ইংরেজরা। মাহার যুবকদের ফৌজি-প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় এবং ইংরেজরা মাহার-সেনার সহযোগিতায় এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে পুনে অঞ্চলে তাদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করে। আরও একটা তথ্য আমাদের উল্লেখ রাখতে হবে, তা হলো আদিবাসীরাও (শূদ্র রূপে চিহ্নিত নয়) তখন (দাহিরের সময়) বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেছে, আমাদের এই অনুমান বর্তমান তথ্যের নিরিখে।
হিন্দু-বৌদ্ধদের মধ্যে ধর্মীয় বিদ্বেষ—যে কোন পর্যায়ে গিয়েছিল—তা আজ বলা মুশকিল। কিন্তু, বিদ্বেষ প্রশমনের একটি পদ্ধতি পরস্পরকে গ্রহণ করা, বৌদ্ধধর্মে নানা দেবদেবীর পূজাঅর্চনা এর উদাহরণ এবং পরবর্তীকালে গৌতম বুদ্ধকে হিন্দুর অবতার হিসাবে গণ্য করা—আর একটি উদাহরণ। সংঘর্ষ-সমন্বয়ের তত্ত্ব-অনুসারে এটা ঘটলেও প্রাণহানির ঘটনা বেশি হওয়ায় বৌদ্ধ-জনগণ প্রাণভয়ে হয় পালিয়েছে, না-হয় প্রাণ বাঁচাতে ইসলামে আশ্রয় নিয়েছে… তখন শাসকের ধর্ম ইসলাম। হয়তো এ কারণে বাঙালি-হিন্দুরা বাংলার মুসলমানকে ‘নেড়ে’ (<ন্যাড়া, মুণ্ডিতমস্তক) আখ্যা দিয়েছে।
আমরা যদি ইতিহাসে ‘ষোড়শ মহাজনপদ’-এর মানচিত্র দেখি, দেখব, পরস্পর যুদ্ধ-বিগ্রহে রত এক ভারতবর্ষ, যে দারায়ুসের সময় থেকে আলেকজান্ডারের আক্রমণ পর্যন্ত, কেবল আক্রান্তই হয়েছে, তারপর আবার আক্রান্ত হতে দেখব—মহম্মদ-বিন-কাশিম থেকে ইংরেজ আমল পর্যন্ত। প্রায় বারোশো বছর… এই বারোশো বছরে ‘হিন্দু রজনীতি’র ইতিহাস যেমন শাসক-সহায়কের ইতিহাস হয়ে উঠেছে, তেমনই উচ্চবর্ণের রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষা তাদের অনেককেই ইসলামে, খ্রিস্টে ধর্মান্তরিত করেছে, আবার শূদ্র-শ্রেণির ইতিহাস—হিন্দুর ধর্মপরিচয় থেকে বেরিয়ে যাওয়ার ইতিহাস। কিন্তু উভয়পক্ষ তাদের অতীতের ‘আত্মপরিচয়’ ভুলতে পারেনি। সন্দেহ নেই বিষয়টি সমাজ-মনস্তত্ত্বের জটিল বিষয় হয়ে আছে। হিন্দু সমাজ-সংস্কৃতিতে শূদ্র আজও ভিত্তি-স্বরূপ কিন্তু ধর্মান্তরিত শূদ্র (বৌদ্ধ-মুসলমান-খ্রিস্টান) ও অ-শূদ্র (মূলত আদিবাসী ও অন্যান্য ধর্মান্তরিত) হিন্দুমানসে ‘শত্রু’ হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। এবং ইংরেজ আমলে শাসকের রাজনীতিতে ‘ভেদনীতি’ চর্চার ক্ষেত্রে এরা—এক মুসলমান ছাড়া আর সকলে নতুন এক আত্মপরিচয়ে পরিচিত হয়েছে—‘দলিত’। গড়ে উঠেছে দলিতমানস অন্তঃসারে যা রাজনৈতিক ও সাহিত্যিক—এই মানসের গড়ে-ওঠা ‘ভীমা-কোরেগাঁও’তে (১৮১৮ খ্রিঃ) শুরু হয়েছিল বলে মনে করা যেতে পারে। এবং পুরো ব্রিটিশ শাসনে তার বিকাশ ঘটেছে মহারাষ্ট্রে: জ্যোতিবা ফুলে, বি. আর. আম্বেদকর; দক্ষিণ-ভারতে শ্রীনারায়ণ গুরু, ই. ভি. রামস্বামী; বঙ্গদেশের গুরুচাঁদ ঠাকুর—এঁদের হাতে। বিশ শতকে এই রাজনীতির তাত্ত্বিক ও কর্মী-সংগঠক হলেন—বাবা সাহেব আম্বেদকর।
এই সময়ে হিন্দু রাজনীতি ‘দলিত’-এর প্রতিশব্দ হিসাবে ‘হরিজন’ তৈরি করে। মনে রাখতে হবে, উনিশ শতকে ‘দলিত রাজনীতি’র যেমন বিকাশ ঘটেছে, তেমনই হিন্দু ধর্মে তৈরি হয়েছে সংস্কার আন্দোলন, অর্থাৎ রাজনীতিও হয়েছে সংস্কারমুখী—‘হরিজন’ সে-ই সংস্কারজাত শব্দ।
মানুষ রাজনৈতিক অ্যানিম্যাল!
ইতোমধ্যে ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতার রাজনীতি হিন্দু-মুসলমানে ভাগ হয়ে গেছে (১৯২০ থেকে ১৯৩৪ ঘন ঘন দাঙ্গা হয়েছে—১৯২৩ থেকে ’২৬—এই তিন বছরে ব্রিটিশ ভারতে ৭০টির বেশি দাঙ্গা সংঘটিত হয়, যেন পরস্পরের বিরুদ্ধে ‘স্বাধীনতা যুদ্ধ’), দলিত রাজনীতিও বেশ সাকার হয়ে উঠেছে। এই প্রেক্ষিতে ঘরে-বাইরে বেশ চাপে পড়েছে ব্রিটিশের রাজনীতি (=সাম্রাজ্যবাদ)। এবং অভ্যন্তরীণ শান্তি বজায় রাখতেই তৈরি হয়—‘ভারত শাসন আইন, ১৯৩৫’। এই আইন মোতাবেক নির্বাচন উপলক্ষে ব্রিটিশ বিরোধী ভারতের রাজনীতিতে মুসলমান ও দলিত/হরিজন পৃথক পৃথক রাজনৈতিক-সত্তা হিসাবে স্বীকৃতি পেল। অর্থাৎ ব্রিটিশ ভারতের রাজনীতি তিন ভাগে ভাগ হলো অফ দ্য রেকর্ড (?)—হিন্দু রাজনীতি; দুই, মুসলমান রাজনীতি; এবং তিন, দলিত/হরিজন রাজনীতি…
দলিত-রাজনীতির প্রথম প্রকাশ যদি ‘ভীমা-কোরেগাঁও’কে ধরা হয়, তা হলে প্রায় ১১০ বছর পর দলিত-চেতনার প্রথম প্রকাশ্য বিদ্রোহ ‘মনুস্মৃতি’ পোড়ানো, ১৯২৭ খ্রিঃ ২৫ ডিসেম্বর; নেতৃত্ব দেন বাবা সাহেব আম্বেদকর। এই যে দলিত-চেতনার বিদ্রোহ—ব্রিটিশের ঔপনিবেশিক রাজনীতির নিরিখে একে আন্তর্জাতিকও বলা যেতে পারে, যদিও সেক্ষেত্রে যুক্তি সাজানো একটু মুশকিল কিন্তু এটা যে ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরুদ্ধে ‘স্বাধীনতা যুদ্ধ’ এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই ।
কিন্তু উনিশ শতকে উপ্ত হয়ে ব্যাপ্ত হয়েছে আর-একটি বিদ্রোহচেতনা যা তার জন্মলগ্ন থেকেই আন্তর্জাতিক এবং একটি রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে দেশে দেশে ছড়িয়ে পড়েছে, আমাদের দেশেও—বলা যায় তা দলিত রাজনীতির সমসাময়িক, ‘কমিউনিস্ট রাজনীতি’ হিসাবে তা আখ্যাত।
শত্রুতা মূলক মিত্রতা নীতি
অর্থাৎ ব্রিটিশ আমলেই ভারতভূমিতে পাঁচটি রাজনৈতিক সম্প্রদায়ের কাজকর্ম শুরু হয়েছিল, আগে তিনটির কথা বলা হয়েছে, অফ দ্য রেকর্ড হিন্দু দলটির বিপরীতে ঘোষিতভাবে হিন্দু দলের গড়ে ওঠাও তখন শুরু হয়ে গেছে, এটা চতুর্থ আর পঞ্চম হলো ‘কমিউনিস্ট পার্টি’—ধর্ম তাদের রাজনীতির বিষয় নয় আবার বিষয়ও, ধর্মকে তারা উৎসাদন করতে চায়। তাদের মূল লক্ষ্য শোষণ নিপীড়ন থেকে মানুষের মুক্তি। যে কারণে সাম্রাজ্যবাদী (<ধনতান্ত্রিক) রাজনীতি ও কমিউনিস্ট (>সমাজতান্ত্রিক) রাজনীতি পরস্পরের জাতশত্রু হয়ে আছে। অর্থাৎ এ দেশেও ব্রিটিশের অন্যতম শত্রু তখনকার কমিউনিস্ট পার্টি। কিন্তু—কেবল ব্রিটিশেরই নয়, এ দেশের বণিক শ্রেণিরও ঘোষিত শত্রু কমিউনিস্ট ও সমাজতন্ত্রীরা। এটা বোঝা গেল ১৯৩৭-এর নির্বাচনের পর, কংগ্রেস পরিচালিত বোম্বাই ও মাদ্রাজ সরকার কমিউনিস্ট ও সমাজতন্ত্রীদের উপর পুলিশি সন্ত্রাস কায়েম করে, কেবল এ-ই নয়, ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির যে চলন ব্রিটিশ রাজনীতিতে দেখা যাচ্ছিল, তা-ই দেখা গেল ভারতীয় দলগুলির সরকার চালানোর ক্ষেত্রে—এক কথায় তা ক্ষমতার অপব্যবহার ও দুর্নীতি; দলে ও সরকারে।
পরাধীন ভারতে দেশীয় রাজনীতির এই বিভাজন ‘স্বাধীনতা’র ধারণাটাই বদলে দিয়েছিল—একটা সময়ে স্বাধীনতার মানে ছিল ‘ব্রিটিশ-শাসন’ থেকে মুক্ত হওয়া কিন্তু তা যে আর থাকেনি তা প্রকট করল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (১৯৩৯)—মন্ত্রীসভাগুলি থেকে বেরিয়ে এল কংগ্রেস, কংগ্রেসে ভাঙন… তৈরি হলো ফরওয়ার্ড ব্লক (অক্ষশক্তির পক্ষে, সশস্ত্র পথে ব্রিটিশ তাড়ানো—‘শত্রুর শত্রু আমার মিত্র’), হিটলারকে আদর্শ মেনে গড়ে উঠল ‘হিন্দু নেশন স্টেট’-এর (ইসলামিক নেশন স্টেট ধারণার বিপরীতে) ধারণা তথা সংগঠন (আরএসএস), মুসলিমরা ইংরেজদের পক্ষে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যোগ দিল, ভারতীয় প্রেক্ষাপটে নিরপেক্ষ থাকল কংগ্রেস, স্বাধীনতা আন্দোলন ফিরে পেল তার পূর্বের গতি (১৯৪২, ভারত ছাড়ো আন্দোলন) কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টি এই আন্দোলন থেকে দূরে থাকল তাদের নীতিগত প্রশ্নে (তাদের স্বপ্নের দেশ—সোভিয়েত রাশিয়া আক্রান্ত)… আর দলিত রাজনীতির কোনও অবস্থান পরিবর্তন হয়েছিল কিনা, এ বিষয়ে আমাদের হাতে কোনও তথ্য প্রমাণ নেই।
এক বিচিত্র গণতন্ত্রের প্রেক্ষাপট নির্মাণ
খুব স্পষ্টভাবে স্বাধীনতা অর্জনের রাজনীতি—‘ভারতীয় নেশন স্টেট’-এর ধারণা ভেঙে দিয়ে কমবেশি পাঁচটি রাজনৈতিক সংগঠন তথা ‘গণচেতনা’র জন্ম দিয়েছে। এক, দেশীয় ধনিক-বণিকের দল ‘কংগ্রেস’ (১৮৮৫), মুসলমানদের জন্য ‘মুসলিম লিগ’ (১৯০৬), হিন্দুদের জন্য ‘হিন্দু মহাসভা’ (১৯১৫), শ্রমিক-কৃষক-মেহনতিদের জন্য ‘কমিউনিস্ট পার্টি’ (১৯২০, মতান্তরে ‘২২) ও দলিতদের জন্য ‘ইনডিপেন্ডেন্ট লেবার পার্টি’ (১৯৩৬)—(এই দলগুলি অবশ্য পরবর্তীকালে ভাঙাগড়ার মধ্য দিয়ে যাবে) এর তাৎপর্য হলো (কোনও বিশ্লেষণ না করেই বলা যায়), দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আমরা ‘ভারতীয় জাতিরাষ্ট্র’ নির্মাণের মতো স্বাধীনতা অর্জন করতে পারিনি—ব্রিটিশরাই গড়ে দিল মুসলমানদের জন্য নির্দিষ্ট রাষ্ট্র (=জাতিরাষ্ট্র/পাকিস্তান) আর বাকি ব্রিটিশ-ভারতের চার রকমের ‘গণচেতনা’ সম্পন্ন রাজনৈতিক মানুষের নেতৃত্বকে—‘সার্বভৌম, গণতান্ত্রিক, সাধারণতন্ত্র’ গঠনের স্বাধীন উদ্যোগ নিতে বলে—তারা উপনিবেশের দখল ছেড়ে দিল। অর্থাৎ আমরা স্বাধীনতা পেলাম। অথচ ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে ১৮৫৭ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত ১৪০০০ এর বেশি সাধারণ মানুষ শহীদ হয়েছেন (শহীদদের অভিধান: ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম, pib.gov.in, Posted On: 08 MAR 2019, by PIB Kolkata)। কিন্তু অচিরেই বোঝা গেল, জাতধর্ম নিরপেক্ষভাবেই তাঁদের আবেগ-আশা মূল্যহীন। কেননা, উচ্চবর্গের মানুষ রাজনৈতিক ক্ষমতায় আসীন ও ক্ষমতার ‘উপভোক্তা’ ও তারা আর খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থান-শিক্ষা-চিকিৎসার (= বেসিক নীড্স) নিরিখে আমজনতা যে তিমিরে ছিল, সে-ই তিমিরেই আছে বরং আরও গাঢ় হয়েছে সে-ই অন্ধকার।
এই প্রেক্ষিতে কমিউনিস্টদের দেওয়া স্লোগান ‘ইয়ে আজাদি ঝুটা হ্যায়’ সত্য হয়ে উঠেছে আর ধীরে ধীরে বিকাশমান গণতান্ত্রিক পরিসরে বিকশিত হয়েছে ‘হিন্দু নেশন স্টেট’-এর ধারণা, গঠিত হয়েছে ‘ভারতীয় জনসংঘ’ (১৯৫১) এবং ১৯৫৭ ‘রিপাবলিকান পার্টি অফ ইন্ডিয়া’, ‘দলিত জাতি’র স্বার্থ রক্ষাকারী রাজনৈতিক দল-এর সমাজ-মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ অবশ্যই স্বাধীনতার (= বেসিক নীড্স) প্রশ্নে ‘উত্তর-ঔপনিবেশিক গণচেতনা’কে বিষয় কোরে করতে হবে, এই পরিসরে তা আলোচনায় নিয়ে আসা প্রসঙ্গান্তর হওয়া স্বাভাবিক—এই বিবেচনায় আমরা বিরত থাকছি; আশা করব, পাঠক এই বিষয়ে যথেষ্ট জানা-বোঝার মধ্যেই আছেন।
সংসদীয় গণতন্ত্র ও দারিদ্র্য দূরীকরণনীতি
দারিদ্র্যের সাধারণ অর্থ ‘বেসিক নীড্স’-এর অভাব। আমজনতার এই অভাব পূরণ করবার নীতি গ্রহণ ও রূপায়ণ করতে পারলেই, তাদের স্বাধীনতার স্বাদ দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু তা কীভাবে সম্ভব—এই বিষয়ে আমাদের দেশের সরকারগুলির পক্ষে (কেন্দ্র-রাজ্য) আদর্শগতভাবে কোনও কর্মসূচি নেওয়া সম্ভব হয়নি। আর এই পরিসরে সমাজতান্ত্রিক আদর্শ ও হিন্দু জাতীয়তাবাদী আদর্শ প্রচার আমজনতার মধ্যে নতুনভাবে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তোলে—প্রথমটির বিশ্বাস: সমাজ-রাষ্ট্রের বৈপ্লবিক পরিবর্তন না ঘটিয়ে, কৃষক-মেহনতি মানুষ স্বাধীন হতে পারে না; আর দ্বিতীয়টি এই বিশ্বাস গড়ে তোলে যে, পাকিস্তানের মতো হিন্দুজাতি-রাষ্ট্র কায়েম না করতে পারলে স্বাধীনতা অধরা থেকে যাবে।
প্রথম ‘আদর্শ’ দেশে ‘নকশাল পন্থা’র জন্ম দিয়েছে। তার ঘোষিত প্রতিপক্ষ এক কথায় ‘বুর্জোয়া শ্রেণি’ (=রাষ্ট্র/ভোগবাদী উচ্চ-মধ্যবিত্ত) আর দ্বিতীয় ‘আদর্শ’ থেকে জন্ম নিয়েছে ‘হিন্দু সন্ত্রাসবাদ’ তার ঘোষিত প্রতিপক্ষ মুসলমান—শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘দাঙ্গার ইতিহাস’ থেকে দেখা যাচ্ছে—১৯৬৮ থেকে ১৯৭৫ পর্যন্ত ২৬৪২টি দাঙ্গার ঘটনা ঘটেছে! মৃত্যু ১৪৭০; আর ‘আজকাল ওয়েবডেস্ক’ (৪ মে ২০১৮)-এর প্রতিবেদন থেকে জানা যাচ্ছে—‘ইতিহাস বলছে, ১৯৬৭ থেকে ১৯৭৫ সালের মধ্যে নকশালবাড়ি আন্দোলনে মৃত্যু হয়েছিল দশ হাজারেরও বেশি মানুষের।’ পৃথকভাবে দলিত-নিগ্রহ তথা হত্যার কোনও পরিসংখ্যান (ওই সময়ের প্রেক্ষিতে) আমরা পাইনি! কিন্তু সাম্প্রতিক অতীতের খবর (যা ‘দলিত নিগ্রহ’ শব্দ দুটি দিয়ে গুগলে সার্চ করলে পাওয়া যাবে) থেকে অনুমান করা যায়, বিশেষ করে ‘তফশিলি জাতি-উপজাতি নির্যাতন রোধ আইন, ১৯৮৯’—এই অনুমানের পক্ষে একটি দিশা দিতে পারে।
এইসব তথ্যের ভিত্তিতে অনুমান করা যেতে পারে যে, একটি ‘সাংবিধানিক জাতি’ হিসাবে ভারতীয় জনগণকে গড়ে তোলার ক্ষেত্র প্রস্তুতির জন্য কংগ্রেস ১৯৭৬ সালে সংবিধানের প্রস্তাবনায় ‘সমাজতান্ত্রিক’ ও ‘ধর্মনিরপেক্ষ’ শব্দ দুটি তত্ত্ব হিসাবে গ্রহণ করেছিল। কিন্তু ‘মিশ্র অর্থনীতি’কে ধনতন্ত্রের আগ্রাসন (= দুর্নীতি ও স্বজনপোষণ) থেকে তখনকার সরকার যেমন মুক্ত রাখতে পারেনি, তেমনই ‘ছদ্ম ধর্মনিরপেক্ষতা’র রাজনীতিও প্রকট হয়ে পড়েছিল। কমবেশি ২৫ বছর (১৯৫১-’৭৫) ওই নেতিবাচক প্র্যাকটিসের পর কংগ্রেসের বিশ্বাসযোগ্যতা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। ১৯৭৭-এর নির্বাচনে কংগ্রেস সরকারের পতনই তার অন্যতম কারণ হিসাবে দেখা যেতে পারে। উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, এই সময়েই হিন্দুত্ববাদী সংগঠনের প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ সহযোগিতায় গঠিত হয় ‘জনতা পার্টি’; এবং ১৯৮০-তে দল ভেঙে ‘ভারতীয় জনতা পার্টি’ তৈরি হয়। ‘এক্সক্লুসিভ’ হিন্দুত্ববাদী দল হিসাবে তার আত্মপ্রকাশ এবং মতাদর্শগতভাবে সে অ্যান্টি-কমিউনিস্ট, অ্যান্টি-মুসলমান এবং দলিত বিদ্বেষী— এক কথায় একটি ‘অসাংবিধানিক’ দল হিসাবে তাকে চিহ্নিত করেছেন অনেকেই। এখানে একটি প্রশ্ন রেখে আমরা পরের কথায় ফিরবো, প্রশ্নটি হলো: এটা কীভাবে সম্ভব?
ভারতের দুর্বল গণতন্ত্র ও সংখ্যালঘুর জোট সরকার
ভারতের গণতন্ত্র পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় এবং সম্ভবত সবথেকে দুর্বল গণতন্ত্র; কারণ, তার জনগণ নানা ভাবে বিভাজিত, গণতান্ত্রিক ঐক্য নেই (নীতিমালার সে-ই এক বাণ্ডিল লাঠির গল্প তুলনা হতে পারে)। আমাদের আলোচনায় আসা কমিউনিস্ট পার্টি ও রিপাবলিকান পার্টির কথাই ধরা যাক—কমিউনিস্ট পার্টি ভাঙতে ভাঙতে তার নানান গ্রুপ—অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদ আর বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে লড়াইতে নিজেরাই ঐক্যবদ্ধ নয়, এমনকি অনেক সময় নিজেরাও বুর্জোয়াদের মতোই প্রায় আচরণে। একই ব্যাপার রিপাবলিকান পার্টির ক্ষেত্রে, ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরুদ্ধে ঐক্যটাই তো মজবুত হতে পারল না!
কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে, বুর্জোয়া পার্টিও-কিন্তু ভেঙেছে! ভেঙেছে, কিন্তু ভাঙন কমে এসেছে, তার কারণ বোধহয় এই যে, অর্থনীতি রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করছে খোলাখুলিভাবে। এখানে একটা জিজ্ঞাসা আছে—কমিউনিস্ট ও দলিত উভয় রাজনীতি—শোষণ নিপীড়ন-নিগ্রহ থেকে মানুষকে মুক্ত করতে চায়, তা হলে, নিজেদের মধ্যে এত ভাঙন কেন, কেনই-বা কমিউনিস্ট ও দলিত ভাবুকেরা পরস্পরের মধ্যে ঐক্য গড়ে তোলেননি?
এর উত্তর পাওয়া যাবে উভয় রাজনীতির দৃষ্টিভঙ্গি ও লক্ষ্যের মধ্যে। মনে রাখতে হবে, ঔপনিবেশিক শাসন এ দেশে কায়েম না হলে, দলিত-শ্রেণির রাজনৈতিক উত্থান কবে হতো, আদৌ হতো কিনা বলা মুশকিল। এই উত্থানের জন্য ব্রিটিশ ধনতন্ত্রের প্রতি দলিত ভাবুকদের আনুগত্য থাকবে, এটা স্বাভাবিক। কিন্তু ভারতের ব্রাহ্মণ্যবাদী ধনতান্ত্রিক রাজনীতি তার জন্মলগ্ন (অন্তত আড়াই হাজার বছরেরও আগে বৌদ্ধ জাতকের সেরিবান-সেরিবার গল্প মনে রেখে) থেকেই সমাজকে কেবল ‘কর্মে ভাগ’ (Division of Labour) করেনি, কর্মী-সমাজেকেও ভাগ করে (Division of Labours) রেখেছে— এটা দলিত রাজনীতির দৃষ্টিভঙ্গি, তার লক্ষ্য ‘কাস্টলেস সোসাইটি’ গঠন, যেখানে সব মানুষের ‘কমন রাইট্স’ (= সামাজিক মর্যাদা) থাকবে। অর্থাৎ রাজনীতিটা কাস্ট স্ট্রাগলের বিষয়। অন্য দিকে কমিউনিস্ট রাজনীতির দৃষ্টিভঙ্গিও ‘ক্লাস স্ট্রাগল’ যার আশু লক্ষ্য ‘সমাজতন্ত্র’ প্রতিষ্ঠা। যেখানে থাকবে সব মানুষের সম্পদের সমান ভাগ, ইক্যুয়াল শেয়ার।
দৃষ্টিভঙ্গির এই ভিন্নতা হেতু কমিউনিস্টরা ধনতন্ত্রকে নির্বিশেষ দেখেন, কিন্তু দলিত ভাবুকদের দৃষ্টিতে ভারতের ব্রিটিশ ধনতন্ত্র নির্বিশেষ নয়, বিশেষত এ কারণে যে—‘Casteism is Contrary to Capitalism’। এর অর্থ এ দেশে ধনতন্ত্র জাত-তন্ত্র বিকাশের পরিপন্থী হয়ে দেখা দিয়েছে। অর্থাৎ ধনতন্ত্রের বিকাশ ঘটলে, জাত-তন্ত্র থাকবে না। এই বিশ্বাস। তা যদি হয়, ধনতন্ত্রের চূড়ান্ত বিকাশ শ্রেণি সংগ্রামকে বিপ্লবের পথে নিয়ে যাবে—কমিউনিস্টরা তো এ রকমই বিশ্বাস করেন!
তা হলে দেখা যাচ্ছে, একটা বোঝাপড়া হতে পারত—সেটা সম্ভব ছিল নেতৃত্বের জাত-পরিচয়কে অস্বীকার করবার সংস্কৃতি গড়ে তোলার মাধ্যমে, বিশেষ করে নির্বাচনের রাজনীতিতে এটা সম্ভব ছিল। আর দলিত ভাবুকেরা এটা ভাবতে পারতেন যে, বিভাজনের রাজনীতি ছাড়া ধনতন্ত্র বাঁচতে পারে না—তাঁদের যতটা উন্নতি তা ওই ভেদনীতি থেকেই এসেছে। এটা সত্য। এটা মেনে নিলে—ভেদই চিরন্তন মানতে হয়। এই অনুষঙ্গে মনে পড়ছে, চায়ের ঠেকে শোনা একটি কথা, কেউ একজন উদাহরণ দিয়ে বলেছিলেন যে—ধনতন্ত্র বাঁচিয়ে রাখে মারার জন্য; যেমন, ব্রয়লার মুরগি পালন। যাই হোক, ব্রিটিশ-উত্তরকালে উভয় রাজনীতির যে বিভাজন, তা ওই ধনতান্ত্রিক রাজনীতির কারসাজি মাত্র। বিপরীত দিক থেকে বলা যায়, ধনতান্ত্রিক মূল্যবোধের বিরুদ্ধে, উভয় রাজনীতি তাদের স্ব স্ব ক্ষেত্রে নতুন অর্থনৈতিক মূল্যবোধ গড়ে তুলতে যত্নবান ছিল না। যত্নবান ছিল না—এ কথা আমরা কীসের ভিত্তিতে বলছি ?
অথবা সংরক্ষণের রাজনীতি
ভিত্তিটা হলো এই যে, ব্রিটিশ রাজনীতির ভেদনীতি ও অফ দ্য রেকর্ড দুর্নীতি ব্রিটিশ-উত্তর শাসক ও শাসক-সহায়ক শ্রেণি তাদের রাজনীতিতে বহাল রেখেছে। আমাদের আলোচ্য বিষয়ে ভেদনীতির প্রাসঙ্গিক উদাহরণ হলো ‘সংরক্ষণ নীতি’। এই নীতি ‘সাংবিধানিক’ কিনা তা নিয়ে আর্টিকেল ১৪-র নিরিখে বিতর্ক আছে, বিশেষ করে শিক্ষা ও চাকরির ক্ষেত্রে। ‘বিতর্ক’ সরিয়ে রেখে আমরা ‘সংরক্ষণ’কে তত্ত্ব হিসাবে গ্রহণ করে ‘সংরক্ষণের রাজনীতি’টা যে ঠিক কী, বুঝতে চাইব। কেননা, ‘রাজনীতির সংরক্ষণ’ ব্রিটিশ আমলে যা শুরু হয়েছিল, তা আজও চলছে, মোটামুটি বোধগম্য কিন্তু জাত-গোষ্ঠি ‘সংরক্ষণের রাজনীতি’ যেন অস্তিত্বের সংকট-ই ডেকে আনছে, যেমন ‘ইয়্যুথ ফর ইকুয়ালিটি’র সংরক্ষণ-বিরোধী আন্দোলন বা সংরক্ষণের পক্ষে জাঠ আন্দোলন—এক্ষেত্রে নতুন কোনও বয়ান রচনা না কোরে, ‘সংরক্ষণের রাজনীতি’ বিষয়ে বর্তমান এই আলোচনার আলোচক-কৃত অপর এক লেখার বয়ান/ভাবনাকে অনুসরণ করব: ‘সংরক্ষণ’—এই শব্দটির মধ্যে প্রচ্ছন্ন রয়েছে, অস্তিত্বের প্রশ্ন, সংকটাপন্ন অস্তিত্বকে অবলুপ্তির কবল থেকে রক্ষা করার প্রস্তাবনা। যেমন সংরক্ষিত বনাঞ্চল কিংবা বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের জন্য অভয়ারণ্য। এইসব সংরক্ষণের সঙ্গে অবশ্য মানবজাতির অস্তিত্ব রক্ষার বিষয়টি ওতপ্রোত জড়িয়ে আছে। কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে—সংরক্ষণের বিষয়টি ভারী অদ্ভুত। কেননা, মানুষই সংরক্ষিত করছে মানুষকে। সামাজিক মানুষ এক্ষেত্রে দুই ভাগে বিভক্ত—এক ভাগে সংরক্ষক অর্থাৎ রাষ্ট্রক্ষমতার কেন্দ্রে থাকা মানুষ—রাজনৈতিক মানুষ, যারা উচ্চবর্গ, উচ্চবর্ণ বা নিপীড়ক-রূপে চিহ্নিত। অন্যভাগে সেইসব মানুষ, যারা প্রান্তিক—নিম্নবর্গ, নিম্নবর্ণ বা দলিত—এক কথায় নিপীড়িত-রূপে পরিচিত।
এই মানুষগুলোর বিপন্নতার স্বরূপ—প্রথমত, খাদ্য ও বাসস্থানের অভাবজনিত বিপন্নতা, যে বিপন্নতায় বাঘ-হাতি লোকালয়ে অনুপ্রবেশ কোরে জনজীবনকে বিপন্ন করে—তেমনই এরা ‘সিভিল সোসাইটি’র মধ্যে ঢুকে পড়ে অশান্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়, আর ‘সংরক্ষণ’-এর প্রশ্নটা উঠেছে ঠিক এইখানে; দ্বিতীয়ত, স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসেবে তার শিক্ষা, চিকিৎসা ও কাজের অভাবজাত বিপন্নতা যা তাকে অধিকারের প্রশ্নে ‘বিদ্রোহী’ করে তুলতে পারে। অতএব সংরক্ষণের ঘেরাটোপে তাকে নিয়ে আসা জরুরি (‘মানবিক রাজনীতির ধারণা’, সুরঞ্জন প্রামাণিক)।
সংরক্ষণ বিষয়ক সে-ই রচনায় অধিকারের ব্যাপারটা বুঝতে গিয়ে, মণ্ডল কমিশনের রিপোর্ট-এর সঙ্গে দেওয়া একটি সারণি দেখতে হয়েছিল। যার শিরোনাম ছিল—বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর অধিকারের হার (শতকরা হিসাবে)—১৯৮০ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে প্রকাশিত ওই রিপোর্ট অনুসারে: তৎকালীন মোট জনসংখ্যার ১৫ শতাংশের অধিকারে ছিল ৯২ শতাংশ জমি ও ৮৭ শতাংশ চাকরি এবং মোট জনসংখ্যার ৮৫ শতাংশের অধিকারে ছিল ৮ শতাংশ জমি ও ১৩ শতাংশ চাকরি। অতএব, অধিকার সাপেক্ষে, নিম্নবর্গের অবস্থান ও অবস্থা সহজেই অনুমেয়।
এই তথ্যের ভিত্তিতেই একটা প্রশ্ন ওঠে, তার আগে, ব্যাবসা ও রাজনীতিতে ‘অধিকার’-এর শতকরা হার জানানো যাক: উচ্চবর্গের (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য) হাতে যথাক্রমে ৯৪ শতাংশ ও ৬৬ শতাংশ; বাদবাকিটা নিম্নবর্গের (অনগ্রসর জাতি, তপশিলি জাতি/উপজাতি, ধর্মীয় সংখ্যালঘু) হাতে। এসবের ভিত্তিতে লেখা হয়েছিল: অনুমান করা যায় বলেই বিস্ময়ের সঙ্গে একটা প্রশ্ন জাগে—৯২ শতাংশ প্রাকৃতিক সম্পদ, ৯৪ শতাংশ অর্থসম্পদ, ৬৬ শতাংশ রাজনৈতিক ক্ষমতা এবং ৮৭ শতাংশ প্রশাসনিক ক্ষমতা যাদের অধিকারে তারা এই অধিকার কীভাবে কায়েম করল?
সমাজ-ডারউইনবাদ সজোরে ঘোষণা রেখেছে, ‘মেধার জোরে!’ এর উত্তর আমরা খুঁজেছি বেদ-উপনিষদের সমাজবাস্তব থেকে—আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি: মোট জনসংখ্যার ১৫ শতাংশের মেধা ও পেশীশক্তি—উৎপাদনের প্রাকৃতিক উপাদান ও উপায়ের ওপর কায়েম করে রেখেছে সর্বাধিক দখল। আর এ কারণে ১৫ শতাংশকে সংরক্ষণের ‘রাজনীতি’ করা ছাড়া উপায় নেই। তারা মনে করে, নিম্নবর্গের যে যে জাতির অধিকারে মোট ১৩ শতাংশ চাকরি ও ৮ শতাংশ জমি আছে, তাদের মধ্যে তথাকথিত মেধাশক্তিকে সংরক্ষিত কোরে, উচ্চবর্গের ক্ষমতা-কেন্দ্রে ঢুকিয়ে নিতে পারলে, অবশিষ্ট নিম্নবর্গকে পশুবৎ ব্যবহার করা যেতে পারে এবং জনকল্যাণ অর্থনীতির (= রাজনীতির) নামে দান-অনুদান-অনুগ্রহের ‘রাজনীতি’ চর্চার মাধ্যমে নিজেদের অধিকারকে সুরক্ষিত করা সম্ভব।
কিন্তু তা যে সম্ভব নয়, ইতোমধ্যেই তা প্রমাণ হয়ে গেছে—দেশের অভ্যন্তরে এক যুদ্ধকালীন পরিস্থিতি বিরাজ করছে। প্রকাশ্যে আসছে দলিত বিদ্বেষ, মুসলিম বিদ্বেষ। ক্ষমতার কেন্দ্রে ঢুকে পড়া ‘দলিত’ তার পদবি পরিবর্তন করছে—স্বেচ্ছায় বা পারিপার্শ্বিক চাপে বাধ্য হয়ে। বিশেষ করে বাঙালি-দলিত সমাজে এ ঘটনা নজর কাড়ার মতো। এছাড়া নিম্নবর্গের যে ৩৪ শতাংশ রাজনৈতিক ক্ষমতায় আছে, নির্বাচনের সময় তাদের ‘জোট-সঙ্গী’ হওয়ার বিষয়টি বিশ্লেষণ করলেই ব্যাপারটা বোঝা যাবে—বোঝা যাবে ‘কাস্ট স্ট্রাগল’ কীভাবে ‘ক্লাস’ তৈরি করে দেয়!
উপেক্ষিত মানবিক রাজনীতির স্পেস
কিন্তু আমরা অন্য কথাও বলব, তার আগে একটি প্রশ্নের উঁকিঝুঁকি দেখা যাচ্ছে—বিশ শতকের এক পরিসংখ্যান নিয়ে এই একুশ শতকে ‘জাতপাত, অধিকার’-ইত্যাদি বিষয়ে যে যুক্তি আমরা সাজিয়েছি, তাতে কোনও ভুল হচ্ছে না তো? না। ভুল নেই। কারণ, উচ্চবর্গ ও নিম্নবর্গের অনুপাতের হেরফের ঘটবার মতো কোনও ঘটনা ঘটেনি, যতদিন না তা ঘটছে, ততদিন ওই ‘সারণি’ ভ্যালিড! যাই হোক, এবার অন্যকথা: নির্বাচনের সময় সব দলই ‘অসাংবিধানিক’ রাজনীতি করে থাকে (হিংসাশ্রয়ী ভোটপ্রচার, কর্মী সমর্থক/প্রার্থী খুন, ছাপ্পাভোট ইত্যাদি); ক্ষমতা দখলের পর শাসক দলগুলির বিরুদ্ধে প্রায়শই ‘স্বেচ্ছাচার’ বা ‘অগণতান্ত্রিক কার্যকলাপের’ অভিযোগ ওঠে; মানবাধিকার ও সাংবিধানিক অধিকার—দুটি অধিকারই অবহেলার শিকার হয়…
কোনও উদাহরণ রাখা হলো না, আশা রাখি পাঠক তাঁর অভিজ্ঞতা থেকে উদাহরণ চয়ন করতে পারবেন! বরং নতুন অর্থনৈতিক মূল্যবোধ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ‘যত্নবান’ হওয়ার যে কথা আমরা বলেছি, সে-ই ‘স্পেস’-এর কথা বলাটা বোধহয় জরুরি; কেননা, এই চর্চার মাধ্যমে আমাদের সংসদীয় রাজনীতি ‘সংবিধান’ বহির্ভূত হয়ে গেছে! অতএব, ১ নম্বর স্পেস হলো সংবিধানের ‘প্রস্তাবনা’ (বিশেষ করে ’৭৬-এর পর), দুই, আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সনদ (এ-ও একটি সংবিধান)। উভয় রাজনীতি তাদের নির্বাচনের কর্মসূচি তথা প্রতিশ্রুতি—এই দুই সংবিধান-অনুসারে দেওয়া-নেওয়ার কথা ভাবতে পারতো।
বাবা সাহেব আম্বেদকর সংবিধান বিষয়ে যে কথা বলেছিলেন, তা স্মরণে রেখে, দলিত রাজনীতি ‘সংবিধান’কে ‘চ্যাম্পিয়ন’ করার রাজনৈতিক উদ্যোগ নিতে পারতো (এখনও সুযোগ আছে)। একইভাবে ‘গণতন্ত্রের সংগ্রামে জয়ী হওয়া’র লক্ষ্যে কমিউনিস্ট রাজনীতি ‘আইনের শাসন’ কায়েম করবার জন্য উদ্যোগী হতে পারতো, উদাহরণ সৃষ্টির সুযোগ ছিল। পাশাপাশি মানবাধিকার সনদে স্বাক্ষর করা দেশের রাজনৈতিক দল হিসাবে সকলেরই দায় ছিল ‘মানবাধিকার’কে প্রতিষ্ঠা দেওয়া (এখন এটা দাবি হিসাবে কর্মসূচিতে আসতে পারে)।
অথবা ‘প্রতিবেশীকে নিজের মতো ভালোবাসো!’
কিন্তু এই দায় কোনও রাজনৈতিক দলই পালন করেনি। বরং কেউ কেউ সংবিধান বাতিল করার কথাও বলেছেন। অধিকারের প্রশ্নে কেউ আর্টিকেল ১৪-কেই অপ্রাসঙ্গিক মনে করেন, ওই মণ্ডল কমিশনের রিপোর্টের নিরিখে, যেখানে উচ্চবর্গ ও নিম্নবর্গের অধিকারেই রয়েছে আকাশ-পাতাল ফারাক সেখানে ‘ইক্যুয়াল’ শব্দের যে-কোনো রূপ-ই বিসদৃশ। অনেকেই সংবিধানের প্রসঙ্গ তুলেছেন, কিন্তু তাকে ব্যবহার করতে পারেননি। এ দেশে সাংবিধানিক কর্তব্য পালন করতে গিয়ে ‘হত’ হতে হয়! ‘মানবাধিকার’-এর দাবি তুললে, তা হয়ে যায় রাষ্ট্রদ্রোহ! গণতান্ত্রিক অধিকার দাবি করলে, তা সরকার বিরোধিতার নামান্তর! এসব ভয়ংকর ব্যাপার-স্যাপার। অতএব নীরব থাকাই ভালো। কারণ, কেউ কেউ বলেন, আমরা একইসঙ্গে—যে যখানেই বাস করি না কেন, সে-ই স্পেসটা তিনভাগে ভাগ হয়ে, একে অন্যের ভেতর ঢুকে আছে—হিন্দু-ভারত, মুসলমান-ভারত আর দলিত-ভারত। চাকরি ক্ষেত্রে এটা সংঘগতভাবে খুব ভালো বোঝা যায়। আর বোঝা যায় প্রতিবেশীর সঙ্গে যুদ্ধ-সম্ভাবনায়।
‘কমন রাইট্স’ ও ‘ইক্যুয়াল শেয়ার’-এর যে ধারণা আমাদের রাজনীতিতে ছিল, আছে, তার বিরোধ থাকবে কিনা, এই বিষয়টি নিয়ে রাজনীতিকরা ভাবতে পারেন, এই ভাবনার প্রস্তুতি হিসাবে ‘আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সনদ’-কে অবশ্য-চর্চার বিষয় করা জরুরি, কেননা, এই সনদ যুদ্ধের বিরুদ্ধে এক প্রস্তাবনাও বটে! এবং সংবিধান—একটি স্বাধীন দেশ গঠনের দিশা! ইতোমধ্যেই ‘সংবিধান’ হাতে অধিকার-আন্দোলন শুরু হয়েছে… এক মানবিক ভারত তথা সাংবিধানিক জাতীয়তাবাদ বা শক্তিশালী (সমাজতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ যা অধিকার-বৈষম্যকে হ্রাস করতে পারে) গণতন্ত্র গড়ে তোলা সম্ভব কিনা রাজনৈতিক দলগুলি তা ভাবতে পারে! বিশেষ করে ক্লাস ও কাস্ট স্ট্রাগলের নিরিখে যারা রাজনীতি করছেন। মনে রাখতে হবে, উভয় রাজনীতির জন্ম ব্রিটিশ শাসনের পরিবেশে… কে বলতে পারে ‘জন্মচিহ্ন ক্যানসারে’ বদলে যাচ্ছে কিনা!