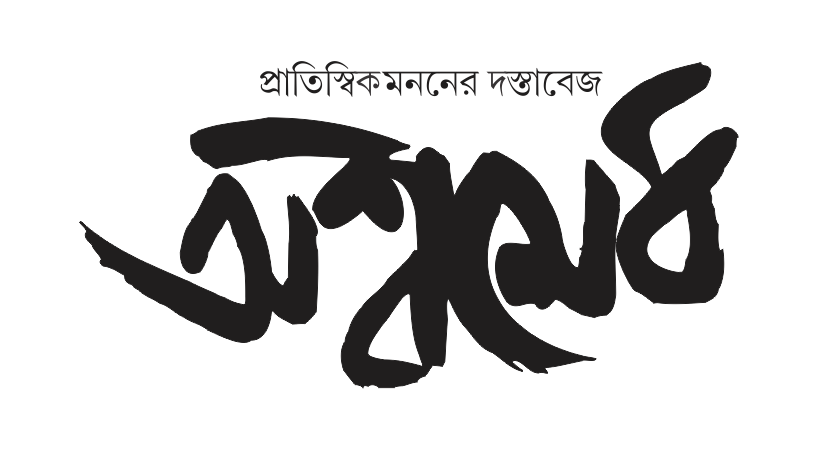যে সময়ের মধ্য দিয়ে আমরা চলেছি তার বৈশিষ্ট্যগুলোকে যদি চিহ্নিত করতে চাই, তার চোরাস্রোতগুলোকে যদি চিনে নিতে চাই তবে একটি শব্দ প্রথমেই টুপ্ করে কাগজের ওপর এসে পড়ে—’প্রযুক্তি’—যে সঙ্গে নিয়ে আসে এক দীর্ঘ নেতি-র মিছিল—পণ্যসংস্কৃতি, বাজার-অর্থনীতি, বিত্ততন্ত্র, বৈদ্যুতিন মাধ্যম; সর্বগ্রাসী যান্ত্রিকতা, সদ্বাস্তবতা, বিচ্ছিন্নতা…। আক্রান্ত আঞ্চলিক ভাষা-সংস্কৃতি, স্মৃতি, স্থায়িত্ব, সূক্ষ্মতা, আত্মিক স্থৈর্য… (ক্রমশ)।
এই যে দৃশ্যমান ও অদৃশ্য প্রভাবগুলোর স্বরূপ কী এবং তার মোকাবিলা করতে কবিতা ও লিটল ম্যাগাজ়িনের দীর্ঘস্থায়ী ভূমিকা ও গুরুত্ব কী কী তার আলোচনার জন্য এই পরিসর যথেষ্টই কম। তবুও, উল্লেখমাত্র হলেও, এই বিষয়টি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ অথচ অনালোচিত বলেই এইমাত্র উদ্যোগী হলাম।
যেমন, ইতোমধ্যে, এই প্রভাবেই হয়তো বা, আমরা দেখতে পাচ্ছি সাহিত্য-শিল্পের নান্দনিক মানের অবনমন ঘটছে, সূক্ষ্মতার ঘনত্ব কমে যাচ্ছে, অন্তর্নিহিত মানমাত্রার পরিবর্তে মোড়কের অসমানুপাতিক গুরুত্ব বাড়ছে। কেননা প্রযুক্তি অন্তরঙ্গ থেকে বহিরঙ্গেই আমাদের বেশি নির্ভর করতে শেখায়। যেমন, প্রযুক্তি পছন্দ করে ত্রুটিহীনতা তথা পরোৎকর্ষ। ‘সিক্স সিগমা’ বা ‘জ্যাম’ জাতীয় উৎকর্ষ-সংস্কৃতির জ্ঞান, কর্পোরেট ছাড়িয়ে মাঠে-ঘাটেও নেমে এসেছে। কেননা দর্শনেও আমরা উৎকৃষ্ট সাম্যবাদী সমাজে ত্রুটিহীন মানুষকে দেখতে চাই মার্ক্সীয় কল্পরাজ্যে। সম্পূর্ণতার এই যে কল্পরাজ্য যা মুক্তিকামী ও সংবেদী সাধারণের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গির অসংগতি ও হতাশার সৃষ্টি করে। কবিতা তার চিরকালীন অপূর্ণতার প্রতীকী নিয়ে প্রযুক্তির বিপরীতে আমাদের সংবেদকে জীইয়ে রাখবে, রোবটিকতার বিপরীতে মানবতার আদি ও অকৃত্রিম অ্যাম্বাসাডর হিসেবে, ত্বরণ বাতিক, লাগাতার কার্যকারিতা ও সমঝোতার ঊর্ধ্বে বৈচিত্র্যের তথা রকমারিত্বের পৃষ্ঠপোষক, সমানুভূতি ও সহিতত্বের এক জীবনাদর্শ সঙ্গে করে।
চমক বা রোমাঞ্চ বা শিহরনের ঝোঁক আর এক উপহার প্রযুক্তির। আমরা হিংসা, আতঙ্ক, জখম, আচরণ, সম্পর্ক এমনকি গবেষণাতেও তার সন্ধান করছি। কবিতা এই হুজুকের বিপরীতে আমাদের পারস্পরিক শ্রদ্ধা, বিস্ময়, পরমতসহিষ্ণুতা ইত্যাকার চিরকালীন সংবেদকে রক্ষা করছে, করবে।
পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে বাংলা ভাষার ধারা বহনের যে সমস্যাকে সংকট বলে কেউ কেউ দেখেন, অন্যেরা কেউ কেউ তা মানতে রাজী নন। শহুরে মধ্যবিত্ত বিশ্বায়িত প্রতিযোগিতায় তার স্থানাঙ্ক টিকিয়ে রাখবার বা উন্নত করবার আপ্রাণ চেষ্টায় যে প্রজন্মকে রেখে যাচ্ছে আত্মপরিচয়ের সংকটে, যার ফলাফল আমরা দেখতে পাচ্ছি: আত্মহত্যা, স্নায়ুবৈকল্য, হতাশা এবংবিধ রোগের প্রাদুর্ভাবের মাধ্যমে। কিন্তু গ্রামবাংলার বা মফস্সলের অধিক সংখ্যক মধ্যবিত্ত ও শহুরে নিম্নবিত্তরা এখনও প্রযুক্তির স্বয়ংক্রিয় নাগালের মধ্যে এসে পৌঁছোয়নি। আর তারাই শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির ধারা বহন করে যাচ্ছে, যাবে। বিশ্বায়নের ফলে আঞ্চলিক ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতির যে ক্ষতি হয়ে চলেছে তার রক্ষা জেনে বা না-জেনে লিটল ম্যাগাজ়িনই বিচ্ছিন্নভাবে তবু একত্র ফলে করে চলেছে।
‘প্রগতি’ শব্দটির বা তার ধারণার আমদানি প্রযুক্তির হাত ধরেই। সভ্যতাকে বিশিষ্টায়িত করা হয় এই ধারণাতেই। হ্বিটগেনস্টাইনের মতো দার্শনিকরা এর বিপরীতে সূক্ষ্মদর্শিতা, স্বচ্ছতা ইত্যাদির গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর মত হলো, প্রগতি ব্যাপারটি উল্লম্ব—তার পরিবর্তে চাই ‘পরিবর্তন’ যা অনুভূমিক, ব্যাপ্ত।
প্রযুক্তির হাত ধরে বৈদ্যুতিন মাধ্যমের প্রচণ্ড রমরমা। এর প্রতীক সাঙ্ঘাতিক। এরা শুধু আমাদের পাঠ, স্মৃতি, স্থায়িত্ব, সূক্ষ্মতাতেই স্লো-পয়জন করছে না—এরা বিকৃত করছে ভাষাও। প্যাথলজির রমরমার সঙ্গে সঙ্গে অত্যধিক নির্ভরতার কারণে চিকিৎসকদের যেমন অভিজ্ঞতা ও প্রজ্ঞার চর্চা কমে আসছে তেমনি বৈদ্যুতিন মাধ্যম আমাদের স্মৃতির সম্পদকে অগ্রাহ্য করে ইতিহাসকে মৃত্যুমুখে ঠেলে দিচ্ছে। এই ক্ষেত্রে লিটল ম্যাগাজ়িনের, গ্রুপ থিয়েটারের ভূমিকা অনস্বীকার্য।
বাজার-সংস্কৃতি আমাদের সম্পর্ককে কার্যকারিতায় পর্যবসিত করছে। বর্তমান প্রজন্ম যাকে হোমে লাগে না যজ্ঞেও লাগে না তার সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে আগ্রহী নয়। ঠিক যেমন যেই দেশটি ফাইনান্স নেটওয়ার্কে নেই, সে পৃথিবীর মানচিত্রেও নেই—এমনই বিধান গ্লোবাল নেটওয়ার্কের। তার ফলে সমাজ পরিণত হচ্ছে গোষ্ঠীতে—ফাংশনাল কমিউনিটিতে—যেমন, ছেলের সহপাঠীদের অভিভাবকদের গোষ্ঠী, বাবার সহকর্মী বা সহযাত্রীদের গোষ্ঠী… ইত্যাদি ইত্যাদি। বন্ধু এখন অংশীদার, প্রতিবেশী বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই প্রতিযোগী—হাসি-কান্না, বিরোধিতা-সমর্থন সবই স্ট্র্যাটেজি অর্থাৎ কৌশল। এই যে সর্বক্ষণ স্বার্থবুদ্ধিসম্পন্নতা বা আত্মনেপদী চর্চা বা যান্ত্রিকতার ব্যবহারিকতার সঞ্চারণ তার বিরুদ্ধে লিটল ম্যাগাজ়িন ও তার কবিতার ‘শত জলঝর্ণার ধ্বনি’ আমাদের প্রকৃতি-র সঙ্গে লগ্ন করে রাখবে, যতই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ি তার থেকে। বিশ্বায়নের কু-প্রভাবে দুটি বড় সংকটের একটি পরিবেশ অন্যটি মূল্যবোধ। প্রকৃতি দুয়েতেই আছে নিসর্গ হয়ে বা স্ব-ভাব হিসেবে। এই দুয়ের রক্ষার জন্যই আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতি, মূল্যবোধ, সৃজন-মনন চর্চার ধারা বহনের ভীষণ প্রয়োজন। প্রযুক্তির, পণ্যের, বিজ্ঞাপনের, বৈদ্যুতিন মাধ্যমের রঙিন হাতছানির বিপরীতে আদর্শের গোপন দহনে ঋদ্ধ থেকে।
আমাদের চিন্তা থাকে বিবেকের মোড়কে। প্রযুক্তি বন্ধুবেশে ঢুকে ওই বিবেককে খুলে ছুঁড়ে ফেলে আর চিন্তাকে ব্যবহার করে নিত্যনতুন আবিষ্কারের, সৃজনশীল চমকের কাজে। চিন্তা ও বিবেকের যে সংশ্লেষ তাকে গড়ে তোলে কাব্যচর্চা, সাহিত্যচর্চা, শিল্পচর্চা, ইতিহাসচর্চা… কার্যকারিতা ও যান্ত্রিকতাকে সে-ই প্রতিরোধ করে। হ্বিটগেনস্টাইন বলেন, যা সুশ্রী তা-ই সুন্দর নয়। আমরা একটি কবিতার অনেক অর্থ পাই। প্রযুক্তি চায় গণউৎপাদনের মতে একই ছকে ক্রেতার মানস-প্রক্রিয়া, ক্লোন্ড ক্রয়াভ্যাস, ক্রেডিট কার্ড…। আমরা বলি শতফুল বিকশিত হোক, শতমত বিচ্ছুরিত হোক। আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতা, হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তা তত্ত্ব, তার হাত ধরে কোয়ান্টাম তত্ত্ব, হ্বিটগেনস্টাইনের ব্যবহারভিত্তিক শব্দার্থের পরিবর্তনের ধারণা এসবই প্রযুক্তির ম্যাক্রো তথা গোদা কালচার, নিশ্চিতকরণ তথা একমুখীনতার চেষ্টা, একমাত্রিকতার সংস্কৃতির প্রসারের বিরোধী। লিটল ম্যাগাজ়িন বিজ্ঞানের সেই তত্ত্বকেই রেয়াত করে, যা তার মানবিকতাকে রক্ষা করতে, তার আত্মিক উন্নয়নের চর্চাকে সাহায্য করে।
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুক্তি-পদ্ধতির যে ছক যা একবগ্গা, যা একইরকম ভাবতে শেখায়, আমাদের চিন্তাকে একই খাতে বওয়াবার ফাঁদ পেতে রাখে, যেমন, সংবাদপত্র তাদের ছকবাঁধা সন্দর্ভের মধ্যেই আমাদের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ভাবনাচিন্তাকে আবদ্ধ রাখতে ছক আঁটে। এর বিরুদ্ধে সুযোগ্য নিঃশব্দ বিদ্রোহ করে কবিতা, যে কোনও ছককে মান্য করে না, যে শুধু সত্য ও সুন্দরের সন্ধানে বোধের অস্ত্র নিয়ে ক্রমাগত মূল্য সংযোজন করে চলে।
সেজন্যেই যদি কবিতাতেও ছকের ছায়া দেখি, লিটল ম্যাগাজ়িনে যদি ছকের আবদ্ধতা পাই তখনই ভয় হয়। যে ছক-বিরুদ্ধ, উদ্ভট, একেবারে ভিন্ন, প্রভাব-বিরোধী অথচ আমার ‘সনাতন বাংলা’, ‘সনাতন ভারত’ তার মধ্য দিয়ে ফুটে উঠছে—এমন কিছু দেখবো বলে তরুণতরদের দিকে চেয়ে থাকি—তারা কি প্রযুক্তির এই চোরাগোপ্তা স্লো-পয়জনগুলোর আঁচ পাচ্ছেন? তাহলে কেন দেখি না লিটল ম্যাগাজ়িনে সে-ই জেহাদের আছড়ে পড়া? তারা অন্তত এটা নিশ্চয়ই জানে যে, সময়কে একটা কাঠামো দিতেই সংগীত ধ্বনির আর কবিতা শব্দের ব্যবহার করে।
২.
আধুনিককালের মানুষকে আর হোমো স্যাপিয়েন্স না বলে হোমো টেকনোলজিকাস বলা হচ্ছে। অনেকেই একমত হবেন নিশ্চয়ই যে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি হলো নতুন যুগের ধর্ম, যারা নতুন নতুন চমক ও অলৌকিকতার উদ্ভাবন করে চলেছে। একজন আদিম মানুষের চোখ দিয়ে দেখলে বর্তমান বিশ্বকে অ্যালিসের ওয়ান্ডারল্যান্ডের মতো মনে হবে। কিন্তু যারা এই জগতের মধ্যে আছেন, তাদের বরং বিস্ময়ের অনুভব উবে যাচ্ছে। তাই গণমাধ্যমে হিংসা, যৌনতার মাত্রা চড়াতে হচ্ছে ক্রমান্বয়ে। অন্যদিকে, যে বিস্ময়, রহস্যবোধ থেকে শিল্পকলার জন্ম, তা আজ প্রায় অন্তর্হিত। তার পরিবর্তে জায়গা করে নিচ্ছে চমক, শিহরন; অর্থাৎ আনন্দের পরিবর্তে উল্লাস।
অ্যারিস্টোটল তাঁর ‘মেটাফিজিক্স’ গ্রন্থের প্রথম লাইনেই লিখেছিলেন—’সব মানুষই স্বভাববশত জানতে চায়’। সকলেই জানেন, আমাদের সহজাত কৌতূহলই শিল্পকলা ও বিজ্ঞানের উন্নতি সাধন করেছে। জগৎ সম্পর্কিত জ্ঞানই আমাদের প্রয়োজনানুযায়ী প্রকৃতিকে ব্যবহার করার ও তার ওপর নিয়ন্ত্রণ কায়েম করতে সমর্থ করেছে। সময়-বাঁচানো, শ্রম-বাঁচানো উপায় আমাদের স্বাচ্ছন্দ্য বাড়িয়েছে। প্রযুক্তি আমাদের জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে যে উপকার করে চলেছে তার সুবাদে তাকে ‘অলৌকিক কর্মী’ আখ্যা দিলে কেউ নিশ্চয়ই আপত্তি করবেন না। কিন্তু সবাই-ই জানেন যে, পরিবেশের ক্ষয় ও অবনমনের কারণ এই প্রযুক্তিই। কোনও কিছুই আর আমাদের দূষিত করার ক্ষমতা ও নাগালের বাইরে নেই—স্থল, জল, বায়ু, পর্বত, সমুদ্র…। আমাদের আধুনিক খাদ্যাভ্যাস জিনগত অবক্ষয় ও রোগের প্রার্দুভাব ঘটাচ্ছে। শহরমুখী মানুষের ঢল অধিকাংশের জীবনযাপন বিপজ্জনক করে তুলছে। পৃথিবীর উৎকৃষ্ট সব মেধা সামরিক-প্রযুক্তিতে নিযুক্ত—যার ফলে পৃথিবী নিউক্লীয় অস্ত্রের এক বিশাল ভাঁড়ার তথা এক জীবন্ত আগ্নেয়গিরি হিসেবে প্রস্তুত। পাশ্চাত্যের শিল্পবিপ্লবের ফলে কাঁচামালের চাহিদা যেমন উপনিবেশবাদের সূচনা করেছিল, তেমনি অর্থনীতির ভুবনায়ন নব্য-উপনিবেশবাদের পত্তন করেছে, যার অবধারিত ফল অসাম্যের বাড়বাড়ন্ত যার রোগলক্ষণ হলো: গণদারিদ্র্য, বেকারত্ব, নিরক্ষরতা, অপুষ্টি এবং মনুষ্যেতর জীবনধারনের পরিস্থিতি।
এই প্রযুক্তি যে আভ্যন্তরীণ অবক্ষয়কে পুষ্ট করছে—তার মূল রোগলক্ষণ হলো যে, আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি যান্ত্রিক হয়ে পড়ছে, আর, শিকড়-বিচ্ছিন্ন মানুষ, অনন্বয়িত মানুষ, স্নিগ্ধতা ও স্ফূর্তি-বর্জিত মানুষ, নীরসতা ও বিষণ্ণতায় নিমজ্জিত মানুষ আমাদের পরিণতি। এর হেতু লুকিয়ে আছে ক্রমাগত বিচ্ছিন্নতায়—প্রকৃতির আরোগ্যকারী ভূমিকা থেকে, প্রতিবেশী মানুষের সরলতা ও উষ্ণতা থেকে, জীবনের ‘সাধারণ ফূর্তি’ ও সমৃদ্ধ আনন্দ থেকে,—যার উদ্ভব হয় সুস্বভাবের মানুষের সঙ্গে সামাজিক মিথস্ক্রিয়ায়, যারা পৃথিবীর ঘ্রাণ, বায়ু-বৃষ্টি-সূর্যালোকের অনুভব ভালোবাসেন, অর্থাৎ এক কথায় পৃথিবীর প্রেমে ও সংবেগে যারা মগ্ন থাকেন।
এইভাবে, টেকনোপলিস সৃষ্টি করে মনোবিকার সম্পন্ন খুনি, নাস্তিবাদী ও সন্ত্রাসবাদী। অতিরিক্ত প্রযুক্তির পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া হলো মানবস্বভাব ও যাপনের স্বতঃস্ফূর্ততার বিনাশ। যেমন, গণমাধ্যম সাধারণ মানুষের চিন্তা করার ক্ষমতাকে বিনষ্ট করে তাকে ক্রীতদাসে পরিণত করতে উদ্যত। দায়িত্ববোধ, আত্মমর্যাদাবোধ ও শিষ্টতাবর্জিত মনুষ্যেতর জীবনযাত্রায় লগ্ন হয়ে পড়ছে মানুষ। প্রযুক্তির এই অপচয়জনিত প্রভাব-প্রতিক্রিয়ার দায় কি আমরা প্রযুক্তিকেই দেবো? আমাদের গান্ধিজি তো বলেছিলেন যে: আমি যন্ত্রের বিপক্ষে নই, কিন্তু আমি তার চূড়ান্ত বিরোধী যখন তা আমাদের ওপর কর্তৃত্ব করতে উদ্যত। আমরা তার কথাকে সন্দেহের চোখে দেখেছিলাম। তিনি ঘৃণা করতেন বিশেষাধিকার ও একচেটিয়া অধিকার। স্যুমেকার গান্ধির দর্শনের সমার্থক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে লিখলেন—‘স্মল ইজ বিউটিফুল’।
বিকল্প প্রযুক্তি পেশ করলো দুই কিসিমের নকশা—নিরবচ্ছিন্নতা ও গণতান্ত্রিক ধাঁচের সংগঠন। যে সম্পদ বাড়ন্ত তা যেন কাঁচামাল হিসেবে গণ্য না হয়ে পুঁজি হিসেবেই মান্য হয়। তাঁরা পরামর্শ দিলেন বাড়ন্ত সম্পদের পুনর্নবীকরণ ও অমূল্য শক্তির সংরক্ষণ, উৎপাদন-সুবিধার বিকেন্দ্রীকরণ এবং গণতান্ত্রিক আত্ম-নিয়ন্ত্রণের। স্যুমেকার অন্বিষ্ট হিসেবে নির্দিষ্ট করলেন (ক) যথোপযুক্ত অস্তিত্ব রক্ষার উপায় (খ) মানবদক্ষতার ক্রমবিকাশ (গ) সামূহিক কাজে যৌথ অংশগ্রহণের মাধ্যমে আত্মকেন্দ্রিকতাকে জয় করা। কেননা, বৃহৎ শিল্প, গণউৎপাদন-ই ভোগ্যপণ্যবাদের স্রষ্টা ও নিয়ামক। এবার আসি আসল কথায়, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যে প্রগতি তার বিপরীতে নৈতিক অবনতি সবচেয়ে উদ্বেগের কারণ। বস্তুগত সমৃদ্ধির বিপরীতে আধ্যাত্মিক দৈন্য সংকটের হেতু। আমাদের অন্তর হারিয়ে গেছে আমাদের বাহিরে। উন্নত উপায় চলেছে অনুন্নত গন্তব্যের পথে। মানবসমাজে বিজ্ঞান এক আশীর্বাদ হিসেবে গণ্য, তার মানে এই নয় যে, আমাদের অন্তর সংকুচিত হয়ে জীবনের বহিরঙ্গের মাত্রাবৃদ্ধি ঘটবে। আমাদের সৃষ্টির একটি উপকরণের অপব্যবহারে আমরা নিজেদের ধ্বংস করবো, যদি তা মেনে না নিই তবে আধুনিক পৃথিবীর সৃজনশীল যাপন ব্যক্তিগত চরিত্রের ও সামাজিক ন্যায়বিচারের নৈতিক উদ্দেশ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা দাবি করবে। আমরা টয়েনবিকে স্মরণ করতে পারি এই মর্মে যে, এই পৃথিবীর ছাব্বিশটি সভ্যতার উত্থান-পতনের পারম্পর্যে পতন কখনও বহিরাগত আক্রমণের কারণে ঘটেনি, বরং আভ্যন্তরীণ অবক্ষয়েই ঘটেছে।
যদি প্রযুক্তিগত প্রক্রিয়ার সঙ্গে নৈতিক চর্যার বিচ্ছেদ ঘটে, তবে এবারেও আত্মমগ্ন, ভোগ্যপণ্যবাদী সমাজ অকালে ধ্বংস হতে পারে। সুতরাং বিজ্ঞানের ক্রান্তি ও আধুনিক জীবনে ব্যক্তি-স্বাধীনতার সঙ্গে তাল মেলাতে পৃথিবী-গ্রামের যাপনের নিরবচ্ছিন্নতা দাবি করে মূল্যবোধের সংস্কার। মানুষকে ব্যবহার করা ও দ্রব্যসামগ্রীকে ভালোবাসার পরিবর্তে চাই দ্রব্যসামগ্রীকে ব্যবহার করা ও মানুষকে ভালোবাসার প্রত্যাবর্তন। যন্ত্র, মুনাফা ও সম্পত্তি যেন মানুষের তথা মানবিক সম্পর্কের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে না ওঠে। ভালোবাসাকে নতুন করে চেনা, জানা, বোঝার মধ্য দিয়ে এই পৃথিবীটাকে ভালো বাসা-য় রূপান্তরিত করার কাজটি ভীষণ জরুরি। ছাত্রাবস্থায় সমাজবাদে আস্থা রেখে যখন আধ্যাত্মিকতার পক্ষে যুক্তি বিন্যস্ত করতে উদ্যোগী হতাম তখন রে রে করে উঠতো বন্ধুস্বজন। তখন কখনও কখনও মনে হতো নিজের চিন্তা-অনুভবে কোথাও ফাঁক থেকে গেছে। আজ যেন, এত কাল পরে, সেই বিশ্বাসের যুক্তিতে নিজের সুপ্ত আস্থা ফিরে পাচ্ছি।
তখন প্রশ্ন ছিল মানুষ কি শুধুই ইন্দ্রিয়নির্ভর বাসনার কিংবা অনুশীলননির্ভর রীতির চরিতার্থতাকামী সত্তা? মানুষ কি পশুজগতের সাধারণ নিয়ম অর্থাৎ যোগ্যতমের টিকে থাকা জাতীয় ধারণার অধীন? গান্ধিজি, স্বামীজি ও কবিগুরুর চিন্তা ও কর্মের সমন্বিত উপলব্ধির কিছুই কি আমাদের উত্তরাধিকারে অবশিষ্ট থাকবে না? সাম্য, ন্যায় ও স্বাধীনতা এসব কি শুধুই রাজনৈতিক অধিকার নাকি নৈতিক মূল্যবোধ যা কিনা অধিকারের থেকে দায়িত্ব ও কর্তব্যকে অগ্রাধিকার দেয়! মানুষ তো জগতের মুখপাত্র, কেয়ারটেকার মাত্র—শাসক বা মালিক তো নয়। একসময়ে অতিরিক্ত ধর্মাচার যেমন মানুষকে পৃথিবীর দায়িত্ববোধ থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে, তেমনি পরবর্তীকালে রাজনৈতিক অধিকারবোধ তাকে কর্তব্য থেকে অব্যাহতি দিয়েছে। তার ফলে প্রযুক্তির অপচয়জনিত কারণে তার অবক্ষয় বা ভেঙে পড়া সে অবলীলাক্রমে সৃষ্টির ওপর চাপিয়ে দিয়ে নির্লিপ্ত রয়েছে। আজ তাই অন্তঃপ্রকৃতি ও বহিঃপ্রকৃতি অর্থাৎ মূল্যবোধ ও পরিবেশ দুইই ভাঙনের প্রায় চূড়ান্ত পর্যায়ে সমুপস্থিত।
৩.
গত দু-দশকে উপরিউক্ত কথাগুলোয় পরিবর্তনের কোনও সুযোগ তো প্রশস্ত হয়ইনি, বরং আরও প্রকট হয়েছে এ কথার বাস্তবতা তথা প্রমাণিকতা। অন্তঃ ও বাহির প্রকৃতিকে একসাথে একটি জীবন দর্শনের মাধ্যমে ধরে নেওয়া যায়। তার নাম হয়েছে ‘জীবনের এক প্রক্রিয়াগত দৃষ্টিভঙ্গি’ (সিস্টেম্স ভিউ অফ লাইফ)। জীবনের প্রক্রিয়াগত বোধের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরিজ্ঞান হলো এই স্বীকৃতি যে, সব জীবন্ত ব্যবস্থার সংগঠনের মৌলিক প্রতিমান হলো নেটওয়ার্ক। যেখানেই আমরা দেখি জীবন, সেখানেই দেখা যায় নেটওয়ার্ক-কে। বস্তুত জীবনের দৃষ্টিভঙ্গির যান্ত্রিক থেকে প্রক্রিয়াগত আদিকল্পে পরিবর্তনের অন্তঃস্থলে আমরা পাই রূপকালঙ্কারের মৌলিক পরিবর্তন—জগতকে যন্ত্র হিসাবে দেখা-র থেকে তাকে নেটওয়ার্ক হিসাবে বোঝা-য়।
এইসব জীবন্ত নেটওয়ার্কের অন্তরঙ্গ পরীক্ষার মাধ্যমে দেখা গেছে যে, এদের মূল বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, তারা আত্ম-সংগঠনী। ব্যবহারিক ভাবে, এটা অটোপোইয়েসিস তত্ত্ব, যার গোদা মানে হলো ‘আত্ম-নির্মাণ’। জীবন্ত নেটওয়ার্কগুলো নিরবচ্ছিন্ন ভাবে নিজেদের সৃষ্টি বা পুনঃসৃষ্টি করে তাদের উপাদানগুলো রূপান্তরিত ও প্রতিস্থাপিত করার মাধ্যমে। এইভাবে তারা ধারাবাহিক কাঠামোগত পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে চলে তাদের ওয়েব-সদৃশ সাংগঠনিক বিন্যাস রক্ষা করার প্রক্রিয়ার সূত্রে। সুস্থিতি ও পরিবর্তনের এই সহাবস্থান বস্তুত জীবনের এক মূল বৈশিষ্ট্য।
জীবনের এই প্রক্রিয়াগত বোধের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দার্শনিক তাৎপর্যগুলোর অন্যতম হলো মন ও চেতনার এক মহতী ধারণা। দেকার্তের অনুসারী হয়ে বিজ্ঞানী ও দার্শনিকরা ৩০০ বছরেরও বেশি সময় ধরে মনকে এক অধরা সত্তা হিসাবে মনে করেছেন এবং এটা কল্পনা করতে পারেননি যে, কীভাবে এই ‘চিন্তন বস্তু’ শরীরের সঙ্গে সম্পর্কিত। জীবনের প্রক্রিয়াগত দৃষ্টিভঙ্গির সুস্পষ্ট অগ্রসরণ হলো, মনকে বস্তু ভাবার ওই কার্তেসীয় দৃষ্টিভঙ্গিকে পরিত্যাগ করা এবং উপলব্ধি করা যে, মন ও চেতনা বস্তু নয় বরং প্রক্রিয়া।
মনের এই মহতী ধারণাটি আজ জ্ঞানের স্যান্টিয়াগো তত্ত্ব নামে পরিচিত, যে-তত্ত্বের মুখ্য পরিজ্ঞান হলো জ্ঞানের চিহ্নিতকরণ, জানার প্রক্রিয়া ও জীবনের প্রক্রিয়ার সঙ্গে। অবগতি হলো যে, ক্রিয়া জীবনের নেটওয়ার্কগুলোর আত্ম-সংঘটন ও আত্ম-স্থায়িত্বকরণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। এইভাবে জীবন ও জ্ঞান অবিচ্ছিন্ন ভাবে সম্পর্কিত। জীবনের সকল স্তরে বস্তুর সঙ্গে ওতপ্রোত এই জ্ঞান। এই তত্ত্ব অনুযায়ী মন ও জড়বস্তু আর দুই ভিন্ন বর্গে অন্তর্ভুক্ত নয় বলে মনে হয়, বরং তাদের দেখা যেতে পারে জীবনের অবভাসগত দুটি পরিপূরক দিকের প্রতিনিধি হিসাবে—প্রক্রিয়া ও কাঠামো। জীবনের সব স্তরে মন ও জড়বস্তু, প্রক্রিয়া ও কাঠামো অভিন্নভাবে সম্পর্কিত।
জ্ঞান, উপরিউক্ত তত্ত্বে যেভাবে বোঝা—জীবনের সকল স্তরে সংযুক্ত এবং তার ফলে চেতনার চেয়েও অনেক প্রশস্ত এক অবভাস—যার অর্থ সচেতন, যাপিত অভিজ্ঞতা—যা হলো এক বিশেষ রকমের জ্ঞানীয় প্রক্রিয়া যা এক নির্দিষ্ট স্তরের জ্ঞানীয় জটিলতায় উন্মোচিত হয় যার জন্য প্রয়োজন এক মস্তিষ্কের ও এক উন্নততর স্নায়ুতন্ত্রের। এই বিশেষ জ্ঞানীয় প্রক্রিয়ার মুখ্য বৈশিষ্ট্য হলো আত্ম-অবহিতি। বলা বাহুল্য, এই আলোচনায় চেতনার আধ্যাত্মিকতার মাত্রাও অন্তর্ভুক্ত। আমরা খুঁজে পাই যে, আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার সারাৎসার জীবনের প্রক্রিয়াগত দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে পুরোপুরি সংগতিপূর্ণ। আমাদের রবীন্দ্রনাথও তো বলেছেন, আধ্যাত্মিকতা হচ্ছে জীবচৈতন্যের জন্ম—বিশ্বচৈতন্যের মধ্যে। অর্থাৎ, বিশ্বাত্মার সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করা-ই হচ্ছে আধ্যাত্মিকতা। আমরা যখন আমাদের চারদিকে জগতের দিকে চোখ রাখি, তা সে বিজ্ঞানের বা আধ্যাত্মিক চর্চার প্রসঙ্গেই হোক, আমরা খুঁজে পাই যে, আমরা বিশৃঙ্খলা ও যদৃচ্ছতার মধ্যে নিক্ষেপিত নই, বরং এক মহৎ শৃঙ্খলার, জীবনের এক জমকালো ঐকতানের অংশ বিশেষ। আমরা শুধুমাত্র জীবনের অণুগুলোকে পরিবেশন করি না, বরং তার মৌলিক সাংগঠনিক রীতিগুলোকেও করি—অজড় জগতের অন্যান্যদের কাছে। বস্তুত, আমরা মহাবিশ্বের অংশ এবং এই অংশভাক হবার অভিজ্ঞতা আমাদের জীবনকে গভীরভাবে অর্থপূর্ণ করে তোলে। এখন আরও বেশি বেশি প্রকট হয়ে উঠছে যে, আমাদের সময়ের বহুমুখী ভূমণ্ডলীয় সংকট যথা শক্তি, পরিবেশ, জলবায়ুর পরিবর্তন, দারিদ্র্য ইত্যাদিকে আর বিচ্ছিন্ন ভাবে বোঝো যাবে না। এসব হলো প্রক্রিয়াগত সমস্যা, যার অর্থ হলো এরা সবকটিই আন্তঃসম্পর্কিত ও পরস্পর নির্ভরশীল, আর তাদের প্রয়োজন যথোপযুক্ত প্রক্রিয়াগত সমাধান।
কেন আমরা এই প্রসঙ্গের অবতারণা করলাম? বাস্তবতাকে বুঝতে? কেননা, কবিতা হলো ভাষা ও বাস্তবের এক মহৎ মধ্যবর্তী—তাই? কবিতা তো, এও জানি, এক সীমা-লঙ্ঘনকারী শক্তি। সাধারণ যোগাযোগের সীমাকে ভেঙে দেয়। সেটা করতে গিয়ে জগতকে জানার-বোঝার বিকল্প মডেল উত্থাপন করে। তার সঙ্গে মিথস্ক্রিয়ায় লিপ্ত হয়। ভাষার অনন্ত সম্ভাবনাকে আবিষ্কার করে কবিতা। কবিতা মদত দেয় সংকেতকের অগ্রগণ্যতাকে। বাস্তব কখনও চেতনার তাৎক্ষণিক সুগম নয়। চেতনা এই অর্থে সংকেতকদের অনিবার্য মীমাংসা।
কবি-র ও লিটল ম্যাগাজ়িনের যে বৈপ্লবিক ভূমিকাকে মাথায় রেখে এই সন্দর্ভ-নিবেদন তা কি প্রকৃতই অন্তত-আভাসিত নাকি ‘কল্পস্বর্গবাদী’ এক বিলাস-ভ্রমণ? কবিতা-রচনা (সৃজন নয়?) যখন প্রায় এক প্রকল্প-নির্মাণ (যা সৃষ্টির অধিক?) আর লিটল ম্যাগাজ়িন অনেকাংশে চর্বিত-চর্বণ বা বাণিজ্যপ্রবণ—এই ব্যাখ্যা (নাকি বিবৃতি)-র পর আমাকে কি লিটল ম্যাগাজ়িন ও তরুণ কবি এই মায়ের-পোয়ের গুরুত্ব-দায়িত্ব বা গুরু-দায়িত্ব নিয়ে আবার ব্যাখ্যার অতিকথনে দায়ী হতে হবে? আমি বরং এ যাত্রায় শিরোনামের সামান্য পরিবর্তন প্রস্তাব করি—’তরুণ কবি-র গুরুত্ব ও লিটল ম্যাগাজ়িনের দায়িত্ব’-এর পরিবর্তে ‘লিটল ম্যাগাজ়িনের গুরুত্ব ও তরুণ কবি-র দায়িত্ব’। তরুণ কবিকে সত্তা-র রাখালের দায়িত্ব আর লিটল ম্যাগাজ়িনকে মরুদ্যানের মর্যাদা দেওয়া মাত্র প্রশ্ন উঠবে—কে কবি? কোনটিই বা লিটল ম্যাগাজ়িন? আমি যদি লিটল ম্যাগাজ়িনকে নৈতিকতা আর কবিকে আধ্যাত্মিকতার মানদণ্ডে দেখি (ধরে নিচ্ছি আধ্যাত্মিকতাকে উপযুক্ত অর্থে বুঝবেন) তবে নিশ্চয়ই বন্ধুস্বজনেরা এখনও রে রে করে উঠবেন! তাহলে এই লেখাটি উত্তরকালের জন্য তোলা থাক।