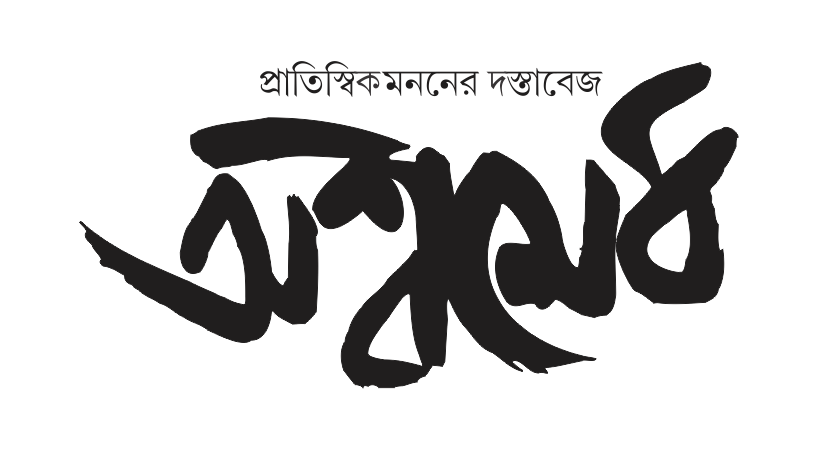বহুদিনের সাধ ছিল যাব জাভা, বরবদুর আর সুযোগ হলে বালি। খ্যাপার মন সততই বৃন্দাবন। যে খেতে চায় চিনি তার পাশে থাকে চিন্তামণি। সেই চিন্তামণি হলেন আমার স্বর্গীয় বুড়ি পিসিমা। যিনি আমায় প্রশ্রয় দিয়ে বাঁদর করেছেন এক যৌথ পরিবারে বড়ো হবার সূত্রে। যথেষ্ট উসকানি দিয়েছিলেন আমার বুড়ি পিসি। যিনি বিধবা হয়ে ফিরে এলেন আমাদের যৌথ পরিবারে—যখন তিনি বছর কুড়ির এক বিধবা যুবতী। উনি ছিলেন কিছুটা হিটলারের মতন, ডিকটেটর টাইপ। বুড়ির জয় হোক।
সেই বুড়ি চিন্তামণির আশীর্বাদে তাই সুযোগ এসেও গেল। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে গবেষণার সুবাদে প্রয়োজন ছিল সাবেক সিয়াম অধুনা থাইল্যান্ড এবং ইন্দোনেশিয়া যাবার। এইসব পাগলামি চলছে বহুদিন ধরে। শুধু চাকরি ছেড়ে আর্ট মাস্টারির। স্বভাবতই, দুই দশক মাসমাইনে নেই। শুধু সরকারি ফেলোশিপ। খ্যাপা খুঁজে ফেরে পরশপাথর—বলছেন সেই কবি, তাই এভাবেই চলা। সে সূত্রেই দেখে নেওয়া গেল চীন দেশের তাওইস্ট মন্দির ও পাহাড়গুলো।

যাই হোক, গুগুল ঘেঁটে ঠিকানা মিলল। শহর যোগজাকার্তার কাছের গ্রামে থাকেন বিখ্যাত চিত্রকর আফান্দির কন্যা কার্তিকা আফান্দি। ই-মেল করলাম ওঁর মিউজিয়ামের ঠিকানায়। উত্তর মিলল এক সপ্তাহ বাদে। তুমি কি শান্তিনিকেতন-এর ছাত্র ছিলে? সমস্যা নেই, চলে এসো। আমার প্রশ্ন ছিল, ওখানে গেলে কত খরচ আর কী করতে হবে বলুন? উত্তর এল, তোমার এয়ার ফেয়ার কি তোমাদের সরকার দেবে? জানালাম—হ্যাঁ। তাহলে আর কী খরচ? চলে এসো। আমার প্রশ্ন আবার, আপনার জন্য কী নিয়ে যাবো? লিখলেন—অমিত, পারলে রান্না করবার মশলা নিয়ে এসো, বিশেষ করে ঘি আর গরম মশলা। কী অদ্ভুত চাহিদা, আমি তো হেসে কুল!
যাই হোক, প্লেনের টিকিট কাটলাম—সস্তার, এয়ার এশিয়া। কলকাতা-কুয়ালালামপুর-জাকার্তা হয়ে যোগজাকার্তা। মাঝরাতে আকাশে ওড়া। পরদিন কুলালামপুর আর জাকার্তা হয়ে দুপুর দুটোয় যোগজাকার্তায় পৌঁছোলাম। ইমিগ্রেশন হয়ে এয়ারপোর্টের বাইরে বেরিয়ে ইতিউতি চাইছি, যাব কোথায় আর কেই-বা নিতে আসবে জানি না। সহসা এক মধ্যবয়সি মানুষ আমায় ডাকলেন,—আপনি কি মিস্টার অমিতাভ, ইন্ডিয়া থেকে আসছেন? হ্যাঁ—বলতেই, তিনি বললেন,—মামি আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন, আসুন। ওঁর সঙ্গে ট্রলিতে ব্যাগ-পত্তর নিয়ে বাইরে এসে দেখলাম, এক অসম্ভব টুকটুকে সুন্দরী বৃদ্ধা একটা লাল গাউন পরনে, বসে আছেন হুইল চেয়ারে।
তুমি অমিত? হ্যাঁ, ম্যাডাম। শোনো, আমাকে আর ম্যাডাম ডাকবে না, বলবে—মামি, ঠিক আছে? ইবু কার্তিকাও বলতে পারো। আমি এইটুকু জানতাম, জাভানিজ ভাষায় ইবু মানে মা। তোমার মা আছেন, কত বয়স ওঁর? বললাম, প্রায় সাতাশি হবে। তিনি জানালেন, আমি তিরাশি। পুনরায় প্রশ্ন করলেন—তোমার বউ, ছেলেমেয়ে? একটি বউ আর এক মেয়ে। আমার উত্তর শুনে বললেন, তুমি তো হিন্দু—তাই একটি বউ-ই হবে। তাঁকে জানালাম, আমার স্ত্রী, অনিতা একজন ভাস্কর। সে-ও কি শান্তিনিকেতনে পড়েছে? হ্যাঁ, ম্যাডাম। তাঁর কণ্ঠে প্রচ্ছন্ন ক্ষোভ,—আবার ম্যাডাম।

কার্তিকা নিয়ে এসেছেন একটা পেল্লায় গাড়ি। মধ্যবয়সি মানুষটি ওঁর জামাই, নাম বোয়েদি। পরে জানলাম, ওঁর নামটি হয়েছে ইন্দোনেশিয়ায় ১৯০২ সালে গড়ে ওঠা—‘বোয়েদি ওটোমো’ নামক জাতীয়তাবাদী আন্দোলন অনুসারে। ওলন্দাজ শাসকদের বিরুদ্ধে প্রথমে তৈরি হয় এই আন্দোলন। আর সেই সূত্রেই গড়ে উঠেছিল, ‘তামান সিসওয়া’ শিক্ষা আন্দোলন। আমার এই দেশজ বিপ্লব নিয়ে সামান্য পড়া ছিল, তাই এঁদের রাজনৈতিক ভিত্তি চিনে নিতে খুব অসুবিধা হয়নি। আমার গবেষণার প্রয়োজনে ইন্দোনেশিয়ার শিল্প আন্দোলনের খোঁজ করতে গিয়ে এই রাজনৈতিক দিশার কথা জানতে পারি। সে সুবাদেই বিশ্বভারতী পত্রিকা, অরুণ দাশগুপ্ত, জাভা যাত্রীর পত্র, রবীন্দ্রভবন আর কলাভবন মিউজিয়ামের ছবির কালেকশন এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার খান সাতেক ছবি দেখার সুযোগ পেলাম। এভাবেই সংযোগ আশি-উত্তর বয়সি কার্তিকা আফান্দির সঙ্গে আমার।
গাড়িতে উঠেই ওঁর জিজ্ঞাসা শুরু হলো—ইন্ডিয়ান মশলা এনেছো নিশ্চয়ই? জানো-তো, আমরা যখন শান্তিনিকেতনে ছিলাম (১৯৪৮ সালে), তখন আমার মা ভারতীয় রান্না শিখেছিলেন—অনেক। আচ্ছা বলো তো, মীরা, যিনি খুব ভালো স্কাল্পচার করতেন, আছেন কেমন? তুমি কি কর্নেল সেনগুপ্ত কে চেনো? উনি তখন জাকার্তায় ভারতীয় মিশনে ছিলেন। আমার বাবাকে উনি ভারতে যাবার ব্যাপারে সহায়তা করেছিলেন। আমার বাবার তখন অত নাম হয়নি। মা ও আমি বাবার সঙ্গে গেলাম তোমাদের শান্তিনিকেতনে। জানো-তো, আমার মা (মারিয়াতি) ওখানে অবসর যাপনের জন্য শুরু করলেন—এমব্রয়ডারি। আমাদের পরিবারের বন্ধু ছিলেন নন্দলাল বসুর মেয়ে, গৌরীদিদি। আর একজন গৌরী ছিলেন আমার বাবার বন্ধু, তাঁর স্বামী ছিলেন খুব বড়ো লেখক (ওঁর কথা শুনে আমার মনে হলো, সম্ভবত উনি গৌরী আইয়ুব)। আমার মা তখন মজে গেছেন এমব্রয়ডারিতে। বাবা তাঁর মাস্টারমশাই নন্দলাল বসুর উপদেশে ভারতের নানা জায়গায় ঘুরছেন স্কেচ করতে। বাবা তখন বেনারসে, আমরাও গেলাম পরে। শান্তিনিকেতনে আমরা থাকতাম যে বাড়িতে, সেখানে প্রায়ই আসতেন কিংকরদাদা। কী কাজ পাগল মানুষ আর ছটফটে। আমার বাবাকে তুমি ওঁর জাভার সংস্করণ বলতে পারো। আমি চুপ করে শুনছিলাম ওঁর কথা। রামকিংকরের একটা অ্যালবাম ওঁর জন্য নিয়ে গেছিলাম। ওঁকে দিতেই, বললেন—অমিত, এই অ্যালবামটা ভাগ্যিস তুমি নিয়ে এসেছো, তাই ওঁর কাজ দেখবার সুযোগ পেলাম। বড়ো শিল্পী ছিলেন।
বিমানবন্দর থেকে ওঁর গ্রাম প্রায় কুড়ি কিলোমিটার। রাস্তার দু-পাশে ধানখেত আর নারকেল, কলা, সুপারির গাছ। দু-ধারে বাঁশ আর বন্য ঘাস দিয়ে তৈরি ছোটো ছোটো সব গ্রাম্য সুন্দর কুটির। ইন্দোনেশিয়ার মধ্য-জাভার গ্রামগুলি যেন আমাদের উত্তর-পূর্ব ভারতের মতো। গাড়ি যেন চলেছে উত্তরবঙ্গ হয়ে আসাম ছুঁয়ে বার্মার দিকে। সেই সুপারি গাছ বাঁশ আর বেত দিয়ে তৈরি একচালা ছোটোখাটো মুদির দোকান দু-পাশে ধান আর ভুট্টার খেত। আমার কেন জানি মনে পড়ে গেল দ্বীপময় ভারত বইটির কথা, সুনীতিবাবুর।
গাড়িটি থামল এক বিশাল বাঁশের তৈরি দরজার সামনে। একটা সাইন বোর্ড-এ লেখা—ভিলেজ আফান্দি। সেই দরজাটি পার হয়ে যা দেখলাম, তার আয়তন প্রায় কুড়ি একর হবে মনে হয়। শান্ত এক নীপবন। বাগানের দিকে চেয়ে আছি। একটা ছোটো পুকুরে শালুক তো অন্য জলাশয়ে শ্বেতপদ্ম। কেয়ারি করা নানান গুল্ম, ফুলের গাছ। বিস্তীর্ণ বাগানে গাছতলায় জিরিয়ে নেবার জন্য কিছু বিচালির কুটির নীল আকাশের নীচে। একধারে ভাস্কর্যের জন্য স্টুডিও, অন্যপাশে বিশাল গ্যালারি, সেমিনারের জন্য অপূর্ব এক স্পেস, ওপাশে মেটাল কাস্টিং-এর জন্য একটা সুন্দর দালান। পরে জেনেছিলাম, ভিলেজ আফান্দির এইসব কিছু দেখাশোনা করেন ইবু আফান্দির জামাই বোয়েদি, যিনি নিজেও চিত্রশিল্পী। মেয়ে-জামাই থাকেন তাঁর কাছেই।
ইবু কার্তিকা বললেন, আমার এই গ্রাম, আমার প্রতিবেশী, মেয়ে জামাই ও নাতিপুতি—এই সবাইকে নিয়েই আমার শিল্পচর্চা। ছবি আঁকা, মূর্তি গড়া, বাগান, স্টুডিও দেখাশোনা করা—এসব নিয়েই সময় কেটে যায়। তোমার নিশ্চয়ই শান্তিনিকেতনের কথা মনে হচ্ছে? এখানে যেমন শান্ত-স্নিগ্ধতা। অন্যপাশে কিন্তু উত্তাপ। যা শান্তিনিকেতনে নেই। ওই দিকে, ধরো মাইল বিশেক দূরে। মেরপা। মধ্য-জাভার সবচেয়ে ভয়ংকর আগ্নেয়গিরি। আমার বাবার খুব প্রিয় ছিল, মেরপার ফুটন্ত লাভার টগবগানি। আমাদের প্রায়ই নিয়ে যেতেন ওই আগ্নেয়গিরির পাদদেশে।
আমার অতিথিদের জন্য একটা গেস্ট হাউস আছে। কিন্তু আমি চাই তুমি আমার পাশেই থাকো অমিত। সময় যদিও কম কিন্তু গল্প করা যাবে, ভালোভাবে আর বসতে পারি না পায়ের সমস্যার জন্য, হুইল চেয়ারে বসেই গল্প করা যাবে। ইবুর কথা মতো আমার থাকার ব্যবস্থা হলো তাঁর বিশাল কটেজের মধ্যে এক সুন্দর ঘরে। ঘরের মাঝখানে বার্মাটিকের কারুকাজ করা এক উঁচু পালঙ্ক। জাভানিজ আলংকারিক আবহ। বিছানায় ফুল তোলা জাভানিজ সুতির চাদর। সুগন্ধে ম-ম করছে ঘরটি।
ইবু কার্তিকা খুঁটিয়ে খবর নিলেন, আমার গবেষণার বিষয়ে। সেখানে ডাচ-ইন্ডিজ বা ইন্দোনেশিয়ার শিল্পীদের প্রসঙ্গ এবং আফান্দির ভূমিকা। দেখলাম, জাভার এক সাধারণ গ্রামে বাস করেও তাঁর নখদর্পনে, তাঁর দেশ সহ সারা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার আধুনিক শিল্পচর্চার খবর। বললেন, ভারতীয় আধুনিক শিল্পের সম্পর্কে খুব একটা জানি না। জাকার্তায় একটা প্রদর্শনী এসেছিল বছর কয়েক আগে। তখন আমি আমস্টারডামে, তাই দেখা হয়নি।
আর সিনেমা?—হ্যাঁ, বম্বের সিনেমা। এদেশে খুব রমরমা। আমার নাতনিরা খুব দেখে। ওই যে খুব নাচে, শাহরুখ খান, ওর নাম জানে সবাই। আপনি? বম্বে থাকতে আমরা অনেক দেখেছি। বাবা খুব পছন্দ করতেন। দেশে ফিরেও যোগজা শহরে সিনেমা দেখতে নিয়ে যেতেন বাবা। আমাদের একজন পছন্দের নায়ক ছিল, নাম শশি কাপুর। কথা প্রসঙ্গে আমার হঠাৎ মনে পড়ে গেল, মামি কার্তিকার বাবা আফান্দির কথা। প্রশ্ন করি, আফান্দি তো ফরাসি ইম্প্রেশনিস্ট শিল্পের একটি ইন্দোনেশিয় সংস্করণ—তাই না? জানো-তো, এটা সবাই বলে, কিন্তু আফান্দি আদতে জাভানিজ। ইবুর কথার সূত্রে আমি বলি, আমার মনে হয়, ওই যে—আপনার গ্রামের কাছে মেরপা আগ্নেয়গিরি, সম্ভবত ওটাই আফান্দিকে উত্তেজিত করেছিল, ফরাসি ইম্প্রেশনিস্ট শিল্পকলা থেকে কিছু নেবার জন্য—কি বলেন? কথাটা ভুল নয় অমিত। আসলে কী জানো, ইম্প্রেশনিস্টদের বর্ণ-উচ্ছ্বাসকে বাবা সঠিক চিনেছিলেন। জাভার দৃশ্যরূপকে মেলাতে পেরেছিলেন পোস্ট-ইম্প্রেশনিস্টদের সঙ্গে। মেরপার লাভা স্রোতের মধ্যে যে রঙের পাগলামি সেটা উনি ধরতে পেরেছিলেন পোস্ট-ইম্প্রেশনিস্টদের রঙের ব্যবহারকে চিনে নিয়ে। ইবু কার্তিকার সঙ্গে গল্প করতে করতে কখন রাত এগারোটা বেজে গেছে খেয়াল করিনি।
পরদিন সকালে, ঘর থেকে বের হয়েই দেখলাম ইবুকে। এর মধ্যেই তাঁর স্নান করা হয়ে গেছে। পরনে নতুন গাউন। মাথায় একটা লাল ফুল লাগিয়েছেন, অনেকটা করবীর মতো। বসে ড্রয়িং করছেন আপন মনে। একজন নারী, যিনি এভাবেই বাঁচেন প্রতিদিন, তিনি কিন্তু স্বঘোষিত নারীবাদী নন। আমায় দেখেই বললেন,—বরবদুর দেখে এসো। আগামীকাল বোয়েদি তোমায় নিয়ে যাবে।
আফান্দি যোগসূত্রেই আমার বরবদুর দেখা। যা আমি ছাত্র-বয়স থেকে দেখার অপেক্ষায় ছিলাম। আঙ্কোরভাট দেখেছিলাম আগে। ব্যাঙ্কক থেকে টানা বাসে সিয়েম-রিপ গিয়ে। বহুবার নামতে হয়েছিল চলার পথে। কারণ একটাই, শ্রীযুত পল পট নামে এক উন্মাদ কমিউনিস্ট। যিনি প্রায় লাখ দশেক সাধারণ মানুষকে হত্যা করেছিলেন। আঙ্কোরভাটের বিস্তৃত জঙ্গলাকীর্ণ মন্দির প্রাঙ্গণে তাই প্রচুর শঙ্খচূড় সাপ ফণা তুলে দিব্যি ঘুরে বেড়ায়—এরা সম্ভবত ওই পল পটের আত্মীয়স্বজন।
যাই হোক, প্রসঙ্গে ফেরা যাক। শুধু দেখা হয়নি—বরবদুর, তাই মন অস্থির ছিল এতদিন। প্রায় ঘণ্টা দুয়েক পর পৌঁছোলাম বরবদুর স্তূপের কাছে। আমি এ-যাবৎ বরবদুর স্তূপের ছবি দেখেছিলাম মাত্র। ছবিতে দেখা সেই বরবদুর একটা জঙ্গমতা নিয়ে চোখের সামনে সহসা এভাবে হাজির হওয়ায়—এই বিশাল পর্বত-খোদাই ভাস্কর্যকে নিতেই পারছিলাম না। তাই হাঁকপাঁক করে স্তূপের চারপাশ দেখতেই থাকি। আমি কিছুতেই বুঝতে পারছিলাম না, কোথা থেকে দেখা শুরু করব। এই বিশাল কর্মকাণ্ডটি খুঁজে পেয়েছিলেন এক ইংরেজ লেফটেন্যান্ট, স্যার থমাস স্ট্যান্ডফোর্ড, ১৮১৪ সালে। বুদ্ধকে উৎসর্গীকৃত এই স্তূপ—বরবদুর, অষ্টম শতাব্দীর শৈলেন্দ্র রাজবংশের সময় তৈরি হয়। জাভানিজ ভাষায় এর নাম ছিল—কান্ডি বা চণ্ডী। যা শেষ করতে প্রায় একশো বছর সময় লেগেছিল। এর স্থপতি ছিলেন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী সাধক-কবি-দার্শনিক, গুনধর্ম। এইসব কথা বলে যাচ্ছিলেন বোয়েদি। আমি শুধু শুনে যাচ্ছিলাম বোয়েদির কথা। ইতোমধ্যে একটা করে ডাব খেলাম আমি ও বোয়েদি। মধ্য-জাভায় মুসলিম আধিক্যের জন্য অন্য পানীয় পান নিষিদ্ধ। অনেকটা আমাদের গুজরাটের মতন। তাই ডাব-ই ভরসা মাত্র সার। দেখলাম, বরবদুর-এর মূল স্থাপত্য অনেকটা পিরামিডের মতো হলেও, আদতে চৈত্য স্তূপ ও পাহাড়—সব মিলিয়ে একটা সার্বিক গড়ে ওঠা। নিটোল ভাস্কর্য। যেটি আদতে ত্রিমাত্রিক মণ্ডল যা স্পর্শ করবে এক ধ্যানস্থ বুদ্ধকে আর এই পরিবেশের পাহাড়কে নিয়ে চলে যাবে আকাশে। সব মিলিয়ে একটা সামগ্রিক দর্শন। সেভাবেই গড়ে উঠেছিল বরবদুর। ততক্ষণে আমার তো ঘোর লেগে গেছে।
দেখলাম, ঠিক যেন সেই আকাশের তলায় বৃদ্ধি পাওয়া একটা ভাস্কর্যের গঠন। নীল আকাশকে সংগত করছে যুগপৎ স্থাপত্য আর খোদাই-কর্ম। পুব-দেশীয় শিল্পকলার এটাই মনে হয় বৈশিষ্ট্য। এভাবেই গড়ে উঠেছিল মমল্লপুরম, এলোরা, সারনাথ বুদ্ধ, আঙ্কোরভাট, পাগান, এমনকি মায় মিশরের পিরামিডগুলো। মনে পড়ে গেল, ছাত্রাবস্থায় কলাভবনে থাকতে দেখেছিলাম, মিশরের পিরামিডের ছবি। বরবদুর—বরবদুর আর সত্যি দূর নয়। দেখেই চলি শুধু। এভাবে দেখতে নেই, মনে হলো কেন যেন। দেখারও একটা নিয়ম থাকে, স্তূপ দর্শনের। কীভাবে দেখতে হয়, কী সেই নিয়ম?—জানি না যে! তাই ঘুরপাক খাই। বরবদুর-এ সাপ নেই, পল পটও নেই সেই কাম্বোডিয়ার মতো। ঘুরে ফিরে দেখি, একটা পাহাড়, যেখানে খোদিত হয়ে আছে—সময়। স্তূপের একদম ওপরে দেখলাম একটা খাঁড়াই, এক দণ্ড—ছত্র নেই অবশ্য। বোয়েদি বললেন, ওটা শূন্য। হয়তো ওটি শূন্য থেকে গেছে কারণ আবার ফিরে আসবেন বুদ্ধ, অন্যরূপে, মানব জগতকে মুক্তি দিতে।
মনে পড়ে গেল, গৌতম বুদ্ধকে প্রশ্ন করেছিলেন তাঁর ছাত্র আনন্দ। দীর্ঘ ধ্যানের মাধ্যমে কী পেলে তুমি? বুদ্ধ উত্তর দিলেন, কিছুই না। তবে তোমায় বলি, আমি কী হারিয়েছি ধ্যানের সূত্রে। তা হলো— রাগ, উত্তেজনা, মৃত্যুভয়, বার্ধক্য নিয়ে হতাশা।
ইতিমধ্যে আমি প্রায় অতিক্রম করে ফেলেছি সার্বিক বরবদুর স্তূপ। অবশেষে গেলাম চূড়ায়। আর অন্য কোনো নিয়ম প্রকৃতই জানা নেই। শিল্পকে, ভাস্কর্যকে দেখার জন্য, তাকে চিনতে মগ্ন হওয়া ছাড়া। এভাবেই আমার শিল্পে বাঁচা।
ফিরতে রাত হলো। কী দেখলে অমিত? বরবদুর। আর কিছু নয়? দেখলাম, নীল এক আকাশ। আর কিছু নয়? দেখেছি, কীভাবে জীবন খোদিত হয়ে আকাশের নীচে গড়ে ওঠে। ঠিক বলেছ অমিত, এভাবেই মেরপার লাভা স্রোতে যে চিত্রকলা হতে পারে তা চিনেছিলেন আমার বাবা। এখন প্রায় মধ্যরাত। টুকরো টুকরো কথা হচ্ছিল ইবু কার্তিকার সঙ্গে আমার। এই মাঝরাতেও দেখলাম, অনেক পাখি উড়ছে আকাশে। দূরে কোথাও একটা পাখি ডাকছে কুব কুব আওয়াজ করে। বেশ শীতল একটা হাওয়া সারা গ্রামকে মাতিয়ে দিচ্ছে। এ হাওয়ায় মেরপার লাভা স্রোত মনে হয় উথালপাতাল। বুঝি নেমে আসবে আর ক্যানভাসের ওপর উপচে পড়বে।
আমি আর মামি দুজনেই কথা বলে যাচ্ছিলাম যা আসে মনে। এই ইন্দোনেশিয়ায় থুড়ি ডাচ-ইন্ডিজে তৈরি হলো আর্ট কলেজ নয়—গিল্ড বা আটালিয়ের, যেখানে তৈরি হলো কিছু কারিগর চিত্রশিল্পী যারা ওলন্দাজদের ফরমায়েশিতে ছবি আঁকতো। পাহাড়, বন, মানুষজন, নিত্য জীবন—সবটাই ছিল পুবদেশীয় লোকজীবনকে চিনে নেওয়া—সবটাই ছিল, ডাচদের গুছিয়ে শোষণের জন্য।
ইউরোপে তখন মায়াময় ইস্ট-কে জানতে চায় মানুষ। তোমাদের দেশেও, ইংরেজ, দ্বিতীয় শ্রেণি পর্যটক আঁকিয়েরা, সব ডকুমেন্ট করে ছবি আঁকতো—ঠিক বলেছি কি-না? নিশ্চয়ই—আমি বলি। তিনি বলে যান—তখন চীন দেশের সেরামিক, যাকে আমরা চিনিওসার বলি তার-ও খুব ডিম্যান্ড। এভাবেই শুরু হলো আমাদের নতুন শিল্পকলা। মনে হয় ভারতেও ব্রিটিশরা একইরকম ব্যবস্থাই করেছিল—কি বলো অমিত? আমি বলি, আপনি ভুল বলেননি। মামি বললেন, তবুও ইউরোপ থেকে আমরা অনেক শিখেছি এবং এই শিক্ষাকে যে আমরা নিজেদের মতো ব্যবহার করেছি তার প্রমাণ—আফান্দি।
এমনকি, অমিত, তুমি যদি আমার বাবা, আফান্দির কথাই বলো—তাহলে বলতে হয়, তিনি যে সময়ে জড়িয়ে পড়েছিলেন তামান সিসওয়া সাংস্কৃতিক আন্দোলনে, শুরু করেছিলেন দেওয়াল-চিত্র আঁকা শহরের অনেক জায়গায়। ছবিতে তাঁর তেল রঙের ব্যবহারটাই দেখো না। তুলির চেয়ে উনি আঙুল দিয়ে আঁকতে বেশি স্বচ্ছন্দ ছিলেন। এটা হয়তো তুমি কিছুটা বুঝবে, এই জন্য যে, তোমরা ভারতে হাত দিয়ে ভাত খাও। আমরা শান্তিনিকেতনে থাকতে হাত দিয়ে খেতাম। এটাও এক ধরনের ইন্টারলাইজ়েশন—আমি বলি। বুঝতে পারছিলাম যে, এই বিচিত্র শিল্প আলোচনাটি বহুদূর বিস্তৃত হবে, যার কোনো আপাত সমাধান নেই। এমনকি পশ্চিমি শিল্পকলার থেকে এই এশীয়-শিল্পীরা ঠিক কী গ্রহণ করেছেন—তা আমরা জানি কতটা? আমাদের শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক, শিল্পী সুব্রামানিয়ন। আমাদের কাছে মানিদা, এই পূর্ব-পশ্চিমের শৈল্পিক আদানপ্রদান নিয়ে অত্যন্ত জরুরি আলোচনা করেছেন, তাঁর নানা প্রবন্ধে। যেখানে আছে শিল্প শিক্ষার বিস্তৃত আলোচনা।

দেখতে দেখতে আমার প্রায় দু-সপ্তাহ কেটে গেল ইবুর এই গ্রামে। মাঝে একদিন গিয়ে দেখে এলাম সে-ই মেরপা আগ্নেয়গিরির তলদেশ। একটা ধোঁয়ার গন্ধ আর এক কুণ্ডলী আগুনের আলো। এবার দেশে ফেরার পালা। এলাম জাকার্তা শহরে। শিল্প-সমালোচক, জাকার্তা আর্ট কাউন্সিল-এর এক কিউরেটর, বান্ধবী হেলি মিনাত্রি ও ইবুর ব্যবস্থাপনায় এক গেস্ট হাউসে আমার থাকার ব্যবস্থা হলো। মুসলিম আধিপত্যের কারণে এখানেও মদ্যপান নৈব-নৈবচ! প্রায় তিনদিন কেটে গেল, মিউজিয়াম দেখতে। সারাদিন চা-ই ভরসা মাত্র সার এবং যথারীতি সেই ডাব। জাকার্তা আর্ট মিউজিয়ামে দেখলাম ওদের এশীয় শিল্প সংগ্রহ। যদিও ভারতীয় আধুনিক শিল্পের কোনো নিদর্শন সেভাবে চোখে পড়ল না। চোখে পড়ল কেবল, সমকালীন ভারতীয় শিল্পী হিসাবে রবীন্দ্র রেড্ডির একটা ছোটো কাজ। মনটা বিষণ্ণ হয়ে গেল, আরও অনেক অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভারতীয় শিল্পীদের কাজ নেই দেখে। না নন্দবাবু, না রামকিংকর, না বিনোদবাবু, না মানিদা—কেউই নেই। ভাবা যায়? অন্যদের কথা না হয় বাদ দিই, কিন্তু এঁরা কেন উপেক্ষিত হলেন? এমনকি রবীন্দ্রনাথের আঁকা ছবিও নেই, একটিও না!
মধ্যরাতে, জাকার্তা থেকে আকাশে ওড়ার আগে ইবু কার্তিকা ফোন করলেন,—অমিত, ঠিক আছো তো? তোমার মা’কে, স্ত্রী আর কন্যাকে আমার ভালোবাসা জানিও—ভালো থেকো। আর তোমার স্ত্রী, অনিতাকে নিয়ে এসো নেক্সট টাইম।—এই শেষ সংলাপ। তখনও জানতাম না, আমার মা, নৈহাটির বাড়িতে ইতিমধ্যে পড়ে গিয়ে ফিমার বোন ভেঙে হাসপাতালে। আমায় কেউ জানায়নি মায়ের নির্দেশে। যাতে আমি দুম করে কাজ ছেড়ে না ফিরে আসি। কলকাতায় এলাম আরেক মধ্যরাতে। কলকাতার ফ্ল্যাটে, ভাত-কলাই ডাল, পোস্ত খেতে খেতে জানলাম—এই সংবাদ। পরদিন সকাল থেকে আমাদের সবার নিত্য হাসপাতাল আর বাড়ি। মা চলে গেলেন তার সাতদিন বাদে, আমাদের একা রেখে। ইবুকে ই-মেল করে জানালাম সে-কথা, এক সপ্তাহ বাদে। উনি উত্তর দিলেন—আমি জানি, তোমার বেদনা এখন কেমন। কিন্তু ভয় নেই, ভেবো আমিও একজন তোমার মা, বিদেশী হলেও। ভালো থেকো।

কেন জানি না, এইরকম সম্ভাব্য ভাইরাস আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুভয়ের অবস্থায় খুব মনে পড়ছে, আফান্দি ভিলেজ-এ কাটানো কয়েকটা দিনের অভিজ্ঞতার কথা। মনে পড়ছে, বরবদুরের চূড়োর সেই ছত্রহীন দণ্ডটাকে। যার নীচে আবার হয়তো ফিরে আসবেন বুদ্ধ—মানব জগতের ত্রাতা হয়ে।
প্রচ্ছদ ও লেখায় ব্যবহৃত ছবি সৌজন্য :
Affandi Museum (Yogyakarta), Madam Victoria Memorial Hall, www.amitavaasia.com