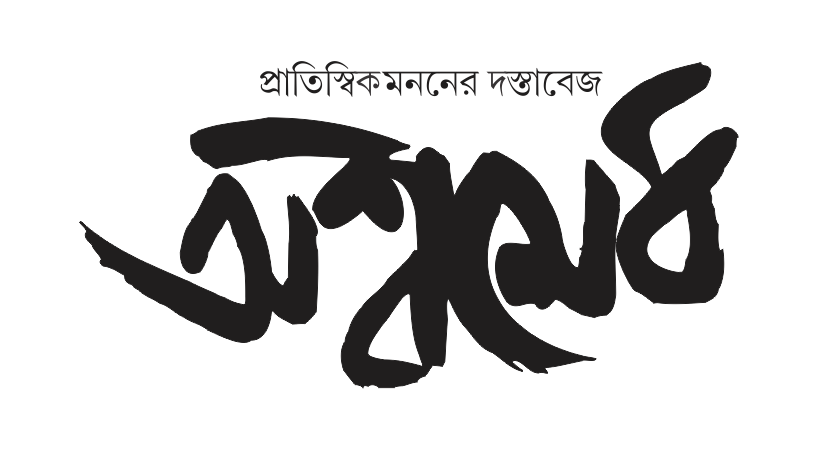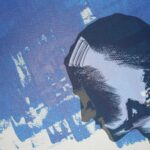স্বয়ং অমিতাভ বচ্চনও জিজ্ঞাসা করতেন—‘তো, লক কর দিয়া যায়ে?’ কিন্তু এ এমন এক ফ্যাঁকড়া যে, জিজ্ঞাসারও সময় নেই, তাই দড়াম করে ‘লকডাউন’ করে দিল গোটা দেশ। নাকি প্রায় গোটা বিশ্ব? সব পাখি ঘরে ফিরল, সব নদী, ফুরোলো এ জীবনের সব লেনদেন। সারাক্ষণ এই যে সময় পাই না বলে কিছু করতে পারছি না, না হলে পুরো ফাটিয়ে দিতাম বলে ভাবতাম মনে মনে, সেই ‘সময়’ এক লাফ দিয়ে উঠে এল কোলে। এইবার? সময় ব্যাপারটা যে নেহাতই অজুহাত, আসল সমস্যা যে নিজের অপদার্থতা—সেটা টের পেলাম আবার। আলসেমি করেই নষ্ট করে দিলাম প্রায় পুরোটা। হাতে রইল আফসোস—‘কিছুই তো হলো না’…
কিন্তু একেবারেই কি কিছু করিনি? এই যে মাথার ভিতর কিলবিল করে নানারকম চিন্তা…অলস চিন্তা (অলস মস্তিষ্ক নাকি শয়তানের কারখানা)…এই যে টুকটাক এ বই সে বই নেড়েচেড়ে দেখছি…বা হয়তো দু-চার লাইন লিখছি…না হলে হয়তো কোনো ফিল্ম দেখছি…এগুলো কি কিছুই করা নয়? সব সময়ে যে পাটোয়ারি অর্থে কিছু করতেই হবে, এমন মাথার দিব্যি কে দিয়েছে? কাজ মানে কি এক এমন গাছ, যাকে ফলবান বা ফুলবান হতেই হবে? নিষ্ফলা বা ফুলহীন হলেও তো কোনো কোনো গাছ পাতাবাহার!
না, আমার কোনো বাহার নেই। তাই নিজেকে বুদ্ধিজীবী প্রমাণেরও কোনো দায় নেই আমার। ফলে আমার কোনো ভয় হয় না। যা ইচ্ছে তাই পড়তে পারি, দেখতে পারি। ইচ্ছে হলে আমি যেমন গ্যালিয়ানো পড়ি, তেমন আবার ইচ্ছে হলে ইন্দ্রজাল কমিক্সও পড়ি; ইচ্ছে হলে যেমন আব্বাস কিয়েরোস্তামি দেখি, তেমনই আবার ধুমধাড়াক্কা মারপিটের ‘সাউথ ইন্ডিয়ান’ ছবিও দেখি। মোদ্দা কথা হলো, ভালো লাগছে কিনা! আবার কখনো-কখনো কিছুই করি না। স্রেফ কিচ্ছু না। হাতের মুঠো গলে শুধু পিছলে যেতে দিই সময়ের স্রোত। আর সেই স্রোতের ভিতর থেকে ফুটে ওঠে গোধূলির আলো।
শঙ্খ ঘোষের সেই যে একটা কবিতায় ছিল না—‘রক্তে কি গোধূলি দেখা যায়? যাওয়া ভালো?’ ভালো কী খারাপ—আমি জানি না। শুধু জানি—শব্দই রক্তের ভিতরে জাগিয়ে তুলতে পারে গোধূলির আলো, মদের নেশা, সময়ের বিষ। আর সে সবের স্বাদ পেতেই আমাকে বারবার ফিরে যেতে হয় কবিতার কাছে। ফিরে যেতে হয় শব্দের ভাস্কর্যে, যেখানে সব অতিরিক্ততা ছেঁটে দিয়ে শ্রাবণঘন গহন মোহে টলটল করে ওঠে আমাদের বোধের শীর্ষবিন্দুগুলি। সব পাখি ঘরে ফেরে, সব নদী…
সারা পৃথিবীর আলস্য ভর করেছে যার উপর, নিজের কাছে ফিরে যেতেও তার নানা ছুতো লাগে। সে তো খণ্ড খণ্ড হয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, এলোমেলো হয়ে আছে আজ। তাই কখনো-কখনো সে নিজেই তৈরি করে তোলে সেইসব ছুতো, সেইসব পথ। না হলে যে আর ফেরা হবে না তার! আর ফিরতে না পারলে, লক্ষ্মী যখন আসবে তখন কোথায় তারে দেবো রে ঠাঁই? নিজের মধ্যে কী করে তৈরি করে তুলবো সেই পদ্ম? তাই সেই রকমই কিছু ছুতো তৈরির ফিকির আর ফন্দিতে ফেরার চেষ্টা নিয়ে কেটে যায় তার।
যেমন আমার প্রাণের কবি প্রণবেন্দু। বারবার ফিরে যেতে আর আশ্রয় নিতে ইচ্ছে করে তাঁর কবিতায়। কিন্তু আলস্যবশত তা হয়ে ওঠেনি বেশ কয়েক মাস। হঠাৎ একটা কাজের ছুতো তৈরি হয়ে ওঠায় আমি আবার নতুন করে সুযোগ পেয়ে যাই প্রণবেন্দু দাশগুপ্তর কবিতাসমগ্রর মধ্যে ঢুকে পড়ার আর তা নিয়ে মেতে ওঠার। এমনি মাঝে মাঝে খুচরো পড়া এক জিনিস, আর কাজের জন্য যখন ধারাবাহিক ভাবে কোনো কবিকে পড়া হয় কালানুক্রমের সঙ্গে মিলিয়ে, তখন সে কবির বিকাশের চেহারাটা একটা সমগ্রতার মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়। টের পাওয়া যায় প্রণবেন্দুর ওই মৃদু অনুচ্চকণ্ঠের কবিতাগুলোর মধ্যে আস্তে আস্তে কী তীব্রভাবে মিশে যাচ্ছে সমসময় আর চারপাশের সমাজের রক্তপাত! রক্তাক্ত হয়ে উঠছে তার শব্দ আর ছবি।
একইভাবে অন্য আরেকটি কাজের ছুতো ধরে এর কিছুদিন আগেই অবশ্য আবার ধারাবাহিক ভাবে পড়ছিলাম শঙ্খ ঘোষের সমস্ত কবিতা আর সাক্ষাৎকার। একইভাবে একজন কবির সমগ্র মুখ ভেসে উঠছিল সামনে। সে মুখের চেহারা অন্য। আর ধারাবাহিক ভাবে না পড়লেও, কাটা-কাটাভাবে পড়ছিলাম জয়দেব বসুর লেখা কিছু কবিতা, সাহিত্য সংক্রান্ত অল্পস্বল্প কিছু গদ্য। এই দুইজন কবির পরই প্রণবেন্দুর কবিতায় ঢুকে যাওয়ায় হয়তো প্রণবেন্দুর ওই রক্তাক্ত হয়ে ওঠার মুহূর্তগুলো চোখে পড়ছিল বা টের পাচ্ছিলাম খুব সহজে। জানি না ঠিক। তবে হয়তো হতেও পারে সেই কারণে।
কিন্তু শুধুই কি আগে পড়া কবিতা আবার নতুন করে পড়া? একেবারে টাটকা নতুন লেখা পড়ার অভিজ্ঞতাও তো অভিনব। আমাদের স্কুলজীবনে আমরা পেয়েছিলাম বাংলার এক অনন্য শিক্ষককে—দুর্গা দত্ত। তবে স্কুল পেরোনোর অনেক পরে খোঁজ পাই যে তিনি অসাধারণ কবিতা লেখেন। প্রমা থেকে অনেকদিন আগে তাঁর একটা কবিতার বই ছিল—ধৃতরাষ্ট্র উবাচ। এমনকি কেরালায় গিয়ে দীর্ঘদিন থেকে তিনি মালায়ালাম শিখেছেন অনুবাদের জন্য। মালায়ালাম ভাষা থেকে বাংলায় প্রচুর কবিতা অনুবাদও করেছেন তিনি। কিন্তু পৃথিবীতে আমার থেকেও অলস ব্যক্তি যদি কেউ থাকে, তাহলে সে হলেন তিনি। কবিতা লিখলে বা অনুবাদ করলেই তাঁর কাজ শেষ। তারপর সে লেখা ছাপা হলো কী হলো না, অন্য কেউ পড়ল কী পড়ল না, এমনকি সে সব লেখা নিজের কাছেও রইল না হারিয়ে গেল—সে সব ফালতু ব্যাপারে তাঁর কোনো আগ্রহ বা মাথাব্যথা নেই। লিখে ফেলেছি মানেই কাজ শেষ। এহেন এক ব্যক্তি লকডাউনের আগে গেছিলেন তাঁর দাদার বাড়ি দুর্গাপুরে। গিয়ে আটকে গেছেন। আর ফিরতে পারছেন না। আর সেই আটকে থাকা অবস্থার মধ্যেই স্রোতের মতো লিখে ফেলেছেন একগুচ্ছ কবিতা। অবশ্য বাড়ি ফিরলেন বহুদিন পর। আর আমি মাঝে মাঝেই তাঁর কবিতা পড়ার জন্য খোঁচাই বলে, হয়তো অতিষ্ঠ হয়েই একদিন মেইল করে পাঠিয়ে দিলেন সেই গুচ্ছ। পড়তে পড়তে তো আমি মুগ্ধ। ওদিকে মাথায় কাজ করছিল এক গোপন ষড়যন্ত্র। ফলে আমার মুগ্ধতার সঙ্গেই তাঁকে জানাই যে এর আগের যা যা লেখা আছে, সে-সবও পড়তে চাই। এরপর ছোটো ছোটো ইনস্টলমেন্টে আসতে থাকে আরও কবিতা। আর আমি তার থেকে ঝাড়াইবাছাই করে, তৈরি করে তোলার চেষ্টা করি একটা পাণ্ডুলিপি। করেও ফেলি। আর মোটামুটি তৈরি হয়ে যাওয়ার পর তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিই সেটা একটা ফাইনাল চেহারা দেওয়ার জন্য। প্রথমে তিনি বোঝানোর চেষ্টা করেন যে এসব করে কী হবে, আমরা অকারণেই পণ্ডশ্রম করছি। আমরাও ছাড়নেওয়ালা নই। ফলে আমাদের জেদের কাছে একসময়ে নতিস্বীকারে বাধ্য হন। এই কাজটা করতে গিয়ে আমি বারবার টের পাচ্ছিলাম সদ্য নতুন পড়া কবিতার উত্তাপ আর আলো।
কিন্তু সব পড়াই কি কাজের জন্য? তাহলে অকাজের পড়ার আনন্দ ঠাঁই পাবে কোথায়? আর আমার মতো অলস লোকের জন্য তো অকাজটাই হলো আসল। এমনিতেই অলস লোকেদের জন্য আদর্শ হলো—স্মৃতিকথা, আত্মজীবনী, চিঠিপত্র, ব্যক্তিগত গদ্য এসব পড়া আর এলোমেলোভাবে খানিক পুরোনো পত্রপত্রিকা ঘাঁটা। ফলে আমার ক্ষেত্রেই বা তার ব্যতিক্রম হয় কী করে! তাই আস্তে আস্তে নেড়েচেড়ে দেখতে দেখতে পড়া হয়ে গেল দেবেশ রায় বা মৃণাল সেনদের মতো খ্যাতিমানদের আত্মকথার পাশাপাশি এক অখ্যাত চা-কুলির আত্মকথা বা কোনো অনামা অজানা গৃহবধূর আত্মকথা। আর রবীন্দ্রনাথের জীবিতকালের শান্তিনিকেতন নিয়ে পড়লাম প্রমথনাথ বিশী বা রমা চক্রবর্তীর স্মৃতিচারণ। আসলে এইসব স্মৃতিচারণ বা আত্মকথা পড়তে পড়তে নিজেও যেন সেই সময়ের বা সেই ইতিহাসের অংশ হয়ে যাই। আমার সামনেই যেন ঘটে চলেছে সে-সব। আর আমি শুধু নিজের পরিচয় লুকিয়ে দেখে যাচ্ছি। ইতিহাস আর কোনো পড়ার বিষয় থাকে না তখন, রক্তমাংসে তা জ্যান্ত হয়ে ওঠে। অথবা হয়তো এভাবেও বলা যায় যে, বর্তমানের যে সময়বৃত্তকে আমরা জ্যান্ত বলে জানি আর যে অতীতকে ভাবি মৃত, এই ধরনের বই সেই মরাকেও জ্যান্ত করে তোলে। তখন বরং যাকে জ্যান্ত বলেই জানি, সেই যায় অনেকটা অপ্রাসঙ্গিক হয়ে। আমরা তখন ঢুকে পড়ি এক আলাদা সময়বৃত্তে। টাইম মেশিনের থেকেও এ রোমহর্ষক। কারণ, টাইম মেশিন বড়োজোর দেখাতে পারে অন্য সময়ের বহির্বাস্তবকে। কিন্তু এইসব বই বহির্বাস্তবের সঙ্গে সঙ্গে খুলে দেখায় অন্য সময়ের অন্তর্বাস্তবকেও।
সময়। এও এক আশ্চর্য ব্যাপার। আচ্ছা, যেভাবে ডিপ ফ্রিজে জল রেখে দিলে, জমে বরফ হয়ে যায়, তার আর কোনো প্রবাহ থাকে না, সেভাবে সময়ও কি কখনও জমে যেতে পারে? আব্বাস কিয়েরোস্তামির ‘টোয়েন্টিফোর ফ্রেম্স’ দেখতে দেখতে ভাবছিলাম কিছুদিন আগেই। বরফ যেমন বাইরে রেখে দিলে আস্তে আস্তে গলে যায়, সে রকম সময়ও যেন আস্তে আস্তে গলে যায় এই ফিল্মে। দালির গলে যাওয়া ঘড়ির কাঁটা ঘুরতে থাকে আমার মাথায়। কখন শুরু হয়েছিল এই ‘সময়’? বিগ ব্যাং-এর থেকেই নাকি এই ব্রহ্মাণ্ডে সময়ের শুরু। আবার এ ব্রহ্মাণ্ড গুটিয়ে যখন ব্ল্যাক হোলে পরিণত হবে, তখন নাকি সময়েরও শেষ হবে এখানে। তাহলে ওই শুরুর আগে কি সময় ছিল না? বা এই শেষের পরে কি আর সময় থাকবে না? কিন্তু কোথায় থাকবে সেই না-থাকা? কোন ধারণাহীন পাত্রে? আর তাকে তাহলে কী নাম দেবো আমরা? নিঃসময়? নাকি সময়হীনতা? জানি না। আবার সময়ও কি এক রকমের? তাহলে এই যে কোনো ফিল্ম দেখার সময়ে ‘রিয়েল টাইম’-এর অনেক বড়ো একটা খণ্ড গুটিয়ে এসে ফিল্মের একটা ছোট্ট ‘রিল টাইম’-এর মধ্যে ধরা দেয়, তাতে আমাদের বুঝতে কোনো অসুবিধা হয় না কেন? তাহলে কি আমাদের মনের মধ্যে সময়ের গতি আর বহির্জগতের সময়ের গতি সমান নয়? তাহলে কি সময় আদৌ সমসত্ত্ব? নাকি ওয়াল্টার বেঞ্জামিন যাকে ‘সমসত্ত্ব শূন্য সময়’ বলেন, তা নেহাতই এক নির্মাণ? এই চতুর্থ মাত্রার বক্রতায় গিয়ে কেমন যেন সব গুলিয়ে যেতে থাকে। একটা উচ্চতা পর্যন্ত গিয়ে তারপর আমার চিন্তা আর কোনো ব্রিজ খুঁজে পায় না। সামনে অজানা অচেনা খাদ। তাই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ি।
এইরকমই হতো পূর্ণেন্দু পত্রীর? আসলে কিছুদিন আগেই পড়ছিলাম তাঁর ‘পদ্যপাগলের পাণ্ডুলিপি’। আর পড়তে পড়তে তাঁর উপর রাগ হচ্ছিল প্রচণ্ড। অনবদ্য এই বইয়ের প্রায় প্রতিটা লেখা যখন বিবরণে আর বিশ্লেষণে প্রায় তুঙ্গশিখর ছুঁয়ে ফেলতে চাইছে, ঠিক তখনই লেখক শেষ করে দিচ্ছেন সেই প্রবন্ধ। ফলে এ বই পড়তে গিয়ে অসমাপ্ত সঙ্গমের মতো একটা চূড়ান্ত অতৃপ্তি তৈরি হচ্ছিল আমার। পরে বুঝলাম এ হলো পাঠককে সক্রিয় করে তোলার এক ভঙ্গি। একাকী গায়কের নহে তো গান। তাই লেখক যেখানে শেষ করছেন, সেখান থেকেই পাঠক নিজের চেষ্টায় শুরু করবে যাত্রা। একজন কবি ও শিল্পীর যোগ্য ভঙ্গি তো এটাই। নোটবই লেখার কোনো দায় তাঁর নেই। একইভাবে হয়তো কোনো কোনো স্রষ্টা মনে করেন যে, বহির্বাস্তবের সঙ্গে সরাসরি কোনো বাহ্যিক সঙ্গতি বা সাযুজ্য রাখার দায় তাঁর নেই। অন্তর্লীন একটা যোগাযোগ তো থাকেই, কিন্তু বাহ্যিক স্তরে না-ও থাকতে পারে। একেই কি তাহলে বলে সুড়ঙ্গলালিত সম্পর্ক?
এইসব এলোমেলো হাজারো চিন্তার চাষ চলে মাথায়। কথায় বলে—নেই কাজ, তো খই ভাজ। ফলে আমার অলস মাথাতেও ফটাস ফটাস করে ফুটতে থাকে এসব খই। আচ্ছা, এই যে ‘আমি’, ‘আমার’ এসব বলছি, কে এই আমি? এই আমি কি বিচ্ছিন্ন কোনো সত্তা? তাহলে কি বলা যায় যে, ‘আমি’ এবং ‘আমি নয়’ এই দুইয়ের মধ্যেই ভাগ হয়ে আছে গোটা জগৎ? আবার যদি এই আমি-কে এভাবে ভাবি যে—আমি একজন বাঙালি, আমি একজন মানুষ, আমি একজন প্রাণী, আমি একজন জীব, আমি একজন পৃথিবীবাসী, আমি সৌরজগতের একটা অংশ, ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র হলেও আমি মহাবিশ্বের একটা অংশ—তাহলে? এক ভাবে ভাবলে, আমি না থাকলেও এই মহাবিশ্বের কিছুই যায় আসে না, সে তার নিজের ছন্দেই চলত। আবার আরেক ভাবে ভাবলে, এই বিশ্ব নাকি শূন্যের বিরোধী! তাহলে কি আমি না থাকলে সেই শূন্যতার ভারেই তা গুটিয়ে এসে ভেঙে পড়ত? ‘আমি’ কি তাহলে ‘আমি নয়’ নিরপেক্ষ? নাকি এই ‘আমি’-র জন্যই টিকে আছে ‘আমি নয়’ অংশটি? এভাবে ভাবলে তো এই ‘আমি’-টা ছড়িয়ে পড়ে সমগ্র ‘আমি নয়’-এর মধ্যে। তখন কি ‘আমি’ আর ‘আমি নয়’-এর মধ্যে থাকে কোনো ব্যবধান? নাকি এই দুইয়ের মধ্যে যখন আমাদের মন সত্যিই দুলে উঠতে পারে পেন্ডুলামের মতো, এই ‘আমি’ চলে যেতে চায় ‘আমি নয়’-এর দিকে আর ওই ‘আমি নয়’ এগিয়ে আসতে চায় এই ‘আমি’-র দিকে, সেই টানাপোড়েন থেকেই তৈরি হয়ে উঠতে পারে আমাদের জীবনবোধ? এই যে আমিত্বের বৃত্তের ছড়িয়ে পড়া আর তারপর আবার গুটিয়ে আসা—এ কি হৃৎস্পন্দনের কথা মনে করিয়ে দেয় না? এইসব এলোমেলো চিন্তার প্যাঁচে পড়েই সময় কেটে যায়। অথচ প্যাঁচ খোলে না কোথাও। বরং বাড়তে থাকে। ফলে নিজের দিকে তাকিয়ে তখন শুধু দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে অস্ফুটে বলার থাকে—‘অব তেরা কেয়া হোগা রে, কালিয়া?’
এক সময়ে ভাবতাম যে, লেখা অনেকটা ঘুড়ি ওড়ানোর মতো। কখনও লাটাই থেকে সুতো ছাড়তে হয়, কখনও গোটাতে। সেই নিয়ন্ত্রণটা ঠিকভাবে করতে পারলেই লেখাটা ঠিকঠাক হয়। তখনও বুঝতাম না যে, মাঝে মাঝে ঘুড়ি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। সে নিজের মতো উড়তে থাকে, নিজের নিয়মে। তাকে আর তখন নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। তখন বরং তাকে তার মতো ছেড়ে দিতে হয়। সে এবার নিজের মতো উড়ে যাক। সে খুঁজে নিক তার নিজস্ব আকাশ। হৃদয় আমার প্রকাশ হবে সেই অনন্ত আকাশে…