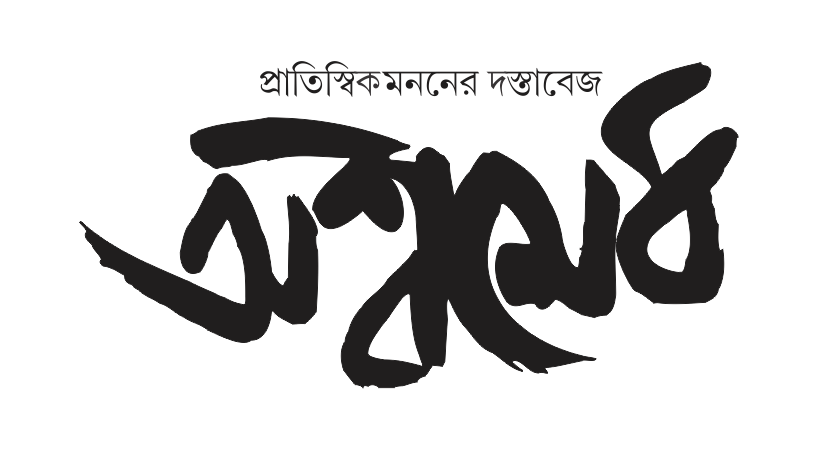‘একজন নামজাদা গল্পকার হলেন জ্যোৎস্না কর্মকার’—ঠিক এভাবে প্রবন্ধ শুরু করতে পারলাম না! আর এই না-পারার জন্য স্বস্তি এবং অস্বস্তি বোধ করছি একইসঙ্গে। স্বস্তি হচ্ছে এই ভেবে যে, বহু লেখার নেশায় বা প্রচারের প্রতিযোগিতায় থাকতে চাননি তিনি। দায়বদ্ধ পারিবারিক ও চাকরি জীবনে ব্যস্ততার পাশাপাশি, ‘বহু লেখা’র প্রতি তাঁর অনিচ্ছা হলো অন্যতম কারণ। সৃষ্টি ও স্রষ্টার বিজ্ঞাপনী প্রচারে সংকোচ বোধ করেন তিনি। এবং সেটা ‘মেকআপ সর্বস্ব’ নয়। রাজনৈতিক অবস্থান নেই, অ থেকে ঔ সাহিত্য সংগঠন কিংবা সম্মেলনে যোগদান নেই। স্বভাবতই, প্রচারের খ্যা ধাতুতে সময়োপযোগী হয়ে ওঠেননি তিনি। আর, অস্বস্তির কারণ হলো—গল্পকার জ্যোৎস্না কর্মকারের বহুপাঠী না হওয়া! রবীন্দ্র চোরাবালি[১] আজ নেই, কিন্তু, কলকাতা-চোরাবালিতে অনেক প্রান্তিক রচয়িতা অপরিচয়ের অন্ধকারে হারিয়ে গেছেন ও যাচ্ছেন। বাংলা সাহিত্যের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড কলকাতা নির্ভর। সে মেরুদণ্ড আঁকড়ে রূপকথার কলম পাঠককুলে প্রচার পরিচিতি পায়; অথচ স্বতন্ত্র, ঋজু প্রান্তিক কলম পায় না! বর্তমান সময়ে এ অবস্থার পরিবর্তন ঘটলেও তা এ পর্যন্ত যথেষ্ট হয়ে ওঠেনি।
জ্যোৎস্না কর্মকারের জন্ম থেকে বড়ো হয়ে ওঠা পুরুলিয়ার অনগ্রসর গ্রামাঞ্চলে। জেলার ‘ছত্রাক’ পত্রিকায় তাঁর প্রথম কবিতা ও গল্প প্রকাশ পেয়েছিল আশির দশকে। এ পর্যন্ত তাঁর রচিত শতাধিক গল্প, কবিতা প্রকাশ পেয়েছে। প্রকাশিত চারটি গল্পগ্রন্থ হলো—‘টুনির বারোমাস এবং খিদে’ (১৯৮২), ‘মেনকার সাবান’ (১৯৯৬), ‘ইচ্ছের গন্ধ’ (২০০৪) ও ‘জলবাসর’ (২০১৮)। ‘পুরুলিয়ার মেয়ে’র কলমে ভিড় করে এসেছে সেখানকার প্রান্তিক জীবনের নানা বাস্তব ঘটনা, সমস্যা, লোকবিশ্বাস, লোককথা, জীবন-সংগ্রামের কথা।
নারীর জীবন-কথা নির্মাণে আশাপূর্ণা দেবী, মহাশ্বেতা দেবী এঁদের যোগ্য উত্তরসূরিদের মধ্যে জ্যোৎস্না কর্মকার নিঃসন্দেহে একজন। তাঁর নির্মিত কথাখ্যানে যে বাস্তবতা ধরা পড়েছে, তার অভিঘাত আমাদের রক্ত-মাংস-মজ্জা ছাড়িয়ে আরও গভীর কোথাও প্রোথিত হয়ে যায়। তাঁর কথাখ্যানের মূল উপাত্ত হলো—নারী। কিন্তু উপাত্ত এক হওয়ায়, কয়েকটি গল্পাখ্যান পড়ে বা না পড়ে, লেখিকার উপস্থাপিত বিষয়, চরিত্রের ধরন সহ উপস্থাপন পদ্ধতি যে একই হবে—তা ভেবে নেওয়া অন্ধের হস্তী দর্শন সর্বস্ব হবে। নানা বর্গের নারী, একই বর্গস্থিত পরস্পর বিরোধী নারী, ভিন্ন অবস্থান, ভিন্ন সমস্যা, প্রেম-ভালোবাসা-মাতৃত্বে নারী—এক কথায় স্বতন্ত্র এক নারীবিশ্ব রচনা করেছেন জ্যোৎস্না কর্মকার। তাদের হেরে যাওয়ার গল্প, সংগ্রামের গল্প তাঁকে প্রতিপদে অন্তর থেকে বিঁধেছে। তিনি ছিলেন একজন সরকারি হোমের আধিকারিক। সেখানে তিনি কাছ থেকে দেখেছেন, পিতা-মাতা-সন্তান-স্বামী-সমাজ পরিত্যক্ত নানা শ্রেণির, নানা বয়সের নারীদের। ক্ষেত্রসমীক্ষার দ্বারা বহু শ্রম, আগ্রহ ও যত্নে, প্রতিকূলতাকে ছায়াসঙ্গী করে লেখার উপাদান সংগ্রহ করেছেন একজন সমাজসেবক, সাংবাদিকদের মতো। তাই তো দৃঢ়তার সঙ্গে তিনি বলতে পারেন—‘যা দেখিনি, তা আমি লিখতে পারি না। পাঠককে লেখা খাওয়ানোর মানসিকতা আমার ছিল না, নেই।’[২]
“আশির দশকে জ্যোৎস্নার প্রথম গল্পগ্রন্থ ‘টুনির বারোমাস এবং খিদে’ যখন প্রকাশ পায় তার এক আধ বছর আগে থেকেই জ্যোৎস্নাকে আমি দেখেছি পুরুলিয়ার গ্রামে ঘরে ঘুরে ঘুরে গল্প তুলে আনতে।”[৩]
—যাতে, বাংলার সেই কোন টাঁড় প্রান্তরের নারী-যন্ত্রণার অব্যক্ত চিৎকার, তীব্রতাহীন শব্দব্রহ্ম শিক্ষিত, নাগরিক সমাজের কানে প্রবল ধাক্কা মারে। তাঁর লেখা যেন বলতে চায় ‘নারীবাদ’ অনেকাংশে এক শৌখিন উদ্যোগ হয়ে রয়েছে মাত্র। তিনি মার-মার কাট-কাট নারীবাদী নন। তিনি মানুষের হয়ে কথা বলেন। মানুষ-নারীর কথা বলেন।
“তিনি নারীবাদী লেখক না-হয়েও বিশ্বাস করেন, প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কৃতির দ্বারা প্রান্তিকায়িত বা নিপীড়িত, সভ্যতার সেইসব পিলসুজদের সমাজ যতক্ষণ না মর্যাদা দিচ্ছে, নারী বিচ্ছিন্নভাবে নিজের লড়াইয়ে জয়ী হতে পারে না। এমনকী, উন্মাদ-বাতুল-ভিখারি-ভবঘুরের মতো সামাজিক বর্জ্যদের নিজস্ব প্রতিবেদন অভিনিবেশ দাবি করে।… তাঁর গল্পের ভেতর দিয়ে ধরা পড়ে এক অবমানিত নারী-সমাজের জগৎজিজ্ঞাসা, তাঁর সত্তাদর্শনের সংকট; প্রান্তের স্থানাঙ্ক থেকে কেন্দ্রকে দেখার বিশেষ প্রকরণ। প্রান্তে নিক্ষিপ্ত নারীরা প্রতিমুহূর্তে নিজেদের প্রান্তসীমা অতিক্রম করতে চায়, আর প্রতি মুহূর্তেই তারা অনুভব করে, প্রান্তই চির নির্দিষ্ট করে দিয়েছে তাঁদের জীবনের পরিসর।”[৪]
তাঁর সৃষ্ট ‘অন্য নারীবিশ্ব’র এমনই কয়েকটি নারী-জীবনের কথা জানব আমরা। যাঁরা কেউ কেউ চাক্ষুষ ভাবে হয়তো পরিচিত, কিন্তু অনুভবের পরিচয়ে নয়। তো, আবার কেউ সম্পূর্ণ অপরিচিত।
টুনি (‘টুনির বারোমাস এবং খিদে’) :
টুনির বয়স ১২ বছর। মা নেই। বাবা জনার্দ্দন খেটে-খাওয়া মজুর। টুনির প্রতি পিতৃসত্তা জনিত কোনোরকম টান জনার্দ্দন অনুভব করে না। রক্ত-ঘাম ঝরানো উপার্জনে তার নিজেরই ভাত-নেশা জোটে না ঠিক মতো। তার উপর টুনি! টুনি তাই গরু-ছাগলের মতো চরে চরে খাবার খোঁজে সকাল থেকে সন্ধ্যে। বারোমাস টুনির কেবল একটাই শখ আহ্লাদ—খাবার। যত্ন নয়, বাবা জনার্দ্দনের নির্লিপ্ত অবহেলায় টুনি মুখঝামটা দেয়। শ্লীল অশ্লীলের তোয়াক্কা করে না। যে বাবা দু-বেলা, দু-মুঠো খাবার দিতে পারে না মেয়েকে, ১২ বছরের কিশোরী টুনি সে বাবাকে তিরস্কার করে বলে—
“বলি খাতে দিবি নাই ক্যানে শুনি, জন্মটা তো খুব দিতে পারেছিলি। আমি কি তর পায়ে ধইরে সাধতে গেছলাম…”[৫]
খিদে। একটি দীর্ঘস্বর ও একটি হ্রস্বস্বর নিয়ে গড়ে ওঠা এই ছোট্ট শব্দটি ব্ল্যাকহোলের ক্ষমতা ধরে। মানুষকে চালিত করার ক্ষমতা রাখে। খেয়াল রাখতে হবে, দুর্ভিক্ষের খিদে আর অনাহারীর খিদে কিন্তু এক নয়। তাই, পরিস্থিতিভেদে পৃথকভাবে এগ্জিস্ট করা দুজন মানুষকে দু-ভাবে চালিত করে এই খিদে। টুনি অনাহারী। হাঁড়িতে ভাত নেই, কিন্তু প্রকৃতি আছে। টুনি পেট ভরিয়ে নেয় ফল খেয়ে, শিকার করা ইঁদুর ঝলসে খেয়ে, প্রতিবেশীর দেওয়া দৈব্যভোগ চুরি করে। এসব বিষয়ে সে দ্বিধাহীন ও পটু। ষড়রিপুর সবকটির সঙ্গে খিদের যোগ বড়ো গভীর। শূন্য পাকস্থলি মানুষকে অসহায়, অমানবিক, অপরাধী করে তুলতে পারে নিমেষে। যেমন, সুবোধ ঘোষের ‘সুন্দরম্’, কমলকুমার মজুমদারের ‘নিম অন্নপূর্ণা’, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘শাস্তি’।
‘পোস্টমাস্টার’-এর রতন, ‘প্রথম প্রতিশ্রুতি’র কিশোরী সত্যবতী আর টুনি সম-বয়সের। অথচ কত তফাত! পরিবেশ আর চাহিদা কিশোরী টুনিকে এভাবেই গড়ে তুলেছে। দিয়েছে বয়সের ব্যাস্তানুপাতিক হারে বেড়ে ওঠা মানসিক গঠন। ননীর অবয়বে পুষ্ট লক্ষ্মী-সরস্বতীর মূর্তি টুনি নয়। টুনি হলো মাটি দেবার আগে খড়ের কাঠামো বা আঁটন। যার প্রথম ও শেষ চাহিদাই হলো দু-বেলা পেট ভরা খাবার। সত্যবতী গাছে চড়তে পাড়ত, তাই সে ডানপিটে। কিন্তু, টুনি সে অর্থে ডানপিটে নয়। ১২ বছরের টুনি, পাথর ছুঁড়ে এক নিশানায় মেঠো ইঁদুর মারতে পটু, গাছে চড়ে কাঁচা, পাকা ফল পাড়তে পটু। উদ্দেশ্য খাদ্য সংগ্রহ, কোনোরূপ বিনোদন নয়। বাংলা সাহিত্যে এই কিশোরী টুনি এক বিরল চরিত্র।
দেবী (‘অন্ধকারে জোনাকি এবং দেবীরা’) :
আরেক কিশোরী চরিত্র হলো দেবী। বয়স ১৪ বছর। এই চোদ্দ বছর বয়সেই সে ন-মাসের গর্ভবতী! দেবীর বান্ধবীরা এখনও স্কুল যায়। কিন্তু, দেবীর সে সৌভাগ্য হয়নি। তার বিয়ে দিয়ে দেওয়া হয়েছিল ১২ বছর বয়সে। প্রান্তিক গ্রামাঞ্চলে আজও অল্পবয়সে মেয়ের বিয়ে দিয়ে দেওয়া হয়। ‘গৌরীদান’-এর পুণ্য নয়, মেয়ে তাড়াতাড়ি শ্বশুরঘর যাবে, বাচ্চার জন্ম দেবে, খেটে খাবে—এই হলো মানসিকতা। ‘গতর’-ই হলো শেষকথা। খবরের কাগজে নিজের বিয়ে রুখে দেবার ঘটনা প্রায়ই চোখে পড়তে পারে। কিন্তু, এই দেবী কোনো প্রতিবাদ করতে পারেনি। সে, শরীর ছেড়ে দিয়েছিল বিয়ের পিঁড়িতে, স্বামীর সোহাগে। গর্ভবতী দেবী কেবল নির্জনতায় নিঃসঙ্গ মনে মা-কে চিঠি লেখে—
“কুন্তি তো বাসে করে শহরের ইস্কুলে যায় পড়তে। এখন আমিও ইস্কুলে পড়লে কত ভালো হতো৷…ইখানে [শ্বশুরবাড়ি] সবসময় বড়ো দোষী হঁয়ে থাকতে হয় মা। জোরে হাসলেও দোষ। অল্প জোরে কথা বললেও দোষ, খিদে লাগলেও দোষ।”[৬]
রোজ কাক ডাকা ভোরে উঠতে হয় দেবীকে। ঘর-উঠোন ঝাঁট দিতে হয়। পুকুরে হাঁস ছাড়া, গোয়ালের গোবর ফেলা, খড় দেওয়া, শুকনো ঘুঁটে তোলা ও ঘুঁটে দেওয়া, নদী থেকে জল আনা, উনুন জ্বেলে রান্না করা, সবার শেষে খাওয়া তারপর বাসন মাজা! দশভূজা না হওয়া দেবীকে দু-হাতে সব করতে হয়। এত সবের সঙ্গে উপরি হিসাবে আছে, শাশুড়ি ও দিদি-শাশুড়ির পাকা চুল বেছে দেওয়া, উকুন মারা। দেবী একদণ্ড বসে আছে দেখলেই ফরমাশের জোয়ার আসে।
এহেন দেবী ন-মাসের অন্তঃসত্বা। আসন্ন মাতৃত্ববোধের কোনো মমত্ব তার জাগে না। তার মনে হয় পেটে যেন এক মস্ত বড়ো টিউমার বয়ে বেড়াচ্ছে সে।
“চৌদ্দ বছরের দেবীর এটা ন-মাস।…অস্বস্তিতে হাঁসফাঁস করছে ওর ছোটোখাটো শরীরটা।… চৌদ্দ বছরের দেবী, আসন্ন মাতৃত্বের আলোতে যার মুখটা চকচকে হয়নি। চোখের কোলে কালি বসে গেছে।”[৭]
নাগরিক সমাজে দেবীদের কথা রূপকথার মতো। কিন্তু, প্রান্তিক গ্রাম্য সমাজ সম্বন্ধে যাঁদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে, তাঁরা চিনবেন এমন দেবীদের। এই দেবীদের লড়াই ত্রিশূলধারী দেবীর চেয়েও কঠিন। এই দেবীরা লড়াই চালিয়ে যায় প্রতি ক্ষণে। জিতে যাবার জন্য বা দৃষ্টান্ত স্থাপনের জন্য নয়, কেবল টিকে থাকার জন্য।
শুকুরমনি (‘নকল বুঁদি’) :
বীরহোড় মেয়ে শুকুরমনি। গতর খাটিয়ে খায়। স্বামীর উপার্জনে তথাকথিত নিম্নবর্ণের নারীরা নির্ভর করে না। বাস্তবিক, নির্ভর করলে সংসার চলবেও না। বিবাহ একটা সম্পর্ক। শরীরী চাহিদা বাদে দুজনেই গতর খাটিয়ে খায়। রোজকার-রোজ খাদ্য সংগ্রহই হলো তাদের কাছে আসল চ্যালেঞ্জ। শুকুরমনি তাই সিজিনের সঙ্গে রোজগারও বদলায়।
’কাঠকুড়ুনী, পাতাকুড়ুনী, মহুলের দিনে মহুলকুড়ুনী… বর্ষায় যায় ধান রুইতে। অঘ্রাণে ধান কাটতে।’[৮]
খিদের সঙ্গে লড়াই করতে করতেই এদের জীবন-চক্রের সমাপ্তি ঘটে। গতর নিংড়ে পেটের জন্য দিনপাত করা শুকুরমনির মেজাজও তাই সর্বদা তিরিক্ষি। স্বামী ক্যাঁদের চালচলনে বেগরবাই দেখলেই সে ফুঁসে ওঠে—‘ইঃ ভাত দিবার ভাতার লয় কিল মারবার গোঁসাই’…[৯]
টাঁড় ভূমিতে ফসল ফলে না। শাক, শেকড় যে যা পায় তুলে খায়। পুরুলিয়া শহরে মজুর খাটতে যায় অনেকে। এহেন গ্রামে শুকুরমনি শোনে, অঙ্গনওয়াড়ি থেকে গর্ভবতী মহিলা ছ-বছরের শিশু ও সদ্য মায়েদের প্রোটিনযুক্ত খাবার ও কাপড় দেওয়া হচ্ছে। গিয়ে দেখে, ইতিমধ্যে বেশ বড়ো লাইন পড়েছে। শুকুরমনিও লাইনে দাঁড়ায়। কিন্তু, শুকুরমনি লাইনে দাঁড়ানোয় সকলে অবাক হয়। কারণ, তার তো কোনো সন্তান নেই। আর, গর্ভবতীই বা সে হয় কী করে? তার স্বামী ক্যাঁদের তো সেই কবে থেকে গ্রাম ছাড়া! অথচ দেখা যায়, শুকুরমনির পেট ছ-মাসের পোয়াতির মতো ফুলে ঢোল হয়ে আছে!
“কে বইলেছে আমার ছেলে হবেক লাই? দ্যাখ, দ্যাখ আমার পেটটা। লজর কইরে ভাল করে ইদিকে কত বড় পেট হঁয়েছে।… হামি পুয়াতি বটি, বুঝা তর টাকলা অফিসারকে। দিয়া করা হামাকে শাড়ি। আমিও রোজ খাবার লুব, ঘাঁটা লি-ব-অ-অ, গ—।”[১০]
শুকুরমনির মরদ দীর্ঘ সময় নিরুদ্দেশ। এ সময়ে, তার গর্ভবতী হওয়া যে তার ও তার আসন্ন সন্তানের কলঙ্ক, সে সব ভেবে দেখার এতটুকু প্রয়োজন অনুভব করে না শুকুরমনি। কারণ—‘গায়ের কাপড়টাও তো নাই বললেই হয় শুকুরমনির। কদিন খাওয়া হয় নাই কে জানে।’[১১]
শেষমেষ শুকুরমনি খাবার, কাপড় পেয়ে যেত হয়তো। কিন্তু, হঠাৎ ভিড়ের মধ্যে থেকে নিরুদ্দেশ থাকা স্বামী ক্যাঁদা লাফিয়ে পড়ে শুকুরমনির উপর। নিজের কানে সে তার বউয়ের কুকীর্তি শুনেছে। নিরুদ্দেশ ছিল ভয়ে। এখন গ্রামে ফিরেই বউয়ের ব্যাভিচার শুনে ঝাঁপিয়ে পড়েছে শুকুরমনির উপর। কিন্তু এরপরই, সেখানকার সকলে হতভম্ব হয়ে যায়। তার সঙ্গে পাঠকও। কারণ, সেই ধস্তাধস্তিতে শুকুরমনির গর্ভ খসে পড়ে! আর দেখা যায়, বাবুদের বাড়ি থেকে পাওয়া ছেঁড়া টেরিলনের একটা লাল জামা দিয়ে নকল গর্ভ বানিয়েছিল শুকুরমনি!
লাল রং দিয়ে লেখক কি রক্ত বোঝাতে চাইলেন? গর্ভকে ভিক্ষার পাত্র রূপে ব্যবহার করতে বাধ্য হওয়া মায়েদের গর্ভের? নাকি স্বার্থবাদী সমাজের অন্তরের রক্তক্ষরণের রক্ত? ডাস্টবিন উপচানো খাদ্যস্তূপের নীচে তলিয়ে যাওয়া হাভাতে শুকুরমনিদের হাহাকার বাবুদের কানে পৌঁছাক এতটুকু আশা এ আখ্যান অবশ্যই করতে পারে। হাওড়া, শিয়ালদা, বর্ধমান রেলস্টেশন চত্বরে এমন মায়েদের হামেশাই আমরা দেখি। নাক সিঁটকে গালাগাল, কটুক্তি ছুঁড়ে চলে আসি। যদিও, এদের গর্ভ নকল থাকে না। কিন্তু ব্যবহৃত হয় সেই ভিক্ষাপাত্র রূপেই।
শাগতুলি ডোম (‘জলকন্যার নুনভাত’) :
শাগতুলি বাঁশের ছিলা দিয়ে ঝুড়ি, ফুলের সাজি এসব তৈরি করে শহরের হাটে বিক্রি করে আসে। সম্প্রতি তার দুই ছেলেমেয়ের জ্বর হওয়ায় সে তার স্বামীকে হাটে পাঠিয়েছিল। ভেবেছিল, স্বামী রতন ফিরলে ঝুড়ি বিক্রির টাকায় অসুস্থ ছেলেময়ের জন্য মুখে রুচবার মতো কিছু একটা করে খাওয়াবে, ওষুধ কিনবে। কিন্তু দেখা যায়, রতন ঝুড়ি বিক্রির সব টাকা মদের ভাঁটিতে উড়িয়ে এসেছে। বাচ্চা দুটোর কথা ভেবে মা শাগতুলি অস্থির হয়ে ওঠে, ফুঁসতে থাকে ক্রোধে। ‘নিম অন্নপূর্ণা’-র মতো শাগতুলির বুকও মোচড় দিয়ে ওঠে। নিরুপায় সে। বাচ্চা দুটোর ঝোল-ভাত খাবার অশ্রুসিক্ত, একঘেয়ে বায়নায় পোষা মোরগটা কাটতে উদ্যত হয় সে। আর তা দেখে নেশাগ্রস্ত রতন তেড়ে এসে চুলের মুঠি ধরে শাগতুলির পিঠে কিল, চড়, ঘুষি বসাতে থাকে এলোপাতাড়ি। কারণ, ওটা তার লড়াই-এর মোরগ। অনেক লড়াই জিতিয়ে মদ খাবার টাকা এনে দিয়েছে পয়া মোরগটা। বাচ্চা দুটোর কান্না ও নিজের অক্ষমতার প্রতি বীতশ্রদ্ধ শাগতুলি আত্মহত্যা করবে ঠিক করে পদ্মবাঁধে ছুটে যায়। তবে, মরদের গায়ে হাত তোলা নিয়ে সে অভিমানী হয়নি। কারণ, শাগতুলি মনে করে শত ঝগড়া, হাতাহাতি যাই হোক ‘মরদের ভালোবাসা’ এমনই হয়।
‘মরদে একটু আধটু মারবে না এ কথাটা ভাবতেই খারাপ লাগে শাগতুলির।’[১২]
—গল্পটা এরপর শাগতুলির নিরুদ্দেশে বা ট্র্যাজিক মৃত্যুতে শেষ হতে পারত। কিন্তু, তা হয়নি। বরং, এখান থেকেই যেন গল্পটা শুরু হয়।
জলে ডুবে মরতে পদ্মবাঁধে ঝাঁপিয়ে পড়া শাগতুলি, নিজের কাণ্ডজ্ঞানের কথা ভেবে জলের তলায় হঠাৎ হেসে ওঠে আপন মনে। শাগতুলি মনে মনে ভাবে, কীভাবে সে এই পদ্মবাঁধের জলে, ডুবে মরতে পারে? পদ্মবাঁধের তলদেশেই তো তার জীবন-দেবতা লুকায়িত। হতদরিদ্র শাগতুলি সেই কোন ছোটো থেকে অকালের সময় পদ্মবাঁধের তলা থেকে শামুক, গুগুলি, ঝিনুক তুলে আনে। দুর্গাপুজোর সময় পদ্মফুল তোলে। সে সব বিক্রি করে দুটো পয়সা পায়। আর এ বাঁধ তো তার পালক-মা, যশোদা মা। বাঁধের বড়ো গর্ভেই তো তার দ্বিতীয় জন্ম। শাগতুলির প্রাণ-ভ্রমরা পদ্মবাঁধেই। এবার সেই পদ্মবাঁধের জলে ডুবে মরবে কী করে সে?
‘শাগতুলি ডোম জলে ডুবে মরবে—এ আবার হয় নাকি। জলেই তো ওর বসতি।… জল থেকেই তাকে তুলে আনতে হয়েছে বাঁচার রসদ।’[১৩]
আত্মহত্যার উদ্দেশ্যে জলে ঝাঁপানো শাগতুলি যখন জলের তলদেশে পৌঁছোয় তখন তার হাত-পা-মন অবশ হওয়ার বদলে উলটে সচল হয়ে ওঠে। এরপর ঘণ্টাখানেক ধরে সে, জলের তলা থেকে শামুক, গুগুলি সংগ্রহ করে, আঁচলে ভর্তি করে বাড়ি ফিরে আসে। মরতে গিয়ে বাঁচার রসদ নিয়ে ফিরে আসে শাগতুলি।
দিন আনা, দিন খাওয়া মানুষদের জীবনে জটিল সংবর্ত নেই। খাবার, খাবার আর খাবার। এ জোগাড় করে উঠতেই তারা দিশাহারা। শাগতুলিরা তাই মরতে গিয়েও মরে না, আরও দ্বিগুন মানসিক বলে বাঁচার রসদ নিয়ে ফিরে আসে।
মুংলী ও সাবিত্রী (‘মুখ’) :
কলাপাতি গ্রামের দুই নারী—মুংলী আর সাবিত্রী। একজন নিরক্ষর আরেকজন স্কুল ফাইনাল পাশ করা শিক্ষিত নারী। কিন্তু দুজনেই বিধবা। বাস্তবিক, একই কয়েনের এপিঠ-ওপিঠ। দুই নারীরই ভাগ্যনিয়ন্ত্রক হয়ে ওঠে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ।
কয়েকদিনের বুকের ব্যথায় ভোমর মাঝি মারা যায়। জানগুরু বলে, গ্রামে ‘বিষাই’ আছে। সুতরাং আরও অনেকের অনিষ্ট হবে। তাছাড়া হপন মাঝির দুধেলা গাই, তার দাদা পদকের একদিনের রক্ত-পায়খানায় মৃত্যু ও পদকের বড়ো ছেলে মাহিন্দীর সর্পদংশনে মৃত্যু হয়েছে। তাই, নিকটবর্তী মান্যগণ্য সাঁওতাল সমাজের সকল মানুষ ও জানগুরুকে আহ্বান জানানো হয় কলাপাতি গ্রামে। সভা বসে পঞ্চায়েত মেম্বার হপনের ভিটেয়। অনুমান সাপেক্ষ, যথাসাধ্য আপ্যায়ন জানগুরুরা পেয়ে থাকবেন।
নানা কারসাজি, তন্ত্রোচ্চারণ করার পর জানগুরুরা পদকের বিধবা স্ত্রী, হপনের বউদি মুংলীকে ডাইন সাব্যস্ত করে। স্বামী ও জ্যেষ্ঠ পুত্রের মৃত্যুর পর মুংলী তার আরেক পঙ্গু সন্তানকে নিয়ে হপনের বাড়ির লাগোয়া বাড়িতে থাকত। জানগুরুদের এমন সিদ্ধান্তের পর একদল সাঁওতাল টাঙ্গি-তলোয়ার-লাঠি নিয়ে তেড়ে যায় মুংলীর ঘরের দিকে। মুংলী আগাম তার বীভৎস পরিণাম আঁচ করতে পেরে সন্তানকে ফেলেই প্রাণভয়ে জঙ্গলে পালায়। এদিকে মুংলীকে না পেয়ে অন্ধবিশ্বাসে উন্মত্ত মানুষগুলো মুংলীর বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয়। আলো আর ধারালো হাতিয়ার নিয়ে জঙ্গলে খুঁজতে বেরোয় মুংলীকে। প্রসঙ্গত, জরিমানা না দিয়ে ডাইন অপবাদ নিয়ে পালিয়ে যাওয়া আরও মারাত্মক সাঁওতাল সমাজে।
ডাইনি নিয়ে বিশদে আলোচনা এখানে সম্ভব না। তবে, সাঁওতাল সমাজ-সংস্কারক শিক্ষিত কয়েকজন সাঁওতাল মানুষের সঙ্গে কথা বলে জেনেছি—অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভিকটিমের নিকট কোনো আত্মীয় টাকা খাইয়ে জানগুরুদের হাত করে ‘ডাইনি’ অপবাদ দেওয়া করায়। অবলা বিধবা নারীদের জমিজায়গা হাতিয়ে নিতে। ডাইনি প্রথা নিয়ে রচিত অনেক কাহিনিতে এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির উপর আলোকপাত করা হয়নি। জ্যোৎস্না কর্মকার বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়েছেন। গল্পে দেখি, বিধবা মুংলী তার পঙ্গু ছেলের খরচপত্রর জন্য স্বামীর ভাগের কিছু পরিমাণ জমি বিক্রি করে দেয়, দেওর হপনকে না জানিয়ে। আর এতেই হপন অসন্তুষ্ট হয়।
“আগে মেথির [হপনের স্ত্রী] সঙ্গে ভালোই ভাবসাব ছিল মুংলীর। এখন ভাব একটু কেন বেশ ভালোই চটকেছে।… টাকার জন্য পদকের বিশাল জমিজমার একটা ছোটো অংশ রাবণকে বিক্রি করার পর থেকেই হপনও ভালো করে কথা বলে না আজকাল।”[১৪]
ঘটনার কিছু পর, অর্থাভাবের দরুন মুংলী আবার কিছু জমি বিক্রি করতে উদ্যত হলে, হপন উল্লেখিত সভাটি ডাকে।
‘এই হপনই এখন লোক জড়ো করেছে। লোক ডাকলে আসবে নাই বা কেন। হপন যে এখন একজন হোমরাচোমরা পার্টি মেম্বার।’[১৫]
মুংলীর মতোই স্বামীহীনা সাবিত্রীর জীবনেও ওই একই রাতে নেমে আসে নারকীয় দুঃস্বপ্ন। ভোর থেকে রাত, বাড়িতে চাকরের মতো মুখ বুজে খেটে চলা স্বামীহীনা সাবিত্রীকে সে রাতে তার শাশুড়ি, দেওর, ভাজরা মিলে অকথ্য নির্যাতনে আধমরা করে রক্তাক্ত, অচেতন অবস্থায় ফেলে রাখে। উদ্দেশ্য দলিলে সই করানো। জ্ঞান ফিরে পেয়ে শতছিন্ন সাবিত্রীও মুংলীরই মতো প্রাণভয়ে টলতে টলতে জঙ্গলে ঢোকে। একই রাতের অন্ধকার, সমাজের বিপরীত মেরুর দুই নারীর জীবনে আঁধার ঘনিয়ে তোলে। শিক্ষা ও ডিগ্রিতে পেডিকিওর-মেনিকিওর করা নখ-দাঁতের অধিকারী দ্বিপদী পশুদের থেকে পালিয়ে মুখোশহীন শ্বাপদদের মাঝে গভীর জঙ্গলে দুই নারী আশ্রয় নিয়েছিল প্রাণ বাঁচাতে।
মেনকা (‘মেনকার সাবান’) :
প্রান্তিক অঞ্চলে ধর্ষণ, ব্যভিচারের ঘটনা প্রায়ই ঘটে থাকে। কিন্তু, লোকলজ্জার ভয়ে তা সামনে আনেন না বহু নারী। বিত্তবান বাড়ির পুরুষেরা দরিদ্র মেয়েদের অল্প কিছু টাকার বিনিময়ে বা প্রেমের ফাঁদে, নিম্ন মূল্যের কিছু প্রসাধনী দ্রব্য দিয়ে আয়ত্তে আনে। আর, সময় সুযোগে তাদের যৌন লালসার শিকার বানায়। মেনকাও এমনই একজন ঠকে যাওয়া বা অভাবের তাড়নায় ঠকতে বাধ্য হওয়া যুবতী। সে, তার পাড়াতুতো কন্ট্রোলকাকার যৌন লালসার শিকার হয়। নানা সময়ে এই কন্ট্রোলকাকা তাকে চুল বাঁধার ফিতে, সুগন্ধী সাবান, তেল এসব বিনামূল্যে দিয়েছে। বদলে সুবিধা মতো মেনকার বুকে, পাছায় হাত দিয়েছে। তার কুমারীত্ব নষ্ট করেছে। ব্যবসায়ী কন্ট্রোলকাকার স্বল্প মূল্যের ফিতে, সাবানের ‘ইনভেস্টমেন্ট’-এর ফলস্বরূপ মেনকা গর্ভবতী হয়ে পড়ে অচিরেই।
মেনকা তখন বুঝতে পারে সে অন্তঃসত্ত্বা, যখন দু-মাস ধরে পিরিয়ড্স হয় না তার। লোকনিন্দার ভয়ে গ্রামের স্বাস্থ্যকেন্দ্রের দিদির কাছেও কিছু বলে উঠতে পারে না সে। মেনকা জানে এ খবর গ্রামে একবার রটে গেলে টোন টিটকিরির ফোয়ারা ছুটবে। কেউ তাকাবে না তার দিকে ঘেন্নায়। আবার যারা তাকাবে, তারা চোখ দিয়েই চেটে নেবে তার শরীর। লোকনিন্দার ভয়ে মেনকা বেছে নেয়, গর্ভ নষ্ট করার প্রান্তিক পদ্ধতি ‘কাঠি নেওয়া’।[১৬] এ বিষয়ে ওস্তাদ কালীর মা। গা শিউরে ওঠা সে পদ্ধতির শব্দ-সংযমী বর্ণনা দিয়েছেন লেখিকা—
“কয়েক থাক ইটের ওপর দুদিকে পা দিয়ে পায়খানায় বসার মতো বসতে হয়। কাঠিটা জায়গা মতো রেখে একটা একটা করে ইট একজন কেউ সরিয়ে সরিয়ে দেয় আর কাঠিটা সেই মতো একটু একটু করে ঢুকতে ঢুকতে একসময় ব্রহ্মাণ্ড ফুটো করে দেয়।”[১৭]
দিশাহারা, কিংকর্তব্যবিমূঢ় মেনকা চোখ-কান বুজে একদিন নিজে নিজেই মুড়ি ভাজার ধারালো, শক্ত বাঁশের কুঁচিকে যোনিতে ঢোকাতে যায়। এতে, হঠাৎ খোঁচা লাগার মর্মান্তিক যন্ত্রণায় সে কাতরে অনুচ্চ কেঁদে ওঠে৷ তার মনে পড়ে যায়—‘কাঠি নিতে গিয়েই শামলি পচে মরলো।’ [১৮]
‘কাঠি নেওয়া’ পদ্ধতি প্রান্তিক অঞ্চলে গোপনে আজও চললে অবাক হওয়ার নেই। সেখানে হয়তো কনডোম, গর্ভনিরোধক বড়ি অপ্রতুল কিংবা চক্ষুলজ্জার ভয়ে ব্যবহার করা হয় না। বাস্তবিক, এ শতকেও শহর, মফস্সলের অগণিত শিক্ষিত মেয়ে স্যানিটারি ন্যাপকিন, ব্রা, প্যান্টি, গর্ভনিরোধক বড়ি কিনতে পারে না! কারণ, পুরুষতান্ত্রিক সমাজের তৈরি করা চক্ষুলজার অচলায়তন। ‘কাঠি নেওয়া’ পদ্ধতিতে লম্বা কাঠি দিয়ে (যোনি-পথে জরায়ু) তীব্র খুঁচিয়ে ক্ষত সৃষ্টির দ্বারা ভ্রূণকে পচিয়ে নষ্ট করা হয়। জরায়ুতে পচন ধরে কিংবা যোনিতে সেপটিক থেকে ঘা হয়ে পচন ধরে শামলির মতো এতে অনেকেই মারা যায়। কিন্তু এ পথ কেন? এর উত্তর, নিন্দা। যে সমাজব্যবস্থা তার মুখে খাবার, গায়ে কাপড় তুলে দিতে পারে না, উলটে তার দৈন্যতাকে ব্যবহার করে সেই সমাজই তাকে ধর্ষণ করে কিংবা স্বেচ্ছা ধর্ষিত হবার পথে নামতে বাধ্য করে। সেই সমাজের-ই নিন্দার ভয়ে। জ্যোৎস্না কর্মকারের সাহসী কলমে মেনকা-বৃত্তান্ত না উঠে এলে বাংলা সাহিত্যে এ প্রান্তিক সমাজ-বাস্তবতা হয়তো অজানাই রয়ে যেত।
মিস মোহিনী (‘জলবাসর’) :
মুনিয়া, সন্তানের ভরণ-পোষণের জন্য মিস মোহিনী নাম নিয়ে চটুল ভোজপুরী গানের সঙ্গে অশ্লীল ডান্স করে বেরায় গ্রামে গঞ্জে, মফস্সলের পাড়ায়-বেপাড়ায়। টাইট কাঁচুলি, ঝকমকে ছোটো পোশাক পরে শরীরী বিভঙ্গে যৌন উত্তেজনা ছড়িয়ে দেয় দর্শকদের মধ্যে। পাগল হয়ে ওঠা দর্শক মোহিনীর কোমর, বুক ছুঁয়ে দেখতে হুড়োহুড়ি ফেলে দেয়। কত পুরুষের যে স্বপ্নের সহচরী মিস মোহিনী, মিস ডায়মন্ডরা! কোনো কোনো অনুষ্ঠানে সারারাত নাচতে হয় চটুল গানের তালে তালে। অত্যুৎসাহে কখনও গুলিও চলে যায় লোকাল পার্টির তাবড় নেতা বা সমাজপতির বন্দুক থেকে। সে গুলি ছিটকে আহত হবার শঙ্কা থাকে। হয়ও। শ্লীলতাহানী হবার সম্ভাবনা তো থাকেই। এমনকি রেপ পর্যন্ত। বাইজি, নাচনি, লেডি ডান্সারদের জীবন প্রায় এক প্রবাহের। এত ঝুঁকি সত্বেও মোহিনীরা ডান্স করতে যায়। পুরুষ-মনে আগুন ধরায়। কারণ, অধিকাংশের পরিবারে অর্থের টান। আমরা ভুলে যাই, এই মিস মোহিনীরাই সন্তানের মা। অনুষ্ঠান তাদের পেশাদারিত্ব মাত্র। পণ্য ভেবে নেওয়ার বাইরেই তাদের প্রকৃত পৃথিবী। লেখিকা এ দিকটি দক্ষতার সঙ্গে চেতন করিয়েছেন আমাদের। এমনই এক ডান্সারকে দেখতে নিভৃত সাজঘরে গিয়েছিল লালসায় পরিপূর্ণ এক পুরুষ। কিন্তু—
“এ কাকে খুঁজছে সে? কাকে দেখছে?… এখানে [সাজঘর] যে বসে আছে সে তার বুক উদোম করে দু-দুটি শিশুকে পরম মমতায় দুধ খাওয়াচ্ছে। এই স্তনদায়িনীই একটু আগে স্টেজ মাতাচ্ছিল।”[১৯]
আলাস্কা, শকুন্তলা, প্রজ্ঞাপারমিতাদের ভিড়ে টুনি, মেনকা, শাগতুলি, মুংলী, মিস মোহিনীরা পরিচিতি পায় না। কেউ জানে না তাদের জীবন-যন্ত্রণার অব্যক্ত রোদনের ভাষা। জ্যোৎস্না কর্মকারের কলমে ফোটোশপের কারসাজি নেই। কাহিনির শব্দ, ভাষা, সংলাপ, চরিত্র লোকসমাজ থেকে তুলে আনা। তাঁর সৃষ্ট নারীবিশ্বে বিচিত্র সব নারী, পরস্পরের থেকে পৃথক সমস্যায় প্রত্যেকে জর্জরিত। ভিন্ন জীবন-বোধ, ভিন্ন লড়াই। তবু তারা এক। তাদের লড়াইয়ের ক্ষেত্র আলাদা, কিন্তু, লক্ষ্য এক। যেমন, গ্রাম্য টিয়ামনি তার ঠোঁটে সালকের জন্য প্রিয় পুরুষের কাছে আকর্ষণীয় হয়ে উঠতে পারছে না (‘ইহলোক’); সরকারি রুরাল অফিসার ঊর্মি ভিড় বাসে শ্লীলতাহানীর শিকার হয়। ভাইয়ের বয়সি এক ছেলে ভিড় বাসে ঊর্মির ঊরুতে হাত দেয়, বগলের ফাঁক দিয়ে ছুঁতে চায় বুক (‘লাগাম’); গ্রামে বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কে জড়িয়ে পরার জন্য গ্রাম পঞ্চায়েতে শাস্তিবিধান হয়—দুরাচারী পুরুষটির বোনের ইজ্জত নেবে কুলোটা বধূটির স্বামী (পৃথিবী); দারিদ্র্যের চাবুকে আগাপাশতলা ছাল ছড়ে যাওয়া গ্রামের সকল বয়সের নারীরা বিড়ি বাঁধার কাজ করে। মজুরি মাত্র দেড় টাকা প্রতি এক হাজার বিড়ির বিনিময়ে (‘ঘেরাও’)। এমনই এক দরিদ্র মা, লক্ষী। সন্তানের মুখে খাবার তুলে দেবার জন্য মজুর খাটে দিনে আর আঁধারে পতিতাবৃত্তি করে অল্প কিছু টাকার বিনিময়ে। তাদের খদ্দের হলো খেটে-খাওয়া পুরুষেরা (‘রেললাইন’)। ভিক্ষা করে রোজ-আনা রোজ-খাওয়া দুঃখীকে ভোটের দিন জোর করে ভিক্ষা করতে যেতে দেওয়া হয় না। ফলে সেদিন দুঃখী তার বাচ্চাকে নিয়ে খিদের যন্ত্রণায় কাতরায় সারারাত। যে কারণে তাকে ভিক্ষা করতে যেতে দেওয়া হয়নি গণতন্ত্রের অমূল্য সেই ভোটটি দিতে গিয়ে ভিখারি দুঃখীর উপলব্ধি হয়—‘…পুষ্টিহীন চোখে সবকটা ছাপকেই তার একধরনের গুবরে পোকা মনে হচ্ছিল।‘[২০]
কত কম শব্দে, বৃহৎ ও নগ্ন-বাস্তবকে ধরলেন জ্যোৎস্না কর্মকার তাঁর সহজাত শব্দ-সংযমী প্রতিভায়। হানলেন তীব্র শ্লেষ, বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক সিস্টেমের বিরুদ্ধে।
জ্যোৎস্না কর্মকার এবং তাঁর নারীবিশ্বের নারীরা পাঠকদের কাছে ব্রাত্য হয়ে আছে দেখে অবাক ও আহত হতে হয়। তাঁর নির্মাণ তা ‘ডিজার্ভ’ করে না। মহাশ্বেতা দেবীর মতো জ্বলন্ত অঙ্গারসম শব্দ, বাক্য, ন্যারেটিভ তাঁর নয়। তাঁর শব্দ থেকে উপমা কবিতার মতো। এক ঠান্ডা আগুনের মতো। যা নিভে যায়নি, অপেক্ষায় আছে দাবানলের। সে ঠান্ডা গনগনে আগুন মনের অতলে গিয়ে ধিকিধিকি জ্বলতেই থাকে। সব শেষে বলব, জ্যোৎস্না কর্মকারের গল্প আয়েসে সময় কাটাবার জন্য নয়, প্রতিটি শব্দ, বাক্যবন্ধকে মনোযোগ সহকারে আত্মস্থ করতে হয়। এখানেই তাঁর স্বাতন্ত্র্য ও সফলতা।
লেখিকার মুখোমুখি:
প্র: আপনার গল্পসাহিত্য তো এক স্বতন্ত্র নারীবিশ্ব। নারীদের কথা বলার এই তাগিদ কীভাবে এল?
উ: আমার স্বীয় গোলার্ধটি নারী-বেষ্টিত। যেমন পারিবারিক, তেমনি ও ততখানি কর্মজীবনও। বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রণায় জর্জরিত, নানা বয়সের, নানা ধর্মের, নানা বর্ণের নারীদের দেখেছি একদম কাছ থেকে। পরিবারে মায়ের অব্যক্ত কান্না দেখেছি। রান্নার জন্য মাটির হাঁড়ি ব্যবহার হতো। সে হাঁড়ি কোনো কারণে ভেঙে গেলে মায়ের প্রতি অশ্লীল তিরস্কারের বিষ-বাণ ধেয়ে আসত। ছোটো আমি দাঁড়িয়ে তা শুনতাম। দেখতাম মায়ের চোখের জল। যা আমাকেও বিদ্ধ করত ভিতর থেকে। তখন থেকেই মায়ের হয়ে, বলতে গেলে মেয়েদের হয়ে আমার কান্নার শুরু। ছেলে নয়, পরের পর মেয়ে গর্ভে ধরার জন্য শারীরিক নিগ্রহ দিনের পর দিন সহ্য করতে হয়েছিল মা-কে। যৌথ পরিবারে সে সব পীড়ন আরও বেড়েছিল বাবার অসুস্থতার পর। এছাড়া, ব্যক্তিজীবনে পরিবার থেকে, প্রতিবেশী সমাজ থেকে অসংখ্যবার আঘাত পেয়েছি। দুমড়ে-মুচড়ে গেছি। আবার দাঁড়িয়েছি। পরিবারের অর্থনৈতিক দুরাবস্থায় আমাকে কাঁধ দিতে হয়েছিল। বোনরা ছিল। তাদের বড়ো করা আমার কর্তব্য ছিল। এসব ছাড়া, কর্মজীবনে মহিলা ও শিশুদের নিয়ে দীর্ঘ সময় সমাজকল্যাণ দপ্তরে কাজ করেছি। পরবর্তীকালে অবহেলিত, দুঃস্থ, ভবঘুরে মেয়েদের হোমের দায়িত্বে ছিলাম। হোম বিভিন্ন ধরনের হয়। এ জীবন আমায় প্রান্তিক নারীদের সংগ্রামকে চিনিয়েছে। বুঝেছি, তাদের লড়াই বড়ো অন্যরকম! তাদের নিরুপায় অবস্থা আমার ভিতরে আঁচড় কাটত। রাত ফুরিয়ে গেছে কত, তাদের কথা ভাবতে ভাবতে। কলম ধরলে তাই তারা সবার সামনে এসে দাঁড়ায়। নিজেই নিজের কাছে ওদের হয়ে দাবি রাখি। ফলত…।
প্র: শুনেছি আপনার বাবা একজন সক্রিয় বামপন্থী কর্মী ছিলেন?
উ: হ্যাঁ। তিনি অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির একজন অন্যতম সংগঠক এবং নেতা ছিলেন। চায়না অ্যাগ্রেশনের সময় জেলবন্দি করা হয় তাঁকে। মানসিক টর্চার সহ্য করেছেন জেলে। পাগল কয়েদিদের সঙ্গে বাবাকে দিনের পর দিন রাখা হয়েছিল। দেখেছি তার ফল কী ভয়ানক হয়েছিল। সেই পীড়নই নাড়িয়ে দিল পরিবারের ভিত। জেল থেকেই বাবা সিজোফ্রেনিয়ায় আক্রান্ত হলেন। অসুস্থতার কারণে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল তাঁকে। এরপর তো পরিবার ও আমার জীবন বহু উত্থানপতনের গ্রাফ। রাঁচিতে চিকিৎসার খরচ, ঘরে-বাইরে হেনস্তা এসব নানা ঘটনা চলছিলই। যৌথ পরিবারে আট ভাই বোনকে নিয়ে মায়ের সংগ্রাম। তারই মাঝে আমাদের বেড়ে ওঠা।
প্র: লেখালেখির শুরু কেমন করে?
উ: লেখালেখির আগেই লেখালেখির শুরু হয়ে গিয়েছিল মনে মনে। প্রথমে কবিতা। মনের কষ্ট, যন্ত্রণা, অসহায়তাগুলো নির্জন সিঁড়িবিহীন ছাদে উঠে কাগজে উজার করে দিতাম। তারপর, তৎক্ষণাৎ ছিঁড়ে কুটিকুটি করে হাওয়ায় উড়িয়ে দিতাম। আমার যন্ত্রণার ধ্বনিগুলো ছাদ থেকে ছোঁড়া কাগজের টুকরোর সঙ্গে ভেসে ভেসে ছড়িয়ে পড়ত ঘাসে, পাঁচিলে, আস্তাকুঁড়ে…আর আমি ভেজা চোখে দেখতাম দু-চোখ ভরে। পরে ছদ্মনামে স্কুলের দেওয়াল পত্রিকায় লেখা দিয়েছি। প্রশংসা শুনেছি অপরিচিতর থেকে। ভালো লাগত। তারপর স্বনামে কলেজ ম্যাগাজিনে। বি. এড. পড়ার সময় প্রথম গল্পটি লিখি। আর, সারা বাংলা শরৎ সাহিত্য প্রতিযোগিতায় প্রথম হই।
প্র: আপনার গল্পের নারী চরিত্ররা, যেমন ধরুন, মেনকা… এই যে ‘কাঠি নেওয়া’ পদ্ধতি, এর কথা কোথাও শুনেছিলেন? এমন কাউকে দেখেছিলেন?
উ: প্রথমেই তোমায় বলি, আমার গল্পের বেশিরভাগ নারী চরিত্ররা চাক্ষুষ দেখা, নয়তো কাছের কারও থেকে শোনা। কল্পনার কালিতে চরিত্ররা দাঁড়িয়ে নেই। গল্পে তাঁদের রক্ত-ঘাম-কান্না-লড়াই-অসহায়তা বাস্তবের। পাঠককে লেখা খাওয়ানোর কথা ভাবিনি কোনোদিন। প্রসঙ্গে আসি, কর্মসূত্রে আমি যখন পুরুলিয়ার মানবাজারে ছিলাম তখনই তিন-চার জনের কথা শুনেছিলাম, যাঁরা কাঠি নিয়েছিলেন। ভাবলেই গা শিউরে ওঠে! তবে মেনকাকে আমি দেখেছিলাম। মেয়েটি আমার এক কর্মীর অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের উপভোক্তা ছিলেন একসময়। প্রায়ই তাঁর কর্মকাণ্ডের কথা শুনতাম। অবাক ও শিহরিত হতাম। গল্পে যে চরিত্র, বাস্তবের মেনকাও তাই। এ প্রসঙ্গে জানাই, জ্ঞানদাময়ী নামে আমার অতি প্রিয় ও বাধ্য একজন কর্মী ছিলেন। বিধবা। সে-ও অবাঞ্ছিত মাতৃত্বের কলঙ্ক থেকে বাঁচতে এই কাঠি নিয়েছিল। যা থেকে সেপটিক হয়ে বহু যন্ত্রণা পেয়ে সে একসময় মারা যায়। বাঁকুড়া হাসপাতালে মারা গিয়েছিল ও। আমি সে সময় বাইরে ছিলাম। ফিরে এসে শুনেছিলাম, হাসপাতালে যন্ত্রণায় কাতরাতে কাতরাতে সে অনেকবার আমায় খুঁজেছিল। কেবল নাকি একবার দেখতে চেয়েছিল। হয়তো কিছু বলত! সে সব তো আর জানা হলো না! যাই হোক, সেই যন্ত্রণা, আফশোসের ভার থেকেই লেখা হয়ে গিয়েছিল—‘মেনকার সাবান’। আরও জানলে অবাক হবে, যেহেতু জ্ঞানদাময়ী কাঠি নিতে গিয়ে মারা গিয়েছিল, তাই তার দেহ দাহ করেননি গ্রামের লোকেরা। কাছের একটা বনে ফেলে দেওয়া হয়েছিল জ্ঞানদার শরীরটা। কাক, শকুনে ছিঁড়ে খেয়েছিল সে শরীর।
প্র: মেনকাদের কথা বলতে গিয়ে ‘অশ্লীল’ শব্দ এসে যাবার কথা মনে হয়নি? পাঠক, সমাজ কীভাবে রিঅ্যাক্ট করবে…!
উ: না। যা—যা, তা—তাই-ই ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছি। কোনো সংশয় মনে আসেনি। তবে বলব, মেনকাদের কথা স্নো-পাউডার দিয়ে বলা-ই হলো অশ্লীলতা।
প্র: ‘নারীবাদ’ বিষয়টিকে কীভাবে দেখেন?
উ: নারীদের আমি ‘নারী’ নয়, মানুষ হিসাবে দেখি। নিজে একলা নারী হওয়ায় নারী-মানসিকতা অনুভব করতে পারি। এ কথা তো স্বীকার করতেই হয় যে, শোষিতের মধ্যে শোষিত হচ্ছে নারীই। কুসংস্কার, দমনপীড়ন, পুরুষ ও নারী মনের অন্ধকারগুলো হামলে এসে আঁচড় দেয় নারী অস্তিত্বে। আর শারীরিক, মানসিক ভাবে ক্ষতবিক্ষত করে নারীদের।
প্র: আপনার গল্পে পুরুষ চরিত্র সেভাবে আসেনি কেন?
উ: এসেছে তো। তবে কম। কারণ, আমি মেয়েদের যেভাবে চিনি, বুঝতে পারি, পুরুষদের পারি না। মেয়েদের দুঃখ-যন্ত্রণা-আহ্লাদ-আনন্দ-লজ্জার কথা তারা আমায় বলে। আমি দেখি, অনুভব করি। যা পুরুষদের ক্ষেত্রে ঘটেনি। তার মানে তো এটা নয় যে, পুরুষ বা ছেলেরা অত্যাচারিত হয় না? বরং মেয়েদের মতোই কখনো-কখনো তারাও অত্যাচারিত হয়। বর্তমান সমাজের গভীর ব্যধি হচ্ছে ধর্ষণ। খবরের কাগজ খুলতেই ভয় লাগে! মর্মান্তিকতায়, পাশবিকতায় একে অপরকে টেক্কা দিতে চায় যেন! ছেলেরাও তো ধর্ষিত হয়। কিন্তু, মেয়েদের মরতে হয় কলঙ্কের জন্য। ছেলেদের তা হয় না। রাস্তার পাশে কিছু কিছু ধাবায় কিশোর ছেলেদের উপর চলে যৌনপীড়ন। যাকে ‘দেওয়াল ধরা’ বলে। সমস্ত দিন খাটুনির পর যৌনপীড়ন অনেকেই সহ্য করে নেয় পেটের দায়ে। কিন্তু, নারী ধর্ষণের তুলনায় সে সংখ্যা খুবই কম। অস্বীকার করা তো যায় না যে, ধর্ম-বর্ণ-বর্গ-বয়স-সমাজ ভেদে নারীরাই অত্যাচারের মাড়াইকলে প্রতিক্ষণে, নানাভাবে পেষিত হচ্ছে। নারী শরীর ভোগ্যপণ্য ছাড়া আর কিছু নয়? আমার কলমে তাই নারীরা আসেন, আসবেন। তাঁদের যন্ত্রণা আমি অনুভব করি মরমে মরমে।
প্র: এমন কোনো অভিজ্ঞতা, যা নিয়ে লিখব ভেবেও লেখা হয়ে ওঠেনি?
উ: আছে। আমার হোম জীবনের অভিজ্ঞতা বড়ো নির্মম সত্য। ইচ্ছা আছে এ নিয়ে বিস্তারে লিখব। [প্রকাশিত—‘মেয়েদের হোম’, গাঙচিল, ২০২০] তাছাড়া, গল্প লেখার মতো অভিজ্ঞতা তো অনেক আছে। সব লেখা সম্ভব না। এ মুহূর্তে যেমন একটা ঘটনা মনে পড়ছে। আমি তখন পুরুলিয়া কিংবা বাঁকুড়ায় প্রোজেক্টের কাজ করছি। একদিন একটা মেয়ে এসে হঠাৎ বলে কিনা, আমি লাইগেশন করব দিদিমণি। শুনেছিলাম ওর স্বামী নেই। সে-কথা ওকে বলতেই, ও খেঁকিয়ে উঠেছিল—‘তো? আমার গতরে কি খিদে নাই?’
প্র: আচ্ছা, গল্পকার জ্যোৎস্না কর্মকার বহুপাঠী না হওয়ার কারণ কী মনে হয়?
উ: পাঠক তাঁর রুচি মাফিক পড়বেন। তাঁর অপচ্ছন্দ হলে বাতিল করবেন। এখানে কিছু বলা ন্যায়সঙ্গত নয়। তবে, অপছন্দ করতে হলেও তো পড়া দরকার। সেক্ষেত্রে প্রচার বা বিজ্ঞাপনের ভূমিকা অনস্বীকার্য। মফস্সল থেকে বই বের হবার পর তা প্রচারের ক্ষেত্রে ঘাটতি তো ছিলই। আর এটাও সত্যি প্রান্তিক মানুষের কথা মানুষ পাতে নেয় কম। এ অভাব পূরণ হচ্ছে বটে। যদিও আরও কত অজানা কথা রোজ রোজ জন্মাচ্ছে প্রান্তিক ঘরে ঘরে। দেখো, হিমা দাস [অ্যাথলিট] আজ দেশের মুখ উজ্জ্বল করল। তার চোখের জল আমাদের চোখও সিক্ত করল। একটা স্টেজের সফলতা তাকে পরিচয় দিল। কিন্তু, এমন কত হিমা দাস প্রান্তিক অঞ্চলে প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করে চলেছে তার হিসাব নেই। তারা রোজ জিতছে, রোজ হারছে। কালি ও কলম তাদের জীবন-যুদ্ধকে সম্মান জানাতে পারে। আর এক্ষেত্রে, তাদের পরিচিতির মাঝে মফস্সলের কাগজের সেভাবে প্রচার না পাওয়াটা প্রাচীর হয়ে দাঁড়াচ্ছে, স্রোত হবার পরিবর্তে।
[সাক্ষাৎকারটি ২০১৮ সালের বিভিন্ন সময় জুড়ে কিছুটা লিখিত ও ফোন মারফত নেওয়া।]
সূত্র নির্দেশ:
১. বসু, বুদ্ধদেব। প্রবন্ধ সংকলন, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, পরিমার্জিত দে’জ সংস্করণ, ১৯৮২, পৃ- ৬৭।
২. ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার, দূরাভাষ, ১৯ জুন ২০১৮।
৩. চট্টোপাধ্যায়, বিশ্বদেব। ‘বিচার বিতর্ক ও সন্ধানের গল্প’, পাক্ষিক মানসাই সংবাদ, সম্পা: বিশ্বদেব চট্টোপাধ্যায়, কোচবিহার, জানুয়ারি, ১৯৯৮।
৪. কর্মকার, জ্যোৎস্না। ভূমিকা, ‘ইচ্ছের গন্ধ’, অমৃতলোক সাহিত্য পরিষদ, মেদিনীপুর, ১ম প্রকাশ ২০০৪।
৫. কর্মকার, জ্যোৎস্না। নাম গল্প, ‘টুনির বারোমাস এবং খিদে’, পরিবেশক-পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১ম প্রকাশ ১৯৮২, পৃ. ১।
৬. কর্মকার, জ্যোৎস্না। অন্ধকারে জোনাকি এবং দেবীরা, ‘টুনির বারোমাস এবং খিদে’, পরিবেশক-পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১ম প্রকাশ ১৯৮২, পৃ. ১০।
৭. ঐ, পৃ. ৪।
৮. কর্মকার, জ্যোৎস্না। নকল বুঁদি, ‘টুনির বারোমাস এবং খিদে, পরিবেশক-পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১ম প্রকাশ ১৯৮২, পৃ. ৪৩।
৯. ঐ, পৃ. ৪৩।
১০. ঐ. পৃ. ৪৯।
১১. ঐ. পৃ. ৪৮।
১২. কর্মকার, জ্যোৎস্না। জলকন্যার নুনভাত, টুনির বারোমাস এবং খিদে, পরিবেশক-পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১ম প্রকাশ ১৯৮২, পৃ. ১০২।
১৩. ঐ, পৃ. ১০৩।
১৪. কর্মকার, জ্যোৎস্না। ‘মুখ’, সই গল্প সংকলন, সম্পা: নবনীতা দেব সেন, লালমাটি, কলকাতা, ১ম প্রকাশ ২০১৩, পৃ. ২২৫।
১৫. ঐ, পৃ. ২২৬।
১৬. প্রাগুক্ত।
১৭. কর্মকার, জ্যোৎস্না। নাম গল্প, মেনকার সাবান, রক্তকরবী, কলকাতা, ১ম প্রকাশ ১৯৯৬, পৃ. ৮৬।
১৮. ঐ, পৃ. ৭৮৬।
১৯. কর্মকার, জ্যোৎস্না। নাম গল্প, ‘জলবাসর’, গাঙচিল, কলকাতা, ১ম প্রকাশ ২০১৮, পৃ. ১৪১।
২০. কর্মকার, জ্যোৎস্না। গমের শীষ, ‘টুনির বারোমাস এবং খিদে’, পরিবেশক-পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১ম প্রকাশ ১৯৮২, পৃ. ১২৯।
প্রচ্ছদ ছবি, ফেসবুক