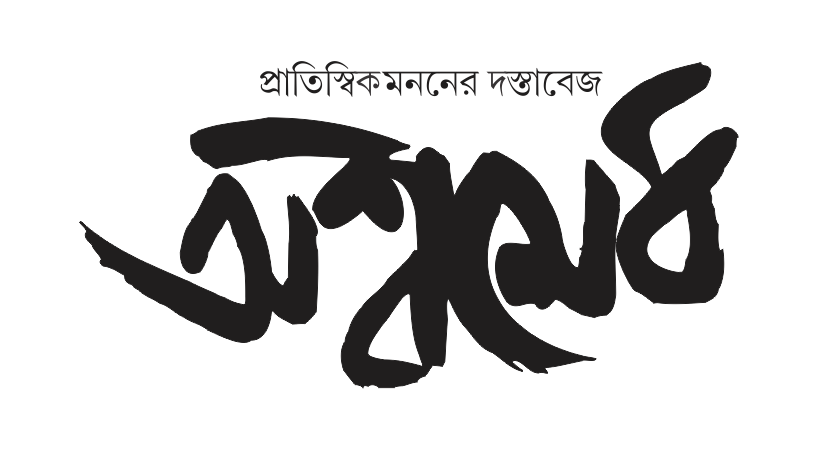বন্দী ভাবে, আমাদের স্বাধীন ভারতের জেলখানায় এমন মিথ্যার প্রশ্রয় এমন অমানুষিক অত্যাচার কখনো থাকতে পারবে না। [১]
নাহ্, স্থানকালপাত্র নির্বিশেষে এই উদ্ধৃতিটির সর্বজনীনতা প্রমাণের কোনো দায় আমার নেই। কোনো পরাধীন ঔপনিবেশিক দেশের জেলবাসীদের কী স্বপ্ন থাকতে পারে, সে ব্যাপারে আদৌ কোনো সার্বভৌম মত আছে কিনা, সেই আলোচনাও আপাতত অবান্তর। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, যে উদ্ধৃতিটি ব্যবহৃত হলো, সেটি একজন মহিলার লেখা। এবং আমাদের আলোচনার মূল আলোকপাতটা সেখানেই। আমরা দেখতে চেষ্টা করব, এই উদ্ধৃতি বেয়ে ‘স্বাধীন ভারত’ পর্যন্ত পৌঁছালে সেই উত্তর-উপনিবেশ এবং আপাত স্বাধীন দেশে মহিলারা যখন কয়েদখানার আখ্যান লিখছেন, তখন সেই উপরিউক্ত স্বপ্নগুলোর ঠিক কতটা পালাবদল হয়, আর কতটাই বা স্বপ্নভঙ্গ। আর কয়েদকথনের কোথায় কোথায় রয়ে গেল সেই পালাবদলের সূত্র।
১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ভারতবর্ষ ঘোষিতভাবে স্বাধীন। এই ‘স্বাধীন’ দেশে যাঁরা বন্দি হবেন রাজনৈতিক কারণে, অর্থাৎ সরকারের বিরুদ্ধে ঘোষিত বিরোধিতায় সামিল হবেন যে মেয়েরা—আলোচনা তাঁদের নিয়ে। তাঁদের নাম জয়া মিত্র (‘হন্যমান’) বা মীনাক্ষী সেন (‘জেলের ভেতর জেল’)। আমরা চাইব তাঁদের বন্দিদশায় লেখা অভিজ্ঞতাকেই পড়ে নিতে।
ইতিমধ্যে, আমরা আমাদের ফোকাসকে অনেকটা নির্দিষ্ট করে তুলেছি। স্থান-কাল-পাত্র সম্বন্ধে আমরা নিশ্চিত। প্রশ্নটা আপাতত তাঁদের অবস্থান নিয়ে। তাঁদের রাজনৈতিক অবস্থান। যেহেতু তাঁরা নারী আবার উত্তর-ঔপনিবেশিক দেশের রাজনৈতিক বন্দিও, ফলে আমাদের আলোকপাতে একটা সংকট থেকেই যায়। কীভাবে তাঁদের দেখা উচিত। রাজনৈতিক বন্দি হিসেবে, নাকি নারী হিসেবে? নাকি সুযোগমতো আপতনবিন্দু পালটে পালটে আমরা দেখে নেব কখন তাঁরা নারী আর কখন নিছক বন্দি। আসলে সমস্যাটা তাঁরা কীভাবে নিজেদের কথা লিখছেন, তার উপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে থাকে।
ভাষা আর কথন। লঙ (langue) আর পারোল (parole)। গঠনবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে একটা ভাষা কাঠামোর এই দুটিই উপাদান। সস্যুর[২] এই দুটিকে কীভাবে ব্যাখা করছেন দেখে নেওয়া যাক—
The language (langue) itself is not a function of the speaker. It is the product of passively registered by the individual. It never requires premeditation…
Speech (parole), on the contrary, is an individual act of the will and the intelligence, in which one must distinguish: (1) the combinations through which the speaker uses the code provided by the language in order to express his own thought, and (2) the psycho-physical mechanism which enables him to externalize these combinations.
সস্যুরকে ব্যাখা করতে গিয়ে হোল্ডক্রফ্ট[৩] বলছেন কিছু অনিবার্য বৈশিষ্ট্যের কথা, যা লঙ আর পারোলকে স্থাপন করে দুটি বিপরীত মেরুতে। লঙ হলো সামাজিক, আবশ্যিক, গোষ্ঠী গঠিত, প্রথাগত, অপরিকল্পিত। অন্যদিকে পারোল হলো ব্যক্তি নির্মিত, প্রয়োগ নির্ভর, প্রথা রহিত এবং পরিকল্পিত।
এখন লঙের বিশেষণগুলোর দিকে একটু ভালো করে খেয়াল করলে দেখা যাবে—যে সমাজ, যে প্রথা, যে গোষ্ঠীর ওপর ভর করে ভাষা দাঁড়িয়ে থাকে, সেই সবই একটা ক্ষমতা-ব্যবস্থার প্রতিনিধি মাত্র। ভাষা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে যা মানুষ আত্মস্থ করে নিতে থাকে। যেহেতু ভাষা কারও ব্যক্তিগত চয়নের ওপর নির্ভরশীল নয়, তাই সেই বিশেষ সামাজিক উচ্চাবচকে সম্পূর্ণ হজম করে না নেওয়া ছাড়া মানুষের কোনো উপায় থাকে না। বলা বাহুল্য, এই উচ্চাবচর কেন্দ্রে কখনও থাকে পুরুষ, কখনও শ্বেতাঙ্গ তো কখনও শহরবাসী।
এর বিপরীত কোনো স্বর নির্মাণের চেষ্টা তাই সবসময়েই হয় পারোলের হাত ধরে। যা কেবলমাত্র ব্যক্তিগত কোনো একক স্বর হয়ে উঠতে পারে। ভাষাকে আশ্রয় করেও যা পালটে দিতে পারে তার প্রথানুগত্য। যাকে মেনে চলতে হয় না কেন্দ্রের অনুশাসন, বরং কেন্দ্রের সঙ্গে এক সংলাপধর্মিতাতেই তৈরি হয়ে যায় এক স্বতন্ত্র কথন। ঠিক এইভাবেই নারীদের কয়েদকথন রপ্ত করে নেয় একটা আলাদা ভঙ্গি। ব্যক্তি-নির্বিশেষে সেই ভঙ্গি একইরকম, এমন দাবি হয়তো আমরা তুলতে পারব না। কিন্তু এইটুকু বুঝতে পারব যে কীভাবে নারী তার নিজের ভাষায় নিজের কথা বলে। পুরুষতান্ত্রিক ভাষা কাঠামোকে অগ্রাহ্য করে।
এই আলোচনায় আমরা চাইব আলোচ্য কয়েদকথনগুলিতে নারীর ভাষা ব্যবহারের কয়েকটি নির্দিষ্ট এলাকা চিহ্নিত করতে। যে এলাকায় কয়েদকথনগুলি নিজেদের সঙ্গে কথোপকথনে নীত হয়। লক্ষ্যণীয়ভাবে, অধিকাংশ কয়েদকথনের কথনস্বর বহুবচন হয়ে ওঠে। সহবন্দিদের কথা বলা কয়েদকথনের প্রায় একটি বর্গচিহ্নের মতো। আমরা দেখতে চাইব, সেই সংরূপচিহ্নকে নারীর ভাষা কীভাবে ব্যবহার করছে। তা কি নিছক ‘নারীর ভাষা’ না কি তার নিজস্ব সামাজিক-রাজনৈতিক কারণ রয়েছে? উপরন্তু ‘আমরা’ শব্দের মধ্যে আসলে কাদেরকে ধরতে চান তাঁরা? কদের নিয়ে ‘আমরা’ হয়ে ওঠে বন্দিনিদের জবানি? তার মধ্যে উপস্থাপনের দূরত্ব থাকে না তো? এর পাশাপাশি আমরা চেষ্টা করব ক্ষমতাতন্ত্রের মধ্যে তাঁদের অবস্থান বুঝে নিতে। কারণ বন্দিনিরা আসলে ‘বন্দিনি’ই। তাদের প্রথম এবং শেষ পরিচয় সেটাই। বলা বাহুল্য, রাষ্ট্র ওরফে পুরুষতন্ত্রই তাদের বন্দি করে। ফলে বন্দি জীবনের অভিজ্ঞতার কথা লিখতে গেলে এমন একটা স্বর খুঁজে নেওয়া জরুরি যে স্বর একটা বিকল্প বয়ান নির্মাণ করবে। কিন্তু এই স্বর খুঁজে নেওয়ার পদ্ধতিটা কয়েদকথন বিশেষে আলাদা রকম। আমরা চেষ্টা করব, সেই আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষিত মিলিয়ে মিলিয়ে সেই স্বরগুলোকে সন্ধান করতে।
লুস ইরিগারে [৪] অনেকদিন আগেই স্বীকার করছেন, নারীর আলাদা ভাষাকে। পুরুষের ভাষায় নারী কথা বলে না। তাকে আলাদা একটা কথন-প্রক্রিয়া রপ্ত করে নিতে হয়েছে আগেই। কেমন সেই কথন?
It [women’s language]…demonstrates an inherent richness which leaves nothing to be desired from men’s language, in particular, a taste for intersubjectivity, which it would be a shame to abandon in favor of men’s more inaccessible subject-object relations.
যে আন্তঃসম্পর্কের কথা ইরিগারে বলছেন, ঠিক সেই আন্তঃসম্পর্কের ভিত্তিতেই বন্দিনিরা বলেন ‘আমরা’। কারণ তাঁর প্রবন্ধের গোড়াতেই ইরিগারে দেখিয়েছেন, কীভাবে নারীর কথনে প্রকাশ পায় আরেকজন বা আরও একাধিক অস্তিত্বের উপস্থিতি। আর সেই জন্যেই নারীর কয়েদকথনে কখনও নারী আর কোনো ‘একক’ ব্যক্তিসত্তা থাকে না। হয়ে ওঠে ‘আমরা’। অনায়াসে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাকে ফেলে নারী কথা বলে বহুবচনে। জয়া মিত্র বা মীনাক্ষী সেন-এর কথনে আমরা দেখে নিতে চাইব তেমনই কিছু বিষয়।
কিংবা শুধু বহুবচন বলে সীমাবদ্ধ করে তুলব না আমরা। দেখতে চাইব আরেকটু বিশদে। আপাতত এই উদ্ধৃতিটুকুকেই নেওয়া যাক—
আর শিখার নিষ্ঠুরতা কিংবা অত্যাচারের বর্ণনা কোনও একটি লেখায় সম্পূর্ণ হয় না। আসগরীর কঙ্কাল শরীরে, শাহানাজের রক্ত ধারায়, রানীর ভাঙা কোমরে প্রতিটি মাতৃহীন অনাথ শিশুর গায়ের চামড়ায়, সর্বত্রই শিখার অত্যাচারের চিহ্ন। শিখার উপস্থিতির সময়ে তার হাতে প্রহৃত হয়নি এমন বন্দিনী বোধ করি পাওয়া যাবে না। এমনকি শিখার নিজের দলের লোকও তার মধ্যে পড়ে যাবে।
আর আমাদের সঙ্গে শিখার যে সংঘর্ষের ইতিহাস, সে এক পুরোপুরি আলাদা কাহিনী।[৫]
প্রথমত, এখানে যার বিরুদ্ধে সবাই রুখে দাঁড়িয়েছে, সে একজন ‘মেট’। এবং নারী। এবং যারা রুখে দাঁড়িয়েছে তারাও নারী। যখন ‘আমাদের’ বিশেষণ ব্যবহার করা হয়, তখন যে গোষ্ঠীবদ্ধতা, সমষ্টিচেতনার কথা উঠে আসে, তার মূল সুরটি নারীত্বের। অথচ, তারাই বিদ্রোহ ঘোষণা করেন, করল একজন মহিলা মেট-এর বিরুদ্ধে। তার কারণ কি মহিলাটি তখন পুরুষতন্ত্র ওরফে রাষ্ট্রশক্তির প্রতিভূ, তাই? নাকি ক্ষমতা-ব্যবস্থায় সে উচ্চবর্গ শাসক ওরফে শোষকও? আসলে এক্ষেত্রে এই প্রতিটি পরিচয়ই শিখার অঙ্গ হয়ে ওঠে। কিন্তু, যদি তাও হয়, তাহলে তো এটাও সত্যি, যে মহিলাটিও আসলে একইরকমভাবে পিতৃতন্ত্রের শিকার। সে-ও একটা সামাজিক ঘেরাটোপের ফসল। যখন নারী তার বক্তব্য প্রকাশের সময় ‘অপর’ অস্তিত্ব বিষয়ে সচেতন, তখন সেই ‘অপর’ এর অন্যান্য অবস্থান বিষয়ে সচেতনতা থাকাটাও একইরকম স্বাভাবিক। তাই সহস্র প্রতিবাদ, এমনকি রক্তপাত সত্ত্বেও সেই সামাজিক পরিকাঠামোর কথা আমাদের মনে করিয়ে দেন মীনাক্ষী—
কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও তো সত্য যে শিখা এক ‘অস্ত্র’, শিখা এক ‘পুতুল’। শিখা এক ‘রোবট’। সব রোবট এক ছাঁচে তৈরি হয় না। তার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য তো থাকবেই। কিন্তু সে কাজ করে কর্তার ইচ্ছায়। তাকে তৈরি করা হয়। তাকে সুযোগ দেওয়া হয়। সে ব্যবহৃত হয়। [৬]
সেইজন্যই শুধুমাত্র নারীত্বের আলোকে নয়, আমরা এঁদের কথনভঙ্গি আলোচনা করার সময় খেয়াল রাখব, এঁরা প্রত্যেকেই রাজনৈতিক কারণে কারাবাস বরণ করে নিয়েছেন। এবং এঁদের কথনক্রিয়া এঁদের স্বতন্ত্র চয়ন। যদিও কোরা কাপলান[৭] বলেন, ভাষার পাশাপাশি সমাজ আসলে থাবা বাড়ায় কথনের এলাকাতেও, এবং তাকে আদৌ কোনো ব্যক্তিগত ব্যবহার হিসেবে স্বীকৃতি দেয় না, বরং তাকে করে তোলে শাসকশ্রেণির মুখপাত্র, তবু, কাপলানের কথার উলটো পথে হেঁটেই আমরা দেখে নেব, সেই সামাজিক আধিপত্য স্বীকার করে নেওয়ার সঙ্গেই কেমনভাবে নারী মিশিয়ে দেয় তার নিজস্বতার চোরাস্রোত। শুধুমাত্র একজন নারী হয়ে নয়, বরং উত্তর-ঔপনিবেশিক দেশের বন্দি হয়েও। এই কয়েদকথনগুলোর জন্য তাই মীনাক্ষী সেন বা জয়া মিত্রর রাজনৈতিক পরিচয়টাও সমান জরুরি। এই পরিচয়ের প্রেক্ষিতেই আমরা পড়ে নেব ওয়ার্ড্রেস বা মেটের বিরোধিতায় একজোট হওয়ার প্রসঙ্গ।
কিন্তু রাজনৈতিক বন্দি এবং নারীত্বের যে দু-রকম অস্মিতার কথা আমরা বলছি, তার কি আদৌ তেমন কোনো স্পষ্ট সীমা নির্দেশক আছে? ‘নারীর ভাষা’-এই বিশেষ উপবিভাজনের সৃষ্টির পেছনে যে রাজনীতি আছে, তাও তো একটা ক্ষমতা-ব্যবস্থাই। তারা কখনও রাষ্ট্রের রূপ ধরে প্রতিবাদীকে জেলে বন্দি করে, কখনও পুরুষতন্ত্রের রূপে ‘অপর’কে গৃহবন্দি করে।
সেই ভাষার রাজনীতিটাকেই উদ্দেশ করতে চান জয়া মিত্র। বার বার। তার কয়েদকথনে ফিরে ফিরে আসে, যারা যে এলাকার, তাদের নিজস্ব ভাষা। ‘হন্যমান’[৮] বরাবর পাতা ওলটালে চোখে পড়বে নানা রকমের উপভাষা, যাকে আমরা শহরের ‘মান্য চলিত বাংলা’ থেকে আলাদা করতে গিয়ে ‘ডায়লেক্ট’-এর সীমানাভুক্ত করে ফেলেছি—
উমরার হাড়গিলান এইঠেই থাকিবার দিদি, এইঠেই থাকিবার। উমরার ঘরত ছোয়া আছে। ছোয়ার বউ আছে। কিন্তু ক্যানং নিগাবে? এই বুড়িখান কি আরো আট কি নয় বছর বাঁচি থাকিবার পারে? এই মরণ ফাঁদের ঘরটাত্?
(পৃ. ৩৪)
নাগো। ওদের নাকি তুমি মারবে, কিন্তুক আমাদের বিপদ হয় এমন তো কিছু করবে না, তাই আমার আর আনন্দদির তোমাকে পাহারা দেওয়া। নিজের পর ঘিন্না হয়ে গেল ভাইপো। (পৃ. ৩৭)
উঁচোটের বেথায় শয্যেশায়ী, অমনধারা বেথা আমি অনেক দিখিচি বাপু—দু চার দিন দেখব তা’পরে এমন ওষুদ দোব যে তোমার বেথা পালাতে পথ পাবেনি। (পৃ. ৪২)
মানিকচান্দ মইরা গেছে দিদি গো।…হায় গো দিদি, সে যে মোর জাহান ছিল গো চাচী বিনু যে জাইন্ত নাই। (পৃ. ৬২)
ও গে আল্লাগে আমি আল্ পালি না—আমালে তুই নিয়া যা গে আল্লা। (পৃ. ৬৭)
নাই আনালি বিটি। চৌদ্দ বছর গেলে তবে খালাস পাব। ততদিনে কোথা বা বৌ রইবে, কুথা বা ঘর।… হঁ বিটি, কত হপ্তায় চৌদ্দ বছর হয়? (পৃ. ৭১)
আপনার পিঠে দরদ আছে, ডাগদরবাবু বোলেছিলেন। আচ্ছা খাট নিবেন না—হর হপ্তা সাহেব জেলর যে আপনাকে শুধান অসুবিধা আছে কি না, তখন বোলেন না কেন দরজা খুলে দিতে? (পৃ. ৩৬)
আই নো, আই নো ইন্ডিয়ান সালিস্ বেলি গুৎ—কান্ত ম্যানিজ—অল গো আউৎ।
(পৃ. ৯৫)
উপরে যতগুলো পঙ্ক্তি উদ্ধার হলো এর প্রতিটিকেই আমরা চিহ্নিত করতে পারি আলাদা ভাষা হিসেবে। বা আলাদা ‘ডায়লেক্ট’। প্রথমটি কোচবিহারের ভাষা। সেখানে কামরূপী-রাজবংশীর ছাপ স্পষ্ট। তারপর রাঢ়ী। এবং যথাক্রমে, পুষ্প নেইয়ার সুন্দরবনের বাদা অঞ্চলের ভাষা, মালতীর পূর্ব-পাকিস্তানের ভাষা, বিহারি মুসলমানদের, পূর্ব-পাকিস্তান ফেরত ভাঙা বাংলা, নিধু মেঝেন-এর সাঁওতালি মেশানো বাংলা, বিমলা ভাবির হিন্দি প্রভাবিত আধো বাংলা আর ফরাসির আধজানা ইংরেজি। এই সবগুলিকেই জয়া মিত্র ব্যবহার করতে চাইছেন তাঁর লেখায়। শুধু জয়া মিত্র নয়, মীনাক্ষী সেনের বইয়ের পাতা ঘাঁটলেও চোখে পড়বে, এমন অজস্র সংলাপ, যেগুলো তথাকথিত নাগরিক শিক্ষিত মানুষের কথ্যভাষায় রচনা নয়। ‘নাগরিক’ ‘শিক্ষিত’ মানুষের যে ভাষা, যাকে আমরা অধ্যায়ের শুরুতেই ‘লঙ’ বলে চিনে নিয়েছি, এবং দেখেছি, সেটা কীভাবে একটা শ্রেণির মতাদর্শকে বহন করে এবং চাপিয়ে দেয় ‘অপর’এর ওপর, সেই ভাষার বাইরে গিয়েই জয়া মিত্র হাঁটার চেষ্টা করছেন। গুরুত্ব দিচ্ছেন কথ্যভাষার ওপর। কারণ ছাপার হরফ তো আসলে মান্যতাপ্রাপ্ত এক বিশেষ পাঠের কথা বলে শুধুমাত্র। অন্যত্র এক প্রবন্ধে জয়া বলেন,
…জীবনযাপনের ‘মেনস্ট্রিম’ ক্রমশ সব ‘অন্যরকম’কে অগ্রাহ্য করতে শুরু করল। সেই মূলস্রোতের টান এত বেশি হল যে দোকান আর পণ্যে ভরে উঠল গৃহস্থালী। শুধু মেয়েদের বাক্ভঙ্গি নয় সমস্ত ‘অন্য’দেরই নিজ নিজ বাক্ধারা, স্থানিক ভাষা, ডায়ালেক্ট মুছে গেল শহুরে কলকাতা-শান্তিপুরী ভাষার তলায়।…
ছাপাখানা যেমন একদিকে মুক্তি ও অধিকার এনে দিল, অন্যদিকে রহিত করল ভিন্নতাকে।… মান্যতার দাপট এত বেশি হল যে এমনকি স্কুল কলেজের শিক্ষা পাওয়া তো বটেই, না পাওয়া মেয়েরাও সেই ভাষাকেই নিজেদের লেখার বাহন করলেন। [৯]
সেই মান্যতার দাপট এড়িয়ে জয়া মিত্র চাইছেন, এমন এক ভঙ্গি, যা একান্তই ব্যক্তিক। একক। আত্মগত। যা নারীর নিজস্ব। যেমন করে ইরিগারে বলেন। অবশ্য, এই অন্যান্য ‘ডায়ালেক্ট’কে নিজের লেখায় ঠাঁই দেওয়ায় অন্য আরেক ধরনের উদ্দেশ্যসাধনও হয়। আমরা এবার সেই আলোচনাতেই আসি।
জয়া মিত্র বা মীনাক্ষী সেনের রাজনৈতিক অবস্থানটাই এমন, যে, সেটা বাধ্য করে ‘আমার’ গল্পকে ‘আমাদের’ গল্প হয়ে উঠতে। এঁরা সকলেই রাজনৈতিক বন্দি। তা থেকে কিছু কিছু বিষয় স্পষ্ট হওয়া যায়।
যখন জয়া মিত্র বা মীনাক্ষী সেন লিখছেন, তখন ভারতবর্ষ খাতায় কলমে স্বাধীন রাষ্ট্র। কিন্তু যে স্বাধীনতা ভারত লাভ করেছে, সে উচ্চবর্গের স্বাধীনতা। তাই স্বাধীনতা ঘোষণার পরও কৃষকের অবস্থার কোনো হেরফের হয় না। দেসাই বলেন, ভারতীয় সংবিধান তার যাবতীয় মৌলিকত্ব সমেত আসলে সেই আধা-সামন্ততান্ত্রিক বুর্জোয়া ব্যবস্থাকেই টিকিয়ে রাখে।[১০] তাই যখন কৃষকেরা বিদ্রোহ করে, তাদের জন্য দমনমূলক ব্যবস্থা নিতে হয়। স্বাধীন ভারতের নকশাল আন্দোলন প্রাক-স্বাধীন যুগের তেভাগারই এক ধারাবাহিক পর্যায়। নকশাল আন্দোলনে প্রথম যারা সক্রিয় হয়েছিলেন, তারা সকলেই কৃষক। এবং আন্দোলনকে সক্রিয় করে তুলতে যারা আগ্রহী ছিলেন, তারাও কৃষকদের কথাই ভাবছেন। উত্তর-ঔপনিবেশিক কৃষিজীবী ভারতের ধ্বস্ত অর্থনীতিতে বিদেশী পুঁজিকে আহ্বান জানালে, তাতে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হন কৃষিজীবী সম্প্রদায়ই। শুধু কৃষিজীবী নয়, পাশাপাশি নকশাল আন্দোলন বলবে এক নিম্নবিত্ত সমাজের গল্প। এই উপনিবেশ উত্তর-উপনিবেশের জাঁতাকলে যারা সবচেয়ে বেশি শোষিত। কিন্তু তাদের পাশে যারা দাঁড়াচ্ছেন, তারা আদৌ সব সময়ে সেই নিম্নবর্গ/নিম্নবিত্ত স্তর থেকে উঠে আসা কি? এজন্যই এক্ষেত্রে আত্মপরিচয়টার প্রশ্নটা একটু গোলমেলে। জয়া মিত্র বা মীনাক্ষী সেনের সঙ্গে জেলের আর পাঁচটা মানুষের কোথাও হয়তো প্রতিনিধিত্বগত উপস্থাপনের একটা দূরত্ব থেকেই যায়।
চারু মজুমদার যে ঐতিহাসিক আটখানা দলিল লিখে নকশাল বিদ্রোহের প্রধান হোতা হন, সেই দলিলে স্পষ্টতই উল্লেখ ছিল শোধনবাদী সরকার, যে কিনা বিদেশী পুঁজিকে আমন্ত্রণ জানিয়ে আসলে সর্বহারার সর্বনাশ ডেকে আনছে, তার বিনাশ চাই। অর্থাৎ, সর্বহারার সমাজ গড়ার আদর্শেই মীনাক্ষী সেন, জয়া মিত্রের মতো মানুষজন আন্দোলন চালান। এবং গ্রেপ্তারও হন। নকশাল আন্দোলন নিয়ে আলোচনায় রবীন্দ্র রায়[১১] বলছেন,—‘The Naxalites fought in the cause of a class other than their own.’ চারু মজুমদার তাঁর ঐতিহাসিক আটটি দলিলের সপ্তমটিতে সরাসরিই বলেন, ‘… বিশেষ করে মধ্যবিত্ত জনতার দায়িত্ব হচ্ছে এই মুক্ত অঞ্চল গড়ে তোলার কাজে কৃষকের আন্দোলন গড়ে তোলা।’ [১২]
এবং যে ‘মধ্যবিত্ত জনতা’কে তিনি ডাক দিচ্ছেন, তারা জয়া মিত্র বা মীনাক্ষী সেনের মতো ঘর থেকেই উঠে আসা। বলা বাহুল্য তারা কোনোদিন সরাসরি চাষের কাজে যুক্ত ছিলেন না। শুধু উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে সংযুক্তি নয়, বরং তাদেরকে ডাকা হয়েছিল, পার্টির আদর্শ প্রচারের জন্যও খানিকটা, আর খানিকটা শ্রমিক-কৃষককে মিলিতভাবে শিখিয়ে দেওয়ার জন্য যে, কোন রাষ্ট্রীয় পরিকাঠামো তাদের পীড়নের পেছনে দায়ী। তাই সব মিলিয়ে তাদের শ্রেণিগত অবস্থান ছিল বেশ স্পষ্ট।
কয়েদকথনের ক্ষেত্রেও এই সীমারেখা অটুট ছিল। জেলে কোনো ধনী দেখেননি মীনাক্ষী সেন, সে-কথা স্বীকার করেছেন বার বার। আর তাদের মতো ‘মধ্যবিত্ত’ও শুধু তারাই ছিল, যারা সেই উত্তাল ছয়-এর দশকের শেষ, আর সাতের দশকের শুরুর বন্দি। তাহলে, বাকি যারা পড়ে রইল, তারা হলো সর্বহারা শ্রেণি। পথহারা, উদ্বাস্তু, পকেটমার, চাষি, মজুর, বস্তিবাসী, বেশ্যা—এরা সবাই নির্দিষ্ট একটা শ্রেণির প্রতিনিধি। সামাজিক বিপ্লব হয়ে সর্বহারার সমাজ প্রতিষ্ঠা হলে, যারা সেই সমাজের পুরোভাগে থাকবে। তাদের শ্রেণি-অবস্থানের সঙ্গে নিজেদের এক সারিতে দেখতে চেয়েছেন বলেই জয়া মিত্র মীনাক্ষী সেনরা ডিভিশনবাড়ির বাড়তি সুবিধে নিতে অস্বীকার করেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও উপস্থাপনের দূরত্বকে এড়ানো যায় না। আর সেই কারণেই হয়তো বা জয়া বা মীনাক্ষী বেছে নেন, তাঁদের লেখার সংলাপধর্মিতা। সংলাপের মধ্যে ঠাঁই পায়, কয়েদিদের নিজস্ব স্বরে বলা কথাগুলো। তাঁরা আশ্রয় করেন সেই ‘ডায়লেক্ট’, যা সেই বিশেষ শ্রেণির মানুষদের কথ্য যাপন। তাই শুধুমাত্র নারীর অস্মিতা-সন্ধান দিয়েই পড়ে ফেলা যায় না, মীনাক্ষী-জয়ার কথনভঙ্গিকে। তার মধ্যে মিশে থাকে ব্যক্তিগত রাজনৈতিক মতাদর্শও। জয়া মিত্রর লেখায় আমরা আগেই দেখেছি, মান্যতার দাপটে স্কুল-কলেজের শিক্ষা পাওয়া মেয়েরাও কীভাবে রপ্ত করে নিচ্ছে শহুরে ভাষা। তাই হয়তো জয়া মিত্র ধরতে চাইছেন এমন একটা সমগ্রকে যারা তথাকথিত ‘স্কুল-কলেজ’এর শিক্ষা পাওয়া নয়, বরং যাদের জীবনে মান্যতা এখনও অতটাও প্রভাব ফেলতে পারেনি। ঔপনিবেশিক বাঙালি সমাজে যারা সুবিধাভোগী শ্রেণি, যারা ‘ভদ্রলোক’, তাদের সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুতে দাঁড়িয়ে থাকে যে বঞ্চিত শ্রেণি এবং যাদের কথা বলার মতাদর্শেই বিশ্বাসী ছিল নকশালরা।
তাইজন্যেই, মীনাক্ষী সেন তাঁর কয়েদকথনকে ভাগ করছেন যে অধ্যায়গুলো দিয়ে, সেই অধ্যায়গুলোর নাম আসলে তাঁর সহবন্দিদের নামে। ‘শংকর’, ‘জাহান-আরা’, ‘চম্পারাণীর মরণ বাঁচা’, ‘মিতাকথন’, ‘বিদ্যেসুন্দরীর বিচার’—প্রতিটি অধ্যায়ভাগ যেন আসলে অন্য অন্য এক একটি গল্প, একেকটা আলাদা আলাদা পৃথিবীর গল্প বলতে আগ্রহী হয়, যেন, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা গৌণ, শুধুমাত্র সহবন্দিদের কথা বলবেন বলেই কলম ধরেছেন মীনাক্ষী। তাই দেখিও আমরা। জেলের অভিজ্ঞতার পাশাপাশি, জেলের বাইরের পৃথিবীতে তাদের জীবন নিয়েও কথা বলেন তিনি। অনেক সময় গল্প বলার ঢঙে, কখনও বা পাঠককে সচেতন করে দিয়েও, একটা তৃতীয় পক্ষ সুলভ প্রথম পুরুষে তিনি রচনা করে যান ধারাভাষ্য। ফলে কখনো-কখনো প্রায় ‘ভেরিসিমিলিটিয়্যুড’-এর দাবিতেই ‘গল্প’এ উঠে আসে তাদের নিজস্ব সংলাপ, যা মীনাক্ষী সেন বা জয়া মিত্রর নিজের ভাষা নয়। আর ঠিক এইভাবেই জয়া মিত্র বা মীনাক্ষী সেন তাঁদের লেখার মধ্যে প্রান্তের ভাষাকে ধরতে চান। সে আসলে ক্ষমতার পালটা বয়ান নির্মাণের প্রকল্প। সেই বয়ান ছাড়িয়ে বেরিয়ে আসার প্রক্রিয়া। বইয়ের শুরুতেই জয়া মিত্র তাই ঘোষণা করেন, আসলে কাদের কথা বলতে চেয়ে তিনি কলম ধরেছেন—
যারা সচেতনে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল, ডাক দিয়েছিল ক্ষমতা দখল করার, তারা তো অত্যাচার, বন্দীত্ব, মৃত্যু বরণ করেছিল জেনে-বুঝে। তাদের আশ্রয় ছিল দেশের উদ্বেল হৃদয়ে। কিন্তু যারা এসব কিছুই নয়, যারা এই সমাজের মধ্যেই কোনোরকম টিকে থাকতে চেয়ে কিংবা থাকতে না পেরে কোনো অপরাধ করেছে, সামাজিক স্বাস্থ্যের পোকা বাছাই করে ‘সংশোধনের জন্য’ যাদের রাখা হয় জেলে— কীভাবে থাকে সেই মানুষেরা? [১৩]
যেন বা সহবন্দিদের কথা বলার জন্যেই কলম ধরেছেন তাঁরা। মীনাক্ষী সেনের ক্ষেত্রে এ বিষয়ে তাঁর অবস্থান আরও স্পষ্ট। তাঁর অধ্যায়-নামের কথা আমরা আগেই বলেছি। ১৯৭৮ থেকে ‘স্পন্দন’ বা ‘প্রতিক্ষণ’ বা ‘একুশ শতক’-এর মতো পত্রপত্রিকায় তাঁর লেখাগুলো তাঁর কয়েদ-সঙ্গীদের নাম দিয়ে বেরোচ্ছে। যেন শুধু তাঁর অভিজ্ঞতায় বাঁধা পড়া কিছু জেলবন্দি মানুষের জীবন।
কিন্তু এইভাবেই সহবন্দিরা একমাত্র উঠে আসে না তাঁদের লেখায়। অনেক সময়ে তা একটা বিস্তৃত তল্লাট তৈরি করে, যেখানে প্রতিটি বন্দিনি নিজেদের অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেয়। সহবন্দিদের গল্প বলার প্রথম পুরুষের দূরত্ব সেখানে আর থাকে না। প্রান্তবাসী কয়েদিরা বস্তুতপক্ষে একটাই শ্রেণি নির্মাণ করে।
অবিরাম বৃষ্টিতে বাগানময় জল। বাগান খাটনির ছুটি।… চুপিচুপি নিজেদের মধ্যে ঠিক হয়েছে হাডুডু খেলা। দুপুরবেলা ওয়ার্ডারকে ডেকে বলি হঠাৎ খুব দরকার পড়েছে বাইরে যাবার আর সেল থেকে বেরিয়েই দৌড়। ওরা তৈরিই ছিল—ফুলমালা ইতোয়ারী সিস্টার কয়লামুখি আর ওর বৌদি শান্তি সুখী আরও কয়েকজন। বাগানে গাছে নিচে নিচে প্রায় হাঁটুসমান জল। হাডুডু খেলার ছলে হুড়োহুড়ি, ধাক্কাধাক্কি আর খোলা হাসি। (পৃ. ৭২)
বাপীদি দরজার কাছটায় চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল খানিক। তারপর বসে আস্তে আস্তে মাথায় কপালে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। ছোট ছোট খসখসে হাতদুটো দিয়ে মমতা চুঁয়ে চুঁয়ে আমার ভিতরে চলে যাচ্ছে, শুকনো খরার পরে ঝরা শিশিরের জল যেমন মাটির ভিতরে চলে যায়। কতদিন এই হাতগুলো দিদির হাত মায়ের হাত হয় নি! [১৪] (পৃ. ১২৯)
উপরের উদ্ধৃতিগুলোর দিকে চোখ রাখলে কতগুলো বিষয় আমরা বুঝে নিতে পারি। প্রথমত, সহবন্দিদের সঙ্গে এক যৌথজীবনের ছবি এখানে স্পষ্টই ফুটে ওঠে। দ্বিতীয়ত, যে ঘরোয়া নামে সম্বোধন করা হয় সহবন্দিদের, সেখানে এক বৃহত্তর পরিবারের ইশারা পাওয়া যায়। কারাগারের ধারণার মধ্যেই প্রচ্ছন্ন থাকে বিদ্রোহী স্বরকে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখার গল্প। সেইখানে এই সমবেত সত্তা, এই বৃহত্তর পারিবারিক জীবন অবশ্যই রাষ্ট্রিক ক্ষমতা-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে একটা প্রতিরোধের গল্প শোনায়। জয়া মিত্র-মীনাক্ষী সেনের ক্ষেত্রে শ্রেণিও একটা জরুরি ভূমিকা তৈরি করে। কারণ যাদের সঙ্গে আত্মীয়তার কথা বলা হয়, সম্বোধন করা হয়, ‘বাপীদি’ ‘কয়লামুখি’ ইত্যাদি নামে, বা মা বা দিদিকে প্রতিস্থাপন করা হয় তাদের দিয়ে, তারা সমাজের অবহেলিত শ্রেণিরই মানুষ। সেই শ্রেণির সঙ্গে এই আত্মীয়যোগ একটা বিশেষ মতাদর্শের কথাও বলে। উপরন্তু যে শ্রেণি গঠনকে রাষ্ট্র ক্রমাগত প্রশ্রয় দিয়ে গেছে, সেই শ্রেণিবিভাজন লোপে সেই রাষ্ট্রকে চ্যালেঞ্জ জানানোও হয়। অবশ্য, শুধুমাত্র শ্রেণিস্বার্থ বিসর্জন দিয়ে সর্বহারার সঙ্গে একাত্মতার মধ্যে দিয়ে আমরা নকশাল বন্দিনিদের সহবন্দিদের কথা বলতে চাওয়াকে ধরতে পারব না। তার পরতে পরতে অন্য অর্থস্তর চাপা থাকে। মীনাক্ষী সেনও এর ব্যতিক্রম নন—
ওরা সবাই দেখি কাঁদছে। মেয়াদী নম্বর, হাজতি নম্বর, জালঘর—যে-যেখান থেকে এসেছে, সবাই মিলে এ-ওকে জড়িয়ে ধরছে। আর প্রাণখুলে চিৎকার করে কাঁদছে। মেয়াদী নম্বর আজ কানায় কানায় ভরতি। প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশজন মানুষ। সবাই মিলে একসঙ্গে যদি কাঁদে, কেমন যে করে বুকের ভেতর, বলে বোঝানো যায় না। (পৃ. ১১০)
সন্ধ্যা হলে লক বন্ধ হয়। আবার ঘরে ঢুকি। তখন সবাই মিলে আমরা গান গাই। তারপর সবাই মিলে খাবার খাই। … তারপর সবাই মিলে গল্প করি। [১৫] (পৃ. ১৯১)
যে কৌম জীবনের ছবি এই কথাগুলোর মধ্যে ফুটে ওঠে, সেই জীবন কোনো একার জীবন নয়, বলা বাহুল্য। এই সবাই-মিলে-থাকা-র ঘরটাকে খুঁজে নেয় নারীর কয়েদকথন। রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে, পিতৃতন্ত্রের বিরুদ্ধে নিজেদের অবস্থানকে প্রতিষ্ঠা করতে গেলে নিজেদের এক সঙ্গে দাঁড়ানোর প্ল্যাটফর্মটা খুঁজে নেওয়া জরুরি হয়ে পড়ে।
জয়া মিত্র মেয়েদের লেখা কারাকাহিনি নিয়ে কথা বলতে গিয়ে বলেন,
প্রত্যেকটিই নিজস্ব জায়গায় ভিন্ন তবু পাঠককে যেটা সবচেয়ে বেশি অভিভূত করে তা এদের অন্তর্গত ও বহিরঙ্গের মিলের দিক।… খেয়াল করা যাবে, মেয়েরা নিজেদের পর ঘটা অত্যাচারের কথা কম বলছে, অনেক বেশি বলছে সহবন্দিদের কথা।… এটা খুব আশ্চর্যেরও নয় যে রাণী চন্দ থেকে আমেরিকার জোসেফিন আসাটা শাকুর—প্রত্যেকেরই জেলের স্মৃতিকথা ভরা রয়েছে সহবন্দী সাধারণ মেয়েদের কথায়। হয়তো একে মেয়েদের এক স্বভাববৈশিষ্ট্য হিসেবেও চিহ্নিত করা যায়। [১৬]
আর এইভাবেই আমরা নারীর কয়েদকথনের মধ্যে কিছু যৌথতাকে চিনে নিই। যেমন আগে বলা হয়েছিল। তাদের সমষ্টিবোধ, তাদের পুরুষতান্ত্রিক সমাজের বিরুদ্ধস্বর নির্মাণ—সবই আসলে কয়েদকথনের ভাষাকে একটা ভিন্নতর রাজনৈতিক মাত্রা দেয়। আর সেইগুলিকেই আমরা তাদের অন্তরঙ্গের মিল বলে চিহ্নিত করতে পারি।
উৎস নির্দেশ:
১. দাশগুপ্ত, কমলা। ‘স্বাধীন ভারতের কারাগার’; মন্দিরা; শ্রাবণ, ১৩৫৫, পৃ. ২৩৫।
২. Saussure, Ferdinand de. ‘The Object of Study’; Course in General Linguistics; Open Court Publishing Company, 1972, pp 14.
৩. Holdcroft, David. Saussure: Signs, Systems and Arbitrariness; Cambridge University Press, 1991, pp. 20.
৪. Irigaray, Luce. ‘The Question of Other’; Yale French Studies, No. 87, Another Look, Another Woman: Retranslations (by Noah Guynn) of French Feminism.1995, pp.16-17.
৫. সেন, মীনাক্ষী। জেলের ভেতর জেল: হাজতি নম্বর মেয়াদী নম্বর পর্ব; প্রতিক্ষণ পাবলিকেশন প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ১৯৯৪, পৃ. ১৬৩।
৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৪।
৭. “Social entry in patriarchal culture is made in language through speech. Our individual speech does not, therefore, free us in any simple way from the ideological constraints of our culture since it is through the forms that articulate those constraints that we speak in the first place.”–Kaplan, Cora. ‘Language and Gender’; The Feminist Critique of Language: A Reader; edited by Deborah Cameron, Routledge, 1998. pp. 56.
৮. মিত্র, জয়া। হন্যমান; দে’জ পাবলিশিং, ২০০০।
৯. মিত্র, জয়া। ‘দুয়োরাণীর ফোয়ারা’; রোববার; সম্পা: ঋতুপর্ণ ঘোষ, সংবাদ প্রতিদিন; ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০০৮, পৃ. ৩৫।
১০. “The Constitution, in spite of all amendments and verbal nuances, accepts the norms of bourgeois society as the permeating principle underlying all its measures. It treats the right to property as fundamental–hard core right–as the bedrock of the entire endeavour to reconstruct Indian economy.”–Desai, Akshayakaumar Ramanlal. ‘Changing Profile of Rural Society in India’; Agrarian Struggles in India After Independence; edited by A. R. Desai; Oxford University Press, New Delhi, 1986. pp. 15.
১১. Ray, Rabindra. ‘Introductory: Perspectives and Problems’; The Naxalites and their ideology; Oxford University Press, Delhi, 1988, pp. 4.
১২. মজুমদার, চারু। ‘চারু মজুমদারের লেখা ঐতিহাসিক আটটি দলিল’; নকশালবাড়ি: তিরিশ বছর আগে এবং পরে; আজিজুল হক, দে’জ পাবলিশিং, ১৯৯৯, পৃ. ৪৭।
১৩. মিত্র, জয়া। হন্যমান; দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০০, পৃ. ৭।
১৪. প্রাগুক্ত।
১৫. সেন, মীনাক্ষী। জেলের ভেতর জেল: হাজতি নম্বর মেয়াদী নম্বর পর্ব; প্রতিক্ষণ পাবলিকেশন প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৯৪।
১৬. মিত্র, জয়া। ‘বন্দিনী’; রোববার : বন্দিনী; সংবাদ প্রতিদিন, ৯ সেপ্টেম্বর ২০০৭, পৃ. ৬-৭।