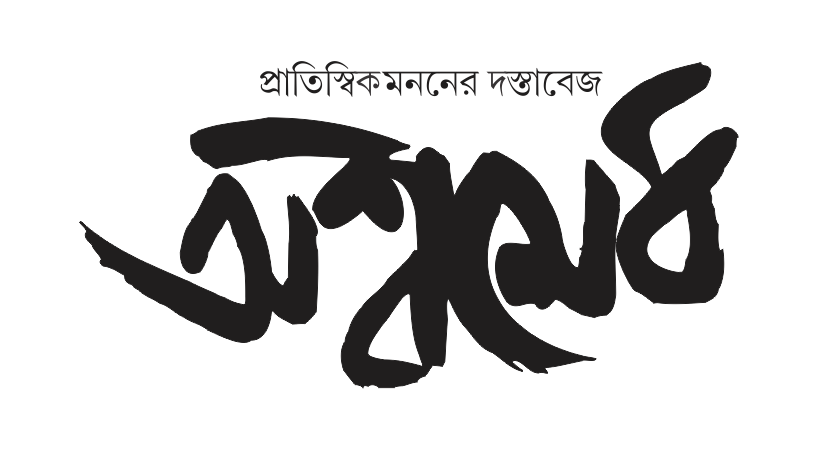যাঁরা বই ভালোবাসেন, তাঁরা কাঙ্ক্ষিত বইটি হাতে পেলেই ভূমাতীত আনন্দ পান। এর জন্য অর্থ-শ্রম-সময় তাঁরা দিয়ে থাকেন। কলেজ স্ট্রিট-গড়িয়াহাট-রাসবিহারী-ডালহাউসি-কাঁকুড়গাছিসহ কলকাতার নানা জায়গায় বইপ্রেমীরা ঘুরে বেড়ান। বই-দোকানির সঙ্গে তাঁদের সখ্যের শেষ নেই। এঁরা লাইব্রেরিতে গিয়েও পুরানো বই-এর সন্ধান করেন। বই-এর দরকারি তথ্যগুলো খাতায় তুলে নেন। অনেকে আবার নকলনবিশকে সাম্মানিক দিয়ে লাইব্রেরির দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের পাতার পর পাতা নকল করান। পরে মগজে পাটিগণিতের অঙ্ক-ঠাসা প্রকাশক দিয়ে সংগ্রাহক-সংকলক গ্রন্থটি প্রকাশ করেন। বিজ্ঞাপনে আর পত্রিকায় ইতিবাচক আলোচনার জেরে পাঠক তা সংগ্রহ করেন। এরপরে স্বত্ববান পাঠকের সংশ্লিষ্ট গ্রন্থলাভ মরীচিকাসম হয়।
অনামি প্রকাশক হলে কথাই নেই। পুরোনো বইটির নতুন করে প্রকাশনার কৈফিয়ত তো থাকেই না, সম্পাদকও আড়ালে থাকেন। তিনি তাঁর সংকলিত বইটি প্রকাশককে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকেন। কোনও পরিমার্জন-পরিবর্ধন নেই, তথ্যের যাচাই নেই, বানান ভুলগুলোকেও দেখা নেই। বরং তাঁর ব্যক্তিগত ইচ্ছেয় পুরোনো বইটির অনেক তথ্য বিলুপ্ত হয়। অথচ ফলাও করে লেখা হয়: ‘প্রথম সেন পাবলিশিং সংস্করণ’ (নামটি কাল্পনিক)। বইটির প্রথম প্রকাশক কে ছিলেন, কত সালে বইটি ছাপা হয়েছিল তা অমুদ্রিত থাকে। সেন মহাশয় এবং তথাকথিত সংগ্রাহক পাঠককে এতটাই লঘু ভাবেন যে, পাঠক বইটি পেলেই খুশি হবেন। পাঠকের বইটি সম্পর্কে কোনও প্রশ্ন থাকবে না। তাঁর লাভের পাল্লায় সরস্বতী লঘু হন, লক্ষ্মী হন গুরু। পাঠক-সংগ্রাহক হারিয়ে যাওয়া বইটির নতুন কলেবর দেখে, গন্ধ নিয়ে প্রাথমিক আনন্দ নিশ্চয় পান। কিন্তু বইটি হাতে নিয়ে তিনি হতাশ হন। কারণ বইটির আঙ্গিকগত রূপান্তরে ক্ষত ও ক্ষতি যথেষ্ট মাত্রায় প্রতীয়মান।
অন্নদাশঙ্কর রায় (১৫. ৩. ১৯০৪-২৮. ১০. ২০০২)-এর ‘পথে প্রবাসে’ (দ্বিতীয় মুদ্রণ আষাঢ় ১৩৮৩) অতিরিক্ত কীটদষ্ট বলে উক্ত বইটি একই প্রকাশকের (মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩) কাছ থেকে সংগ্রহ করি। দ্বিতীয়টি ঊনবিংশ মুদ্রণ ১৪২৫ বঙ্গাব্দ। বিনিময় মূল্যের কথা থাকুক। ঊনবিংশ মুদ্রণে প্রমথ চৌধুরী (৭. ৮. ১৮৬৮-২. ৯. ১৯৪৬)-র ভূমিকাটি বাদ গেছে। অথচ বইটির দ্বিতীয় মুদ্রণেও (আষাঢ় ১৩৮৩) তাঁর ভূমিকা ছিল। অন্নদাশঙ্কর রায় প্রাক্-ভূমিকায় লিখছেন: “একজন অপরিচিত লেখকের রচনা পত্রস্থ করে ‘বিচিত্রা’ সম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় তাকে পাঠকসমাজে পরিচিত হতে দেন এবং শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র সরকার সেটিকে পুস্তকাকারে প্রকাশনের দায়িত্ব নিয়ে লেখককে নিশ্চিন্ত করেন। আর স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে ভূমিকা লিখে দেন কথাগুরু শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয়। এই তিনজনের কাছে লেখক চিরকৃতজ্ঞ।” কথাগুলি একই প্রকাশকের ঊনবিংশ মুদ্রণ ১৪২৫-এও মুদ্রিত হয়েছে। অথচ প্রমথ চৌধুরীর ভূমিকাটি অবলুপ্ত। তাঁর ধীশক্তি, ক্ষুরধার লেখনীতে যে বাণীরূপ ভাষাশিল্পে চিত্রিত, তাঁর ভূমিকাটি হুবহু উদ্ধার করি—
ভূমিকা
আমি যখন ‘বিচিত্রা’ পত্রিকায় প্রথম ‘পথে প্রবাসে’ পড়ি, তখন আমি সত্য-সত্যই চমকে উঠেছিলুম। কলম ধরেই এমন পাকা লেখা লিখতে হাজারে একজনও পারেন না। শ্রীযুক্ত অন্নদাশঙ্করের লেখা পড়লেই মনে হয় যে, তাঁর মনের কথা মন থেকে কলমের মুখে অবলীলাক্রমে চলে এসেছে। এ গদ্যের কোথাও জড়তা নেই এবং এর গতি সম্পূর্ণ বাধামুক্ত। আমরা যারা বাঙলা ভাষায় মনোভাব প্রকাশ করতে চেষ্টা করি, আমরা জানি যে, ভাষাকে যুগপৎ স্বচ্ছ ও স্বচ্ছন্দ করা কতদূর আয়াসসাধ্য। সুতরাং এই নবীন লেখকের সহজ, স্বতঃস্ফূর্ত স্বপ্রকাশ ভাষার সঙ্গে যখন আমার প্রথম পরিচয় হয়, তখন যে আমি চমৎকৃত হয়েছিলুম, তাতে আর আশ্চর্য কি?
এই নবীন লেখকের ইন্দ্রিয় ও মন দুই সমান সজাগ, আর তাঁর চোখে ও মনে যখন যা ধরা পড়ে তখনই তা ভাষাতেও ধরা পড়ে। আমি আগেই বলেছি যে, এই নবীন লেখকের ইন্দ্রিয় ও মন দুই খোলা, আর প্রবাসে গিয়ে তার চোখ কান মন আরও বেশ খুলে গিয়েছিল। তিনি বলেছেন—’আমার চোখজোড়া অশ্বমেধের ঘোড়ার মতো ভূপ্রদক্ষিণে বেরিয়েছে।’ তিনি যে চোখ বুঁজে পৃথিবী ভ্রমণ করেননি, তার প্রমাণ ‘পথে প্রবাসে’র পাতায় পাতায় আছে। আমরা, অর্থাৎ এ যুগের ভারতবাসীরা অর্ধসুপ্ত জাত, আমরা এই বিচিত্র পৃথিবীতে আসি, আর কিছুদিন থেকে চলে যাই। মাঝামাঝি সময়টা একরকম ধ্যানস্তিমিত লোচনেই কাটাই। এর কারণ নাকি আমাদের স্বাভাবিক বৈরাগ্য। আমাদের এই মনোভাবের প্রতি কটাক্ষ করে তিনি বলেছেন: “চুপ ক’রে ঘরে ব’সে ভ্ৰমণকাহিনী লেখা ভালো, বৈরাগ্যবিলাসীর মতো সমস্ত ইন্দ্রিয় নিরুদ্ধ ক’রে সর্ব প্রলোভনের অতীত হওয়া ভালো, সুরদাসের মতো দু’টি চক্ষু বিদ্ধ ক’রে ভুবনমোহিনী মায়ার হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া ভালো”—কিন্তু এ ভালো তিনি চাননি, কারণ তিনি বৈরাগ্যবিলাসী নন। এর ফলে তাঁর ‘পথে প্রবাসে’র মধ্যে থেকে, ‘মানবমানবীর শোভাযাত্রা থেকে কত রঙের পোশাক কত ভঙ্গির সাজ কত রাজ্যের ফুলের মতো মুখ’ পাঠকের চোখের সুমুখে আবির্ভূত হয়েছে।
শ্ৰীমান অন্নদাশঙ্কর লিখেছেন যে—”নতুন দেশে এলে কেবল যে সব কটা ইন্দ্রিয় সহসা চঞ্চল হয়ে ওঠে, তা নয়; সমস্ত মনটা নিজের অজ্ঞাতসারে খোলস ছাড়তে ছাড়তে কখন যে নতুন হয়ে ওঠে, তা দেশে ফিরে গেলে দেশের লোকের চোখে খট করে বাধে, নিজের চোখে ধরা পড়ে না।”
সমগ্র ‘পথে প্রবাসে’ এই সত্যের পরিচয় দেয় যে ইউরোপের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয়ে লেখকের মন বিশেষ চঞ্চল ও ইন্দ্রিয় পুরোমাত্রায় সপ্রাণ হয়ে উঠেছে। এর কারণ, ইউরোপ আমাদের কাছে সম্পূর্ণ নতুন দেশ। আর যিনি কখনো ও-দেশে গিয়েছেন, তাঁরই কাছে এ সত্য ধরা পড়েছে যে, সে দেশটা ঘুমের দেশ নয়, মহাজাগ্রত দেশ। জাগরণ অবশ্য প্রাণের ধর্ম, আর তার বাহ্যলক্ষণ হচ্ছে দেহ ও মনের সক্রিয়তা। কবি দ্বিজেন্দ্রলাল বাঙলা দেশের বিষয়ে বলেছেন যে, এ দেশটা স্বপ্ন দিয়ে তৈরি আর স্মৃতি দিয়ে ঘেরা। এক কথায় যদি ইউরোপের বর্ণনা করতে হয় ত বলতে হয় যে, সে দেশটা গতি দিয়ে তৈরি আশা দিয়ে ঘেরা।
প্রথম বয়সে যখন আমাদের ইন্দ্রিয় সব তাজা থাকে, আর যখন মন বাইরের রূপ বাইরের ভাব স্বচ্ছন্দে ও সানন্দে গ্রহণ করতে পারে, তখন ও-দেশের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ে যেটা আমাদের দেশের যুবকরা সব প্রথম মনে ও প্রাণে অনুভব করে, সে হচ্ছে ও-জগতের প্রাণের লীলা। আমি যখন যৌবনে পদার্পণ করে তারপর ইউরোপে পদার্পণ করি, তখন আমারও মন এই বিচিত্র প্রাণের লীলায় সাড়া দেয়। শ্রীমান অন্নদাশঙ্করের এ-কটি কথায় আমাদের সকলেরই মন সায় দেয়, কারণ আমাদের লুপ্তপ্রায় পূর্বস্মৃতি সব আবার স্বরূপে দেখা দেয়—“ইউরোপের জীবনে যেন বন্যার উদ্দাম গতি সর্বাঙ্গে অনুভব করতে পাই, ভাবকর্মের শতমুখী প্রবাহ মানুষকে ঘাটে ভিড়তে দিচ্ছে না, এক একটা শতাব্দীকে এক একটা দিনের মতো ছোট ক’রে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। সবচেয়ে স্বাভাবিক বোধ হচ্ছে পরস্পরের সঙ্গে প্রতিদিনের প্রতি কাজে সংযুক্ত থেকে নারী ও নরের এক স্রোতে ভাসা।” আজকালকার ভাষায় যাদের তরুণ বলে, তাদের মন এর প্রতি কথায় সাড়া দেবে। কারণ সে হচ্ছে যথার্থ তরুণ, যার হৃদয়মন সহজে ও স্বচ্ছন্দে যা স্বাভাবিক, তাতে আনন্দ পায়। অর্থাৎ যারা কোন শাস্ত্রের আবরণের ভিতর থেকে দুনিয়াকে দেখে না, সে শাস্ত্র দেশীই হোক আর বিলেতিই হোক; শঙ্করের বেদান্তই হোক আর Karl Marx-এর Das Kapital-ই হোক। শ্রীমান অন্নদাশঙ্কর আমার বিশ্বাস বিলেত নামক দেশটা চোখ চেয়ে দেখেছেন, পুস্তকের পত্র-আবডালের ভিতর থেকে উঁকি মেরে দেখেননি। এর ফলে তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্ত যথার্থ সাহিত্য হয়েছে।
‘পথে প্রবাসে’র ভূমিকা আমি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে লিখতে বসেছি দু-কারণে। বাঙলায় কোন নতুন লেখকের সাক্ষাৎ পেলেই আমি স্বভাবতঃ আনন্দিত হই। বলা বাহুল্য যে যিনি নতুন লিখতে আরম্ভ করেছেন তিনিই নতুন লেখক নন। যিনি প্রথমতঃ লিখতে পারেন, আর দ্বিতীয়তঃ যাঁর লেখার ভিতর নূতনত্ব আছে, অর্থাৎ নিজের মনের বিশেষ প্রকাশ আছে, তিনি যথার্থ নতুন লেখক। ‘পথে প্রবাসে’র লেখকের রচনায় এ দুটি গুণই ফুটে উঠেছে। আমরা, যারা সাহিত্যজগতে এখন পেনসন-প্রার্থী—আমরা যে নতুন লেখকদেরও যথার্থ গুণগ্রাহী, এ কথাটা পাঠকসমাজকে জানাতে পারলে আমরা আত্মতুষ্টি লাভ করি।
দ্বিতীয়তঃ, আমি সত্য সত্যই চাই যে, বাঙলার পাঠকসমাজে এ বইখানির প্রচার ও আদর হয়। এ ভ্রমণবৃত্তান্ত যে একখানি যথার্থ সাহিত্যগ্রন্থ এ বিষয়ে আমার মনে কোনও সন্দেহ নেই, এবং আমার বিশ্বাস সাহিত্যরসের রসিক মাত্রেই আমার সঙ্গে এ বিষয়ে একমত। তবে আমি আশা করি যে, ও রসে বঞ্চিত কোনও প্রবীণ অথবা নবীন পাঠক, পুস্তকখানিকে শাস্ত্র হিসাবে গণ্য করবেন না, কারণ তা করলেই সোনা ফেলে আঁচলে গেরো দেওয়া হবে। পৃথিবীতে জলবুদ্বুদের ন্যায় নানা মত উঠছে ও মিলিয়ে যাচ্ছে। মনোজগতে এই জাতীয় মতামতের উত্থানপতনের ভিতরও অপূর্বতা আছে। কিন্তু এইসব মতামতকেই মহাবস্তু হিসাবে দেখলেই তা সাহিত্যপদভ্রষ্ট হয়ে শাস্ত্র হয়ে পড়ে। মতামতের বিশেষ কোন মূল্য নেই, যদি না সে মতামতের পিছনে একটি বিশেষ মনের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। আর এ লেখকের মতামতের পিছনে যে একটি সজীব মনের স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়, সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নেই।
শ্ৰী প্রমথ চৌধুরী
এ তো গেল প্রমথ চৌধুরীর লিখিত ভূমিকার কথা। বানান ভুল, মুদ্রণপ্রমাদ নিয়েও স্বয়ং অন্নদাশঙ্কর রায় লিখছেন (তারিখ: ২৮. ১০. ৯৭): “‘পথে প্রবাসে’র অনেকগুলি সংস্করণ হয়েছে কিন্তু হার্ড কভার এডিশন আর পাওয়া যায় না। সেই অভাবটা পূরণ করতে যাচ্ছেন সেই অবনীন্দ্রনাথ বেরা। এতে অলংকরণও থাকছে, তাই এর নাম হয়েছে শোভন সংস্করণ। তার চেয়েও বড় কথা অবনীন্দ্র এটিকে সম্পূর্ণ নির্ভুল করার জন্য যত্নবান হয়েছেন। আগেকার সংস্করণগুলিতে বেশ কিছু মুদ্রণপ্রমাদ ছিল এবং আমার নিজেরও কিছু ভ্রান্তি, এটিকে প্রামাণ্য সংস্করণ বলা যায়।” (পথে প্রবাসে: অন্নদাশঙ্কর রায়, দ্বিতীয় সচিত্র বাণীশিল্প শোভন সংস্করণ, আগস্ট ১৯৯৯)—কথা হলো, সাধারণ পাঠকের পক্ষে বিভিন্ন প্রকাশনের একই বই সংগ্রহ করা সম্ভব নয়।
বিমানবিহারী মজুমদার (৭. ১. ১৯০০-১৮. ১১. ১৯৬৯)-এর ‘শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান’ (প্রথম সংস্করণ: ২১ ফাল্গুন, ১৩৪৫ এবং দ্বিতীয় সংস্করণ: রাস পূর্ণিমা, ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দুটি সংস্করণই প্রকাশ করেছিল। পরবর্তীকালে সংস্কৃত বুক ডিপো (২৮/১ বিধান সরণি, কলকাতা-৬) এই বইটি প্রকাশ করে। লেখা হলো ‘প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি ২০০৬’। সংস্কৃত বুক ডিপো সংস্করণে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকাটি নেই। অথচ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় কয়েকটি উল্লেখযোগ্য তথ্য ছিল। তাও অবিকল উদ্ধৃত হলো—
দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা
গত বিশ বংসর ধরিয়া এই গ্রন্থের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে বহু আলোচনা হইয়াছে। বিরুদ্ধ আলোচনার প্রধান প্রধান বক্তব্যের সম্বন্ধে আমার মতামত এই সংস্করণে সংক্ষেপে প্রদত্ত হইল। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়ের রচনাকাল সম্বন্ধে আমার পূর্ব্বমত পরিত্যাগ করিয়াছি। অন্যান্য অধিকাংশক্ষেত্রে মত পরিবর্তন করিবার কোন সঙ্গত কারণ দেখি নাই। দ্বিতীয় ও ঊনবিংশ অধ্যায় নূতন করিয়া লেখা হইয়াছে। ঐ দুইটি অধ্যায় পাঠ করিয়া অবিশেষজ্ঞগণও শ্রীচৈতন্য সম্বন্ধে ঐতিহাসিক সত্য নির্দ্ধারণ করিতে পারিবেন আশা করি।
আজ গর্ব্ব ও আনন্দের সঙ্গে প্রকাশ করিতেছি যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানীন্তন পি-এইচ. ডি. পরীক্ষায় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ এই নিবন্ধের অন্যতম পরীক্ষক ছিলেন। বোধহয় ডক্টরেট উপাধিপ্রাপ্ত অন্য কোন ব্যক্তি অনুরূপ সৌভাগ্যের দাবী করিতে পারেন না। অপর একজন পরীক্ষক ছিলেন অধ্যাপক ডক্টর সুশীলকুমার দে। এই গ্রন্থ প্রকাশের তিন বংসর পরে তিনি তাঁহার সুবিখ্যাত Early History of the Vaisnava faith and Movement in Bengal গ্রন্থে ৩৭টি জায়গায় বক্ষ্যমান নিবন্ধের বিভিন্ন স্থান প্রমাণরূপে উদ্ধৃত করিয়াছেন। প্রাচীনপন্থীদের মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক মহামহোপাধ্যায় ৺ফণিভূষণ তর্কবাগীশ মহাশয় “ভারতবর্ষ” পত্রিকায় দশ বারটি প্রবন্ধে ইহার সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন। কয়েকটি ক্ষেত্রে তাহার মত এই সংস্করণে উদ্ধৃত করিয়াছি। প্রমথ চৌধুরী মহাশয় “পরিচয়ে” এই গ্রন্থের সমালোচনায় লিখিয়াছিলেন যে “তিনি (লেখক) জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলকেও প্রাথমিক গ্রন্থ হিসেবে গণ্য করেন। আমার এ বিষয়ে সন্দেহ আছে।” এ সন্দেহ খুবই যুক্তিযুক্ত। তবে কলিকাতা এশিয়াটিক সোসাইটীর গ্রন্থালয়ে জয়ানন্দের গ্রন্থের একখানি প্রায় সম্পূর্ণ ও বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে কয়েকখানি খণ্ডিত প্রাচীন পুঁথি পাওয়া গিয়াছে বলিয়া উহাকে একেবারে উড়াইয়া দেওয়া যায় না।
পরিশেষে আমি আমার অনুজোপম সুহৃদ্ অধ্যাপক ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত মহাশয়ের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি। তাঁহার উৎসাহ ও সহায়তা না পাইলে এই সংস্করণ প্রকাশ করা সম্ভব হইত না। আমার কনিষ্ঠ পুত্র অধ্যাপক শ্রীমান্ ভগবনপ্রসাদ মজুমদার ইহার নির্ঘণ্ট প্রস্তুত করিয়াছে।
শ্ৰীবিমানবিহারী মজুমদার
গোলা দরিয়াপুর, পাটনা,
রাস পূর্ণিমা, ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ
চিন্তাশীল পাঠকের দ্বিতীয় সংস্করণের উপরি-উক্ত তথ্যগুলি জানা অপরিহার্য ছিল। অথচ সংস্কৃত বুক ডিপো-র কর্তৃপক্ষ এ-বিষয়টিতে দৃষ্টি দিলেন না। আবার দুটি প্রকাশনার (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও সংস্কৃত বুক ডিপো) গ্রন্থে বিষয় বিন্যাসেও পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। এতে বোধহয় আমাদের মতো সাধারণ পাঠক বিভ্রান্তির শিকার হন। এঁদের প্রকাশনার আর একটি গ্রন্থ গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্নের ‘শব্দসার’ অভিধান। কালের দাবিকে মান্য করে পুরোনো গ্রন্থের পুনর্মুদ্রণ এবং সংস্করণ অবশ্যই প্রয়োজন। কিন্তু প্রকাশক যত্নশীল হবেন এবং সংস্কারক তাঁর সংস্কার-সাধন-পরিচয় লিপিবদ্ধ করবেন, তবেই তা পাঠকের গ্রহণীয় হবে। সংস্কৃত বুক ডিপো থেকে প্রকাশিত গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন (২৬. ৯. ১৮২২-৩. ১২. ১৯০৩)-র ‘শব্দসার’ অভিধান (পুনর্মুদ্রণ সেপ্টেম্বর ২০১৪) সম্পর্কে অনুযোগ বিস্তর।
বইটিতে সম্পাদকের নাম নেই। ‘নবম সংস্করণের বিজ্ঞাপন’-এ আছে—‘সেগুলিকে সাধারণতঃ পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে পারা যায়। যথা—’ পাঁচটি শ্রেণির উল্লেখ করা হলেও চারটি শ্রেণির কথা এখানে লেখা হলো। বাদ গেল ‘৪র্থ শ্রেণী—খাস বা খাঁটি বাঙ্গলা’। ‘৪র্থ শ্রেণী’ হিসাবে গ্রন্থে যা মুদ্রিত হলো ‘বিভিন্ন ভাষা হইতে গৃহীত’ তা প্রকৃতপক্ষে ‘৫ম শ্রেণী’ভুক্ত। ‘শব্দসার’ অভিধানের অন্য কোনও সংস্করণ (পঞ্চম থেকে নবম) পাঠক দেখলে বুঝবেন, কত নিষ্ঠায় তা সম্পন্ন হয়েছে। আর সংস্কৃত বুক ডিপোর ‘শব্দসার’ অভিধানে ভুলের মাত্রা অত্যধিক। অভিধান আমাদের বানানের সংবিধান। বানানের মান্যতা না থাকলে তা বিপজ্জনক। এঁদের অভিধান ব্যবহার করলে তা বোধহয় শব্দার্থ-ঋদ্ধতার অন্তরায় হবে।
রামেন্দ্রসুন্দর জীবন-কথা: আশুতোষ বাজপেয়ী (গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্, ২০৩/১/১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা) চৈত্র ১৩৩০ সালে প্রকাশিত হয়েছিল বইটি। ড. এম. কে. আলম-এর সম্পাদনায় কে. পি. এম (৬৯ সীতারাম ঘোষ স্ট্রিট, কলকাতা-৯) থেকে ২০০৬ সালে বহরমপুর বইমেলায় পুনঃপ্রকাশিত হয়। ড. এম. কে. আলম-এর সম্পাদনায় গ্রন্থটির প্রথম প্রকাশক, ব্যক্তিবর্গ, প্রতিষ্ঠানের পরিচয় সম্পর্কে তথ্যপূর্ণ টীকা ও নির্দেশিকা থাকবে আমরা আশা করেছিলাম, অন্তত ‘সম্পাদনা’ শব্দটি দেখে তাই মনে হয়েছিল। সবই মরীচিকা!
‘আত্ম-জীবন অর্থাৎ ভাই গিরিশচন্দ্র সেন কর্ত্তৃক বিবৃত আত্ম-জীবনবৃত্তান্ত’ গ্রন্থটি ১২ পৌষ ১৩১৩ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়। এই বইটি বারিদবরণ ঘোষ (জন্ম: ১৫ জুন ১৯৩৯)-এর সম্পাদনায় প্রথম বিগ বুক্স সংস্করণ ২০১৭-তে প্রকাশিত হয়েছে। মূল বইটি তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রন্থাগার থেকে সংগ্রহ করেছেন। বইটির টাইটেল পেজ তার পাথুরে প্রমাণ দেয়। ‘প্রথম সংস্করণ ১৩১৩ বঙ্গাব্দ’ সম্পাদক লিখেছেন। বোধহয় ‘প্রথম সংস্করণ’ নয় ‘প্রথম প্রকাশ’ হবে। বলা বাহুল্য ৩০ জুন ১৯৮৫-তে ‘অনন্য প্রকাশন’ (৬৬ কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩) থেকে প্রকাশক হীরক রায় এই বইটি প্রকাশ করেছিলেন। এই তথ্যটুকু বিগ বুক্স-এর প্রকাশনায় লেখা থাকলে ভালো হতো। তারপর একটি উৎসর্গপত্রও আছে—’বর্তমান অনুসন্ধিৎসু পাঠকদের উদ্দেশে’। এরূপ উৎসর্গপত্রের যৌক্তিকতা বোঝা গেল না। কারণ পুনর্মুদ্রিত গ্রন্থে উৎসর্গপত্র দেওয়া যায় কি? তবে ‘প্রাক্কথন’ ‘ভিন্নধর্মী জীবন: অন্যধর্মী আত্মজীবনী’ অংশের জন্য পাঠক-সাধারণ বারিদবরণ ঘোষের কাছে কৃতজ্ঞ থাকবেন। গিরিশচন্দ্র সেনের (১৮৩৫/৩৬-১৫. ৮. ১৯১০) আত্ম-জীবন আত্মপ্রচার বিমুখ এক সংযত রচনা হিসেবে পাঠকের কাছে চিরকাল সমাদৃত হবে। তথ্যপূর্ণ টীকা ও নির্দেশিকা বইটিতে থাকলে গুরুত্ব বাড়ত।
গোপাল হালদার (১১. ২. ১৯০২-৩. ১০. ১৯৯৩)-এর ‘আড্ডা’ বইটির (প্রথম প্রকাশ: জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৩) প্রকাশক ছিলেন শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (১৯০৯-১৯৯১), এই বইটি বেঙ্গল পাবলিশার্স (১৪ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-১২) থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য মনোজ বসু (২৫. ৭. ১৯০১-২৬. ১২. ১৯৮৭) ও শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বেঙ্গল পাবলিশার্স-এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন। যাই হোক, এঁদের পুরোনো ‘আড্ডা’ বইটির প্রচ্ছদ নেই। বইয়ে প্রচ্ছদ না থাকার কারণ দপ্তরি প্রচ্ছদ অনাবশ্যক মনে করায় তা পরিহার করেছেন। অথচ প্রতিটি বইয়ের প্রচ্ছদ থাকে এবং তা অপরিহার্য। এই প্রচ্ছদ, বইটির সামগ্রিক পরিচয় বহন করে। মূল বইটির প্রতিটি নিবন্ধের শুরুতেই একটি করে তাৎপর্যমণ্ডিত ছবি ছিল।
পুথিপত্র (ক্যালকাটা) প্রাইভেট লিমিটেড থেকে কলকাতা বইমেলা, জানুয়ারি ২০০৪ সালে এ বইটি পুনরায় প্রকাশিত হলো, তাতে লেখা হলো ‘প্রথম পুথিপত্র সংস্করণ’। এর দ্বিতীয় মুদ্রণ হয়েছিল এপ্রিল ২০০৫। এখানে একটি বিজ্ঞপ্তি আছে এইরকম—”বইটি ত্রুটিমুক্তি প্রকাশনার স্বার্থে সম্পাদক ও প্রকাশকের তরফে যথাসাধ্য চেষ্টা করা সত্ত্বেও কিছু ভুলত্রুটি থেকে যাওয়া অসম্ভব নয়। এজন্য কোনোরূপ অবাঞ্ছিত ক্ষতির জন্য সম্পাদক বা প্রকাশক দায়ী নহে।” এমন কথার প্রাসঙ্গিকতা কী তা বোঝা গেল না। কিন্তু এমন ঘোষণা পাঠকের চিন্তন শক্তিকে ব্যাহত করে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। শুধু তাই নয় প্রতিটি নিবন্ধের শুরুতে ‘আড্ডা’য় যে ছবি ১৩৬৩ সালের বইয়ে ছিল—তা পুথিপত্র প্রকাশনায় রক্ষিত হলো না। তবে অমিয় ধরের লেখা ‘গ্রন্থ প্রসঙ্গ’ পাঠকের বইটি পাঠে আগ্রহ সৃষ্টি করবে। দেবযানী হালদার ‘গ্রন্থস্বত্ত্ব’ (< গ্রন্থস্বত্ব) পাবেন কিনা সন্দেহ আছে! অবশ্য আদার ব্যাপারীর এসব খবরের প্রয়োজন কী? মাথা নীচু করে মানছি।
১২৫তম রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে ‘রবীন্দ্র-রচনাবলী’র সুলভ সংস্করণ বিশ্বভারতী থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। সাধারণ পাঠক হিসেবে উক্ত সুলভ সংস্করণ গ্রন্থটি সংগ্রহের অভিজ্ঞতা ভালো ছিল না। ১৯৮৮ সালে গ্রাহক হওয়ার পর, প্রথম থেকে ষষ্ঠ খণ্ড পাওয়া গেল জুন ১৯৮৮-তে। শেষ পঞ্চদশ খণ্ড পাওয়া গেল জুলাই ১৯৯২-এ। পনেরোটি খণ্ড পেতে চার বছর সময় লেগেছিল। অথচ ‘Instruction’-এর তৃতীয় ধারায় লেখা ছিল—‘Coupons for Volumns 1-15 may be Collected from Visva Bharati Publishing Department, 6 Acharya Jagadish Bose Road Calcutta 700017 during the period 1. 6. 88 to 30. 6. 88’ এই সুলভ সংস্করণের রবীন্দ্র রচনাবলীর মুদ্রণ প্রমাদের কথা থাক। ‘ছিন্নপত্র’-এর (প্রথম প্রকাশ: ১৮ জুলাই ১৯১২) অমুদ্রণজনিত প্রাপ্তিহীনতা মেনে নিতে পারা যায় না। সুলভ সংস্করণে ছিন্নপত্র আক্ষরিক অর্থে নামকরণ সার্থক তা চাক্ষুষ করলাম।
উপেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য (১৭. ৪. ১৮৯২-৫. ৮. ১৯৭৪)-র ‘আমার এলোমেলো জীবনের কয়েকটি অধ্যায়’ (প্রকাশক: ‘মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড’, কলকাতা) ১৯৬২ সালে প্রথম মুদ্রিত হয়েছিল। ৫২ বছর পর বইটি একই প্রকাশনা থেকে ২০১৪ সালে পুনমুর্দ্রণ হলো। যদিও পুনর্মুদ্রণের জায়গায় ‘দ্বিতীয় সংস্করণ: ২০১৪’ লেখা আছে। কিন্তু বইটির আষ্টেপৃষ্ঠে সংস্করণের কোনও চিহ্নই পরিলক্ষিত হয় না। বরং বইটির দুটি প্রকাশকালের (১৯৬২, ২০১৪) ব্যবধানেও পৃষ্ঠা সংখ্যা (৪৮০+১২০ = ৬০০) এবং মুদ্রণ একই রাখা হয়েছে। ২০১৪ সালের বইটির কাগজ, মুদ্রণ ভালো নয়। অনেকক্ষেত্রে ছাপা অস্পষ্ট। বইটিতে কোনও টীকা নেই, নির্ঘণ্ট নেই, পুনর্মুদ্রণের প্রাসঙ্গিকতাও নেই। অথচ গ্রন্থালোকের এমন সুদুর্লভ তথ্যের আকর আমাদের জ্ঞানের বিহনে যথার্থ প্রাণের রসদ হয়ে উঠল না।
রেজাউল করীম (১৯০২-১৯৯৩)-এর ‘বঙ্কিমচন্দ্র ও মুসলমান সমাজ’ ব়্যাডিক্যাল প্রকাশনা (৪৩ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৯) থেকে, জানুআরি ২০১৪ সালে প্রকাশিত হয়েছে। এই বইটি ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোম্পানি লিমিটেড, কলকাতা-৭ থেকে ১৯৪৪ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। বইটি সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে মানবসম্প্রীতির একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। রেজাউল করীম তথাকথিত মুসলমান সম্প্রদায়ের ‘আনন্দমঠ’ (১৮৮২)-এর বহ্নি-উৎসবকে সর্বাংশে নিন্দিত করে লিখছেন, “দৃশ্যতঃ মনে হইল ‘আনন্দমঠ’ ভস্মীভূত হইল। কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে ভস্মীভূত হইল মুসলমানের স্বাধীন চিন্তার শক্তি—ভূলুণ্ঠিত হইল মুসলমানের আত্ম-সম্মান ও সুমহান মহিমায় স্পর্ধিত আনন!” (“আনন্দমঠে”র বহ্নি-উৎসব, ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং, পৃষ্ঠা: ৮২) কিন্তু কথা তা নয়, ব়্যাডিক্যাল-এর অরুণকুমার দে-র সম্পাদনায় দুর্লভ গ্রন্থটি প্রকাশিত হলো সত্য, কিন্তু আরও কঠিন সত্য ১৯৪৪ সালে প্রকাশিত উক্ত গ্রন্থটির শেষাংশে ‘বঙ্কিমচন্দ্র: কাজী আবদুল ওদুদ’ (পৃষ্ঠা: ১২১-১৩০) এবং ‘সাম্যবাদী বঙ্কিমচন্দ্র: মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্’ (পৃষ্ঠা: ১৩০-১৪৭) প্রবন্ধ দুটির তিনি অবলুপ্তি ঘটিয়েছেন। কাজী আবদুল ওদুদ (২৬. ৪. ১৮৯৪-১৯. ৫. ১৯৭০)-এর প্রবন্ধটি ‘প্রবাসী’ পৌষ ১৩৪৫-এ প্রকাশিত হয়েছিল এবং মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ (১০. ৭. ১৮৮৫-১৩. ৭. ১৯৬৯)-এর তারিখহীন প্রবন্ধটি ঢাকা শতবার্ষিকী সভাতে পঠিত হয়েছিল। প্রথম প্রবন্ধটি (ওদুদের) পাওয়া গেলেও দ্বিতীয় প্রবন্ধটি (শহীদুল্লাহ্র) আর পাওয়ার কোনও উপায় নেই। এই উল্লেখযোগ্য গ্রন্থটির পুনর্মুদ্রণেরও কোনও আশা নেই। সাধারণ পাঠক এবং গবেষক অরুণকুমার দে-র সম্পাদিত গ্রন্থে এ তথ্যটুকু পাবেন না। অথচ ওদুদ ও শহীদুল্লাহ্র প্রবন্ধ দুটি ভাষার সৌন্দর্যে, ভাবের গভীরতায়, আনন্দের উপাদানে ও সৃষ্টি-বৈচিত্র্যে মানবের চিত্তপটে সত্য-শিব-সুন্দরের আসন করে নিয়েছে। অবশ্য ব়্যাডিক্যাল প্রকাশনায় ‘বঙ্কিমচন্দ্র ও মুসলমান সম্পর্ককে ফিরে দেখা’-কংকর সিংহর (১৯৩৮-২০২০) লেখাটি (পৃষ্ঠা ৭৫-৮৭) তথ্য ও তত্ত্বে সমৃদ্ধ।
যাই হোক, ‘বঙ্কিমচন্দ্র ও মুসলমান সমাজ’ (১৯৪৪) গ্রন্থের পরিশিষ্ট অংশের থেকে ওদুদ এবং শহীদুল্লাহ-র প্রবন্ধ দুটি স্মৃতির অতলে না পাঠিয়ে উদ্ধার করা হলো—
বঙ্কিমচন্দ্র
[কাজী আবদুল ওদুদ, এম. এ.]
কিছুকাল ধরে বাংলাদেশে শত-বার্ষিকী, জয়ন্তী প্রভৃতি উৎসব মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হয়ে চলেছে। এর প্রথমটি যদিও মৃতকে অবলম্বন করে, আর দ্বিতীয়টির অবলম্বন জীবিত, তবু বোঝা যাচ্ছে স্বরূপতঃ দুটি অভিন্ন—দুই ক্ষেত্রেই লক্ষ্য দাঁড়িয়েছে স্মৃতি-চর্চ্চা আর উপলক্ষ কিঞ্চিৎ নব প্রেরণা লাভ। কাজটি এক হিসাবে স্বাভাবিক, সঙ্গতও বটে। পিতৃপুরুষের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন মানুষের চিরন্তন ধর্ম্ম, আর সেই পিতৃপুরুষ যদি কৃতী হন, তবে ত সেই শ্রদ্ধা-নিবেদন হ’য়ে উঠে অনিবার্য্য। কিন্তু একালের বাঙ্গালীর এই ধরণের স্মৃতি-পূজার ব্যাকুলতায় তার বর্ত্তমান দুরবস্থার করুণ সুরও যে বাজছে সে বিষয়ে অবহিত না হওয়া অশুভ বৈ শুভ নয়।
বঙ্কিম-জন্ম শতবার্ষিকী সম্পর্কে এই কথাটি মনে হওয়ার বিশেষ কারণ এই যে, তার সুবিপুল কর্মজীবনের অবসান ঘটেছে অর্দ্ধ শতাব্দীরও কম কাল পূর্ব্বে। যে বিচিত্র ভাব ও কর্ম্ম-ধারার তিনি প্রবর্ত্তক অথবা সহায়ক, সে সবের ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া এ পর্য্যন্ত এতখানি মন্দীভূত হয় নাই যে, শতবার্ষিকী শোভন একটি অপ্রমত্ত শ্রদ্ধা নিবেদনের সুযোগ তাঁর দেশবাসীর ঘটেছে, ফলে তাঁর এই বিশেষ স্মরণোৎসব যথেষ্ট পরিমাণে মর্য্যাদা সম্পন্ন হতে পারছে না। এর একটি দৃষ্টান্ত অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকবে। বঙ্কিমচন্দ্রের স্বভাষী ও স্বদেশবাসীরা আজ প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—হিন্দু আর মুসলমান। যাঁরা তাঁর ভক্ত ব’লে নিজেদের পরিচিত করতে চান তাঁদের সংখ্যা হিন্দু শ্রেণীতে বেশী, আর যারা তাঁর অভক্ত ব’লে নিজেদের পরিচিত করতে চান তাঁদের সংখ্যা মুসলমান শ্রেণীতে বেশী। অভক্ত দল বলছেন, বঙ্কিমচন্দ্র প্রতিভাবান্ যত বড়ই হোক, সাম্প্রদায়িক বুদ্ধি তাঁতে প্রবল। সমস্ত বাঙ্গালীর বা ভারতবাসীর এক জাতীয়তা তিনি চান নাই, তিনি যা চেয়েছেন তার নাম দেওয়া যেতে পারে হিন্দু-সংহতি ও হিন্দু-প্রাধান্য, তাঁর আনন্দমঠের হিন্দু শক্তির পুনরুদ্ধারকামী সন্ন্যাসীরা মুসলমান নির্য্যাতনে যে স্ফূর্ত্তির পরিচয় দিয়েছে তা যেমন উৎকট তেম্নি পৈশাচিক। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের ভক্ত দলের একজন মাননীয় ব্যক্তি তাঁর এমন বিতর্কস্থল আনন্দমঠের এই ব্যাখ্যাই যথেষ্ট মনে করেছেন—আনন্দমঠ একখানি উপন্যাস, উপন্যাসের নায়ক-নায়িকার মতামতকে লেখকের মতামত জ্ঞান করা ভুল, দেশের ইতিহাসের একটি অধ্যায় এতে নিপুণভাবে আঁকা হয়েছে মাত্র।
যাঁরা তাঁকে বিশেষভাবে মুসলমান-বিদ্বেষী জ্ঞান করেছেন, তাঁরা এ কথা বোঝা অপ্রয়োজনীয় মনে করছেন যে, বঙ্কিম-সাহিত্যের কয়েকটি উৎকৃষ্ট চরিত্র মুসলমান সমাজ থেকে সংগৃহীত, আর দায়িত্বপূর্ণ জীবনে বিদ্বেষের স্থান যে নেই এ সম্বন্ধে অকুণ্ঠিত তাঁর মতামত। তেম্নিভাবে যাঁরা তাঁকে একান্তভাবে কল্পনাকুশলী ও অঙ্কন-কুশলী রূপস্রষ্টা জ্ঞান করেছেন, তাঁরা তাঁর সম্বন্ধে এই প্রশ্নের সম্মুখীন হওয়া প্রয়োজনীয় মনে করেন নাই যে, তাঁর চারপাশের লোকদের আশু কল্যাণ-কামনা তাঁর ভিতরে এত প্রবল ছিল যে, শেষ বয়সে শিল্পের ক্ষেত্র ত্যাগ করে প্রচারের ক্ষেত্রে তিনি অবতীর্ণ হয়েছিলেন, আর শিল্পকে প্রচারধর্ম্মী করতে তিনি লজ্জিত হননি কোনদিন। বাস্তবিক বঙ্কিম-প্রতিভা যেমন বিপুল, তেম্নি সবল, তেম্নি জটিল, কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাঁর পূজারী আর বিদ্বেষী দল কেবল তাঁর সরলতায় পুলকিত বা বিচলিত হয়েছেন মাত্র, তাঁর জটিলতা আজো তাঁদের দৃষ্টিপথের বহির্ভূত।
বঙ্কিম-প্রতিভা যে জটিল—সবল ত বটেই—মনে হয় তার পর্য্যাপ্ত উপলব্ধিই তাঁর জন্ম-শতবার্ষিকীতে তাঁর প্রতি, তাঁর দেশবাসীর উপযুক্ত শ্রদ্ধা নিবেদন বলে গণ্য হতে পারে। এক হিসাবে তা সুসম্পন্নও হয়েছে। যাঁরা তাঁর প্রতি প্রবল অপ্রসন্নতা জ্ঞাপন করছেন, তাঁরা প্রকারান্তরে তাঁর শক্তির জয়ধ্বনি করছেন—সত্য ও কল্যাণের বেশ অনেক সময়ে শত্রুর বেশ। বঙ্কিমচন্দ্র স্বদেশ-প্রেমিক ও মানব-প্রেমিক, বঙ্কিমচন্দ্র শক্তির উপাসক ও দুর্বলতার ধ্বংসকামী—এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই; মানবসুলভ সমস্ত ত্রুটিবিচ্যুতি সত্ত্বেও তাঁর প্রয়াস, তাঁর স্বভাষী ও স্বদেশবাসীদের জন্য তাই শেষ পর্য্যন্ত কল্যাণকর ভিন্ন আর কিছু হ’তে পারে না। শুধু প্রয়োজন তাঁর ভক্ত ও অভক্তদের অতিবাদ উপেক্ষা ক’রে দেশের মানসলোকে, তাঁর যথাযোগ্য স্থান নির্দ্দেশের চেষ্টা। সে চেষ্টা অবশ্য সময়সাপেক্ষ—শুধু বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভার জটিলতার জন্য নয়—আমাদের দেশের লোকের মানসিক জটিলতার জন্যও। বঙ্কিম মৃত্যু-শতবার্ষিকী পর্য্যন্ত এ চেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হতেও পারে।
বঙ্কিম-প্রতিভার সত্যকার মর্য্যাদা উপলব্ধির পথে বাধা কোথায় সেই সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলতে চেষ্টা করা যাক। তাঁর প্রতিভা যে জটিল সে সম্বন্ধে খুব বড় একটি কথা এই যে, নিজেকে হিন্দু বলে, হিন্দুর একান্ত মঙ্গলকামী বলে, পরিচিত করবার আগ্রহ তাঁর যত প্রবলই হোক, প্রকৃতপ্রস্তাবে হিন্দুত্বের মর্ম্মগ্রাহী তিনি যতখানি তার চাইতে তাঁর সমসাময়িক ইয়োরোপীয় চিন্তার অনুরাগী তিনি অনেক বেশী। তাঁর মুখের কথায় আর অন্তরের প্রবণতায় এই যে বিরোধ—অনেক প্রতিভার ভিতরেই এমন বিরোধ বিদ্যমান—সে সম্বন্ধে কৌতূহল তাঁর দেশের শিক্ষিত সমাজে কমই অনুভূত হয়েছে। তেম্নিভাবে ভ্রান্ত তাঁর সম্বন্ধে তার দেশবাসীর এই প্রচলিত মত যে তাঁর পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের ইয়োরোপীয় মোহে দিশেহারা বাঙ্গালী ঘরে ফেরার আহ্বান প্রথম স্পষ্টভাবে শুনতে পায় তাঁর সবল কণ্ঠে। প্রথমতঃ বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্ব্ববর্ত্তী বাঙ্গালী অর্থাৎ হিন্দু-কালেজীয় দল ঠিক দিশেহারা নন, তাঁরা বরং বিদ্রোহী, আর তাঁদের সে বিদ্রোহ সবল।
দ্বিতীয়তঃ, দেশের প্রাচীন ঐতিহ্যের সন্ধান তাঁরা নেননি, এ অপরাধে তাঁরা যতখানি অপরাধী তার চাইতে অনেক বেশী শ্ৰদ্ধার অধিকারী তাঁরা এই জন্য যে তাঁদের যুগের ব্যাপক মনুষ্যত্বহীনতার মাঝখানে তাঁদেরই ললাটে প্রথম প্রতিভাত হয়েছিল মনুষ্যত্বের নবকীর্ত্তি। কৈশোরে স্বেচ্ছাচারী এই হিন্দু-কালেজীয় দল পরিণত বয়সে জ্ঞান ও কর্ম্মের নানা ক্ষেত্রে যে দেশের গৌরব বৃদ্ধি করেছিলেন এ কথা সুবিদিত। ফরাসী বিপ্লবের পরের যে নব জ্ঞান-সাধনা ও মানবতা-সাধনা তার প্রতি প্রবলভাবে অনুরাগী যেমন হিন্দু-কালেজীয় দল তেম্নি বঙ্কিমচন্দ্র, আর সেই জন্যই হিন্দু্ত্বের বিদ্বেষী হিন্দু-কালেজীয় দল আর তার পূজারী বঙ্কিমচন্দ্র প্রকৃতপ্রস্তাবে এক সম্প্রদায়ের ভাবুক। ব্রাহ্মদের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের বহু কীর্ত্তিত মতবিরোধও এম্নিভাবে বিচার করে দেখা দরকার। ব্রাহ্মরা খৃষ্ট ধর্ম্মের যত অনুরাগী হয়েছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র তা হন নাই মিথ্যা নয়, কিন্তু ধর্ম্মচিন্তা বিষয়ে ব্রাহ্মদের যেটি শ্রেষ্ঠ দান, অর্থাৎ সগুণ ঈশ্বরের মাহাত্ম্যের নব উপলব্ধি, বঙ্কিমচন্দ্রের তত্ত্বজিজ্ঞাসাও সেই মুখী। হিন্দু-তত্ত্বজ্ঞের চোখে তাই ব্রাহ্মরা যেমন নিকৃষ্ট হিন্দু, বঙ্কিমচন্দ্রও তেম্নি। পুরাতন মতবাদের পুনরুজ্জীবনচেষ্টার এমন পরিণতি এ কালের আর একজন শ্রেষ্ঠ ভারতীয়ের মধ্যেও লক্ষ্য যোগ্য। তিনি প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মা গান্ধী।
নিজেকে বরাবর তিনি বলেছেন সনাতনী হিন্দু। অথচ আধুনিক জীবনের প্রয়োজনে অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে অভিযান যখন তাঁকে করতে হয়েছে তখন তিনি বলেছেন—লিখিত শাস্ত্রই সমগ্র শাস্ত্র নয়, মানুষের অন্তর্নিহিত সত্য ও কল্যাণ আকাঙ্ক্ষাই চরম শাস্ত্র।
শুধু ধর্ম্ম ও সমাজ সংক্রান্ত ব্যাপারে নয়, সাহিত্যেও বঙ্কিমচন্দ্রের প্রচারিত মতামতে আর অন্তরের প্রবণতায় প্রবল বিরোধ বিদ্যমান। শুধু পাপের প্রতি নয়, পাপীর প্রতি অসহিষ্ণুতাও তাঁর উপন্যাসে প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু সত্যকার সাহিত্যিক গৌরব তাঁর রচনা যেখানে লাভ করেছে সেখানে মতামতের পরিবর্ত্তে সহজ কবি-ধর্ম্ম, অর্থাৎ মানবতার প্রতি তাঁর সহজ প্রেম প্রকাশ পেয়েছে অনবদ্য ভাবে। এর দৃষ্টান্ত ভবানন্দ, জেবউন্নিসা, শৈবলিনী, মতিবিবি—তাঁর এই সব অসাধু চরিত্র। এই সব চরিত্রের প্রতি অনাদরের কথা তিনি উচ্চারণ করতে কুণ্ঠিত হননি। কিন্তু যে সব চরিত্রের প্রতি তিনি বিশেষ সমাদর দেখিয়েছেন, যেমন প্রফুল্ল, ব্রজেশ্বর, ভবানী পাঠক, জয়ন্তী, পূর্ব্বোক্ত অসাধু চরিত্রগুলির সঙ্গে তুলনায় এই সব সাধু চরিত্র সহজ মানবতার দিক দিয়েও সাহিত্যিক সৃষ্টি হিসাবে কত হীন!
বাস্তবিক প্রচারক বঙ্কিমচন্দ্রের মাহাত্ম্য অসঙ্গতভাবে বড় করে দেখা হয়েছে। আমি অন্যত্র বলতে চেষ্টা করেছি, এর মুখ্য কারণ রাজনৈতিক; ঊনবিংশ শতাব্দীতে এক বিশেষ রাজানুগ্রহ হিন্দুর লাভ হয়েছিল, তার সঙ্গে গূঢ় যোগ রয়েছে হিন্দু-জাগরণের ও সেই দিক দিয়ে প্রচারক বঙ্কিমচন্দ্রের খ্যাতি-প্রতিপত্তি। কিন্তু এ কাল আমাদের জন্য ব্যাপকভাবে মোহ-নাশের কাল, প্রচারক বঙ্কিমচন্দ্রের বিতর্কিত মাহাত্ম্যের বিঘোষণার চাইতে তাই আমাদের জন্য বেশী প্রয়োজনীয় স্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্রের অপরিসীম মর্য্যাদার উপলব্ধি। সেই স্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্রকে আমরা তাঁর উপন্যাসে স্থানে স্থানে ত পাবই, কিন্তু বিশেষ দৃষ্টি দিয়ে দেখলে তাঁকে পাব তাঁর সমস্ত রচনার ভিতরে যেখানে অনেকটা তাঁর অজ্ঞাতসারে তাঁর বিরাট ও জটিল ব্যক্তিত্ব চমৎকার রূপ লাভ করেছে। এই ভাবে দেখলে তাঁর মনীষা ও ভাবালুতা, প্রেম ও অপ্রেম, জাতীয়তা ও সাম্প্রদায়িকতা সমস্তই পরম অর্থপূর্ণ হয়ে উঠবে তাঁর যুগের পটভূমিকায় বিন্যস্ত হ’য়ে, বোঝা যাবে, তাঁর যুগের তিনি একজন অসাধারণ ব্যক্তি, এদেশের বহু দুঃখে-দুঃখী হিন্দুসমাজে তাঁর জন্ম, সে জন্যে সেই সমাজের বেদনা তিনি ভুলতে পারেননি কোনদিন, কিন্তু শুধু হিন্দুর সন্তান তিনি নন, বৃহত্তর দেশের ও কালেরও তিনি সন্তান, তাই এসবের প্রত্যেকের প্রতি গভীর প্রেমের পরিচয় তাঁর সাধনায় রয়েছে।
বঙ্কিমচন্দ্রকে তাঁর কালের এক বিশেষ সৃষ্টি হিসাবে না দেখে তাঁর দেশ ও দেশবাসীর চিরকালের নেতারূপে যে দেখা হয়েছে এতেই তাঁর প্রতিভা ও দেশবাসীর উপরে তাঁর প্রভাব দুই বিড়ম্বিত হয়ে চলেছে। এ কালে তাঁর এক শ্রেণীর দেশবাসীর অত্যুগ্র বিদ্বেষ এই বিড়ম্বনার একটি পরিচয়-চিহ্ন। অথচ বঙ্কিম-প্রতিভা এমন শক্তিসমন্বিত, এমন বাস্তবমুখী যে তার যোগ্য সাহচর্য্য থেকে তার পাঠকবর্গের অশেষ সুফল লাভেরই কথা। জীবনকে তিনি বহুদিক দিয়ে বুঝতে চেষ্টা করেছিলেন তাতে সন্দেহ মাত্র নেই।
(ঢাকা শতবার্ষিকী উৎসবে পঠিত)
২.
প্রায় সকল সাহিত্যেই কবির লেখনীর আঘাত অক্ষয় হইয়া আছে। মুসলমান মহাকবি ফেরদৌসী মহমুদ গজনীর কুৎসা লিখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার সেই প্রতিশোধলিপিতে যথেষ্ট মুন্সিয়ানা প্রদর্শিত হইয়াছে বলিয়া শাহনামার মতো অমর কাব্যের সহিত উহার সম্বন্ধ থাকার জন্যই উহা আজও লোকমুখে কীর্ত্তিত হইতেছে। অথবা ধরুন বঙ্কিমচন্দ্রের কথা। আয়েসার চরিত্রাঙ্কনের জন্য মুসলমান সাহিত্যিক তাঁহাকে এই বলিয়া গালি দেন যে, তাঁহার এ সৃষ্টি সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক। পাঠানদের অন্দর-মহলে অবরোধ প্রথা খুবই দৃঢ় ছিল; সে ক্ষেত্রে আয়েসা ও জগৎসিংহের ভালবাসা হওয়া দূরে থাকুক, দেখা হওয়াই অসম্ভব। এ অভিযোগ যে সত্য তাহা কোন সমালোচকই অস্বীকার করিতে পারেন না। কেন না বঙ্কিমচন্দ্র কৎলুখাঁ ও ওসমানকে এমন উদার করিয়া সৃষ্টি করেন নাই যে, তাঁহারা সেবা-শুশ্রষার বন্দোবস্তের জন্য শত্ৰুকে অন্তঃপুরে স্থান দিবেন। কিন্তু সত্যদৃষ্টি সমালোচক এই কথা বলিয়াই ত বঙ্কিমচন্দ্রের সৃষ্টি উড়াইয়া দিতে পারেন না। কাব্যের যাহা শ্রেষ্ঠ সম্পদ, সেই রসের দিক হইতে বিচার করিতে গেলে ত বঙ্কিমচন্দ্রের দোষ ধরা যায় না। এই যে বিপন্ন বীরের প্রতি নারী-হৃদয়ের স্বাভাবিক শ্রদ্ধা, এই যে মিলনের চিত্র—যে মিলন জাতি, সমাজ, পারিবারিক বন্ধন সমস্ত গণ্ডীকে অতিক্রম করিয়া নিজের মহিমা ফুটাইয়া তুলিয়াছে, বঙ্কিমচন্দ্রের সে সৃষ্টি ত কোন সাহিত্যরসিকই অবজ্ঞা করিতে পারেন না।
অথবা ধরুন বঙ্কিমচন্দ্রের সৃষ্ট জেবউন্নিসার চরিত্র। জেবউন্নিসা ইতিহাস-প্রথিতা রমণী; তাঁহার বুদ্ধিমত্তার কথা, তাঁহার গুণগ্রাহিতার কথা অনেক ঐতিহাসিকই স্বীকার করিয়া থাকেন। কিন্তু উপন্যাসে জেবউন্নিসার এরূপ বীভৎস চরিত্র অঙ্কিত করিয়া তিনি যে উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে চাহিয়াছেন, তাঁহার রচনা-কৌশলে সে উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয় নাই জেবউন্নিসার এরূপ ঘৃণিত চরিত্রের পাশে রাজপুত রমণীগণের উন্নত চরিত্র অঙ্কিত করিয়া তিনি তাঁহাদের চরিত্রকে আরো মহনীয় করিয়া ফুটাইয়া তুলিতে পারিয়াছেন।
(প্রবাসী—পৌষ, ১৩২৫)
সাম্যবাদী বঙ্কিমচন্দ্র
[ডাঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, এম-এ, বি-এল, ডি-লিট্]
বহু যুগ ধরিয়া যুক্তিতর্কহীন ধর্ম্মের শুষ্ক নীরস গতানুগতিক অনুষ্ঠানে বাঙ্গালীর মন একেবারে মরিয়া গিয়াছিল। এমন সময় আসিল পশ্চিমের অপূর্ব্ব যুক্তিবাদী ভাবধারা। মরা গাঙ্গে বাণ ডাকিল। নূতনত্বের দুকুলপ্লাবী উচ্ছ্বাসে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, মধুসূদন দত্ত প্রভৃতির ন্যায় কেহ কেহ একেবারে গা ঢালিয়া ভাসিয়া গেলেন। যাঁহারা স্থির রহিলেন তাঁহারা বন্যার পলি মাটিতে উর্ব্বর ক্ষেত্রের ন্যায় নব ভাবরাশিতে সমৃদ্ধ হইলেন। বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন এই শেষোক্ত দলের একজন। আজ বাঙ্গালী ‘ধুকড়ী’ মন্ত্র, শিখিয়াছে। বাঙ্গালী পূর্ব্বাপেক্ষা বেশী করিয়া পাশ্চাত্ত্য দর্শন-বিজ্ঞান-সাহিত্যের আলোচনা করিতেছে, ইউরোপ আমেরিকা ঘুরিয়া আসিতেছে। কিন্তু নূতন ভাবে উদ্দাম উন্মাদ হইয়া তেমন আর মাতিয়া উঠিতেছে না। তাহার নূতনত্বের নেশা একরূপ কাটিয়া গিয়াছে।
রুশো, মিল, কঁৎ, বেন্থামের শিক্ষা বঙ্কিমের উপর ব্যর্থ হয় নাই। ভাটপাড়ার গোঁড়া ব্রাহ্মণ-পরিবেষ্টনীর মধ্যে জাত, লালিত-পালিত বঙ্কিম বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের মধ্যে থাকিয়াও মতে সাম্যবাদী হইয়া উঠিয়াছিলেন। কম্যুনিজম, ইণ্টারন্যাশন্যালিজমের তত্ত্ব তিনি জানিতেন। এই সকল শব্দ তাঁহার প্রবন্ধে ব্যবহৃত হইয়াছে। তিনি ‘বঙ্গদর্শনে’ ‘সাম্য’ নামে প্রবন্ধ ধারাবাহিকরূপে প্রকাশ করিয়াছিলেন। রুশো ছিলেন তাঁহার সাম্যবাদের প্রধান গুরু। তাঁহার Le Contract Social বঙ্কিমের গুরুমন্ত্র ছিল। তিনি তিন মহাপুরুষকে পৃথিবীর সাম্য-অবতার বলিয়াছেন, (১) বুদ্ধদেব, (২) যীশুখৃষ্ট, (৩) রুশো। দুঃখের বিষয়, যে মহাপুরুষ আরবের মরু-কান্তার ধ্বনিত করিয়া জলদ-গম্ভীর রবে ঘোষণা করিয়াছিলেন, ‘আন্নাসু সওআসিয়াহ’—সকল মানুষ সমান,—’আল ইন্সানু আখু-ল্ ইন্সানি হাব্বা আম্ কারিহা’—ভালবাসুক বা ঘৃণা করুক, সকল অবস্থাতে মানুষ মানুষের ভাই,—’লা য়ুমিনু আহাদুকুম্ হাত্তা য়ুহি’ব্বুলি আসিহি মা য়ুহি’ব্বুলি নাফসিহি’—যে পর্য্যন্ত কেহ ভাইয়ের জন্য তাহা না ভালবাসিবে, যাহা সে নিজের জন্য ভালবাসে, সে পর্য্যন্ত সে ধর্ম্মবিশ্বাসী (মুমিন) হইবে না—তাঁহার উদার উদাত্ত বাণী বঙ্কিমের কানে পৌঁছে নাই।
বলিয়াছি, রুশো বঙ্কিমের সাম্যবাদের অন্যতম গুরু ছিলেন। কিন্তু অন্ধ গুরুভক্তি তাঁহার কখনই ছিল না। তিনি তাঁহার মত সম্বন্ধে বলিয়াছেন, “অবিমিশ্র বিমল সত্যই যে তাঁহা কর্তৃক ভূমণ্ডলে প্রচারিত হইয়াছিল, এমত নহে। তিনি মহিমময় লোকহিতকর নৈতিক সত্যের সহিত অনিষ্টকারক মিথ্যা মিশাইয়া সেই মিশ্র পদার্থকে আপনার অদ্ভুত বাগিন্দ্রজালের গুণে লোক-বিমোহিনী শক্তি দিয়া ফরাসীদিগের হৃদয়াধিকারে প্রেরণ করিয়াছিলেন।”
সাম্যতত্ত্বে তিনি কি বুঝিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার কথাতেই বলি—”মনুষ্যে মনুষ্যে সমান। কিন্তু এ কথার এমত উদ্দেশ্য নহে যে, সকল অবস্থার সকল মনুষ্যই সকল অবস্থায় সকল মনুষ্যের সঙ্গে সমান। নৈসর্গিক তারতম্য আছে। কেহ দুর্ব্বল, কেহ বলিষ্ঠ, কেহ বুদ্ধিমান, কেহ বুদ্ধিহীন। নৈসর্গিক তারতম্যে সামাজিক তারতম্য অবশ্য ঘটিয়াছে। যে বুদ্ধিমান এবং বলিষ্ঠ, সে আজ্ঞাদাতা, যে বুদ্ধিহীন এবং দুর্ব্বল, সে আজ্ঞাকারী অবশ্য হইবে। রুশোও এ কথা স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু সাম্যতত্ত্বের তাৎপর্য্য এই যে, সামাজিক বৈষম্য নৈসর্গিক বৈষম্যের ফল, তাহার অতিরিক্ত বৈষম্য ন্যায়বিরুদ্ধ এবং মনুষ্য জাতির অনিষ্টকর। যে সকল রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থা প্রচলিত আছে, তাহার অনেকগুলি এইরূপ অপ্রাকৃত বৈষম্যের কারণ। সেই ব্যবস্থা-গুলির সংশোধন না হইলে মনুষ্যজাতির প্রকৃত উন্নতি নাই। মিল একস্থানে বলিয়াছেন, এখনকার যত সুব্যবস্থা, তাহা পূর্ব্বতন কু-ব্যবস্থার সংশোধন মাত্র। ইহা সত্য কথা; কিন্তু সম্পূর্ণ সংশোধন কালসাপেক্ষ। তাই বলিয়া কেহ মনে না করেন যে, আমি জন্মগুণে বড় লোক হইয়াছি, অন্যে জন্মগুণে ছোট লোক হইয়াছে। তুমি যে উচ্চকুলে জন্মিয়াছ, সে তোমার কোন গুণ নহে; যে নীচকুলে জন্মিয়াছে, সে তাহার দোষ নহে। অতএব পৃথিবীর সুখে তোমার যে অধিকার, নীচ কুলোৎপন্নেরও সেই অধিকার। তাহার সুখের বিঘ্নকারী হইও না। মনে থাকে যেন যে, সেও তোমার ভাই, তোমার সমকক্ষ। যিনি ন্যায়বিরুদ্ধ আইনের দোষে পিতৃ-সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন বলিয়া, দুর্দ্দণ্ড, প্রচণ্ড প্রতাপান্বিত মহারাজাধিরাজ প্রভৃতি উপাধি ধারণ করেন, তাঁহারও যেন স্মরণ থাকে যে, বঙ্গদেশের কৃষক পরাণ মণ্ডল তাঁহার সমকক্ষ এবং তাঁহার ভ্রাতা। জন্ম দোষ-গুণের অধীন নহে। তাহার অন্য কোন দোষ নাই। যে সম্পত্তি তিনি একা ভোগ করিতেছেন, পরাণ মণ্ডলও তাহার ন্যায়সঙ্গত অধিকারী।”
Proletariat এবং Intelligentziaর ব্যাপারে বঙ্কিমচন্দ্র কিন্তু সাম্যবাদের ধুয়া ধরিয়া নির্ঘাত একাকার পছন্দ করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন,—“যখন জনসমাজে ধন-সঞ্চয় হইল, তখন কাজে-কাজেই সমাজ দ্বিভাগে বিভক্ত হইল। একভাগ শ্রম করে, একভাগ শ্রম করে না। এই দ্বিতীয় ভাগের শ্রম করিবার আবশ্যকতা নাই বলিয়া তাহারা করে না। প্রথম ভাগের উৎপাদিত অতিরিক্ত খাদ্যে তাহাদের ভরণপোষণ হয়। যাহারা শ্রম করে না, তাহারাই কেবল সাবকাশ, সুতরাং চিন্তা, শিক্ষা ইত্যাদি তাহাদেরই একাধিকার। যে চিন্তা করে, শিক্ষা পায় অর্থাৎ যাহার বুদ্ধি মার্জ্জিত হয়, সে অন্যাপেক্ষা যোগ্য ও ক্ষমতাশালী হয়, সুতরাং সমাজ মধ্যে ইহাদের প্রধানত্ব হয়। যাহারা শ্রমোপজীবী, তাহারা ইহাদের বশবর্ত্তী হইয়া শ্রম করে। অতএব প্রথমেই বৈষম্য উপস্থিত হইল। কিন্তু এ বৈষম্য প্রাকৃতিক, ইহার উচ্ছেদ সম্ভাবনা এবং উচ্ছেদ মঙ্গলকর নহে। বুদ্ধ্যুপজীবীর জ্ঞান ও বুদ্ধির দ্বারা শ্রমোপজীবীরা উপকৃত হয়, পুরস্কার স্বরূপ উহারা শ্রমোপজীবী অর্জ্জিত ধনের অংশ গ্রহণ করে।”
বঙ্কিম বলেন,—লোক-সংখ্যার বৃদ্ধি এবং তৎসহ বিবাহ-প্রবৃত্তি দমনে ও উপনিবেশ স্থাপনে অপ্রবৃত্তির কারণে আমাদের দেশের শ্রমোপজীবীর অবনতি আরম্ভ হয়। এই অবনতির ফলে ক্রমশঃ শ্রমোপজীবী ও বুদ্ধ্যুপজীবীর মধ্যে যে বৈষম্য সৃষ্টি হয়, তাহা অমঙ্গলজনক। তাঁহার ভাষা উদ্ধৃত করি,—“একবার অবনতি আরম্ভ হইলেই সেই অবনতিরই ফলে আরও অবনতি ঘটে। শ্রমোপজীবীদিগের যে পরিমাণে দুরবস্থা বৃদ্ধি হইতে লাগিল, সেই পরিমাণে তাহাদিগের সহিত সমাজের অন্যান্য সম্প্রদায়ের তারতম্য অধিকতর হইতে লাগিল। প্রথমে ধনের তারতম্য—তৎপরে অধিকারের তারতম্য। শ্রমোপজীবীরা হীন হইল বলিয়া তাহাদের উপর বুদ্ধ্যুপজীবীদিগের প্রভুত্ব বাড়িতে লাগিল। অধিক প্রভুত্বের ফল অধিক অত্যাচার। এই প্রভুত্বই শূদ্রপীড়ক স্মৃতি-শাস্ত্রের মূল। এই বৈষম্যই অস্বাভাবিক, ইহাই অমঙ্গলের কারণ।
“আমরা যে সকল কথা বলিলাম, তাহার তিনটি গুরুতর তাৎপর্য্য দেখা যায়—(১) শ্রমোপজীবীদিগের অবনতির যে সকল কারণ দেখাইলাম, তাহার ফল ত্রিবিধ। প্রথম ফল,—শ্রমের বেতনের অল্পতা। ইহার নামান্তর দরিদ্রতা, ইহা বৈষম্যবর্দ্ধক। দ্বিতীয় ফল,—বেতনের অল্পতা হইলেই পরিশ্রেমের আধিক্যের আবশ্যক হয়, কেননা যাহা কমিল, তাহা খাটিয়া পোষাইয়া লইতে হইবে। তাহাতে অবকাশের ধ্বংস। অবকাশের অভাবে বিদ্যালোচনার অভাব। অতএব, দ্বিতীয় ফল মূর্খতা, ইহাও বৈষম্যবর্দ্ধক। তৃতীয় ফল,—বুদ্ধ্যুপজীবীদিগের প্রভুত্ব এবং অত্যাচার বৃদ্ধি। ইহার নামান্তর দাসত্ব। ইহা বৈষম্যের পরাকাষ্ঠা। দারিদ্র্য, মূর্খতা, দাসত্ব। (২) ঐ সকল ফল একবার উৎপন্ন হইলে ভারতবর্ষের ন্যায় দেশে প্রাকৃতিক নিয়মগুণে স্থায়িত্ব লাভ করিতে উন্মুখ হয়। (৩) শ্রমোপজীবীদিগের দুরবস্থা যে চিরস্থায়ী হয় কেবল তাহাই নহে। তন্নিবন্ধন সমাজের অন্য সম্প্রদায়ের লোকের গৌরবের ধ্বংস হয়। যেমন একভাণ্ড দুগ্ধে দুই এক বিন্দু অম্ল পড়িলে সকল দুগ্ধ দধি হয়, তেমনই সমাজের এক অধঃশ্রেণীর দুর্দ্দশায় সকল শ্রেণীরই দুর্দ্দশা জন্মে।”
বঙ্কিমচন্দ্র উপরিউদ্ধৃত মতের উদাহরণ স্বরূপ হিন্দু সমাজের অবনতির ইতিহাস বক্ষ্যমাণরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে উপজীবিকা অনুসারে প্রাচীন আর্য্যেরা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চারি শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছিলেন—শ্রমোপজীবী শূদ্র, বাণিজ্যোপজীবী বৈশ্য, রাজপুরুষ বা রাজা ক্ষত্রিয়, শাস্ত্রোপজীবী ব্রাহ্মণ। এই শেষোক্ত তিন শ্রেণী বুদ্ধ্যুপজীবী। শ্রমোপজীবীর অবনতিতে এক দিকে যেমন শ্রমোৎপন্ন দ্রব্যের অপ্রাচুর্য্য ঘটে, অন্য দিকে তেমনি তাহারা নিজেদের শ্রমোৎপন্ন সামান্য সামগ্রীতে সুলভ সন্তোষ অবলম্বন করে। ফলে, বাণিজ্যব্যবসায়ী বৈশ্যের পতন। যেখানে শ্রমোপজীবী ও বাণিজ্যোপজীবী প্রজাশক্তি দুঃখী, অন্ন-বস্ত্রের কাঙ্গাল, আহারোপার্জ্জনে ব্যগ্র এবং সন্তুষ্টস্বভাব, সেখানেই তাহারা নিস্তেজ, নম্র, অনুৎসাহী ও অবিরোধী। পরিণামে রাজপুরুষেরা স্বেচ্ছাচারী হইয়া উঠে। স্বেচ্ছাচারী হইলেই আত্মসুখরত, কার্য্যে শিথিল ও দুষ্ক্রিয়ান্বিত হইতে হয়। ফলে ক্ষত্রিয়ের অবনতি। শূদ্রের দাসত্বে ক্ষত্রিয়ের ধন এবং ধর্ম্মের লোপ হইয়াছিল। এই তিন বর্ণের অধঃগতির ফলে ব্রাহ্মণের কি অবস্থা হইয়াছে, তাহা ব্রাহ্মণ বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষাতেই বলিব—”অপর তিন বর্ণের অনুন্নতিতে বর্ণগত ঘোরতর বৈষম্যে ব্রাহ্মণের প্রথমে প্রভুত্ব বৃদ্ধি হয়। অপর বর্ণের মানসিক শক্তির হানি হওয়াতে তাহাদিগের চিত্ত উপধর্ম্মের বিশেষ বশীভূত হইতে লাগিল। দৌর্ব্বল্য থাকিলেই ভয়াধিক্য হয়। উপধর্ম্ম ভীতিজাত; এই সংসার বলশীলা অথচ অনিষ্টকারক দেবতাপূর্ণ, এই বিশ্বাস উপধর্ম্ম। অতএব অপর বর্ণত্রয় মানসিক শক্তিবিহীন হওয়াতে অধিকতর উপধর্ম্মপীড়িত হইল; ব্রাহ্মণেরা উপধর্ম্মের যাজক, সুতরাং তাহাদের প্রভুত্ব বৃদ্ধি হইল। ব্রাহ্মণেরা কেবল শাস্ত্রজাত ব্যবস্থাজাল বিস্তার করিয়া ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রকে জড়িত করিতে লাগিলেন। মক্ষিকাগণ জড়াইয়া পড়িল, নড়িবার শক্তি নাই। কিন্তু তথাপি ঊর্ণনাভের জাল ফুরায় না। বিধানের অন্ত নাই। এদিকে রাজ-শাসন প্রণালী দণ্ডবিধি দায় সন্ধিবিগ্রহ প্রভৃতি হইতে আচমন, শয়ন, বসন, গমন, কথোপকথন, হাস্য, রোদন—এই সকল পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণের রচিত বিধির দ্বারা নিয়মিত হইতে লাগিল। আমরা যেরূপ বলি সেইরূপে শুইবে, সেইরূপে খাইবে, সেইরূপে বসিবে, সেইরূপে হাঁটিবে, সেইরূপে কথা কহিবে, সেইরূপে হাসিবে, সেইরূপে কাঁদিবে, তোমার জন্ম-মৃত্যু পর্য্যন্ত আমাদের ব্যবস্থার বিপরীত হইতে পারিবে না। যদি হয়, তবে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া আমাদিগকে দক্ষিণা দিও। জালের এইরূপ সূত্র। কিন্তু পরকে ভ্রান্ত করিতে গেলে আপনিও ভ্রান্ত হইতে হয়, কেননা ভ্রান্তির আলোচনায় ভ্রান্তি অভ্যস্ত হয়। যাহা পরকে বিশ্বাস করাইতে চাহি, তাহাতে নিজের বিশ্বাস দেখাইতে হয়। বিশ্বাস দেখাইতে দেখাইতে যথার্থ বিশ্বাস ঘটিয়া উঠে। যে জালে ব্রাহ্মণেরা ভারতবর্ষকে জড়াইলেন, তাহাতে আপনারাও জড়িত হইলেন।”
আজ হরিজন-আন্দোলনের দিন বঙ্কিমের এই সামাজিক দুর্গতির নিদান বিশেষ মনোযোগের সহিত আমাদের অনুধাবন করা কর্ত্তব্য।
জমিদার ও রায়তের বৈষম্য বঙ্কিমের প্রাণে বড় লাগিয়াছিল। তাই তিনি দুঃখে বলিয়াছিলেন—”জীবের শত্রু জীব, মনুষ্যের শত্ৰু মনুষ্য, বাঙ্গালা কৃষকের শত্ৰু বাঙ্গালী ভূস্বামী। ব্যাঘ্রাদি বৃহৎ জন্তু ছাগাদি ক্ষুদ্র জন্তুদিগকে ভক্ষণ করে। রোহিতাদি বৃহৎ মৎস্য শফরীদিগকে ভক্ষণ করে। জমিদার নামক বড় মানুষ কৃষক নামক ছোট মানুষকে ভক্ষণ করে। জমিদার প্রকৃতপক্ষে কৃষকদিগকে ধরিয়া উদরস্থ করেন না বটে, কিন্তু যাহা করেন, তাহা অপেক্ষা হৃদয়-শোণিত পান করা দয়ার কাজ। কৃষকদিগের অন্যান্য বিষয়ে যেমন দুর্দ্দশা হউক না কেন, এই সর্ব্বরত্ন-প্রসবিনী-বসুমতী কর্ষণ করিয়া তাহাদিগের জীবনোপায় যে না হইতে পারিত, এমত নহে। কিন্তু তাহা হয় না। কৃষকের পেটে যাইলে জমিদারও টাকার রাশির উপর টাকার রাশি ঢালিতে পারেন না। সুতরাং তিনি কৃষককে পেটে খাইতে দেন না।”
রায়তের দুর্দ্দশা দেখাইবার জন্য তিনি যে পরাণ মণ্ডলের করুণ চিত্রটি আঁকিয়াছেন, তাহা একবার সকলকে দেখিতে অনুরোধ করি। দীর্ঘতার ভয়ে আমরা এখানে তাহা উদ্ধৃত করিতে অক্ষম। আজ কৃষক আন্দোলনের দিনে ইহা বারংবার পাঠ করার প্রয়োজন আছে।
তিনি বুঝিয়াছিলেন, এই কৃষকের উন্নতি না হইলে দেশের উন্নতি হইবে না। তাই তিনি বলিয়াছেন—“আমাদের দেশের বড় শ্ৰীবৃদ্ধি হইতেছে। এতকাল আমাদিগের দেশ উৎসন্ন যাইতেছিল, এক্ষণে ইংরেজের শাসন-কৌশলে আমরা সভ্য হইতেছি। আমাদের দেশের বড় মঙ্গল হইতেছে। …“এই মঙ্গল ছড়াছড়ির মধ্যে আমার একটা কথা জিজ্ঞাসার আছে, কাহার এত মঙ্গল? হাসিম সেখ আর রামা কৈবর্ত্ত দুই প্রহরের রৌদ্রে খালি পায়ে এক হাঁটু কাদার উপর দিয়া দুইটি অস্থি চৰ্ম্ম বিশিষ্ট বলদের ভোঁতা হাল ধার করিয়া আনিয়া চষিতেছে, উহাদের মঙ্গল হইয়াছে? উহাদের এই ভাদ্রের রৌদ্রে মাথা ফাটিয়া যাইতেছে, তৃষ্ণায় ছাতি ফাটিয়া যাইতেছে, তাহার নিবারণ জন্য অঞ্জলি করিয়া মাঠের কর্দ্দম পান করিতেছে, ক্ষুধায় প্রাণ যাইতেছে, কিন্তু এখন বাড়ী গিয়া আহার করা হইবে না, এই চাষের সময়, সন্ধ্যাবেলা গিয়া তাহারা ভাঙ্গা পাথরে রাঙ্গা রাঙ্গা বড় বড় ভাত লুণ-লঙ্কা দিয়া আধপেটা খাইবে। তাহার পর ছেঁড়া মাদুরে, না হয় গোহালের ভূমে এক পাশে শয়ন করিবে—উহাদের মশা লাগে না। তাহার পরদিন প্রাতে আবার সেই এক হাঁটু কাদার কাজ করিতে যাইবে—যাইবার সময়, কোন জমিদার, নয় মহাজন, পথ হইতে ধরিয়া লইয়া গিয়া দেনার জন্য বসাইয়া রাখিবে। কাজ হইবে না। নয় চষিবার সময় জমিদার জমিখানি কাড়িয়া লইবেন, তাহা হইলে সে বৎসর কি করিবে? উপবাস—সপরিবারে উপবাস। বল দেখি চশ্মা নাকে বাবু! ইহাদের কি মঙ্গল হইয়াছে? তুমি লেখাপড়া শিখিয়া ইহাদের কি মঙ্গল সাধিয়াছ? আর তুমি, ইংরেজ বাহাদুর—তুমি যে মেজের উপরে এক হাতে হংসপক্ষ ধরিয়া বিধির সৃষ্টি ফিরাইবার কল্পনা করিতেছ, আর অপর হস্তে ভ্রমরকৃষ্ণ শ্মশ্রুগুচ্ছ কণ্ডূয়িত করিতেছ—তুমি বল দেখি যে, তোমা হইতে এই হাসিম সেখ আর রামা কৈবর্ত্তর কি উপকার হইয়াছে? …“আমি বলি অণুমাত্র না, কণামাত্র না। তাহা যদি না হইল, তবে আমি তোমাদের সঙ্গে মঙ্গলের ঘটায় হুলুধ্বনি দিব না। দেশের মঙ্গল? তোমার আমার মঙ্গল দেখিতেছি, কিন্তু আমি কি দেশ? তুমি আমি দেশের কয়জন? আর এই কৃষিজীবী কয়জন? তাহাদের ত্যাগ করিলে দেশে কয়জন থাকে? হিসাব করিলে তাহারাই দেশ—দেশের অধিকাংশ লোকই কৃষিজীবী। তোমা হইতে আমা হইতে কোন কার্য্য হইতে পারে? কিন্তু সকল কৃষিজীবী ক্ষেপিলে কে কোথায় থাকিবে? কি না হইবে? যেখানে তাদের মঙ্গল নাই, সেখানে দেশের কোন মঙ্গল নাই।”
আপনারা দেখিলেন, পরাণ মণ্ডল বা রামা কৈবর্ত্তের জন্য বঙ্কিমের যতটুকু দরদ, হাসিম সেখের জন্যও ততটুকু। এখানে কোন হিন্দু-মুসলমান ভেদ নাই। এই হিন্দু মুসলমান সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র একস্থানে বলিয়াছেন—”আমি। মুসলমানের বাড়ী খাইতে আছে? বাবাজী। এ কান দিয়া শুনিয়া, ও কান দিয়া ভুলিস্? যখন সর্ব্বত্র সমান জ্ঞান, সকলকে আত্মবৎ জ্ঞানই বৈষ্ণব-ধর্ম্ম, তখন এ হিন্দু ও মুসলমান, এ ছোট জাতি ও বড় জাতি এইরূপ ভেদ জ্ঞান করিতে নাই। যে এরূপ ভেদ জ্ঞান করে, সে বৈষ্ণব নহে।” তিনি অন্য স্থানে বলিয়াছেন,—“’গড’ বলি, ‘আল্লা’ বলি, ‘ব্রহ্ম’ বলি, সেই এক জগন্নাথ বিষ্ণুকেই ডাকি। সর্ব্ব-ভূতের অন্তরাত্মা স্বরূপ জ্ঞান ও আনন্দময় চৈতন্যকে যে জানিয়াছে, সর্ব্বভূতে যাহার আত্মজ্ঞান আছে, যে অভেদী, অথবা সেইরূপ জ্ঞান ও চিত্তের অবস্থা প্রাপ্তিতে যাহার যত্ন আছে, সেই বৈষ্ণব ও সেই হিন্দু। তদ্ভিন্ন যে কেবল লোকের দ্বেষ করে, লোকের অনিষ্ট করে, পরের সঙ্গে বিবাদ করে, লোকের কেবল জাতি মারিতেই ব্যস্ত, তাহার গলায় গোচ্ছা করা পৈতা, কপালে কপালজোড়া ফোঁটা, মাথায় টিকি এবং গায়ে নামাবলি, মুখে হরিনাম থাকিলেও তাহাকে হিন্দু বলিব না।”
যে দিন হিন্দু বঙ্কিমের এই বৈষ্ণব মত গ্রহণ করিবে, সে দিন হিন্দু-মুসলমান সমস্যা থাকিবে না। হরিজন সমস্যাও থাকিবে না। সে শুভ দিন কবে আসিবে?
ধনী ও দরিদ্রের চিরন্তন সমস্যাটা বঙ্কিমচন্দ্র ‘কমলাকান্তের’ ‘বিড়াল’ প্রবন্ধে কেমন সুন্দররূপে বিবৃত করিয়াছেন। আমরা ‘কমলাকান্ত’ স্থানে ধনী ও ‘বিড়াল’ স্থানে দরিদ্র দিয়া তাঁহার কথা উদ্ধৃত করিব।
দরিদ্র। “দেখ, আমি চোর বটে, কিন্তু আমি কি সাধ করিয়া চোর হইয়াছি? খাইতে পাইলে কে চোর হয়? দেখ, যাঁহারা বড় বড় সাধু, চোরের নামে শিহরিয়া উঠেন, তাঁহারা অনেকে চোর অপেক্ষা অধার্ম্মিক। তাঁহাদের চুরি করিবার প্রয়োজন নাই বলিয়াই চুরি করেন না। কিন্তু তাঁহাদের প্রয়োজনাতীত ধন থাকিতেও চোরের প্রতি যে মুখ তুলিয়া চাহেন না, ইহাতেই চোরে চুরি করে। অধর্ম্ম চোরের নহে, চোরে যে চুরি করে, সে অধর্ম্ম কৃপণ ধনীর। চোর দোষী বটে, কিন্তু কৃপণ ধনী তদপেক্ষা শতগুণে দোষী। চোরের দণ্ড হয়, চুরির মূলে যে কৃপণ, তাহার দণ্ড হয় না কেন? পাঁচ শত দরিদ্রকে বঞ্চিত করিয়া একজনে পাঁচ শত লোকের আহার্য্য সংগ্রহ করিবে কেন? যদি করিল, তবে সে তাহার খাইয়া যাহা বাহিয়া পড়ে, তাহা দরিদ্রকে দিবে না কেন? যদি না দেয়, তবে দরিদ্র অবশ্য তাদের নিকট হইতে চুরি করিবে; কেননা, অনাহারে মরিয়া যাইবার জন্য এ পৃথিবীতে কেহ আইসে নাই।”
ধনী। “থাম! থাম! তােমার কথাগুলি ভারি সোশিয়ালিষ্টিক্! সমাজ-বিশৃঙ্খলার মূল। যদি যাহার যত ক্ষমতা, সে তত ধনসঞ্চয় করিতে না পায়, অথবা সঞ্চয় করিয়া চোরের জ্বালায় নির্ব্বিঘ্নে ভোগ করিতে না পায়, তবে কেহ আর ধন-সঞ্চয়ে যত্ন করিবে না। তাহাতে সমাজে ধনবৃদ্ধি হইবে না।”
দরিদ্র। “না হইল ত আমার কি? সমাজের ধনবৃদ্ধি অর্থে ধনীর ধনবৃদ্ধি। ধনীর ধনবৃদ্ধি না হইলে দরিদ্রের ক্ষতি কি?”
ধনী। “সামাজিক ধনবৃদ্ধি ব্যতীত সমাজের উন্নতি নাই।”
দরিদ্র। “আমি যদি খাইতে না পাইলাম, তবে সমাজের উন্নতি লইয়া কি করিব?”
সাম্যবাদী বঙ্কিমের চক্ষে স্ত্রীপুরুষের বৈষম্য এড়াইয়া যায় নাই। তিনি বলেন,—”স্ত্রীপুরুষে যে সকল বৈষম্য প্রায় সর্ব্বসমাজে প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকারী সম্বন্ধীয় বিধিগুলি অতি ভয়ানক ও শোচনীয়। পুত্র পৈতৃক সম্পত্তিতে সম্পূর্ণ অধিকারী, কন্যা কেহই নহে। উভয়েরই এক ঔরসে এক গর্ভে জন্ম; উভয়েরই প্রতি পিতা-পুত্র-কন্যা মাতার এক প্রকার যত্ন, এক প্রকার কর্ত্তব্য কর্ম্ম; কিন্তু পুত্র পিতৃ-মৃত্যুর পর পিতার কোটি মুদ্রা সুরাপানাদিতে ভস্মসাৎ করে, কন্যা বিশেষ প্রয়োজনের জন্যও তন্মধ্যে এক কপর্দ্দক পাইতে পারে না। এই নীতির যে কারণ হিন্দু শাস্ত্রে নির্দিষ্ট হইয়া থাকে যে, যেই শ্রাদ্ধাধিকারী সেই উত্তরাধিকারী; সেটি যেরূপ অসঙ্গত ও অযথার্থ যে তাহার অযৌক্তিকতা নির্ব্বাচন করাই নিষ্প্রয়োজন। দেখা যাউক এরূপ নিয়মের স্বভাব-সঙ্গত অন্য কোন মূল আছে কি না। ইহা কথিত হইতে পারে যে, স্ত্রী স্বামীর ধনে স্বামীর ন্যায় অধিকারিণী এবং তিনি স্বামিগৃহে গৃহিণী, স্বামীর ধনৈশ্বর্য্যের কর্ত্রী, অতএব তাঁহার আর পৈতৃক ধনে অধিকারিণী হইবার প্রয়োজন নাই। যদি ইহাই এই ব্যবস্থানীতির মূল স্বরূপ হয়, তাহা হইলে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, বিধবা কন্যা অধিকারিণী হয় না কেন? যে কন্যা দরিদ্রে সমর্পিত হইয়াছে, সে উত্তরাধিকারিণী হয় না কেন? কিন্তু আমরা এ সকল ক্ষুদ্রতর আপত্তি উপস্থিত করিতে ইচ্ছুক নহি। স্ত্রীকে স্বামী বা পুত্র এবম্বিধ কোন পুরুষের আশ্রিত হইয়াই ধনভাগিনী হইতে হইবে, ইহাতেই আমাদের আপত্তি। অন্যের ধনে নহিলে স্ত্রীজাতি ধনাধিকারিণী হইতে পারিবে না, পরের দাসী হইয়া ধনী হইবে,—নচেৎ ধনী হইবে না, ইহাতেই আপত্তি। পতির পদসেবা কর, পতি দুষ্ট হউক, কুভাষী, কদাচারী হউক, সকল সহ্য কর,—অবাধ্য, দুর্ম্মুখ, কৃতঘ্ন, পাপাত্মা পুত্রের বাধ্য হইয়া থাক,—নচেৎ ধনের সঙ্গে স্ত্রীজাতির কোন সম্বন্ধ নাই। পতি-পুত্র তাড়াইয়া দিল ত সব ঘুচিল। স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিবার উপায় নাই,—সহিষ্ণুতা ভিন্ন অন্য গতিও নাই। এদিকে পুরুষ সর্ব্বাধিকারী,—স্ত্রীর ধনও তাঁর ধন। ইচ্ছা করিলেই স্ত্রীকে সর্ব্বস্বচ্যুত করিতে পারেন। তাঁহার স্বাতন্ত্র্য অবলম্বনে কোন বাধা নাই। এ বৈষম্য গুরুতর, ন্যায়বিরুদ্ধ এবং নীতিবিরুদ্ধ।… “অনেকে বলিবেন, এ অতি উত্তম ব্যবস্থা, এ ব্যবস্থা-প্রভাবে স্ত্রী স্বামীর বশবর্ত্তিনী হইয়া থাকেন বটে, পুরুষকৃত ব্যবস্থাবলির উদ্দেশ্যই তাই; যত প্রকার বন্ধন আছে সকল প্রকার বন্ধনে স্ত্রীগণের হস্তপদ বাঁধিয়া পুরুষ-পদমূলে স্থাপিত কর,—পুরুষগণ স্বেচ্ছাক্রমে পদাঘাত করুক, অধম নারীগণ বাঙ্নিষ্পত্তি করিতে না পারে। জিজ্ঞাসা করি, স্ত্রীগণ পুরুষের বশবর্ত্তিনী হয় ইহা বড় বাঞ্ছনীয়; পুরুষগণ স্ত্রীজাতির বশবর্ত্তী হয় ইহা বাঞ্ছনীয় নহে কেন? যত বন্ধন আছে, সকল বন্ধনে স্ত্রীগণকে বাঁধিয়াছ, পুরুষ জাতির জন্য একটি বন্ধনও নাই কেন? স্ত্রীগণ কি পুরুষাপেক্ষা অধিকতর স্বভাবতঃ দুশ্চরিত্র? না, রজ্জুটি পুরুষের হাতে বলিয়া স্ত্রীজাতির এত দৃঢ় বন্ধন? ইহা যদি অধর্ম্ম না হয়, তবে অধর্ম্ম কাহাকে বলে বলিতে পারি না।”
স্ত্রী-পুরুষের প্রকৃতিগত বৈষম্যের জন্য যে তাহাদের অধিকারগত বৈষম্য হওয়া সম্পূর্ণ অনুচিত, ইহার সপক্ষে বঙ্কিমচন্দ্র যে কি সুন্দর যুক্তি দিয়াছেন—”মনুষ্যে মনুষ্যে সমান অধিকারবিশিষ্ট। স্ত্রীগণও মনুষ্য জাতি; অতএব স্ত্রীগণও পুরুষের তুল্য অধিকারশালিনী। যে যে কার্য্যে পুরুষের অধিকার আছে, স্ত্রীগণেরও সেই সেই কার্য্যে অধিকার থাকা ন্যায়সঙ্গত। কেন থাকিবে না? কেহ কেহ উত্তর করিত পারেন যে, স্ত্রী-পুরুষে প্রকৃতিগত বৈষম্য আছে, পুরুষ বলবান, স্ত্রী অবলা; পুরুষ সাহসী, স্ত্রী ভীরু; পুরুষ ক্লেশসহিষ্ণু, স্ত্রী কোমলা; ইত্যাদি ইত্যাদি। অতএব যেখানে স্বভাবগত বৈষম্য আছে, সেখানে অধিকারগত বৈষম্য থাকাও বিধেয়। কেননা যে যাহাতে অশক্ত, সে তাহাতে অধিকারী হইতে পারে না।… “ইহার দুইটি উত্তর সংক্ষেপে নির্দ্দেশ করিলে আপাততঃ যথেষ্ট হইবে। প্রথমতঃ, স্বভাবগত বৈষম্য থাকিলেই যে অধিকারগত বৈষম্য থাকা ন্যায়সঙ্গত, ইহা আমরা স্বীকার করি না। এ কথাটি সাম্য-তত্ত্বের মূলোচ্ছেদক। দেখ, স্ত্রী-পুরুষে যেরূপ স্বভাবগত বৈষম্য, ইংরেজ-বাঙ্গালীতেও সেইরূপ। ইংরেজ বলবান্, বাঙ্গালী দুর্ব্বল; ইংরেজ সাহসী, বাঙ্গালী ভীরু; ইংরেজ ক্লেশসহিষ্ণু, বাঙ্গালী কোমল; ইত্যাদি ইত্যাদি। যদি এই সকল প্রকৃতিগত বৈষম্য হেতু অধিকার-বৈষম্য ন্যায্য হইত, তবে আমরা ইংরেজ-বাঙ্গালী মধ্যে সামান্য অধিকার-বৈষম্য দেখিয়া চীৎকার করি কেন? যদি স্ত্রী দাসী, পুরুষ প্রভু, ইহাই বিচার-সঙ্গত হয়, তবে বাঙ্গালী দাস, ইংরেজ প্রভু, এটিও বিচার-সঙ্গত হইবে।… “দ্বিতীয় উত্তর এই, যে সকল বিষয়ে স্ত্রী-পুরুষে অধিকার-বৈষম্য দেখা যায়, সে সকল বিষয়ে স্ত্রী-পুরুষে যথার্থ প্রকৃতিগত বৈষম্য দেখা যায় না। যতটুকু দেখা যায়, ততটুকু কেবল সামাজিক নিয়মের দোষ। এই সকল সামাজিক নিয়ম সংশোধনই সাম্য নীতির উদ্দেশ্য। বিখ্যাতনামা জন স্টুয়ার্ট মিল-কৃত এতদ্বিষয়ক বিচারে এই বিষয়টি সুন্দররূপে প্রমাণীকৃত হইয়াছে। সে সকল কথা এখানে পুনরুক্ত করা নিষ্প্রয়োজন।”
বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার সৃষ্ট নারী-চরিত্রেও তাঁহার নিজের গড়া আদর্শ দেখাইয়াছেন। এ আদর্শ পৌরাণিক আদর্শ নহে। এ আদর্শ সাম্যবাদী বঙ্কিমের স্বরচিত আদর্শ। তাই আমরা দেখি, আদর্শ সতী ভ্রমর স্বামীকে লিখিতেছেন—”যত দিন তুমি ভক্তিযোগ্য, ততদিন আমারও ভক্তি; যত দিন তুমি বিশ্বাসী, ততদিন আমারও বিশ্বাস; এখন তোমার উপর ভক্তি নাই, বিশ্বাসও নাই। তোমার দর্শনে আমার আর সুখ নাই।” এই জন্যই ভ্রমর অন্য স্ত্রীতে আসক্ত স্বামীকে ত্যাগ করিয়া পিত্রালয়ে গিয়াছিলেন। এই জন্য পতিব্রতা সূর্য্যমুখী গৃহ হইতে পলায়ন করিয়াছিলেন। বঙ্কিমের আদর্শে ব্রজেশ্বরের দ্বারা দেবী চৌধুরাণীর পাদ-সংবাহন অন্যায় হয় নাই।
বঙ্কিমচন্দ্র আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন—”দেশে অনেক এসোসিয়েসন, লীগ, সোসাইটী, সভা, ক্লাব ইত্যাদি আছে; কাহারও উদ্দেশ্য ধর্ম্মনীতি, কাহারও উদ্দেশ্য দুর্নীতি; কিন্তু স্ত্রী-জাতির উন্নতির জন্য কেহ নাই। পশুগণকে কেহ প্রহার না করে, এজন্য একটি সভা আছে, কিন্তু বাঙ্গালার অর্দ্ধেক অধিবাসী স্ত্রী-জাতি, তাহাদিগের উপকারার্থ কেহ নাই।” আহা কি দরদের কথা!
বঙ্কিমচন্দ্র যে সাম্যবাদের বীজ বপন করিয়াছিলেন, তাহা এখন অঙ্কুরিত হইয়াছে। আশা করা যায় যে, অদূর ভবিষ্যতে সাম্যতরু নানা ফুলফলে সুশোভিত হইয়া বঙ্গভূমিকে না, না, সমগ্র ভারতবর্ষকে ফুল, ফল ও ছায়াদানে আমোদিত, পরিতৃপ্ত ও সুশীতল করিবে।
(ঢাকা শতবার্ষিকী সভাতে পঠিত)
আমরা সাহিত্য-সমাজের পনেরো আনা পাঠক। আমাদের পক্ষে পুরোনো বইটি পাওয়া খুবই দুঃসাধ্য। অধুনা যেসব পুরোনো বই পুনর্মুদ্রিত হচ্ছে তাও বিভ্রান্তিকর, বইটি লাইব্রেরিতে থাকলে বিধি মেনে তা হাতে পেলে হয়তো পুরোনো বই-এর দর্শন-সুখ হতে পারে কিন্তু এভাবে তার আত্তীকরণ নৈব নৈব চ। পুরোনো বইটির নতুনে রূপান্তরের গন্ধ আমাদের হয়তো সাময়িক আনন্দ দেয়। হারানোর পর প্রাপ্তিতেও সুখ হয়। কিন্তু প্রকৃত বিষয়ের জন্মান্তরে তার নিরুদ্দেশ যাত্রায় মন কেমন উদাস হয়ে যায়।