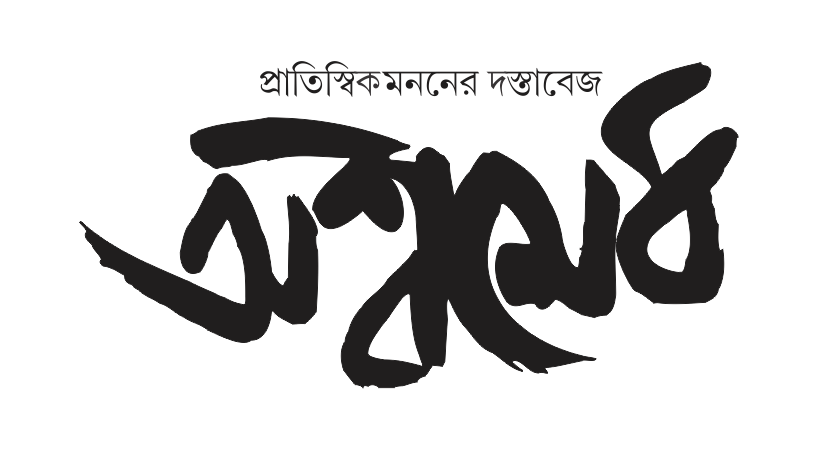আসল কথাটা হলো, নির্জনতা। উৎপলকুমার বসুর একটা কবিতা আছে, ‘লোচনদাস কারিগর’ বইতে:
সে দিন সুরেন ব্যানার্জি রোডে নির্জনতার সঙ্গে দেখা হল।
তাকে বললাম, এ চিঠি তো তোমারই ডাকে দেওয়া।
তুমি মনপড়া জানো না কি? এলে কোন্ ট্রেনে?
আসলে ও নির্জনতা নয়। ফুটপাথে কেনা এক শান্ত নতুন চিরুনি।
দাঁতে এক স্ত্রীলোকের দীর্ঘ কালো চুল লেগে আছে।
নিজের খুচরো অসুস্থতার সুবিধে আছে কিছু। নিজেকে আরও সহজ ও নিবিড় ভাবে চিনে নেওয়া যায়, জলজ শৈশবাবস্থায় আবিষ্কার করা যায়৷ আজ ছাদে রোদ্দুর পোয়াতে গেলাম। একটা টুলের ওপর বসতে হলো, শরীর খারাপ যেহেতু। আর—কী অপার বিস্ময়—আবিষ্কার করলাম টুলের দৈর্ঘ্য এতটাই নাদান যে পাঁচিলটা বড্ড দাদা-দাদা। রাস্তায় কী হচ্ছে, পাশের বাড়ির মহিলা কাপড় কাচছেন, এসব অন্তরঙ্গ জিনিসপত্র আর চোখেই পড়ছে না পাঁচিলের প্রহরায়। দেখছি কেবল আকাশটুকু৷ ঠিক ছোটবেলায় হত যেমন!
শেষ শীতের নীলচে আকাশ। অভাবিত এবং আকস্মিক যোগাযোগে—মাথায় ঘুরছিল মল্লারের সুর। বন্দিশ: ‘বোল রে পাপ্পৈয়ারা’। সামনে দেখছি শুধু ভাসমান সুনীল আকাশ। আর কিচ্ছু না। মাথার গভীরে: ‘বোল রে পাপ্পৈয়ারা।’ আস্তে আস্তে, কী আশ্চর্য, আমার চোখের সামনে থেকে কলকাতা অবসৃত হলো দ্রুত। জেগে রইল এই সুর। মুছে গেল একুশ শতক৷ এই তো দিব্যি দেখতে পাচ্ছি, একটা বিরাট চিল ডানা প্রসারিত করে আলস্যজড়িত হেঁটে যাচ্ছে মেঘ থেকে মেঘের দিকে৷ আমার মাথার মধ্যে ভেসে আসছে বোল রে পাপ্পৈয়ারা। বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই কোনো। মল্লার গাওয়ার উপযুক্ত সময়ও তো নয়। চিলটা ক্রমশ এগিয়ে আসছে উলটো বাড়ির দিকে৷ তার বৃহৎ ছায়া পড়েছে আকাশের গায়ে৷
আমার মাথায়, কেবল বোল রে পাপ্পৈয়ারা।
কলকাতা উবে গেছে, ততক্ষণে। আমি চলেছি এই গানের সুরতালছন্দ যে মাটির, সেই মধ্য- ভারতে। চিল বাহু প্রশস্ত করে এগিয়ে চলেছে বিজয়িনীর মতো৷ মহারাষ্ট্রের সতত-রুখা মাটি শুঁকতে শুঁকতে আর বোল রে পাপ্পৈয়ারা ভাবতে ভাবতে চিলটাকে জরিপ করছি, আর বিদ্যুতের মতো মনে হলো আমি আর কলকাতায় নেই। শরীরী ভাবেই নেই। এই তো চিলটা আঁচল পেতে বসবে, যমুনা কাছেই, দিল্লির ওপর দুপুরের ছায়া বুড়িয়ে এল, বাদশাহ্ বিশ্রাম নিচ্ছেন, ইমনে দরবার আরম্ভ হবে খানিক পর। কেবল, সন্ধ্যারতির আগে, রোশনাইয়ের আগে, আকাশের গায়ে উলকি এঁকে গেল এই আলস্যজড়িত চিল আর শেষ শীতের দুপুর।
বৃন্দাবনী সারংয়ের দুপুর। সাদারং আর আদারং। হোসেন শাহ্ রঙ্গিলার দরবারের দুই ভাই। ওই তো, আকাশ-উপত্যকায় স্পষ্ট দেখছিলাম তাঁদের। চিল ততক্ষণে স্কাইলাইন ছুঁয়ে ফেলেছে। আমায় সে দিয়ে গেল একখণ্ড দিল্লির দুপুর, যমুনার দুপুর, বৃন্দাবনী সারং আর মল্লারের দুপুর। একটা কাঁচা, নিঃসঙ্গ দুপুর।
২.
মালবিকা কানন ম্যাজিক জানেন। কথাটা অবশ্য প্রথম ভাবছি না। এর আগেও, ওঁর গলায় ছায়ানটে আগরা আর রামপুর-সাহসওয়ান ঘরানার বন্দিশ ‘ঝনন ঝনন বাজে বিছুয়া’ শুনেও একই কথা মনে হয়েছিল। কিঞ্চিৎ দ্রুত লয়ের গান থেকে মালবিকা কানন খুলে নেন যাবতীয় জড়োয়া, আর লয়কে করে দেন ঈষৎ ঢিমে। তাতেই ঘটে যায় অভাবিত সমস্ত ম্যাজিক। সিদ্ধ জাদুকর যেমন মিহি সন্তর্পণে তাঁর আস্তিনের রুমাল থেকে টেনে আনেন খরগোশ—মালবিকা কাননের গান শুনলেও, আমি নিশ্চিত, মনে হতে পারে: এ রকমই ছিল তবে বন্দিশের চেহারাটা? ছায়ানটের বহিরঙ্গের ভেতর তবে এতদিন ঘাপটি মেরে ছিল এমনই শান্ত ও সমাহিত সুন্দরতা, এমন নিস্পন্দ আবহ, এমন তুলোট কাগজের মতো ভেসে যাওয়া সুরের প্রাণায়াম? কী করে জানতাম রাগের এমন অপ্রত্যাশিত গড়ন—মালবিকা কানন কখনও না-চিনিয়ে দিলে?
একই ভাবে, গৌড় মলহার রাগটাও এসেছে আমার কাছে, নানা চেহারায়। গৌড় মলহারকে মনে হয় বৃষ্টি-ফুরিয়ে আসা স্নাত বিকেলের রাগ। আকাশে পায়চারি করছে ভাসমান মেঘখণ্ড, ইতস্তত। সদ্য বর্ষায় ফুটে ওঠা বাগানের ফুলটির মতোই, এই রাগ থেকে থেকে জানান দেয় মালবিকা কানন আর মীরা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গলার সজলতা। গতকাল গৌড় মলহার শুনছিলাম ওঁর আর মীরা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গলায়। কেন কে জানে, এঁদের গলায় গৌড় মলহার শুনলে মনে পড়ে যায় শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের ‘আনন্দভৈরবী’, দুয়ের ভেতর আপাত কোনো সংযোগ না-থাকা সত্ত্বেও।
অবশ্য, কেবল শক্তি একাই নন। গৌড় মলহারের সাকিন চিনে রাখেন জয় গোস্বামী-ও।
১৯৯৯। শতাব্দীর শেষ চৌকাঠে দাঁড়িয়ে আছে বাংলা কবিতা। যে-জয় দেড় দশক আগে লিখে ফেলেছেন ‘উন্মাদের পাঠক্রম’, তিনিই লিখবেন এখন ‘সূর্য-পোড়া ছাই’। শতকের শেষ সন্ধিসময়। যে সময় মহাজগৎ-জুড়ে পড়ে থাকে অজস্র পরিত্যক্ত খণ্ড হাড়, খণ্ড উরু। সমস্ত তারামণ্ডল ও গ্রহচরাচরব্যাপী ছেয়ে থাকে অমোঘ কোনো কুরক্ষেত্র।
এ-বইয়ের কবিতাগুলো আকারে ছোট, নামহীন, এবং সংখ্যাচিহ্নিত। গড়ে, খুব বেশি হলে, আট লাইন। তারই ফাঁকে, একটি কবিতায়, বিদ্যুচ্চমকের মতো, মিশে রয়েছে গৌড় মলহার। কাল মালবিকা কাননের ওই ঈশ্বরীসমান নিবেদন শুনতে শুনতে সেই কবিতার তবক খুলে গেল আমার সামনে, দৃষ্টি স্পষ্ট হয়ে এল। কবিতাটি এ-বইয়ের প্রতিনিধিত্বমূলক রচনা বলে মনে করি না। তবু, এ-কবিতায় কান রাখলেই কখনও শোনা যাবে গৌড় মলহারের বুকের কাঁপনটুকু:
পশ্চিমে বাঁশবন। তার ধারে ধারে জল।
বিকেল দাঁড়াল ধানক্ষেতে।
জলে ভাঙা ভাঙা মেঘ। ফিরে আসছে মাছমারা বালকের দল।
খালি গা, কোমরে গামছা, লম্বা ছিপ, ঝুড়ি—
আবছা কোলাহল।
তোমার কি ইচ্ছে করে, এখন ওদের সঙ্গে যেতে?
কয়েদি উত্তর দেয় না। সে শুধু বিকেলটুকু
এঁকে রাখছে ঘরের মেঝেতে!
৩.
কাল রাতে উস্তাদ আমীর খানের দ্বারস্থ হওয়া গেল। প্রায় মাসপাঁচেক পর। এমনিই চালিয়েছিলাম কয়েকটা রেকর্ড। শেষ পর্যন্ত যা দাঁড়াল, তাতে আমার ঘোর কাটেনি—আজ সকাল অবধিও। দ্বিধায় ছিলাম, লেখাটা কি উচিত হবে? মনের একটা দিক সায় দিচ্ছিল না, বলছিল, লিখে রাখলে স্মৃতিটা আর তোমার থাকবে না। ছাপা অক্ষরের বশংবদ হয়ে যাবে। আবার বলার ইচ্ছেটাও সুদূরপ্রসারী।
দুয়ের দোটানায় শেষ অবধি ঠিক করছিলাম, বলেই ফেলি।
আমীর খান শুনছি আমি পাঁচ বছর অন্তত। কোনোদিন এমন অভিজ্ঞতা হয়নি। হ্যাঁ—মেঘ রাগে অবিস্মরণীয় তারানা শুনে শরীর দুলে উঠেছে। ভীষণ জ্বরের ভেতর দরবারি কানাড়ায় দ্রুত তিনতালে ‘কিঁউ বরানে’ শুনে, কপালে আশ্বাস পেয়েছি জলপট্টির। ছিল আরও অনেক রাগ—যা একান্ত সময়ে সহায় হয়ে থেকেছে। কিন্তু সে তো মূর্ত, প্রকাশযোগ্য, শরীরী অভিব্যক্তি! সমস্ত ছন্দ আর দৃশ্যের ওপারে গান কেমন হয়, তা কাল পরখ করলাম, প্রায় পাঁচ বছর পেরিয়ে এসে।
প্রথমে যে রাগ চালিয়েছিলাম, তা হলো বেহাগ। ওঁর জীবনের শেষ কনসার্ট। গাইছেন মহাজাতি সদনে। পুরোদস্তুর অচেনা বেহাগ—রাগের যেসব কিসিম শুনে শুনে অভ্যস্ত আমরা, তার এতটুকু শো-অফ নেই। অলংকাররিক্ত। আভরণবিহীন। আক্ষরিক অর্থেই মিনিমালিজ্ম ছিল ওই বেহাগের গয়না। তখনও স্রোত টের পাইনি অবশ্য। এরপর জোয়ার এল। জল ক্রমে গাঢ় হয়ে উঠল। চলে গেলাম ওই অনুষ্ঠানের শেষ রাগ। সাল ১৯৭৪। কলকাতায় বসন্ত নামছে। ফুরিয়ে আসছে তাঁর জীবন। এই তো, আর কিছু দিন পরেই সাদার্ন অ্যাভিনিউয়ের ডিভাইডারের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়বেন তিনি। তার আগে, ফেব্রুয়ারির কোনো এক অকিঞ্চিৎকর সন্ধ্যা উদ্যাপন করছেন উস্তাদ আমীর খান, বসন্তবাহার গেয়ে। থেকে থেকে ঝাঁকিয়ে দিচ্ছেন রাগের চেনা কৌটোটা।
শেষ অবধি মন দখল করে ফেলল অবশ্য অন্য দুটো রাগ৷ ললিত, মারওয়া। এমনই তার ঘোর যে, এখনও তার থেকে সর্বাংশে বেরোতে পারিনি। এই লেখা তার অপটু স্মৃতিচারণ বলা যায়। গোটা রাতে যতবার ঘুম ভেঙেছে, মনে হয়েছে স্বপ্নের ভেতর আছি, জোর হাওয়ায় সৈকতে তাঁবু উড়ে গেল। ললিতে যখন গাইছেন, ‘যোগিয়া মেরে ঘর আয়ি’—সংগতে হারমোনিয়ামে থ্রিলিং, সম্ভবত, জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ। আমার কেবল মনে পড়ছে, ওই দৃশ্যটার কথা, মাস কয়েক আগে ইন্টারনেটে দেখেছিলাম। উত্তর-মেরু। সন্ধিসময়। সূর্য পালটে ফেলছেন তাঁর দিক। ভোর হচ্ছে এক প্রান্তে৷ মাঝে অথৈ সমুদ্র। উলটো পিঠে, নিয়তির মতো নেমে আসছে রাত্রি। একটা জাহাজ ভেসে চলে গেল দিগন্তে। ললিত গাইতে গিয়ে সকলেই ওই ভোরটাকে দেখিয়েছেন। অবধারিত। স্বাভাবিক। ভোরের রাগ যে। কিন্তু, তার পেছনে ফেলে-আসা রাত্রিটা? যা বসে রয়েছে গোটা চরাচর জুড়ে? ললিতের ভেতর যে এমন শীতল রাত্রিঘোর থাকে, জানতাম কি কখনও?
এরপর, ওই ললিতেই, শুরু হবে বিলম্বিত ‘কাঁহা জাগে রাত’। ঠিক এই মুহূর্তে যা ঘটতে শুরু করল, তা আমার কাছে অনির্বচনীয়। এই বন্দিশ তো আগেও শুনেছি ওঁর গলায়, এমন তোলপাড় করেনি তো? জাদুকর যেন একটা ছোট লাঠি দিয়ে ম্যাজিক করে দিলেন। সচকিতে কিছু এপিফ্যানি।
‘কাঁহা জাগে রাত’ শুনতে গিয়ে আমার মাথায় যে ইমেজটা ঘুরছিল, সেটা সন্ত্রাসের। হিন্দি ভাষা বিশেষ জানি না আমি। আমার কল্পনায়, ওই কথার অর্থ—রাত কখন ফুরোবে? আর কত রাত্রি জেগে থাকতে হবে ঠায়, এই ভাবে?
যেন একটা সর্বব্যাপ্ত অন্ধকারের ভেতর এক শিল্পী গেয়ে চলেছেন, রাত কখন শেষ হবে? শিশুতীর্থ বা এলিয়ট নয়, অমোঘ অনুষঙ্গে আমার মনে পড়ছিল গয়ার ওই ছবিটি—’দ্য পিলগ্রিমেজ অফ সান ইসিদ্রো’—শিশুদের মুখে মুখে অব্যক্ত ত্রাস। কখন রাত ফুরোবে? মনে পড়ছিল একটা ইমেজের কথা। প্রলম্বিত রাত্রি। সাদাকালোয় ভাসছে কোনো একটি মেয়ের মুখ। সে-ও তো ভবিষ্যতের জননী। অথচ, তার মুখে ত্রাস। ভয়। একটা পাহাড়ি ঢালের সামনে তার বসত। তাঁবুর ভেতরে থাকে৷ আর পাহাড়ের সর্বাঙ্গ জুড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে আগুন জ্বলছে৷ পুলিশ এল৷ অপারেশন। জিগ্যেস করছে, বাড়িতে ‘রেড বুক’ আছে? তন্নতন্ন করে খুঁজছে। মনে পড়ছিল আমার ওই আত্মীয়ার কথা, যাঁকে দেখিনি কখনও, যাঁর বাড়িতে পুলিশ এসেছিল, ছেলের ঘরে লেনিন আছে কিনা দেখতে৷ তিনি এই মানসিক চাপ সহ্য করতে পারেননি। স্তব্ধ হৃদয়ে মারা যান।—সকলের হয়ে, একটি নির্জন তানপুরা নিয়ে বলে চলেছেন আমীর খান, কাঁহা জাগে রাত? আমি কোনোদিন ভাবিও নি—সন্ত্রাসকে, টেররকে, উদ্বেগ বা অ্যাংজাইটিকে রাগসংগীতে প্রতিষ্ঠা করা যায় এভাবে। আবদুল করিম খান সাবলাইম৷ ফৈয়াজ খান স্পিরিচুয়াল৷ বড়ে গুলাম আলি খান নিপুণ। কিন্তু একটা আধা-সামন্তবাদী শিল্পমাধ্যমের গা থেকে জল ঝরিয়ে, তার গায়ে ঈষৎ ন্যাকড়া বুলিয়ে, এমন করে আধুনিকতার শিরশিরে ভয়কে স্থাপন করা যায় নাকি? সম্ভব?
এই এখন, লিখতে লিখতেই মনে হচ্ছে—আর কী কখনও এমন করে পাব আমীর খানকে? মন চাইছিল, ওঁর ঐতিহাসিক মারওয়া দিয়ে রাতটা শেষ হোক। ইউটিউবে দেখলাম, একজন আঠারো মিনিটের এলপি রেকর্ড টাঙিয়ে রেখেছেন। সঙ্গে সম্পূর্ণ বেমিল কিন্তু চমৎকার একটা ছবি—কোনো এক ব্রীড়াবনতা অবগুণ্ঠিতা, আনত মুখে প্রিয়তমের জন্য অপেক্ষা করছেন।—হরেন দাসের আঁকা কি? জানি না। দুটো গান, পিঠোপিঠি। ‘গুরু বিনা জ্ঞান নাহি পায়ে’ দ্রুত লয়ের বন্দিশ। তারও আগে, ‘পিয়া নাহি আয়ে’। বিলম্বিত। দুটোর ভেতরেই যন্ত্রণা—হাহাকার বোধ—আসছে না, কিছু একটা আসছে না। সেটা কী?
পরিত্যক্ত স্বপ্ন? সুদিন? ভবিষ্যৎ? সমস্ত গতর থেকে বেদনা চুঁইয়ে নামছে। ঠিক এখানটায় এমন কিছু ঘটে গেল, ভাষায় যাকে ব্যক্ত করতে আমি অপারগ। ওই ‘পিয়া নাহি আয়ে’-র আলাপে খেয়াল করছিলাম, উনি বারংবার ধৈবতের দিকে যাচ্ছেন। কোমল রেখাবকে, যা মারওয়ার শেষ সঞ্চয়—নির্মম ছুঁড়ে ফেলছেন, তার সিংহাসন থেকে। বাকিটা বিস্ময়। বুঝলাম, আর চোখ খুলে রাখার অর্থ হয় না। চোখের ভেতর অনন্ত মহাকাশ। এক ঝাঁক জ্যামিতিতে তারা ঘুরে বেড়াচ্ছে—কাটাকুটি খেলছে— অব্যক্ত একটা আলো আমার চোখে এসে পড়ছে। আমি যে স্মৃতিকে দেখতে পাইনি, আজ তাকে ভাষা দিয়ে বলার চেষ্টা করছি। ওঁর প্রতিটি বিস্তার স্পর্শ করছিল, ধ্যানের অনন্ত চরাচর, পৃথিবীর শেষ প্রান্তর ছাড়া আর কোনো রহস্য অবশিষ্ট নেই যেখানে।
গান ফুরোয়। কথাও। কেবল, চোখের ভেতর ওই যে উজ্জ্বল রশ্মি কাল এসে পড়েছে—আজ, পৌষের এই অবেলাতেও সে সরে যায়নি। একুশ শতকের ধর্ম মেনে, সে হয়তো সরে যাবে।
কেবল, আলোর দাগ পড়ে থাকবে। এই লেখায়।
৪.
আজ ২৫ জুন। এই তো, চার দিন আগেই, পেরিয়ে গেল ২১ জুন। বিশ্ব সংগীত দিবস। বছরে কুল্লে ৩৬৫টা দিন থাকা সত্ত্বেও, আচমকা এই দিনটির প্রতি সংগীতের কেন এমন বিশেষ মমতা? আসলে, ২১ জুন বছরের সবচেয়ে দীর্ঘ দিবস। সূর্য আর পৃথিবীর কী-এক উল্লম্ব লুকোচুরিতেই ঘটে যায় ম্যাজিক—দিন হয় দীর্ঘ, রাত হয়ে আসে সবচেয়ে ছোট।
এমন এক উজ্জ্বল ও রোদেলা দিনে রবীন্দ্রনাথের যে-গানটা আমার মনে পড়ল, তা অবশ্য নিতান্তই অসঙ্গত এবং অস্বাভাবিক। কলকাতায় এখন সবে পা রেখেছে আষাঢ়, দিনমানে আকাশের উপকণ্ঠে যত্রতত্র গজিয়ে উঠছে মেঘ, নিবে আসছে আলো। তারই সঙ্গে তাল মিলিয়ে কী, কে জানে, আমার মনে আসছিল, ‘ছায়া ঘনাইছে বনে বনে।‘ সুমিত্রা সেনের গলায়।
কী এক অব্যাখ্যাত জাদু রয়ে গেছে এই গানে, ভাবছিলাম, যার জন্য একবার এ-গান মনে পড়লে সারাদিন, সারারাত এর আমেজে না-ভেসে উপায় নেই। কী সেই রহস্য? ‘ছায়া ঘনাইছে’—এই বাক্যটির সরল, মেদুর অথচ তীব্র নাশকতাময় ইঙ্গিত? রবীন্দ্রনাথ, যিনি ভীষণ আলোময়, তাঁর কলমে অন্ধকারের এমন স্তব? না কি, সুরের সাঙ্ঘাতিক শারীরিকতা, যার জন্য মনে হয় এ-গান যেন রাত্রির নর্মসহচরী—যে এক বার শরীরে সেঁধিয়ে গেলে আর পালানো যাবে না?
গানটা শুনছিলাম। ধীরে ধীরে। ‘গগনে গগনে ডাকে দেয়া’—এখানটায় রবীন্দ্রনাথ একটা আশ্চর্য উড়াল দিয়েছেন, খেয়াল করছিলাম তা। কী রকম? এই যে ধরুন, গান আরম্ভ হলো ‘ছায়া ঘনাইছে’—এই বিষাদবিবৃতিতে, চোখ বুজলে পরিষ্কার টের পাবেন, আপনার চারপাশটা অন্ধকার, কুয়াশাময়। কারণ, ওই ‘ছায়া ঘনাইছে’ শব্দবন্ধে রবীন্দ্রনাথ মিশিয়ে রেখেছেন কোমল গান্ধারের নিহিত এক চাতুরি। অমোঘ এক ছায়া ঘনাচ্ছে কোমল গান্ধারে।
এখান থেকে মৃদু একটা ঝাঁপ মেরে যখন রবীন্দ্রনাথ উচ্চারণ করছেন ‘গগনে গগনে ডাকে দেয়া’—তখন ওই মুঠোর কোমল গান্ধারটুকু উধাও! সব স্বরই প্রায় শুদ্ধ, দিনের আলোর মতো পরিষ্কার।
কিন্তু, না। সুরের আড়াল কমে আসছিল ক্রমে, মুছে আসছিল অস্পষ্ট ধূসরতাটুকু—কিন্তু ফের যে-কে-সেই। ওই তো, ‘দেয়া’ শব্দের পর ফের একটা বিপজ্জনক বাঁক নিলেন রবীন্দ্রনাথ। আবার চলে এলেন কোমল গান্ধারের আস্তিনে—যেখান থেকে শুরু হয়েছিল তাঁর অভিযাত্রা।
এবং, আবারও, ‘ছায়া ঘনাইছে…’।
বেশ। বোঝা গেল। পরের লাইনে যখন যাচ্ছেন, আমাদের কান উৎকর্ণ—এ বার নিশ্চয়ই পালানো যাবে ওই আলোবিহীন ছায়ামেদুরতা থেকে? ‘কবে নবঘন বরিষণে’—উচ্চারণ করছেন তিনি, স্মৃতির সজল দরজা-জানলাগুলি খুলে যাচ্ছে একের-পর-এক, যেন দিনশেষের আলো এসে পড়ছে ঘরে। এখানেও শুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে প্রতিটি স্বর। আনাড়ি শ্রোতা উৎফুল্ল: নিশ্চয় পেরিয়ে আসা গেল অন্ধকার রাস্তাটুকু। এমনকি, ‘গোপনে গোপনে’, এই রহস্যমাখা শব্দ, তার অভিসারের আলোছায়া—সমস্তটাই প্রকাশ পাচ্ছে শুদ্ধ স্বরে।
কিন্তু আবারও ‘কেয়া’ শব্দটিতে থমকে দাঁড়াই যেন। ‘কেয়া’ বললেই চলত তো। ঠিক যেভাবে, যথেষ্ট ছিল ‘দেয়া’টুকুই। কিন্তু, রবীন্দ্রনাথ তা করেন না। ভাঙেন নিজেকে, নিজের লিরিককে। ফলে, কেয়া নয়। কেয়া-আ-আ-আ। দেয়া নয়। দেয়া-আ-আ-আ। তিন মাত্রার আরোহণ, যেন-বা পাহাড়ের চড়াই। ধাপে ধাপে উঠে যাচ্ছে সমস্ত পিছুটান ফেলে।
এবং, আচমকাই, নিশির ডাক। কোমল গান্ধারের বিপজ্জনক উপত্যকায় ঝাঁপ। ছায়া।
বস্তুত, গোটা গানটাই, খেয়াল করলে বোঝা যাবে, শুদ্ধ আর কোমল গান্ধারের এই টানাপোড়েন। শুদ্ধ স্বর যতবার আড়াল ভাঙতে চাইছে, এগোতে চাইছে কোমল গা-এর নিগড় ভেদ করে—ঠিক ততবারই, কোনো এক মোহিনী আকর্ষণে, তাকে ফিরে আসতে হচ্ছে কোমলের কাছে। উপায়হীন। রবীন্দ্রনাথ বারংবার চেষ্টা করছেন, ওই স্বরের থেকে যদি দূরত্বে থাকা যায়। তিনটে মাত্রা নিচ্ছেন ‘দেয়া’ বা ‘কেয়া’ বলতে। চাইছেন, এগোতে। এগোচ্ছেনও। আরও তিনটে স্বর ওপরে উঠছেন। যাতে চিরকালের মতো দূরে চলে যাওয়া যায় ওই সর্বনেশে, পোড়ারমুখো, কুহকী গান্ধারের থেকে। পুরোনো প্রেমের থেকে। পুরোনো চেনা মুখের থেকে।
পারছেন না। সেই গোপন পাহাড়ি খাদ তাঁকে টানছে। সংগতে থাকছে কেবল একটি মাত্র মিড়—কোমল নিষাদ থেকে কোমল গান্ধারের দিকে সে আগুয়ান। জুড়ে দিচ্ছে দু-তরফকে। সাঁকোর মতো। এতক্ষণ স্বর চেষ্টা করে চলছিল আপ্রাণ, নিজের শুদ্ধতাকে টিকিয়ে রাখার। পারল না। কোন সে মারীচ, যে কেবলই তাকে প্রলুব্ধ করে—ডেকে নেয় ব্যূহে? যার জন্য ঠোক্কর খেতে হয়, ব্যর্থ হয়ে যায় সমস্ত জীবন?
কেবল মনে হয়, এ-ই তো শিল্প। সার্থক শিল্প। যে পরাজয়ের কাছে আনত হতে জানে। যা কিছু ধ্বংস, অথচ যা কিছু সুন্দর—তার কাছে হাঁটু মুড়ে বসে। বিলিয়ে দেয় নিজেকে, নিজের সুরকে।
শুদ্ধ গান্ধারেই যদি সে-দিন থেকে যেতেন রবীন্দ্রনাথ, তা হলে নিশ্চিত সফল হতেন তিনি। সফল হত তাঁর সুর-নির্মিতি। সফল হত তাঁর গান। তিনি তা পারলেন না। বারবার ফিরে এলেন ওই কোমলের কাছে। হারলেন। ব্যর্থও হলেন বই-কি।
সুর জানে—যতবার সেদিন কোমলের নাড়ি কেটেছিলেন তিনি, ততবার তাঁর শিয়রে হানা দিয়েছিল লোভ। এক বিপজ্জনক লোভ!
৫.
নাসা-র নভোযান ভয়েজারের কৌটোয় গচ্ছিত কেশরবাঈ কেসকরের ভৈরবী ঠুমরিটা শুনছিলাম, আর কেঁপে কেঁপে উঠছিলাম। এরকম সাংঘাতিক মর্মভেদী স্বর-প্রক্ষেপণ, হাঁ-মুখো, নাড়িবাহিত আকাচা ধ্বনির সঙ্গে আজকের একুশ শতকে তো আমাদের সাক্ষাৎ হয় না বিশেষ। মনে হলো, কেশরবাঈয়ের এই গাওয়া ভঙ্গিমাটুকুই আজকের দিনে বিরল এবং সংরক্ষণযোগ্য৷
অবশ্য, আমার মন চলে গেল অন্য একটা ব্যাপারে৷ গান শোনার আগে, চোখে পড়ল, এক সাহেব লিখেছেন: তিনি ভীত যে এই আশ্চর্য সৃষ্টিগুলো উন্নততর, বুদ্ধিমান কোনো প্রজাতির কানে ঢোকার আগেই বোধহয় আমাদের এই ব্যাপ্ত, বিরাট, বিপুল সভ্যতা চিরকালের জন্য নিঃশেষ হয়ে যাবে৷
আমি ভাবছিলাম কেবল, কল্পনা করছিলাম, সেরকম কোনো প্রাণীকুল, কখনও যদি শোনে, কেশরবাঈয়ের গাওয়া এই ঠুমরি, সে কী বলবে? কেমন ভাবেই বা শুনবে?
এই ভাবনা নিয়ে গানটা শোনা শুরু করলাম। ভৈরবী বাজছে প্রেক্ষাপটে৷ আমি খালি কল্পনা করলাম, অমল মহাকাশের ভেতর, কোনো এক দূরান্তের জ্যোতিষ্ক থেকে এক ফালি রোদ্দুর ভেসে আসছে৷ যেন-বা সকাল শুরু হয়েছে পৃথিবীতে, আলো এসে পড়ছে সূর্যবাহিত হয়ে, অথচ তা দেখার জন্য কোনো প্রাণ আর বেঁচে নেই। পুরোনো মজে-যাওয়া দেয়ালে ধরেছে শ্যাওলা, তারাই সম্ভবত একমাত্র জীবন, যারা এখনও টিকে থেকে গেছে কোনোক্রমে।
এই বিষণ্ণ পটভূমির ভেতর, সেই বুদ্ধিমান, নন্দন-রসিক, সংবেদী প্রাণীটি একাকী কেশরবাঈয়ের গাওয়া এই ঠুমরি শুনছে। আর তার দেহের ওপর এসে পড়ছে মলিন রোদ্দুর। সে আবিষ্কার করছে, এককালে প্রাণ ছিল এই দুনিয়ায়, ছিল তার সব অনাত্মীয় কারা যেন—যাদের সঙ্গে তার কখনও কোনোদিন দেখা হয়নি, মুখচেনা হয়নি, তবু সে ভেতর ভেতর ওই গায়িকাকে ছুঁতে পারছে, দেখে ফেলছে তাঁর শ্রোতাদের…
এই দৃশ্য আমায় আচ্ছন্ন করে ফেলছিল। আমার এক শিক্ষিকা একবার বলেছিলেন, সকাল ছ’টার সময় হরপ্পা-মহেঞ্জোদারোর লুপ্ত সভ্যতাকে চাক্ষুষ দেখার প্রত্নস্মৃতি। লক্ষ লক্ষ বছরের নৈমিত্তিক অভ্যেসে এ-দুনিয়ায় সূর্য উঠেছে আবার। যারা একদা সেই আলোয় আলোকিত হত, তারা নেই। কেবল তাদের শূন্য স্পেসগুলি পড়ে আছে ছড়িয়ে ছিটিয়ে, দুনিয়াভর।
রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, ভৈরবী হলো সঙ্গবিহীন অসীমের চিরবেদনা। আমি কল্পনা করলাম, আমার অনিত্য, মর পৃথিবীর বুকে সত্যি এমন এক মহাভারতীয় সকাল আসবে যখন মানুষ থাকবে না। সূর্য থাকবে, তারাপুঞ্জ থাকবে, ছাই, গ্রহাণু আর ধূলিকণা প্রহরা দেবে লক্ষ লক্ষ বছরের মতো, কেবল মানুষ থাকবে না। কেবল, এক টুকরো বিস্মৃতির মতো, দূর থেকে ভেসে আসবেন, কেশরবাঈ কেসকর। তাঁর গলায় ওই বিচক্ষণ প্রাণীটির মন বিষণ্ণ হয়ে উঠবে, তাঁর মনকেমন ঘনিয়ে উঠবে, কেবল থাকবেন না গায়িকা, আর তাঁর মতো হাজার-হাজার লক্ষ-লক্ষ মানুষ। এই পৃথিবীর বুকে সেদিন কেবল সুর থাকবে, আর থাকবে আশ্চর্য বিয়োগব্যথা, শূন্যতাস্মৃতি। মুছে গিয়েও, প্রাণের স্মৃতিগুলি থেকে যাবে হাওয়ায়।
প্রাণ অনুপম।
৬.
জীবন আর সভ্যতার গোড়ার কথা এই—
ঘুমন্ত লোকের কোনো ইতিহাস নেই।
ঘুম হলো একটি ভাগ, জীবন তার তিন,
বালুচরের ওপারে ঘুম, গড়িয়ে গেল দিন,
রাত্রিটাকে স্বপ্ন দিয়ে ধরতে যাব যেই—
আজ্ঞা ভাসে, ঘুমের কোনো অতীতকথা নেই।
৭.
বিকেল নেমেছে সবে। রাস্তায় বাতি জ্বলেনি। সাইকেল চালাতে চালাতে একজন মধ্যবয়স্ক খয়াটে চেহারার লোক গলির বাঁকে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। মনে হলো, চোখের সামনে দিয়ে বছরটা চলে গেল৷
কেমন লাগছে? এর মধ্যে ২০২২ হয়ে গেল? ২০২২ বলে কোনো গ্রেগরীয় সালকে কল্পনাও করিনি কখনও, দূরতম দিগন্তেও না। এখন সে আমার বর্তমান। কী আশ্চর্য! এটা আমি যত জনকে জিগ্যেস করলাম, সকলে বলছে। কেউই হজম করতে পারছে না, আমরা একুশ শতকের একুশতম বছর পেরিয়ে এলাম। আজকের দিনটা আমার চৈত্র সংক্রান্তির মতো লাগল। যেন ধু-ধু হাওয়া আর রোদেলা দুপুর ছাড়া এগোনোর কিছু নেই। ঘন সন্ধ্যানীলের ভেতর, নিস্তব্ধ নরম অবসানের ভেতর এ-বছরের যবনিকাপাত হয়ে গেল।
আজ বড় মনকেমন হচ্ছে বিগত বছরটির জন্য। তার মুখ যেন দেখতে পেলাম। কী মায়া-বিষণ্ণ ছিল সে। আজকের বিকেলটা নামল উত্তর-কলকাতার মতো। এরকম ঘনায়মান বর্ষশেষ, এমন ম্লান হেসে তার বিদায় নেওয়া—এ জিনিসটা মনে থাকবে। বছর গতাসু। তার মুখ যেন দেখতে পেলাম।
৮.
এই বিশ্ব মহাকাশযান-স্থিত অন্তরিক্ষ থেকে জরিপ করা ‘গ্লোব’ নামের কোনো সংহত পিণ্ড নয়। এর মধ্যে বৈচিত্র্য আছে, বিবিধতা রয়েছে, এবং রয়েছে সত্তার ক্রম-উত্তরণের দাবি। প্রযুক্তিদাপট যখন করতলগত করে ফেলেছে তামাম ভূগোলক, চ্যাপলিনসম আমলকি-ছলে ফুটবল খেলছে দুনিয়ার সঙ্গে, গড়ে তুলছে নয়া বিশ্বব্যবস্থা-নামের দুনিয়াদারির নবতর সাম্রাজ্যবাদী প্রতর্ক ও প্রকল্পনা—তখন আকাশভরা সূর্যতারা আমার কাছে প্রতিবাদ। যেখানে রবীন্দ্রনাথ নাশকতা চালিয়েছেন এই পণ্য পুঁজি প্রযুক্তি-মধ্যস্থতায় একীকৃত গোলকভাবনার ওপর। শব্দটা হলো—‘বিস্ময়ে তাই জাগে আমার প্রাণ’, এই বাক্যাংশের বিস্ময়ে শব্দটা। আবার অন্তরায় গেলেও দেখব, ফুলের গন্ধে ওঁর ‘চমক’ লাগছে, মেতে উঠছে ‘মন’।
গানের বিস্ময়। গানের চমক।
জার্মান দার্শনিক ওয়েবারের অভিধানে এই ভাবনার নাম: ডিসএনচ্যানমেন্ট৷ ডিসএনচ্যান্টমেন্ট শব্দটার দ্যোতনা সাংঘাতিক—তার কর্তব্য, আধুনিকতার অন্তরালে যে রুক্ষ, অসুন্দর জায়গাটা রয়েছে তার মর্মে পৌঁছোনো। আধুনিকতা, মনে করেন ওয়েবার, আসলে পুরোনো এনচ্যান্টমেন্টের দুনিয়াকে কেড়ে নিয়েছে—বদলে, দিয়েছে যুক্তির দুনিয়া। ডিসএনচ্যান্টমেন্ট। অর্থাৎ, প্রহেলিকা নেই আর। মানুষী সভ্যতায় যে কুয়াশাঘেরা অমলিন শৈশবস্মৃতি ছিল, যার কথা মার্কসও বলেছেন, গ্রিক সাহিত্য, বিশেষত ইস্কাইলাস ওঁর এত প্রিয় ছিল কেন, তার উত্তরে মার্কস বলেছিলেন, কারণ সেই সূর্যকালে (জয় গোস্বামীর থেকে ধার নিলাম শব্দটা। ‘মা মমতাময় অম্লধারা, নগ্নে তোর ভেসে আছি সূর্যকাল থেকে’) সভ্যতার দেখার চোখটা অন্য তরিকার ছিল। সে অনেক কিছু দেখতে পেত, যা সভ্যতার ক্রম-বয়ঃপ্রাপ্তিতে পলিতে মজে গেছে—যার অনেক কিছুই মিথ্যে হয়তো, কুহেলিজড়িত—তার পরতগুলো ধসে পড়ছে আধুনিকতার সামনে এসে। মিথ্যের সৌন্দর্যমায়া-মথিত আস্তরণ, যা সভ্যতার নগ্ন ও নিরাবরণ চোখকে আচ্ছন্ন করেছিল শতাব্দীভর—তাকে টেনে খানখান করে দিচ্ছে আধুনিক। চলভাষ, অ্যান্ড্রয়েড টেকনোলজি এসে যাওয়ায় আমাদের আপাত-একাকীত্ব ও বিস্মিত হওয়ার মেয়াদ ফুরিয়েছে। অপুর ড্যাবা-ড্যাবা চোখ দুটোর কথা ভাবছিলাম। সত্যজিতের তর্জমা যদি না-ও বা থাকত, তবু বিভূতিভূষণের বর্ণনাই কাফি: ওই অপার বিস্ময়-জিজ্ঞাসায় তাড়িত চোখে ঘোর আর চমকের ঝিলমিলি অঞ্জন খেলে যায়, কলকাতায় এসে অপু কলের জলে মুখ ধোয় আর তুর্গেনেভ-নিৎশে হামলে হামলে পড়ে৷ পড়ার পর সে কি হোঁৎকা হয়ে উঠেছিল?—এমন সাদা-কালো উত্তর ‘অপরাজিত’-তে থাকা সম্ভব নয়। কারণ, বাকিটা উপন্যাসের লীলা।
জীবনানন্দের সদুক্তি: জ্ঞানের বিহনে প্রেম নেই। আদম-ইভের প্রণয়স্পর্শলাগা আপেল আমাদের পেটের ভেতর যত এগোতে থাকবে, ইনোসেন্স লুপ্ত হয়ে যাবে। যেমন সুকুমার বলতেন: বড় হলে মানুষ বস্তুত হোঁৎকা হয়। শক্তির একটা কবিতার লাইন মনে পড়ে গেল—’আহা বেশি দিন বাঁচবো না আমি বাঁচতে চাই না।’ একটা খুদে লাইন ছিল: ‘অনভিজ্ঞতা বাড়ায় পৃথিবী, বাড়ায় শান্তি/ প্রাচীন বয়সে দুঃখশ্লোক গাইব না, আমি গাইতে চাই না।’
অনভিজ্ঞতা পৃথিবীকে বাড়ায়। তাকে প্রসারিত করে তোলে। গ্লোবের কোনো প্রসারণ সম্ভব নয়। সে জড়, বিম্বিত, শিলীভূত ও স্থির। রবীন্দ্রনাথের ওই পথিকটি—না, ঋত্বিকের প্রোটাগনিস্ট নন—কেদার-আচ্ছন্ন সকালবেলায় শিশিরবিন্দুর ওপর হেঁটে যান পদচিহ্ন ইতস্তত রেখে। বিস্মিত তাঁর পৃথিবী আর বর্তুল থাকে না তখন, গড়ে ওঠে নতুন জ্যামিতি— বাড়তে বাড়তে বিশ্বপট ছুঁয়ে ফেলে সমস্ত আকাশ।
বিস্ময়ে, এভাবেই গান জেগে ওঠে কখনও-কখনও।
প্রচ্ছদচিত্র সৌজন্য:www.needpix.com