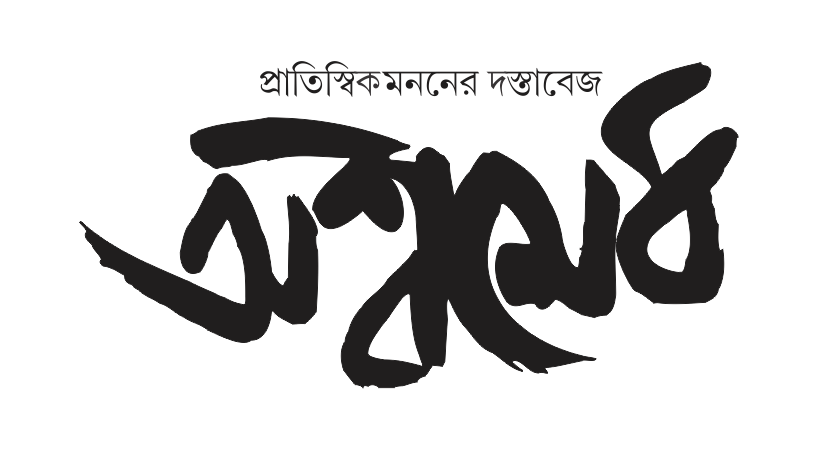সম্প্রতি দুটি ঘটনা ঘটল। প্রথমত, রিজার্ভ ব্যাংক অব্ ইন্ডিয়া ঘোষণা করল, ডলারের বদলে এবার ভারতীয় টাকাতেই লেনদেন করা যাবে, ব্যবসায়ীরা সেভাবেই বিনিয়োগ করতে পারেন, তাঁদের ব্যবসায়। দ্বিতীয়ত, ফরচুন গ্লোবাল ৫০০-র তালিকা প্রকাশ হলো (জুন-জুলাই ২০২২)। উক্ত তালিকায় যে ছবি পাওয়া গেল, তাতে এটা স্পষ্ট যে, বিগত এক দশকে ভারতবর্ষের বিশেষ তরতম সেখানে হয়নি। আমরা জানি, জীবন বীমা কোম্পানি ‘এলআইসি’ কর্পোরেশন হিসাবে কাজ করা শুরু করেছে ইদানীং। তাই উক্ত তালিকায় তার অন্তর্ভুক্তি একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। স্টেট ব্যাংক অব্ ইন্ডিয়া-র ক্রমোন্নতিকে রিজার্ভ ব্যাংক অব্ ইন্ডিয়া-র ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে দেখতে গেলে আমাদের আরেকটু সময় নিয়েই তা দেখতে হবে। তবে তারও আগে নজর রাখতে হবে, পেছনে ফেলে আসা গত এক দশকের দিকে। আর তার ফলে আমরা কিছুটা হলেও হয়তো বুঝব যে, ঘরের বাইরের দেওয়ালে রঙের নতুন পোঁচ পড়লেও, ঘরের ভেতরটায় সেই একইরকমের রংচটা পলেস্তরা খসে পড়া অবস্থাটা রয়ে গেছে।
মুদ্রাস্ফীতির আড়াই প্যাঁচ:
অর্থনীতি বিষয়টাই এমন যে, কিছু বলতে গেলে, ছোটবেলায় শোনা অঙ্কের সেই ধাঁধাটা মনে পড়ে: দুই ভাই হাটে নিয়ে যাচ্ছে বাড়িতে বানানো মেঠাই, বিক্রি করতে। মা তাদের দুজনকে দশ পয়সা করে দিয়েছে পথে খিদে পেলে খাবার জন্য। বড় ভাই ছোটভাইয়ের থেকে দশ পয়সার মিঠাই কিনে খেল। তারপর ছোট ভাই বড় ভাইয়ের থেকে। দু-ভাই বেচাকেনা সেরে দশ পয়সা নিয়ে বাড়ি ফিরল। বেচা কেনা নগদে—কোনো ধার নেই!
কোনো ব্যক্তি একইসঙ্গে বিনিময় মূল্য ও ব্যবহার-মূল্য ভোগ করতে পারে না। এই বিনিময় মূল্যের সঙ্গেই গাঁটছড়া পণ্যের দামের। ‘ইনফ্লেশন’ শব্দটির সংজ্ঞার্থ হিসাবে কোন শব্দটি অধিক গ্রহণযোগ্য ‘মুদ্রাস্ফীতি’ না ‘মূল্যস্ফীতি’—এ নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে চুলচেরা তর্ক আছে।
দাম বাড়ার ঘটনাকে যাঁরা মূদ্রাস্ফীতি বলেন, বা বলতেন, তাঁরা মনে করেন টাকাপয়সার জোগান বেড়ে গেলে বাজারে জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যায়। অর্থাৎ মূল্যবৃদ্ধির কারণ মুদ্রাস্ফীতি। এবং এটিই একমাত্র কারণ। তাই ‘মূল্যবৃদ্ধি’ ও ‘মুদ্রাস্ফীতি’ সমার্থক। ক্ষুদ্র পরিসরের (মাইক্রো) অর্থনীতি বা ধ্রুপদী অর্থনীতিতে বাজারকে দেখা হত স্বতঃস্ফূর্ত ভারসাম্য (অটোমেটিক ইক্যুলিব্রিয়াম) রক্ষিত হওয়া বিকিকিনির ক্ষেত্র হিসাবে। নিছক চাহিদা ও জোগানের মিথস্ক্রিয়ার লীলাভূমি হিসাবে! ক্রমাবনত চাহিদা-রেখা ও ক্রমোন্নত জোগান-রেখার অসি যুদ্ধের, ক্রস সোর্ড টানাপোড়েনের সংজ্ঞাত ভারসাম্য! এবং ভারসাম্যই!
ধরা যাক, নতুন কোনো দ্রব্য বা সেবা উৎপন্ন হয়নি। কিন্তু রাজা, বা সরকার, কিছু টাকাপয়সা ছাপিয়ে বাজারে ছাড়লেন। তাহলে, একদিকে যেমন টাকার জোগান বাড়ল অপরদিকে টাকার মূল্য কমে গেল! অর্থাৎ, টাকার মূল্য হ্রাসের পরিপ্রেক্ষিতে দ্রব্যের মূল্যের (দামের) আপাত বৃদ্ধি ঘটছে। একটা সময় অবধি ধ্রুপদী অর্থনীতি তার চাহিদা জোগানের ভরসা-তত্ত্বকেই সামান্য বিস্তৃত করে বাজারের মূল্যবৃদ্ধিজনিত সাময়িক সমস্যার ব্যাখ্যা দিত। হ্যাঁ, সাময়িক! কারণ তাঁরা মনে করতেন, বাজারের এই চপলতা ক্ষণিকের। এবং তা কিছুটা বিভ্রম। কারণ নতুন ভারসাম্য তৈরি হবে এবং পুরোনো ভারসাম্যের সঙ্গে তার মূলগত কোনো পার্থক্য নেই।
এই তত্ত্ব বাজার যে খুব মেনে চলেছে তা বলা যাবে না। কিন্তু অর্থনীতিবিদরা তাঁদের বাজারের স্বতঃস্ফূর্ত ভারসাম্য-তত্ত্বেই বুঁদ ছিলেন। ১৯৩০-এর দশকের মন্দায় এই ‘বাজার’ ভেঙে পড়ল। পণ্ডিতেরা বিস্তর মাথা ঘামালেন, চুল ছিঁড়লেন—কিন্তু চাহিদা জোগানের ক্ষুদ্র তত্ত্ব (মাইক্রো মডেল) রাষ্ট্রের বৃহৎ প্রেক্ষিতে কোনো সমাধান দিতে পারল না।
এলেন কেইন্স। তিনি অর্থনীতির আলোচনায় আনলেন বৃহৎ (ম্যাক্রো) প্রেক্ষাপট। আনলেন আয় (দেশের ক্ষেত্রে জাতীয় আয়), সঞ্চয়, ভোগ, বিনিয়োগ এবং সরকারের ভূমিকা সম্পর্কে, নতুন তত্ত্ব। তার পরে অর্থনীতির আঙিনায় আসন পেতে বসল—IS-LM Model—এই রেখা দুটিও অসি যুদ্ধের, ক্রস সোর্ড টানাপোড়েনে অঙ্কিত। অনেকটা চাহিদা-জোগান রেখার মতোই! তাই বোধহয় গ্রহণযোগ্যও হলো তাড়াতাড়ি।
ধ্রুপদী শাস্ত্রে টাকাকে ‘মায়া’ হিসাবে দেখানো হত। কেইন্স বললেন যে, নিছক বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে ছাড়াও, টাকার বিশেষ বিশিষ্ট প্রভাব অর্থনীতিতে আছে। মুদ্রা নিরপেক্ষভাবে ব্যবস্থাটি চলছে এমন নয়, মুদ্রাস্ফীতির বিশেষ ভূমিকা আছে অর্থব্যবস্থায়।
যে বিশিষ্ট রূপে আজ আমরা টাকাকে দেখি, তা হলো নোট এবং ধতব মুদ্রা। নোট মানে প্রমিসারি নোট—‘প্রতিজ্ঞা পত্র’। কোনো সংগ্রাহকের সংগ্রহে যেমন থাকতে পারে; পারে মধ্যবিত্তের সংসারেও ‘সঞ্চয়’ হিসাবে। উঁকি দিয়ে দেখা যেতে পারে রিজার্ভ ব্যাংক অব্ ইন্ডিয়ার বৈদ্যুতিন তথ্যভাঁড়েও। আমাদের দেশের এক টাকার নোটের এক পিঠে উপরে লেখা থাকে ‘গভর্মেন্ট অব্ ইন্ডিয়া’ আর উলটো পিঠে ডানপাশের উপরে এবং উলটো দিকে, বাঁ-দিকে একটি এক টাকার ধাতব ‘মুদ্রা’ অঙ্কিত এবং তার নীচে অর্থ মন্ত্রকের পক্ষে স্বাক্ষর থাকে অর্থ সচিবের। অন্য সমস্ত নোটে স্বাক্ষর থাকে রিজার্ভ ব্যাংকের গভর্নরের। লেখা থাকে, ‘আই প্রমিস টু পে দ্যা বেয়ারার দ্যা সাম অব্ ….রুপিজ।’ টাকার দু-পিঠেই লেখা থাকে ‘রিজার্ভ ব্যাংক অব্ ইন্ডিয়া’ এবং তার নীচে ‘গ্যারান্টেড বাই দ্যা সেন্ট্রাল গভর্মেন্ট’। আর থাকে—অশোক স্তম্ভ। সংবিধান স্বীকৃত বিভিন্ন ভাষায় উক্ত ব্যাংক নোটের মূল্যমান। একটা সময়ের পর গাঁধী বাপুও জুড়ে গিয়েছেন ভারতীয় ছাপা নোটের নকশায়।
বোঝাই যাচ্ছে টাকাকে কেন ‘মায়া’ (নন রিয়েল) ভাবা হত। তখন এবং এখনও, এই বিট কয়েন অধ্যুষিত সময়ে। ব্যাংক নোট নিছক একটা ‘প্রতিজ্ঞা পত্র’ ছাড়া তো কিছু নয়—এখন না হয় সরকার তার গ্যারান্টার, এই যা। কিন্তু বেয়ারার-কে গভর্নর কোন সাম অব্ রুপিজ দেবেন? তা হচ্ছে, অর্থ সচিবের স্বাক্ষরিত ওই এক টাকার নোটের…গুণ। একটি নোটের বদলে আরেকটি নোট! এবং ‘মাননীয় বেয়ারার’ যদি কাউকে খুনের বদলে পারিশ্রমিক বাবদ ওই টাকা পেয়ে থাকেন, গভর্নর তাকেও হাস্যমুখে অতগুলি এক টাকা ফেরত দেবেন। আর যদি বেয়ারার-এর কাছে ‘জাল’ টাকা থাকে?
মুদ্রার ক্ষেত্রে এ বালাই নেই। মোটামুটি ভাবে, অন্তত আগে তাই-ই ছিল, ধাতব মুদ্রা। তৈরিতে যে খরচ হয়েছে সেটাই তার ‘দাম’। বেয়াড়া প্রশ্ন করাই যায়, যে, দশটি দশ পয়সার মুদ্রা বা একটি এক টাকার মুদ্রা গলিয়ে (ভাঙিয়ে নয়) যে মূল্য পাওয়া যাবে—তা কি এক টাকার নোটের সমান? এ প্রশ্নের উত্তরের জন্য বহু রণ রক্ত ইতিহাস ঘাঁটতে হবে—আপাতত সে খোঁজ স্থগিত থাক।
ব্যাংক, পোস্ট অফিস, জীবন বীমা প্রভৃতি সরকারি (বা বেসরকারি) আর্থিক লেনদেনে যুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলিতে প্রাপ্য ‘বন্ড’-এর সঙ্গে বাজার-চলতি নোটের দৃশ্যত কোনো পার্থক্য নেই। দুটোই ‘প্রমিস’! তফাত হলো, টাকার বিনিময়ে সুদ মেলে না; কিন্তু বন্ডের বিনিময়ে সুদ পাওয়া যায়। আবার ওই বাজার-চলতি নোটই সরকারি (বা বেসরকারি) আর্থিক প্রতিষ্ঠানে ‘সঞ্চয়’ হিসাবে গচ্ছিত রাখলে সুদ পাওয়া যায়।
এখন সমস্যা হলো এই যে, ‘টাকা’ বা ‘নগদ’ বা ‘অর্থ মূল্য’ বলে চিহ্নিত জীবন-জীবিকার এই বিনিময়-মাধ্যমের জোগান ও পরিমাণ পরিমাপ করা খুবই গোলমেলে একটি বিষয়। সরকার বা রিজার্ভ ব্যাংক যে পরিমাণ টাকা বাজারে জোগান দিল, বাজারে তার প্রভাব বা কার্যকারিতা তার বহুগুণ। একটি দশ টাকা যদি সারাদিনে দশজন মানুষের হাতে ঘোরে তাহলে তা একাই একশো! একশো টাকার আয় প্রবাহিত হলো! আয় (রাষ্ট্রের প্রেক্ষিতে জাতীয় আয়), ভোগ, সঞ্চয়, বিনিয়োগ—এসবই তো রিয়েল সেক্টর—এখানেই রিয়েল সেক্টরের এর সঙ্গে মানিটরি সেক্টরের গোলমেলে প্রতিস্পর্ষী সম্পর্ক।
টাকার জোগান যখন আছে তার চাহিদাও নিশ্চয়ই আছে। কেইন্স বললেন, টাকার চাহিদার তিনটি (মূল) কারণ: প্রথমত বিনিময়ের চাহিদা (Transaction Demand for Money), সাধারণত যে রূপে টাকাকে ব্যাখ্যা করা হয় এবং ধ্রুপদী অর্থবিদরা করতেন। দ্বিতীয়ত আপদকালীন চাহিদা (Precautionary Demand for Money) এবং তৃতীয়ত ফাটকা চাহিদা (Speculative Demand for Money)। ঘোমটার নীচ থেকে বেরিয়ে এসে কেইন্স সপাটে সত্য উচ্চারণ করলেন—টাকার ফাটকা বাজার! প্রথম দু-প্রকার চাহিদা আয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত, কিন্তু শেষেরটি সুদের সঙ্গে সম্পর্কিত। সুতরাং টাকার মোট চাহিদা আয় ও সুদের সঙ্গে সম্পর্কিত।
ধ্রুপদী অর্থশাস্ত্রে বলা হত ভারসাম্য অবস্থায় পূর্ণ নিয়োগ বিরাজ করে—অর্থাৎ জমি, শ্রম, পুঁজির পূর্ণ নিয়োগ তথা পূর্ণ সদ্ব্যবহার হয়। কেইন্স দেখালেন, ভারসাম্য পূর্ণ নিয়োগ ছাড়াও হতে পারে। পূর্ণ নিয়োগ নির্ধারিত হয় শ্রমের বাজারে। ধ্রুপদী অর্থশাস্ত্রে। শ্রমের চাহিদা ও জোগান নির্ধারিত হয় ‘প্রকৃত মজুরি’র (Real Wage) দ্বারা। কেইন্স বললেন, শ্রমের চাহিদা নির্ধারিত হয় প্রকৃত মজুরির সাপেক্ষে কিন্তু শ্রমের জোগান নির্ধারিত হয় ‘নামিক মজুরি’র (Nominal Wage) সাপেক্ষে। তাই ভারসাম্য অবস্থাতেও পূর্ণ নিয়োগ নাও থাকতে পারে। কেইন্স আরও উল্লেখ করলেন, মহামন্দা, মূল্যবৃদ্ধি (মুদ্রাস্ফীতি), অপূর্ণ নিয়োগ (বেকারি) প্রভৃতি সমস্যাগুলিকে—বলা চলে সমস্যাগুলোর পারস্পরিক সম্পর্ক খুঁজলেন। কেইন্স নিদান দিলেন, সরকারি বিনিয়োগের, যাতে ভারসাম্য সত্ত্বেও যে অপূর্ণ নিয়োগ তা কমানো যায়। কিন্তু তাতে সমস্যা হলো মূল্যবৃদ্ধি ঘটতে পারে।
মৃদু মূল্যবৃদ্ধিকে মেনে নিয়ে বেকারির সমস্যাকে হ্রাস করার মডেল সাফল্য পেয়েছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে ১৯৬০-এর দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত। ছয়ের দশকের শেষ দিকে দেখা গেল, (সামান্য!) মুদ্রাস্ফীতির মূল্যবৃদ্ধিকে মেনে নিয়েও বেকার সমস্যাকে নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে না। বলা হলো নিয়ন্ত্রিত মূল্যবৃদ্ধি ঘটিয়ে বেকারি অবসানের মডেল স্বল্প সময়ের জন্য সম্ভব; দীর্ঘ মেয়াদী সময়ে এই মডেল ব্যর্থ। এই সময়েই অর্থনীতির চারটি স্তম্ভের: জমি, শ্রম, পুঁজি, সংগঠন-এর সঙ্গে আরও একটি স্তম্ভের প্রস্তাব এল—’জ্ঞান’। ‘জ্ঞান’-কে শ্রমের থেকে আলাদা করা হলো। সাতের দশকে ফিরে এল বিনিয়ন্ত্রণের ধ্রুপদী মডেল।
নয়ের দশকে অনিয়ন্ত্রিত বিশ্ব অর্থ ব্যবস্থার প্রবর্তন ঘটল। অনিয়ন্ত্রণের দর্শন হলো ধ্রুপদী দর্শন—তবে তখন ছিল রাষ্ট্রীয় কাঠামো, এখন হয়েছে আন্তর্জাতিক কাঠামো! মোদ্দা কথা হলো, দুটি গোদা উপদল আছে। এক পক্ষ (ধ্রুপদী) অনিয়ন্ত্রণে আস্থাশীল; বাজারকে স্বাধীনভাবে খেলতে দিলে, তা আপনা আপনি স্থিতিশীলতা লাভ করে—এই তত্ত্বে বিশ্বাসী। অন্য পক্ষ (কেইন্সিয়ান) মনে করে, বাজারের স্বার্থেই তার উপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ দরকার। এঁদেরই মার্জিত মডেল হলো জনকল্যাণ অর্থনীতি। সাকুল্যে ‘আড়াই’-খানি ধারা।

মুদ্রার অন্য পিঠ:
ধ্রুপদী ধারা যেখানে মুদ্রাস্ফীতিকে অস্বাভাবিক ও ক্ষণিকের মনে করে—মার্কসবাদীরা সেখানে মুদ্রাস্ফীতিকে স্বাভাবিক ও অনিবার্য মনে করে। মন্দা, মুদ্রাস্ফীতি এবং বেকারত্ব একই প্রবাহের বিভিন্ন বিন্দু! একদিকে অপূর্ণ নিয়োগ অন্যদিকে অপচয়—এটাই পুঁজির উত্তরাধিকার!
সমাজে উৎপাদন যতটা ‘নগদ’ বা ‘অর্থ মূল্য’ তৈরি করে তার সবটা সমাজে ফিরে আসে না। চুরি হয়ে যায়। সেই চুরি যাওয়া ‘নগদ’ বা ‘অর্থ মূল্য’, বা ‘উদ্বৃত্ত মূল্য’, সমাজের ক্রয়ক্ষমতায় ক্ষয় ধরায়। অন্যদিকে, যে ক্ষুদ্র অংশের সেই উদ্বৃত্ত মূল্য ভোগ করার কথা আর তারা যা ভোগ করে—তার মোট পরিমাণ হয় স্বল্প (কারণ তারা সংখ্যায় কম); তার উপর তারা সবটা ভোগ করে না। উদ্বৃত্ত মূল্যের একটা অংশ পুঁজিতে পুঞ্জীভুত হয়। কিন্তু এই পুঁজি যাদের থেকে চুরি করা তারা যেহেতু প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত হয়েছে—তাদের আয় কমেছে। এবং তাদের ভোগ-ব্যয়ের কার্যকর চাহিদা কমেছে। এটাই মন্দা। মুদ্রাস্ফীতি ও মন্দা পর্যায় ক্রমে, অনেক সময় একসাথে চলতে থাকে।
দাম হলো অর্থে প্রকাশিত মূল্য বা আর্থিক মূল্য। পণ্যের দাম ও মূল্য সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়াটাই স্বাভাবিক কিন্তু বাস্তবে তা হয় না। বাজারে চাহিদা ও জোগান সমান হলে কোনো পণ্যের দাম তার মূল্যের সমান। বাস্তবে এমন ভারসাম্য দুর্লভ! উৎপন্ন পণ্য সামগ্রীর পরিমাণ যদি ভোক্তাদের প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম না হয়, মানে চাহিদা যদি জোগানের থেকে বেশি হয় তাহলে পণ্যটির দাম তার মূল্য অপেক্ষা বেশি-ই হবে—এই জটিলতাটাই মুদ্রাস্ফীতির কারণ।
শ্ৰম যে তার প্রকৃত মজুরি পায় না (এবং তাই চাহিদা হ্রাস পায়) তা কেইন্স বুঝেছিলেন। অর্থাৎ কেইন্স একরকম ভাবে উদ্বৃত্ত মূল্যের খেলাটি ধরতে পেরেছিলেন। কিন্তু নীতির প্রয়োগে তাঁর তত্ত্ব ব্যবহৃত হয়েছে বাজারকে বাঁচিয়ে তুলতে—অর্থ ব্যবস্থার চালচিত্রের কোনো উত্তরণের জন্য নয়।
ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ সিকিভাগেই বাজার প্রতিযোগিতার আপাত মুখোশ খুলে একচেটিয়া রূপ নিতে শুরু করেছিল। প্রতিযোগিতার তাত্ত্বিক বাজার অনিবার্যভাবেই একচেটিয়া হয়ে যেতে বাধ্য। একজন (স্বল্প) উৎপাদক (বিক্রেতা) এবং অসীম ভোক্তা (ক্রেতা)—এই মনোপলির এক বিশেষ রূপ ‘মনোপসনি’; সেখানে একজন (স্বল্প) ক্রেতা ও অসীম বিক্রেতা—এই আপাত বিরোধী দুটি বাজারকে ‘এক বিশেষ রূপ’ বলার কারণ, উৎপাদনের বাজারে যা মনোপলি, শ্রমের বাজারে তাই মনোপসনি। মনোপলি পণ্যের যে দাম নির্ধারণ করে তা তার মূল্যের থেকে বেশি। প্রতিযোগিতার একটি সামাজিক ভড়ং অন্তত ছিল যে, ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়েই মূল্য-গ্রহীতা—অর্থাৎ দাম স্থির হয় সামাজিক (উৎপাদক/ভোক্তা) টানাপোড়েনে—মনোপলিতে উৎপাদক (বা উৎপাদক ও বিক্রেতা যৌথভাবে) খুল্লাম খুল্লা দাম-নির্ধারক! বড়জোর তিনি তাকিয়ে থাকেন অন্য উৎপাদকদের দিকে অথবা চক্র তৈরি করেন তাদের সঙ্গে।
উদ্বৃত্ত মূল্য যখন ‘পুঁজি’ হিসাবে আখ্যায়িত হতে শুরু করে, সেই জায়মান পুঁজির মধ্যে থাকে যাবতীয় অসামাজিক কাজ: চুরি/লুণ্ঠন/তঞ্চকতা। দানা-বাঁধা পুঁজি প্রতিযোগিতার পর্বে এসে ‘সামাজিক’ রূপ নেয়। উদ্বৃত্ত মূল্যের চুরি চলে যায় আপাত দুর্বোধ্য গণতান্ত্রিক মুখোশের আড়ালে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ সিকিভাগে তা একচেটিয়া ও সাম্রাজ্যবাদী রূপ নেয়। বিংশ শতাব্দীর বিশের দশকে তা চ্যালেঞ্জ্ড হয় সোভিয়েত রাশিয়ায়। ১৯৩০-এর দশকেই তা ভয়ংকর ভাবে মুখ থুবড়ে পড়ে, এবং পরিত্রাণ পায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সুবাদে।
এই দীর্ঘ কালপর্বে নিছক বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে প্রবর্তিত অর্থ (টাকা) বিবর্তিত হয়ে এক মহিমান্বিত নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা নিয়েছে। সে নিজেই হয়ে উঠেছে ‘পুঁজি’! আত্মগত বিমূর্ততা তৈরি করেছে মোহ! এই বিমূর্ততার জন্য সমস্ত রকম চুরিকে সে আত্মসাৎ করে সামাজিক করেছে। অর্থের মানসিক মূল্য প্রকৃত মূল্যের ওঠা নামাকে আড়াল করে। অর্থের বিভিন্ন রূপের: মুদ্রা, বন্ড, ডিবেঞ্চার, নোট, চেক প্রভৃতির চরম বিকাশ ঘটে গত শতাব্দীর কুড়ির দশকে। তারপরই তার চরম পতনটিও ঘটে ১৯২৯-এ!
শ্রমসাধ্য ও সূক্ষ্ম উৎপাদন প্রক্রিয়ার জন্য সোনার মূল্য খুব চড়া। বিনিময়ের মানদণ্ড হিসাবে সোনা স্বীকৃতি লাভ করেছিল। প্রচলিত অর্থের মূল্যায়ন; যদিও পদ্ধতি হিসাবে তা জটিল তবু শ্রমের সঙ্গে অর্থের সম্পর্কের স্বীকৃতি ছিল, স্বর্ণমাণে। সে কারণেই, সমাজে ‘স্ত্রী-ধন’ হিসাবে আখ্যায়িত সোনাকে ঘিরে এত মোহ! ১৯৩০-এর অক্টোবরে আমেরিকার শেয়ার মার্কেটের অপ্রতিরোধ্য পতন শুরু হয়। এ সময়ে ইউরোপের বিভিন্ন শেয়ার মার্কেটে ধস নামে। তেইশটি দেশে কাগুজে টাকা (ব্যাংক নোট)-র সঙ্গে সোনা বা অন্য ধাতুর বাধ্যতামূলক বিনিময়, অনুপাত বাতিল হয়। কারণ টাকা-র ‘দুর্ভিক্ষ’ শুরু হয়েছিল—প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল—অনেক টাকা ছাপার। প্রথমে জাতীয় ক্ষেত্রে, পরে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও স্বর্ণমাণ বাতিল হতে শুরু করে। অর্থাৎ শ্রমের সঙ্গে অর্থের নৈতিক গাঁটছড়া ছিন্ন হয়।
আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এই মান অর্জন করে—লেনদেন উদ্বৃত্ত (Balance of Payment) এবং ধীরে ধীরে, ডলার। সোনা বা শ্রমের সঙ্গে সম্পর্ক না থাকায় ডলারের ‘দাম’-এর জাতীয় উৎপন্নের সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ হবার দায় থাকে না। ব্যাংক তথা লগ্নী সংস্থাগুলোর ‘বিমূর্ত’ ক্ষমতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। এই প্রভূত্ব বিস্তারের জন্য প্রয়োজন ছিল সামরিক শক্তি প্রদর্শন! ’৭১-এর পনেরো অগাস্ট, আমেরিকা, ডলারের সঙ্গে স্বর্ণমাণের শেষ বন্ধনটুকুও ছিন্ন করে।
একদিকে ডলারের বিমূর্ত সামরিক-মূল্য, অন্যদিকে জ্বালানি তেলের শক্তি (ব্যবহার) মূল্য—মূর্ত ও বিমূর্তের সংঘাতে লিখিত হতে থাকে পুঁজির নিয়ন্ত্রণের ইতিহাস। সামরিক শক্তি দিয়ে জ্বালানি শক্তিধরদের বাড়বাড়ন্ত রুখতে আমেরিকাকে সামরিক শক্তির বাজার বৃদ্ধি করতে হয়, তৈরি করতে হয় অস্ত্রের চাহিদা! কিন্তু অস্ত্র তো খাওয়া যায় না—তার সামাজিক মূল্য কীভাবে স্থির হবে? মূল্যটিই হবে আরোপিত মূল্য—অর্থাৎ উদ্বৃত্ত মূল্য চুরি করার নতুন পথ! সামরিক ক্ষেত্রে অধিক লাভজনক সম্ভাবনার জন্য ভোগ্যপণ্য ক্ষেত্রে বিনিয়োগ কমে—সুতরাং উৎপাদন তথা জোগান কমে তৈরি হয় মুদ্রাস্ফীতির অনুকূল অবস্থা।
স্বর্ণমাণের বাধাবিপত্তি উঠে যাওয়ায় নগদ প্রাচুর্য বাড়ে। আরও বাড়ে বিভিন্ন রকম প্রমিসারি নোট—শেয়ার, ডিবেঞ্চার, বন্ড ইত্যাদি। অর্থাৎ অর্থের জোগান (প্রকৃত মুদ্রাস্ফীতির উপাদান) বৃদ্ধি পায়। এই অর্থের সঙ্গে সুদের হারের সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ঠ! কারণ এই ‘টাকা’ বা ব্যাংক নোট তো কার্যত চলে বিশ্বাসের উপর। তাই সুদের হার নিয়ন্ত্রণ কোরে রাষ্ট্রীয় বা কেন্দ্রীয় (এদেশে রিজার্ভ ব্যাংক) ব্যাংক টাকার জোগানকে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে। নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতিগুলি হলো: রেপো রেট, রিভার্স রেপো রেট, সিআরআর, এসএলআর ইত্যাদি।
অর্থের এই বিবর্তনের জন্য বাজার-ব্যবস্থা যেখানে এসে পৌঁছল—সেখানে: ঋণ, নগদহীন লেনদেন, ঋণ পুঁজি (loan capital) এসবের দৌরাত্ম্য বাড়ল। রিয়েল সেক্টর-এর পরিবর্তে মর্যাদা পেল মানিটরি সেক্টর! উৎপাদনের অনুষঙ্গহীন ‘টাকা’ দাপিয়ে বেড়াল সারা পৃথিবী জুড়ে!
মুদ্রাস্ফীতি ও মূল্যবৃদ্ধি:
মন্দা-র স্বরূপ প্রকাশ্যে এসেছিল ২০০৭ সালে। আত্মগর্বী ওয়াল স্ট্রিটের ধস—প্রথম বিশ্বের মহিরুহদের দেউলিয়া হওয়ার খবরের প্রভাবে, ২০০৯ সালে, এদেশে মুদ্রাস্ফীতির হার কমে দাঁড়িয়েছিল ১.৩৮ শতাংশয়। ২০০৮-এর সেপ্টেম্বর থেকে মন্দার প্রভাব দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। জীবিকাহীন হয়ে পড়া মানুষের সংখ্যা বাড়তে থাকে দেশে, বিদেশে। এই মন্দা রিয়েল সেক্টরের মন্দা নয়—এটা ছিল সর্বাথেই আর্থিক ক্ষেত্রের মন্দা; অর্থের বুদ্বুদ ফেটে পড়া! মন্দার মোকাবিলায় বিভিন্ন সহায়তা (Package) ঘোষিত হতে থাকে; যা মূলত সুদ নিয়ন্ত্রণ কোরে ও বিভিন্ন ছাড় দিয়ে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করার চেষ্টা। মন্দার টানে আপাত মূল্যের থেকে দাম হ্রাস পাবার প্রবণতার বিপরীতে মন্দার মোকাবিলায় ‘ত্রাণ’ জনিত মূল্যবৃদ্ধি—এ দুয়ের প্রভাবে শেষমেশ মন্দা পিছু হটল আর মূল্যবৃদ্ধি সামনে চলে এল।
‘অ্যাডভান্টেজ’ মুদ্রাস্ফীতি! আপাত পরস্পর বিরোধী তথ্যে আমরা ভারাক্রান্ত হতে থাকি! ২০০৯ সালের মে মাসে যেখানে মুদ্রাস্ফীতি তলানিতে ঠেকেছিল, বছর পার হতে না হতে ২০১০-এর মে মাসে তা আগের উনিশ মাসের সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছে হলো ১০.১৬ শতাংশ।
জুন মাসের মাঝামাঝি খাদ্যপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি ঘটল প্রায় সতেরো শতাংশ। খাদ্যপণ্যের এই মূল্যবৃদ্ধি একটু বেশি-ই খাপছাড়া। ১৯৯৪-৯৫ থেকে ২০০৪-০৫ এই দশ বছরে মোট মূল্যবৃদ্ধি ছিল প্রায় ৬ শতাংশ আর খাদ্যপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি ৫.৬৪ শতাংশ। মানে আপেক্ষিক ভাবে কম। তাই-ই পরের পাঁচ বছরে কুড়ি শতাংশের কাছাকাছি পৌঁছে গেল! ১৯৯৪-৯৫ থেকে ২০০৪-০৫ সময়কালে খাদ্যপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি ছিল ৪ থেকে ৬ শতাংশের মধ্যে। যখন খাদ্য জোগানের বৃদ্ধি হার ২.৩৯ শতাংশ। অন্যদিকে ২০০৫-এর পর থেকে মূল্যবৃদ্ধি হয়েছে লাগামছাড়া, কিন্তু খাদ্যপণ্যের জোগান তুলনায় বেশি ৪.২৪ শতাংশ।
এই খাপছাড়া পরিসংখ্যানের ভেতর কোনো সরল আন্তঃসম্পর্ক বা কো-রিলেশন খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়! মূল্যবৃদ্ধির এই প্রবণতা মন্দার আগেও ছিল। তাই মন্দার সঙ্গে সরাসরি কো-রিলেশনকে খুঁজে না পেলেও পরোক্ষে এ কথা মানতে হয় যে, মন্দার প্রভাবে একসময় মুদ্রাস্ফীতি কমেছিল।

২০০৫ সালের ১৮ জুলাই, দেশের প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং আমেরিকার রাষ্ট্রপতি জর্জ বুশের সঙ্গে একগুচ্ছ সমঝোতাপত্রে স্বাক্ষর করেন। যার মধ্যে একটি ছিল পরমাণু। সে নিয়ে প্রচুর তর্ক বিতর্কও হলো। ২০০৮-এর যে চুক্তিপত্রে সিলমোহর পড়ল তার নাম—’US-India Knowledge Initiative on Agriculture, Education, Teaching, Research Service and Commercial Linkages.’ সংক্ষেপে কেআইএ বা নলেজ ইনিশিয়েটিভ অন এগ্রিকালচার (চলতি কথায় একেআই বা এগ্রিকালচারাল নলেজ ইনিশিয়েটিভ)। উক্ত চুক্তিপত্রের পর মনমোহন সিং বলেছিলেন, ‘ভারত সবুজ বিপ্লবের সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহযোগিতা পেয়েছিল। আশা করি কৃষি জ্ঞান উদ্যোগ চুক্তিটি ভারতে দ্বিতীয় সবুজ বিপ্লবের দ্যোতক হবে…।’
প্রকাশ্যে এল দেশীয় আমলাতান্ত্রিক উন্নয়নের সঙ্গে ভিনদেশী নিয়ন্ত্রণের আর বেসরকারি সংগঠনের মানবিক পুঁজির সঙ্গে অবাধ পুঁজির লোলুপতার অদৃশ্য দ্বৈরথ। তবে, এ সময়ে যে ঘটনা আমাদের কিছুটা হতচকিত করল—তা হলো খাদ্য বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টের রায় এবং তাতে সরকারের প্রতিক্রিয়া। এমনিতেই এদেশে রাজনৈতিক ও আমলাতান্ত্রিক কলাকৌশলে ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে যখন ফসল কেনা হয় তখন চাষির কাছে আর ফসল থাকে না। তা কেনা হয় বিভিন্ন কায়দায় মজুতদারের থেকে। হয়তো দেখানো হয় ক্ষুদ্র চাষির থেকেই তা কেনা হয়েছে। ফসল ওঠার মুহূর্তে ফসলের দাম থাকে সব থেকে কম, মজুতদার তা কিনে হয়তো সরকারকেই তুলনায় উচ্চমূল্যে (সহায়ক মূল্য) বিক্রি করে উদ্বৃত্ত মূল্যটি ভোগ করে। (২০১০ সালে পশ্চিমবঙ্গে ধান ও আলু কেনা নিয়ে এমন অনেক কেলেঙ্কারি সামনে এসেছে।) তারপর মূল্যবৃদ্ধিতে মানুষ যখন জর্জরিত তখনও সেই মজুত খাদ্য বিক্রি বা বণ্টন না করে গুদামে পচানো হয়েছিল। হয়তো সরকারি জোগান বাড়লে যদি মুদ্রাস্ফীতি কমে, তবে মজুতদারদের লাভ কমতে পারে—এই ছিল আশঙ্কা!
এর ঠিক বিপরীত একটা ছবি আমরা দেখি, এ সময়ে, ২০২২ সালে, হিমঘরের অভাবে পশ্চিমবঙ্গে হুগলি বা নদিয়া জেলার চাষিরা প্রায় সর্বস্বান্ত হয়েছেন, চাষের পর প্রাপ্য পেঁয়াজের দামে। একইরকম ভাবে চাষিরা আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন মহারাষ্ট্রে, পাইকারি মূল্য কমে যাওয়ায়। প্রতিকুল আবহাওয়ার সঙ্গে যেমন কৃষককে যুঝে যেতে হয়, তেমনি উপায়হীন আপস করতে হয় জমির লিজ, ঋণের চড়া সুদের পাশাপাশি সার ও কীটনাশকের কালোবাজারি ইত্যাদির সঙ্গেও। বলা বাহুল্য এই পরিস্থিতিতে সরকারি কৃষিবিল আর সহায়ক-মূল্যের কার্যকারিতা নিয়ে সংশয় থেকেই যায়।
বিশ্ব অর্থনীতির পরিসরে জ্বালানি নিয়ে, পরিবহন জ্বালানির দামের রাজনীতি অনেকদিন থেকেই আলোচকদের আলোচনার কেন্দ্রে। যার জন্য খাদ্যশষ্যর চাষ কমে পৃথিবীব্যাপী দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা ব্যক্ত করছেন তাঁরা। বলা বাহুল্য এদেশের পরিবহন ক্ষেত্রে জ্বালানি হিসেবে সবথেকে বেশি ব্যবহৃত হয় পেট্রোল ও ডিজেল। ২০০২ সালে উদারীকরণের শর্ত মেনে প্রথমেই নিষ্ক্রিয় করা হলো এপিএম বা অ্যাডমিনিস্টার্ড প্রাইস মেকানিজ্মকে। যদিও বাস্তবে দেখা গেল তৈলক্ষেত্রে উদারীকরণের ছোঁয়া বাঁচিয়ে সরকারি নিয়ন্ত্রণের ফাঁস আলগা হওয়া তো দূরের কথা আরও যেন চেপে বসল। পেট্রোপণ্যের মূল্য নির্ধারণ শুরু হলো আইপিপি বা ইমপোর্ট প্যারিটি প্রাইসিং সূচকে। কেরোসিন এবং এলপিজি পিডিএস বা পাবলিক ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম মারফত।
এপিএম পূর্ববর্তী পর্যায়ে পেট্রোপণ্যের আন্তর্জাতিক মূল্যের সঙ্গে দেশজ উৎপাদকের উৎপাদিত পেট্রোপণ্যের মূল্যের সামঞ্জস্য বিধানে নানারকম সূচক নির্ভর এক গড় মূল্য নির্ধারণ করা হত। এপিএম পরবর্তী পর্যায়ে দেশ-বিদেশ সব এক হয়ে গেল। বলা হলো, নিয়ম অনুযায়ী আন্তর্জাতিক মূল্যমান বিচারে ওএমসি বা অয়েল মার্কেটিং কোম্পানি স্বাধীন ভাবে ঠিক করবে পেট্রোল ডিজেলের দাম। কিন্তু কার্যত তা হলো না। ২০০৪ সালে সরকার এক প্রাইস ব্যান্ড চালু করল। এই ব্যবস্থায়—আন্তর্জাতিক বাজারে গত পনেরো দিনের পেট্রোপণ্যের গড় দামের ভিত্তিতে আইপিপি সূচক অনুযায়ী ওএমসি দেশীয় বাজারে পেট্রোল এবং ডিজেলের খুচরো মূল্য নির্ধারণ করে থাকে। বিনিময় মূল্যের সঙ্গে জুড়ল কস্ট অ্যান্ড ফ্রেইট—যা ধরা থাকল ব্যান্ড প্রাইসের সঙ্গে। যার মান গত তিন মাসের আন্তর্জাতিক মূল্যের চক্রাকার হ্রাসবৃদ্ধির গড়ের থেকে দশ শতাংশ বেশি বা কম। তাই নয়, গত এক বছরের গড়ের সঙ্গেও সেই মূল্যকে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা চাই। পরিবর্তিত পরিস্থিতে যদি কোনোভাবে এই প্রাইস ব্যান্ডকে ভাঙতে হয় তবে তা হবে অর্থ মন্ত্রকের মাধ্যমে। ক্রেতার ঘাড়ে মূল্যবৃদ্ধির পুরোটা না চাপিয়ে তৈল ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রক এক্সাইজ ডিউটিকে কেবল কিঞ্চিৎ লাঘব করতে পারে।
এই অবস্থায় দেশীয় উৎপাদকরা চাইলেন অশোধিত পেট্রোপণ্যের পুরোটাই বাইরে থেকে আমদানি করতে। কারণ তাতে আমদানি শুল্কের বা উৎপাদন খরচের ব্যাপার বিশেষ নেই বরং আমদানির পর পরিশোধিত পেট্রোপণ্য ভারতের বাজারে আন্তর্জাতিক মূল্যে বিক্রির সুবিধে। আর হলো-ও তাই। কেননা আমেরিকা মহারাষ্ট্র বা গুজরাত দখল করল না। কোনো অভাবিত কৃত্রিম তৈলসংকট তৈরি হওয়ার পরিস্থিতি ছাড়াই শুধুমাত্র আন্তর্জাতিক স্তরে দাম বাড়ার অজুহাতে সরকারি বেসরকারি তৈল উৎপাদকরা ন্যূনতম বিনিয়োগ ছাড়াই নির্বিরোধ মুনাফার মালিক হলো।
গরিবি হঠাও: আত্মনির্ভরতার এক ধাপ:
কিন্তু প্রশ্ন হলো, মূল্যবৃদ্ধি হলে উৎপাদকের লাভ কী, তার তো বিক্রি কমে যাবে? তা ঠিক। তবে, জীবনধারণের প্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্যবৃদ্ধি যে হারে বাড়ে, চাহিদা সে হারে কমে না। মানে, এ ধরনের পণ্যের চাহিদা-রেখা অস্থিতিস্থাপক। তাই, দাম বাড়লেও মেট আয় বা টোটাল রেভেনিউ বেড়ে যায়। প্রয়োজনীয় পণ্য নিয়ে আগাম বাণিজ্য বা ফাটকা তাই আকর্ষণীয়।
বিভিন্ন লাভজনক সরকারি সংস্থার শেয়ার বেচে যে অর্থাগম হলো তা দিয়ে নতুন শিল্প কিছু কী স্থাপিত হলো, নাকি তা গেল পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপের পদসেবায়? অনেক ঢাকঢোল বাজিয়ে সরকার একশো দিনের কর্ম প্রকল্প চালু করল। বাম-ডান সব দল এই ‘আবিষ্কার’-এর মর্যাদা দাবি করে। সেই বিপুল টাকা (নয়ছয় বাদ দিয়ে) যখন শ্রমিকের হাতে গেল তা সে ধরে রাখতে পারল না, মূল্যবৃদ্ধির কৃষ্ণগহ্বর তা চুষে নিল। অর্থাৎ গরিবের হাত ঘুরে সেই টাকা পৌঁছল কৃষি ও ভোগ্য পণ্যের ফাটকা ব্যবসায়ীর ভাণ্ডারে! এ কী নিছক সমপাতন, নাকি কাউকে ঘুরপথে ‘পাইয়ে দেওয়া’? অতি উচ্চ সহায়ক মূল্য ঘোষণাও সেই কারণেই একই সন্দেহ জাগায়।
তথ্য হিসেবে এগুলি আর আমাদের কাছে তেমন অজানা নয়। কিন্তু আশ্চর্যের এই যে, তথ্যগুলি এতটাই পরস্পর বিরোধী যে কার্যকারণের গভীরতাকে অনুধাবন করতে গিয়ে ভ্রূ-পল্লব শিয়রে ওঠে। কর্মব্যস্ত ২০১৮-১৯ আর্থিক বর্ষে যেখানে জাতীয় গড় আয় ছিল ৬.১ শতাংশ। ২০২০-২১ আর্থিক বর্ষে একদিকে যখন অতিমারির কবলে থমকে থাকা দেশে কর্মহীন, আয়হীন মানুষের সংখ্যাবৃদ্ধি সেখানে জাতীয় গড় আয় বেড়ে হলো ৮.৭ শতাংশ। আবার সেইসময়েই প্রকাশিত হয় গ্লোবাল হাঙ্গার ইনডেক্স। যা জানান দেয়, ভারতবর্ষ আসলে অপুষ্টিতে ভুগতে থাকা একটি দেশের নাম। পরিস্থিতি অবশ্য ২০১০ সালেও উল্লেখযোগ্য কিছু ছিল না।
নব্য পদার্থ বিজ্ঞানে বস্তু ও শক্তি এবং স্থান ও কাল আপেক্ষিক। অর্থনীতি বিজ্ঞান হয়ে উঠতে পারেনি, কিন্তু বস্তু-শক্তি, স্থান-কালের চাপে ও টানে তারও বেশ আঁকুপাঁকু অবস্থা। দ্রব্যের আকাঙ্ক্ষাকে ঘিরে যে শাস্ত্রের বিকাশ তা এখন ‘শক্তি’র দখলদারি পেতে মত্ত। অন্যদিকে, স্থান (মানচিত্রের) দখল যখন শেষ তখন ‘কাল’-এর উপর দখলদারি বিস্তৃত করা ছাড়া উপর কি? বর্তমান স্থান-কালের বিন্দুতে দাঁড়িয়েই যাতে ভবিষ্যতের ‘ট্রেডিং’-টা সেরে ফেলা যায়। অর্থ-পুঁজির ক্রমস্ফীতির আকাঙ্ক্ষাকে ধারণ করতে গিয়ে বর্তমান আত্মসাৎ করছে ভবিষ্যতকে! বর্তমানে দাঁড়িয়ে ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি বিক্রি হচ্ছে—এটাই ফাটকা! ভবিষ্যতের লাভের ফাটকা সম্ভাবনাকেও ‘পণ্য’ হিসাবে বিবেচনা করা হচ্ছে।
২০০৮ সালের বিশ্বের সর্ববৃহৎ আর্থিক মন্দার পরেও হঠাৎ যেভাবে তেজিয়ান হয়ে উঠল ভারতের শেয়ার (ফাটকা) বাজার। সেই বাজারকে বজায় রাখতে হলে, ‘বেসরকারিকরণ সময়ের দাবি!’ ইত্যাদি বলে তো ক্রমাগত শেয়ার মূল্য (এবং ইনডেক্স) বৃদ্ধি করে যেতে-ই হবে।
প্রচ্ছদচিত্র ও অন্য ছবি সৌজন্য: www.needpix.com