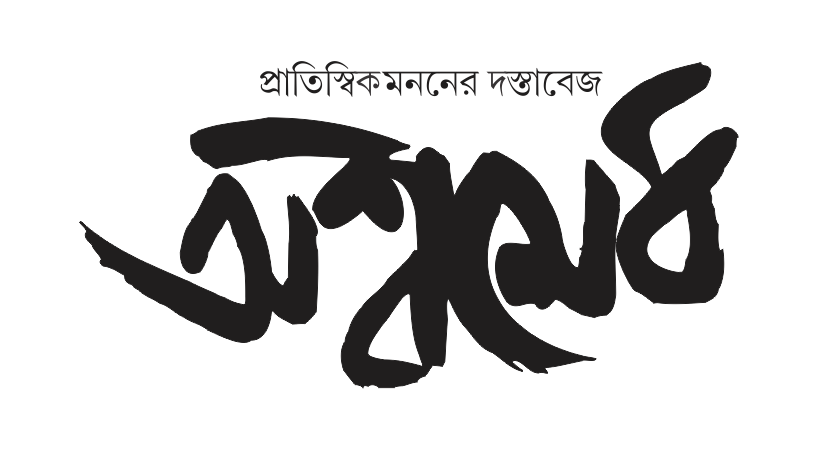২০১৯ সালের ৩১ মে নরেন্দ্র মোদী দ্বিতীয়বারের জন্য প্রধানমন্ত্রী পদে শপথ নিলেন। এর কিছুদিন পরে মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকে জমা পড়ল চারশো চুরাশি পাতার ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি রিপোর্ট (এনইপি ২০২০)। ২০১৭ সালে মন্ত্রক দ্বারা গঠিত ইসরোর প্রাক্তন অধিকর্তা কে. কস্তুরীরঙ্গন কমিটি এই রিপোর্ট তৈরি করেছে। নতুন শিক্ষানীতিতে পাঠক্রমে আমূল সংস্কারের কথা বলা হয়েছে। বর্তমানে চালু নিয়মনীতি যা ১৯৮৬ সালে গৃহীত হয়েছিল, ১৯৯২ সালে তা পরিবর্তিত হয়েছে। এরপর প্রায় তিন দশক বাদে এই উদ্যোগ।
আলোচনায় ঢোকার আগে রবীন্দ্রনাথের ‘শিক্ষার হেরফের’ প্রবন্ধের কিছু অংশ উদ্ধার করা যাক পরবর্তী আলোচনার সুবিধার জন্য। তিনি লিখেছিলেন—“অত্যাবশক শিক্ষার সহিত স্বাধীন পাঠ না মিলাইলে ছেলে ভালো করিয়া মানুষ হইতে পারে না…কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের হাতে কিছুমাত্র সময় নাই। যত শীঘ্র পারি বিদেশীয় ভাষা শিক্ষা করিয়া পাস দিয়া কাজে প্রবিষ্ট হইতে হইবে। কাজেই শিশুকাল হইতে ঊর্দ্ধশ্বাসে দ্রুতবেগে, দক্ষিণে বামে দৃকপাত না করিয়া পড়া মুখস্থ করিয়া যাওয়া ছাড়া আর কোনো কিছুর সময় পাওয়া যায় না…আমরা যতই বি. এ. এম. এ. পাস করিতেছি, রাশি রাশি বই গিলিতেছি বুদ্ধিবৃত্তিটা তেমন বেশ বলিষ্ঠ এবং পরিপক্ক হইতেছে না।” বাস্তবিক এদেশে প্রচলিত শিক্ষা রাশিরাশি নোট মুখস্থ করে ডিগ্রি অর্জনের যন্ত্র ছাড়া আর কিছু হয়ে ওঠেনি। পড়ুয়ার মৌলিক চিন্তাভাবনা, তার সর্বাঙ্গীন বিকাশে সহায়ক হয়ে ওঠেনি।
শিক্ষা সম্পর্কে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বা ভদ্রলোকদের প্রকৃত মনোভাব সর্বদা ইংরেজি শিক্ষার দিকেই ছিল। এটি চরিত্রগতভাবে ঔপনিবেশিক। সে কারণে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের সময়ে কংগ্রেসি মন্ত্রীসভা পরিচালিত রাজ্যগুলিতে শিক্ষা বিষয়ক কমিটির সুপারিশ মানা হয়নি। স্বাধীনতার পরেও দেশে যেসব শিক্ষা কমিশন বা কমিটিগুলো তৈরি হয়েছে তারাও শিক্ষাব্যবস্থায় চরিত্রগত কোনো পরিবর্তন আনতে পারেনি। স্বাধীনতার পরে দেশে মাধ্যমিক এবং উচ্চশিক্ষার ওপর যে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল, সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার ওপর তা হয়নি। ফলে আমাদের পিরামিডকৃতি শিক্ষাব্যবস্থার ভিত্তি অর্থাৎ প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে অবহেলা দেখা গেছে। স্বাধীনতার পরে প্রথম শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়েছিল ১৯৪৯ সালে সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের সভাপতিত্বে। মূল নজর ছিল উচ্চশিক্ষা বিষয়ে। ১৯৫২-৫৩ সালে লক্ষ্মণস্বামী মুদালিয়রের নেতৃত্বে মাধ্যমিক শিক্ষা বিষয়ে দ্বিতীয় শিক্ষা কমিশন তৈরি হয়। তৃতীয় কমিশনের বিচার্য ছিল সর্বস্তরের শিক্ষা যা গঠিত হয়েছিল ১৯৬৪ সালে ডি. এস. কোঠারি বা দৌলত সিংহ কোঠারির নেতৃত্বে। প্রসঙ্গত স্মরণীয় ত্রিশ ও চল্লিশের দশকে জাতীয় শিক্ষা আলোচনার মূল আলোচ্য ছিল প্রাথমিক শিক্ষা, বিশেষত বুনিয়াদী শিক্ষা। আরেকটি কথা এ প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার ভারতে পঞ্চাশের দশক থেকেই ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের চাহিদা বেড়েছে এবং এখন যা মহামারীর আকার নিয়েছে। অর্থাৎ মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে এর প্রত্যক্ষ সম্পর্ক রয়েছে বলা যেতে পারে।
এই পটভূমিতে আমাদের বিচার করতে হবে কস্তুরীরঙ্গন কমিটির সুপারিশ যা জাতীয় শিক্ষানীতি হিসাবে গৃহীত হয়েছে, ২৯ জুলাই ২০২০, মন্ত্রীসভায়। এবং এই রিপোর্টের ভাষায় শিক্ষা আসলে ‘কোয়াসি পাবলিক ওড’। সে কারণে সকলের জন্য শিক্ষার মৌলিক অধিকারকে নিশ্চিত করার কোনো দায়িত্ব সরকার নেবে না। নতুন শিক্ষানীতির খসড়ায় বর্তমান পরীক্ষা পদ্ধতির পুনর্গঠন, শিক্ষক প্রশিক্ষণে জোর দেওয়া, শিক্ষা নিয়ন্ত্রক কাঠামোর পুনর্বিন্যাস, জাতীয় রাষ্ট্রীয় শিক্ষা আয়োগ গঠন, শিক্ষায় সর্বজনীন বিনিয়োগ, প্রযুক্তির ব্যবহারের নিশ্চয়তা এবং বৃত্তিমূলক ও বয়স্ক শিক্ষার প্রসারের ওপর নজর দেওয়া হয়েছে। একটু বিস্তৃতভাবে আমরা আলোচনা করব মূল প্রেক্ষিতের যে মৌলিক পরিবর্তন আসছে তার ওপরে।
জাতীয় শিক্ষানীতির আমূল পরিবর্তনকামী এই দলিলের আলোচনায় আমরা দেখব, আগেকার শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টগুলির সঙ্গে তো বটেই, ১৯৮৬ সালের নয়া শিক্ষানীতি এবং তার প্রেক্ষিতে ১৯৯২ সালের রিপোর্টের সঙ্গেও এর মূলগত পার্থক্য রয়েছে। কারণ এখানে আগেকার রিপোর্টগুলির মূল্যায়ন করে তার সুবিধা অসুবিধা বিচারের ভিত্তিতে প্রয়োজন মতো গতিপথ ঠিক করা নয় বরং আপাদমস্তক সংস্কার করে নতুন দিকে যাওয়ার প্রচেষ্টা। কারণ রিপোর্ট অনুসারে স্বাধীনতা-উত্তর কালে শিক্ষাক্ষেত্রে ‘সমতা’ আনার জন্য নানা পদক্ষেপ নেওয়া হলেও আগের শিক্ষানীতিগুলি কোনো উচ্চমানের প্রতিযোগিতায় সামিলই হয়নি। সে কারণে যে প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে তোলা হবে তা এই দলিলে বলা হয়েছে।
নতুন শিক্ষানীতির রূপায়ণের জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে সরাসরি প্রধানমন্ত্রীর নিয়ন্ত্রণাধীনে শিক্ষার সফল রূপায়ণের জন্য থাকবে জাতীয় স্তরের সর্বোচ্চ কমিশন—রাষ্ট্রীয় শিক্ষা আয়োগ (RSA)। এটি গঠনের পাশাপাশি প্রতিটি রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রীর নিয়ন্ত্রণাধীন রাজ্য শিক্ষা আয়োগ তৈরি করা হবে। এর কাজ হবে রাষ্ট্রীয় আয়োগের সিদ্ধান্তগুলো রূপায়িত করা। রাজ্যের নিজস্ব কোনো ক্ষমতা থাকবে না। রাষ্ট্রীয় শিক্ষা আয়োগে নিয়োগ এবং কাজকর্ম পরিচালনার জন্য রাষ্ট্রীয় শিক্ষা আয়োগ অ্যাপয়েন্টমেন্ট কমিটি (RSAAC) তৈরি করা হবে যার সদস্যরা হবেন প্রধানমন্ত্রী নিজে, চিফ জাস্টিস অফ ইন্ডিয়া, লোকসভার স্পিকার, বিরোধী দলনেতা এবং কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী। শিক্ষানীতির ২৩ নম্বর অধ্যায়ে বলা হয়েছে প্রস্তাবিত ন্যাশনাল হায়ার এডুকেশন রেগুলেশন অথরিটি, ন্যাক, প্রস্তাবিত জেনেরাল এডুকেশন কাউন্সিল, প্রস্তাবিত হায়ার এডুকেশন কাউন্সিল, এনসিইআরটি, এনআইপিএএ এবং প্রস্তাবিত রিসার্চ ফাউন্ডেশনের পদাধিকারীদের নিয়োগ করবে—আরএসএ। অর্থাৎ গোটাটাই হবে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণাধীনে। ১৯৭৬ সালে ৪২তম সংবিধান সংশোধনীতে শিক্ষাকে শুধুমাত্র রাজ্যের অধীনে না রেখে একে যুগ্ম তালিকায় আনা হয় দেশের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকে গুরুত্ব দিয়ে এবং বলা হয়েছিল রাজ্যগুলি যাতে শিক্ষার মানোন্নয়নে কেন্দ্রের সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করে।
নতুন শিক্ষানীতিতে খোলাখুলিভাবে শিক্ষার বেসরকারিকরণকে সমর্থন করা হয়েছে। ২০০৯ সালে চালু হওয়া শিক্ষার অধিকার আইনের মধ্যে অনেক ফাঁকফোকর ছিল। যার ফলে শিক্ষার বাজারিকরণ অনেক গতিশীল হয়েছে। নতুন শিক্ষানীতিতে বেসরকারি উদ্যোগকে ‘মানবহিতৈষী’ বলা হয়েছে। এবং তাকে রূপায়ণের জন্য পাঠ্যপুস্তক পরিকল্পনা, মূল্যায়নের বোর্ড প্রভৃতিতে ব্যক্তির হস্তক্ষেপ নিশ্চিত করার ব্যবস্থা রয়েছে। পিছিয়ে পড়া অঞ্চলগুলিতে বেসরকারি পুঁজির ওপর নির্ভর করে গড়ে তোলা হবে স্পেশাল এডুকেশন জোন। অর্থাৎ স্পেশাল এডুকেশন জোন-এর পর শিক্ষাতে ‘এসইজেড’ মডেল চালু হবে। যদিও বলা হয়েছে আরটিই (রাইট টু এডুকেশন অ্যাক্ট)-কে প্রাক্-বিদ্যালয় থেকে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত বিস্তৃত করা হবে।
বোঝাই যাচ্ছে আগের গৃহীত শিক্ষানীতিগুলির সঙ্গে নতুন শিক্ষানীতির মৌলিক প্রভেদ রয়েছে যার প্রধানতম উদ্দেশ্য শিক্ষায় ‘সমতা’ আনা বা শিক্ষার্থীর ‘সর্বাঙ্গীন বিকাশ’ এর ভাবনার অবকাশ না রেখে ‘উচ্চমানের প্রতিযোগিতা’য় পাল্লা দেওয়ার উপযোগী শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলা। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় চিরকাল বৈষম্য প্রকটভাবেই ধরা পড়েছে, যার পরিণতিতে শিক্ষা একটা বড়ো অংশের মানুষের কাছে অধরাই থেকে গেছে। এই শিক্ষানীতিতে ‘অন্তর্ভুক্তি’র কথা বলা হলেও সম-অধিকারের বিষয়টি এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। দলিত, আদিবাসী, ধর্মীয় ও অন্যান্য সংখালঘু এবং নারীদের সাংবিধানিক অধিকার গুলোকে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। শিক্ষাক্ষেত্রে ‘উচ্চ মান’কে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়ার জন্য বলা হয়েছে একুশ শতকের ‘নলেজ সোসাইটি’র এবং একই সঙ্গে ভারতীয় শিক্ষা ঐতিহ্যের সঙ্গে সংযোগস্থাপন প্রয়াজন। যদিও তাতে রূপায়ণের বিষয়টি ধোঁয়াশা হয়ে আছে। উৎকর্ষ মূলক জ্ঞানসমৃদ্ধ সমাজ গঠনের ভাবনার কথা বলার পাশাপাশি ঘোষণা করা হয়েছে শিক্ষার সর্বজনীন প্রসারের। কিন্তু সকলের জন্য শিক্ষা কর্মসূচীর সফল রূপায়ণের জন্য কোনো পদক্ষেপের উল্লেখ নেই। ২০০১ সালে শুরু হয়েছিল সর্ব শিক্ষা অভিযান। সেই সময় সরকার এলিমেন্টারি এডুকেশনকে সর্বজনীন করার জন্য নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে, ৬-১৪ বছরের ছেলেমেয়েদের বিদ্যালয়ে আনার উদ্যোগ নিয়েছিল। এ কারণে এই অভিযানের আওতায় পার্শ্বশিক্ষকও নিয়োগ করা হয়। যা কেন্দ্র-রাজ্যের যৌথ উদ্যোগ বলা যায়। প্রস্তাবিত নতুন শিক্ষানীতি (এনইপি ২০২০)র খসড়ায় পার্শ্বশিক্ষক, শিক্ষাবন্ধু ইত্যাদি ব্যবস্থা তুলে দেওয়ার কথা বলা হয়েছে।
নতুন শিক্ষানীতিতে পিছিয়ে পড়া দরিদ্র ঘরের পড়ুয়াদের জন্য বেসরকারি স্কুলে সংরক্ষণের বিষয়টি বাতিল করা হয়েছে। স্কুলের ন্যূনতম পরিকাঠামোকে শিথিলতর করে গুরুকুল-পাঠশালা-মাদ্রাসা-বিকল্প বিদ্যালয় বা হোম স্কুল ইত্যাদি গুরুত্বহীন প্রতিষ্ঠান এবং স্বেচ্ছাসেবক ভিত্তিক ব্যবস্থাকে স্বীকৃতি দেবার কথা বলা হয়েছে। বিদ্যালয় স্তরে মেয়েদের শিক্ষা নিয়ে কিছু কথা থাকলেও উচ্চশিক্ষা স্তরে প্রায় কিছুই নেই। ভারতের সংবিধানে সমাজের পিছিয়ে পড়া অংশের শিক্ষার্থীদের শিক্ষাঙ্গনে প্রবেশের সুযোগ দেওয়ার জন্য যে সংরক্ষণ প্রথা চালু ছিল এই দলিলে তার কোনো উল্লেখ করা হয়নি। এটি ছিল ঐতিহাসিকভাবে পশ্চাদপদ শ্রেণির প্রাথমিক শিক্ষাঙ্গনে প্রবেশাধিকারের সহায়ক একটি গণতান্ত্রিক উদ্যোগ। এদের মধ্যে মেয়েরাও রয়েছেন। দেশে শিক্ষার বিস্তারের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের অনুপাত দেখলেই তা বোঝা যায়। মজার বিষয় হলো নারী সহ সমাজের বিভিন্ন অংশ যারা শিক্ষার আঙিনায় আজও দূরে রয়েছে, তাদের পশ্চাদ্পদতার কারণ হিসাবে কুসংস্কারকেই দায়ী করে মন্তব্য করা হয়েছে। অথচ সেইসব সংস্কার অন্ধবিশ্বাসকে ঠেকানোর কোনো কথা নেই। ফলে নারীশিক্ষার বিষয়টি চরমভাবে উপেক্ষিত হবে বলে আশঙ্কার সঙ্গত কারণ রয়েছে।
সংক্ষিপ্ত এই রূপরেখার প্রেক্ষিতে আমরা এখানে মূলত বিদ্যালয় ও প্রাক্-বিদ্যালয় শিক্ষার বিষয়টিই আলোচনা করব, উচ্চশিক্ষার বিষয়টি পরবর্তী আলোচনার জন্য তোলা রইল। নতুন শিক্ষানীতির মাধ্যমে বিদ্যালয় শিক্ষায় যে পন্থায় এবং কারণে অবাধ বেসরকারিকরণের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে তাতে বলা হয়েছে—পরিকাঠামোগত উন্নয়নের অভাব। যথেষ্ট পরিমাণ শিক্ষকের অভাব ও অন্যান্য কাঠামোগত সমস্যাকে কার্যত অস্বীকার করে ‘লার্নিং আউটকাম্স’ ‘পেডাগগি’ আর ‘কারিকুলাম’ এর কথা বলা হয়েছে। শিক্ষার্থীরা কতটা শিখল ‘লার্নিং আউটকাম্স’ তা পরিমাপ করে। কিন্তু এটাও সত্যি, যে সব সময় তা সফল হয় না। পর্যাপ্ত পরিকাঠামো ছাড়া ‘পেডাগগি’ ও ‘কারিকুলাম’ এর ওপর ভিত্তি করে বিদ্যালয় শিক্ষার গুণগত পরিবর্তন করা সম্ভব বলে পলিসিতে যে মন্তব্য করা হয়েছে তার সাপেক্ষে বেসরকারি ক্ষেত্রকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। বর্তমানের বাজার-চালু ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে ওঠা ব্যবসায়ী-বিদ্যালয়গুলিকে বা শিশু/কিশোর কিশোরীদের জন্য কম্পিউটার ভিত্তিক শিক্ষণ সামগ্রী দেখলেই আমরা বুঝতে পারব, কীভাবে পেডাগগি আর কারিকুলাম ভাঙিয়ে ব্যবসা করা যায়। সামান্য অপ্রাসঙ্গিক হবে হয়তো তবু এক্ষেত্রে উল্লেখ করাই যায়, এদেশে বিদ্যালয়ের (বলাবাহুল্য বেসরকারি) পড়ুয়া ছাত্রছাত্রী মাত্রই যেন হবে তথ্যপ্রযুক্তির দক্ষ কর্মী। বিগত কয়েক বছরে সেভাবে না হলেও এই অতিমারীর দিনে আচমকা এক লাফে বেড়ে গিয়েছে অনেকটাই কিশোর-কিশোরীদের কোডিং বা প্রোগ্রামিং শেখানোর গুণাগুণ সম্বলিত বিজ্ঞাপণের সংখ্যা। ‘আত্মনির্ভর’ দেশে ‘স্বদেশী’ প্রতিষ্ঠানে এটি শেখাই যে এ মুহূর্তে ছেলেমেয়েদের একমাত্র কাজ সে-কথা বলা হচ্ছে বেশ জোর দিয়েই। যেন সেটিই জীবনে সাফল্যের একমাত্র চাবিকাঠি। অমনোযোগীর মনোযোগী কিংবা মনোযোগীর আরও বেশি মনোযোগী হয়ে ওঠার সে বয়ান শোনাচ্ছে সমাজের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিবর্গ, পড়ুয়ার বাবা-মা এমনকি পড়ুয়া স্বয়ং।
বিভিন্ন সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে পশ্চাদ্পদ ছেলেমেয়েদের শিক্ষাদান যা আগে সরকারিভাবে বাধ্যতামূলক ছিল। তা বর্তমান শিক্ষানীতিতে শিক্ষা-ব্যবসায়ীদের ‘শুভবুদ্ধি’র ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। অবৈতনিক শিক্ষার ব্যবস্থা করার জন্য বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোয় যে পঁচিশ শতাংশ আসন সংরক্ষিত রাখার ব্যবস্থা ছিল শিক্ষার অধিকার আইন অনুসারে, এই নীতিতে তাকে পুনরায় পর্যালোচনা করে বাতিলের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। আগামী দশ বছরের মধ্যে, ৩-১৮ বছর বয়সিদের বিনামূল্যে বাধ্যতামূলক বিদ্যালয় শিক্ষা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে নতুন নীতিতে। এর আগে যা ছিল ৬-১৪ বছর। এর পাশাপাশি নীতিতে যখন বলা হয়—“স্বাধীনতার পর থেকে দশকের পর দশক ধরে আমরা শিক্ষাকে সমাজের প্রতিটি স্তরে সমানভাবে পৌঁছে দেওয়া নিয়েই শুধু ভেবেছি, শিক্ষার গুণমান নিয়ে ভাবিনি।” অর্থাৎ ‘শিক্ষার গুণমান’ এর দোহাই দিয়ে শিক্ষাকে সমাজের সমস্ত শ্রেণির কাছে পৌঁছে দেবার দায়িত্বটা সরকার/রাষ্ট্র ধীরে ধীরে ঝেড়ে ফেলবে।
কোঠারি কমিশন ‘নেবারহুড স্কুল’ এর ভাবনাকে সরকারি শিক্ষাব্যবস্থায় মর্যাদা দিতে বলেছিল। কারণ সব পড়ুয়ার ঘরের কাছে ভালো, সহজে ভর্তি হওয়া যায় এমন সরকারি বিদ্যালয় থাকলে বেসরকারি বিদ্যালয়ে বেশি খরচ করে পড়াতে যাবে না অভিভাবকেরা। অবশ্য এ ভাবনা কখনোই বাস্তবায়িত হয়নি। বর্তমান শিক্ষানীতিতে যা একেবারেই অপ্রাসঙ্গিক হয়ে গেছে। কোঠারি কমিশন প্রস্তাবিত ‘কমন টাইপ স্কুল’ এর ভাবনাও এর আগে রূপায়িত হয়নি, এখন তো সে ভাবনার কথা ভাবাই বাতুলতা। বরং যা দেখা যায়, সকলের জন্য সাধারণ বিদ্যালয়ের ধারণাকে দূরে সরিয়ে, ক্রেতাদের ক্রয়ক্ষমতার ভিত্তিতে, বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের জন্য আলাদা মানের বিদ্যালয় তৈরির ধারণাকেই প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছে যা সামাজিক-অর্থনৈতিক বৈষম্যকে আরও বাড়িয়েই তুলবে। অর্থাৎ নতুন শিক্ষানীতি ‘শিক্ষা আমাদের মৌলিক অধিকার’—এই ভাবনার মূলেই আঘাত করেছে। শিক্ষা নিয়ে আমাদের যে ভাবনা স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে গড়ে উঠেছে পর্যায়ক্রমে, বর্তমান শিক্ষানীতিতে তার মৌলিক পরিবর্তন করার ফলে স্বভাবতই আমাদের চিন্তায় পরিবর্তন ঘটবে। বর্তমান নীতি অনুযায়ী প্রাক্-বিদ্যালয় ও বিদ্যালয় শিক্ষার বিষয়টি বিবেচনা করলে দেখব, এই ক্ষেত্রটি পুনর্গঠিত হবে মাধ্যমিক বা উচ্চ মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত। যেখানে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ছে বর্তমানে প্রচলিত (১০+২) কাঠামোটি। এই কাঠামোয় প্রাথমিক-উচ্চ প্রাথমিক-মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক (৩+১) এই চারটি পর্যায় ছিল। নতুন শিক্ষানীতিতে উচ্চ মাধ্যমিক বলে কিছু থাকবে না। তার বদলে প্রাক্-প্রাথমিক স্তর থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত যে নতুন পর্যায় বিন্যাসের কথা বলা হয়েছে, তা হলো—৫-৩-৩-৪। অর্থাৎ বয়স অনুসারে শিক্ষার্থীদের চারটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম ভাগে রয়েছে—পাঁচ বছরের মৌলিক স্তর। এই পর্যায়ে তিন বছর প্রাক্-প্রাথমিক, অর্থাৎ গ্রেড-১, তারপর গ্রেড-২। যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণি। দ্বিতীয় ভাগে—তিন বছরের প্রস্তুতিমূলক স্তর। যা গঠিত হবে তৃতীয় চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণিকে নিয়ে। তৃতীয় পর্যায়ে—তিন বছরের মধ্যম স্তর। এটি গঠিত হবে ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণিকে নিয়ে। চতুর্থ পর্যায় চার বছরের মাধ্যমিক স্তর। এর আওতায় থাকবে নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি।
এও বলা হয়েছে, মানের নিরিখে বা বিদ্যালয় পরিকাঠামোর ঘাটতি থাকা বিদ্যালয়ে, যেসব ক্ষেত্রে ছাত্র-শিক্ষকের সংখ্যা অল্প, সে সব বিদ্যালয়কে আরও উন্নত বা সক্ষম করে তোলা হবে। অথবা তাদের অপেক্ষাকৃত অন্য বড়ো বিদ্যালয়ের সঙ্গে সংযুক্ত করা হবে। কারণ এই ধরনের ছোটো ছোটো বিদ্যালয়ে অর্থ বিনিয়োগ করা অলাভজনক এবং সম্পদ ব্যবহারের ‘সাশ্রয়’ হয় না। বিদ্যালয় শিক্ষাকে এক ছাতার নীচে আনার জন্য এই ব্যবস্থার পাশাপাশি একটি নির্দিষ্ট এলাকায় অঙ্গনওয়াড়ি ও অন্যান্য যেসব কেন্দ্র থেকে এখন শিশুদের প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষা পাবার কথা সেগুলিকে এলাকার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সঙ্গে এবং প্রাথমিকটিকে উচ্চ বিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত করা হবে। এতে কোনো একটি এলাকায় বিদ্যালয় পরিচালনার প্রাথমিক ‘একক’ হিসাবে একেকটি বৃহৎ ‘স্কুল কমপ্লেক্স’ গড়ে উঠবে। অর্থাৎ এই ব্যবস্থায় থাকবে নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত একটি উচ্চ বিদ্যালয়, এবং আশপাশের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে প্রাক্-প্রাথমিক থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পঠনপাঠনের ব্যবস্থা করা হবে। কমপ্লেক্সে থাকবে অঙ্গনওয়াড়ি, বৃত্তিমূলক শিক্ষাকেন্দ্র থেকে বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র। খসড়ায় এও বলা হয়েছে যে, এটি হবে একটি আধা-স্বায়ত্তশাসিত একক যেখানে প্রাক্-প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক পর্যন্ত সুসংহত শিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে। বলা হয়েছে বিজ্ঞান-কলা-বাণিজ্যের মতো আলাদা আলাদা বিভাগে জ্ঞান সঞ্চয়ের বদলে বৃত্তিমূলক শিক্ষায় বেশি গুরুত্ব দেওয়া হবে।
প্রতিটি কমপ্লেক্সে শিক্ষক ছাড়াও একাধিক সমাজসেবী ও কাউন্সিলর নিয়োগ করা হবে যারা পড়ুয়াদের দেখভাল করবেন। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক কমপ্লেক্সের নেতৃত্ব দেবেন এবং সামগ্রিকভাবে এই ‘স্কুল কমপ্লেক্স ম্যানেজমেন্ট কমিটি’ ছাড়াও প্রতি বিদ্যালয়েই দশ-বারোজনের ম্যানেজমেন্ট কমিটি থাকবে। বলা হয়েছে, এসবের মাধ্যমে স্থানীয় মানুষের ‘স্বেচ্ছাসেবী’ ভূমিকা বাড়বে এবং বিদ্যালয়ের ওপর ‘জনসমাজের মালিকানা’র বোধ বাড়বে। ১৯৯৪ সালে গঠিত হয়েছিল রামমূর্তি কমিটি। শিক্ষা-শিক্ষক-সমাজের ভূমিকা/সম্পর্ক নিয়ে আলোচনার জন্য। সেই কমিটির রিপোর্টে যদিও শিক্ষকদেরই এগিয়ে এসে স্থানীয় জনসমাজের সঙ্গে ‘জীবন্ত’ যোগাযোগ গড়ে তোলার কথা বলা হয়েছিল। কমিটি এও সুপারিশ করেছিল ‘ফর্মাল’ বিদ্যালয় ব্যবস্থাকে এমন উদার ও মজবুত করে তুলতে হবে, যাতে নানানরকম ‘নন-ফর্মাল’ পদ্ধতি ব্যবহার করে তারা ব্রাত্যদেরও সরকারি শিক্ষার আঙিনায় টেনে আনতে পারে। বর্তমান শিক্ষানীতির খসড়ায় ঠিক এর বিপরীত পথে হেঁটে পিছিয়ে পড়াদের জন্য নিম্নমানের শিক্ষার আলাদা ব্যবস্থাকে কার্যত পাকাপাকিভাবে স্বীকৃতি দিতে চাওয়া হয়েছে।
শিক্ষক ঘাটতি, প্রশিক্ষিত শিক্ষকের অভাব-এর দিকে লক্ষ্য রেখে খসড়ায় বলা হয়েছে, শিক্ষককে শিক্ষা-সংক্রান্ত কাজের বাইরে অন্য কাজে লাগানো যাবে না। বি. এড. কোর্স হবে চার বছরের। উচ্চ মানের সিলেবাস ও ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের বিষয়টিতেও নজর দেওয়া হবে।
এখানে প্রতি বছর কমপক্ষে পঞ্চাশ ঘণ্টার জন্য বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও থাকবে। শিক্ষাদানের জন্য সংগঠিত শিক্ষক-গোষ্ঠী গঠনের বদলে সম্প্রদায়ের স্বেচ্ছাসেবী দলের ওপর সেই দায়িত্ব ছেড়ে দেওয়ার কথা বলা হয়েছে নতুন নীতিতে। অর্থাৎ তা বেসরকারি ব্যবস্থার আওতায় চুক্তিবদ্ধ চাকরিতেই পরিণত হবে। বেকারত্ব বৃদ্ধির সুযোগ নিয়ে সস্তায় চাকুরে নিয়োগ করে প্রাথমিক স্তরে ছেলেমেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থা করে তাদের শিক্ষার ভিতটাই দুর্বল করে দেওয়া হবে।
কারিকুলাম, টেক্সট বই থেকে শুরু করে শিক্ষক নিয়োগ পর্যন্ত গোটা ব্যাপারটা দেখভাল করার জন্য থাকবে—এসসিইআরটি বা স্টেট কাউন্সিল অফ এডুকেশনাল রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেনিং শীর্ষক বিভাগীয় দপ্তর। সরকারি আর বেসরকারি বিদ্যালয়ের সাধারণ গুণমান এবং অধ্যয়ন বিষয়ক নির্দিষ্ট মান বিচার করবে সংশ্লিষ্ট রাজ্যের স্টেট স্কুল রেগুলেটরি অথরিটি বা এসএসআরএ নামে গঠিত নতুন এক নিয়ন্ত্রক পর্ষদ। যে-কোনো প্রকারের শংসা প্রদান বা অ্যাক্রেডিটেশনও এই পর্ষদ দ্বারা পরিচালিত হবে। এই ব্যবস্থায় অন্যান্য পরিচালন পর্ষদ অর্থাৎ এসসিইআরটি ও এসএসআরএ প্রভৃতি সরাসরি আরএসএ বা রাষ্ট্রীয় শিক্ষা আয়োগের আওতায় থাকবে। অর্থাৎ বিদ্যালয় পরিচালনের ক্ষেত্রে বর্তমানের মতো রাজ্যস্তরের বা ডিপার্টমেন্ট অফ স্কুল এডুকেশন (ডিএসই) এর কোনো ভূমিকা আর থাকবে না। টেক্সট বই ইচ্ছেমতো ছাপানো থেকে শুরু করে শিক্ষক নিয়োগের পুরো বিষয়টি নিয়ন্ত্রিত হবে কেন্দ্র থেকে।
রেগুলেশনের ক্ষেত্রে সরকারি আর বেসরকারি বিদ্যালয়ে একই প্রক্রিয়া অনুসৃত হবে। উদ্দেশ্য স্পষ্ট, দুইয়ের মধ্যে অসম প্রতিযোগিতা সৃষ্টি করা। আর চূড়ান্ত লক্ষ্য সরকারি বিদ্যালয় (অলাভজনক) শিক্ষার বিলোপ ঘটানো। নতুন শিক্ষানীতিতে বলা হয়েছে কিছু শর্ত মানলেই বেসরকারি বিদ্যালয় এডুকেশনাল আউটকাম ভালো করার জন্য সরকারি অর্থ সাহায্য পাবে। বেসরকারি বিদ্যালয়গুলোর ফি নির্ধারণে কেন্দ্র বা রাজ্য হস্তক্ষেপ করবে না। প্রতি তিন বছরে একবার করে এসএসআরএ-র পর্যালোচনার ভিত্তিতে বেসরকারি বিদ্যালয়গুলো মূল্যবৃদ্ধির অনুপাতে নিজেদের ফি-ও বাড়াতে পারবে। অর্থাৎ সরকারি পরিকাঠামো, প্রশিক্ষণ সবই নিয়ে এবং সেই কাজ যথাযথ ‘মুনাফা ভিত্তিক’ না হলেও তা করার জন্য সরকারি সাহায্য পাবে বেসরকারি বিদ্যালয়গুলি।
খসড়া নীতিতে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে, বিদ্যালয় শিক্ষার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে শিক্ষার্থীদের জন্য তৃতীয়, পঞ্চম এবং অষ্টম শ্রেণিতে এসসিই বা স্টেট সেনশাস এগজামিনেশন এর ব্যবস্থা থাকবে। বোর্ডের পরীক্ষাতেও বদল আনা হবে। মাধ্যমিক স্তরের (নবম-দ্বাদশ) প্রতিটি বছরকে দুটি করে সেমেস্টারে ভাগ করে মোট আটটি সেমেস্টার থাকবে। প্রতিটি ভাগে ছাত্রছাত্রীরা পাঁচ থেকে ছয়টি বিষয় নিতে পারবে। বিষয় বেছে নেওয়ার ক্ষেত্রে নমনীয়তা থাকবে, যাতে ব্যক্তিগত আগ্রহ ও মেধার পূর্ণ বিকাশ হতে পারে। ভাষা শিক্ষা নিয়ে নতুন শিক্ষানীতিতে যে প্রস্তাব করা হয়েছে তা কার্যত মারাত্মক। এখানে হিন্দি ও সংস্কৃতের ওপর শুধু যে অত্যধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে তাই নয়, ভাষা শিক্ষা নিয়ে কোঠারি কমিশনের সুপারিশকে কার্যত অস্বীকার করা হয়েছে। কোঠারি কমিশনের বক্তব্য ছিল প্রাথমিক স্তরে তিনটি ভাষা শেখানোর চেষ্টা করলে দেখা যায় শিশুর মাতৃভাষার ওপর দখল কমে যায়। এবং শিশুর মানসিক বিকাশ ব্যাহত হয়। সেখানে মাতৃভাষার ওপর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছিল। বলা হয়েছিল পঞ্চম শ্রেণি থেকে বিভিন্ন পর্বে ধাপে ধাপে শিশু তিনটি ভাষা শিখবে তার আগে নয়। আর রামমূর্তি কমিটি বলেছিল, যদি স্থানীয় প্রধান ভাষা শিশুর মাতৃভাষা না হয় তবে মাতৃভাষার পরে তাকেই গুরুত্ব দিতে হবে। অর্থাৎ মাতৃভাষায় দক্ষতা অর্জনের পরেই অন্য ভাষা শিক্ষা। বর্তমান নীতিতে মাতৃভাষার গুরুত্ব নিয়ে অনেক কথা বলা আছে। উচ্চস্তরের মানুষদের ইংরাজির প্রতি আসক্তির নিন্দা রয়েছে কিন্তু তারপরেই বলা হয়েছে শিশুর ‘স্বাভাবিক’ বহুভাষা ‘আয়ত্ত’ (না নকল?) করার ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে প্রাথমিক স্তরেই তিনটি ভাষা শেখানোর পরিবেশ তৈরি করতে হবে। তৃতীয় শ্রেণি (অর্থাৎ প্রস্তাবিত প্রস্তুতিমূলক স্তর)তে পৌঁছোনোর আগেই তার এই তিনটি ভাষায় কথা বলতে পারা এবং প্রাথমিক স্তরের বই পড়তে পারা চাই। তৃতীয় শ্রেণি থেকে অন্য দুটি ভাষায় সে লিখতেও শুরু করবে। মুখে স্বীকার না করলেও সর্বত্র যে ইংরাজি থাকবে তা বলাই বাহুল্য। ভাষা শিক্ষার এই পদ্ধতি কার্যত শিশুহত্যা। এটি বিজ্ঞান সম্মত ভাষাতাত্ত্বিক ভাবনার বিরোধী।
লক্ষ লক্ষ শিশু, যারা নিজেদের বাড়িতে ও সমাজে মাতৃভাষা ছাড়া আর কিছু শোনে না, তাদের প্রাক্-প্রাথমিক স্তর থেকে বিদ্যালয়ে কৃত্রিমভাবে ভাষা শিক্ষার পরিবেশ তৈরি করে তিনটি ভাষার মধ্যে ‘ডুবিয়ে’ (immerse শব্দটি দলিলে লেখা রয়েছে) রাখলেই তারা ভবিষ্যৎ জীবনে ব্যবহার করার মতো দক্ষতা অর্জন করবে এটি ভাবা বাতুলতা মাত্র। বরং এই ভাষা শিক্ষার চাপে ব্যাপক ‘স্কুলছুট’ হবার আশঙ্কা রয়েছে। বিদ্যালয় স্তরে শিক্ষার উদ্দেশ্য—শিশুর স্বাধীন বিকাশ, শিক্ষাকে অসহ্য ভারে পরিণত না করা, চিন্তাশক্তি ও সৃজনের গুরুত্ব বাড়ানো। তার বদলে জোর দেওয়া হচ্ছে শিশুকে যন্ত্রে পরিণত করানোয় (যদিও প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থাও প্রায় এই ভূমিকাই নিয়ে থাকে)।কোনোমতে সংখ্যাজ্ঞান ও ত্রিবিধ অক্ষরজ্ঞান গলাধঃকরণ করানো যা সামাজিকভাবে পিছিয়ে থাকা পড়ুয়াদের শিক্ষাব্যবস্থায় পূর্ণ অংশগ্রহণের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবে।
এক্ষেত্রে একটা কথা অবশ্যই বলা দরকার। নতুন এই শিক্ষানীতিতে বলা হয়েছে, প্রাক্-প্রাথমিকে তিনটি ভাষা শেখানোর দায়িত্বে থাকবেন অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা। এখনও পর্যন্ত যে পদে যোগদানের জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতার মান অষ্টম শ্রেণি পাস। বর্তমানে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের মূল দায়িত্ব শিশুদের পরিচর্যা করা। এবং দু-একটি ব্যতিক্রম ব্যতিরেকে, সেটি তারা দক্ষতার সঙ্গেই করেন। এদের ওপর দুটি দায়িত্বই থাকলে বলাবাহুল্য দুটি কাজই চরম ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। দেশের উচ্চশিক্ষিত বেকারদের কথা ভেবে যদি এই প্রস্তাব দেওয়া হয়ে থাকে তাহলেও, ক্রমহ্রাসপ্রাপ্ত সরকারি চাকরির পরিসংখ্যানের দিকে তাকিয়ে আশার আলো বিশেষ দেখা যায় না। পাশাপাশি বর্তমান শিক্ষানীতিতে এও বলা হয়েছে, উপজাতি প্রধান বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষকের অভাব পূরণ করতে, প্রাথমিক ও উচ্চ প্রাথমিকে যারা পাশ করে যাবে তারাই উক্ত বিদ্যালয়ে নির্দিষ্ট সময় ধরে পড়াবে। এমনকি অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক কিংবা সেনা অফিসার, ভালো ছাত্রছাত্রী এবং সমাজ সচেতন কলেজ ছাত্রছাত্রীরা ‘টিউটর’ হিসাবে স্বেচ্ছাসেবার ভিত্তিতে পড়াবেন। এখানে মহিলা স্বেচ্ছাসেবকরা যারা স্থানীয় সম্প্রদায়ভুক্ত, তারা স্কুলছুটদের বিদ্যালয়ে নিয়ে আসা, বিশেষ ক্লাস নেওয়া প্রভৃতি কাজ করবেন। যদিও তাদের বেতন বা চাকরির শর্ত এসব নিয়ে দলিলে কোনো কথা বলা হয়নি।
অনেক দুর্বলতা, সীমাবদ্ধতা নিয়ে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় ‘ধর্মনিরপেক্ষ’ ও ‘গণতান্ত্রিক’ ভাবনার যে পরিসর ছিল, নতুন নীতিতে সে সব পুরো বাদ দেওয়া হয়েছে। ফলে সামাজিক ভাবে পিছিয়ে থাকা মানুষজনের শিক্ষার আঙিনা থেকে আরও দূরে সরে যাওয়ার, বলা ভালো সরিয়ে রাখবার ব্যবস্থা পাকা করা হয়েছে। ‘উৎকর্ষমূলক জ্ঞানসমৃদ্ধ’ সমাজ গঠনের কথা, শিক্ষার সর্বজনীন প্রসারের কথা থাকলেও সকলের জন্য শিক্ষা কর্মসূচী সফল করার কোনো পদক্ষেপ দেখা যায় না। সর্বশিক্ষা অভিযান মারফত বিশাল সংখ্যক ৬-১৪ বছর বয়সি ছেলেমেয়েদের বিদ্যালয়ে আনার যে কর্মসূচী ২০০১ সালে শুরু হয়েছিল, তার জন্য প্রয়োজন পড়েছিল পার্শ্বশিক্ষক নিয়োগের। যা ছিল শিক্ষায় কেন্দ্র-রাজ্য যৌথ অংশীদারিত্ব ভিত্তিক। নতুন প্রস্তাবে পার্শ্বশিক্ষক বা শিক্ষাবন্ধু জাতীয় পদের বিলোপ—অনেক গালভরা কথার আড়ালে থাকা নীতি-নির্ধারকদের মনোভাবকে পরিষ্কার করে দেয়।
‘আমূল পরিবর্তন’ আনার উদ্দেশ্যে পরিকল্পিত এই শিক্ষানীতি রূপায়ণের প্রধান পর্ব এক দশক ধরে চলবে বলে জানানো হয়েছে। তবে রূপায়ণের লক্ষ্যে কাজ শুরু হবে অনেক আগে থেকেই। অথচ এ প্রসঙ্গে বলা দরকার, শিক্ষার দায়িত্ব সংবিধান অনুযায়ী কেন্দ্র-রাজ্য যুগ্ম তালিকায় হলেও এই নীতি গ্রহণের সময় সমস্ত রাজ্যের মত নেওয়া হয়নি। এমনকি বিশিষ্ট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি, বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা বিভিন্ন শিক্ষক/শিক্ষাবিদ ও ছাত্র সংগঠন এবং সামাজিক সংগঠনের মতামতও নেওয়া হয়নি। যা জানা গেছে সরকারি সূত্রেই (২৯ জুলাই ২০২০ সরকার ৬০ পাতার শিক্ষনীতির পুস্তিকা প্রকাশ করেছে)। ৪৮৪ পাতার নতুন এই শিক্ষানীতি পুরোপুরি কার্যকর হলে নির্দ্বিধায় বলা যেতে পারে ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থা তার স্বকীয়তা হারাবে। বিদ্যালয় শিক্ষার পরিকাঠামোর পরিবর্তনে দশম শ্রেণির যোগ্যতামানে গুরুত্বহীনতার পাশাপাশি উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে কলেজগুলির সরাসরি ডিগ্রি দেওয়ার মধ্য দিয়ে উচ্চশিক্ষায় গুণগতমান হ্রাস, চার বছরের ডিগ্রি কোর্স ও এক বছরের স্নাতকোত্তর চালু হলে ভারসাম্যের সমস্যা—এ সমস্ত বিষয়ে নানা প্রশ্ন উঠে আসছে। সব দেখে শুনে পাঠকের/আমাদের মনে পড়ে যাবে তারাশঙ্করের ‘অগ্রদানী’ গল্পের সেই ব্রাহ্মণকে। নিজের ছেলের পিণ্ড যাকে খেতে হয়েছিল।