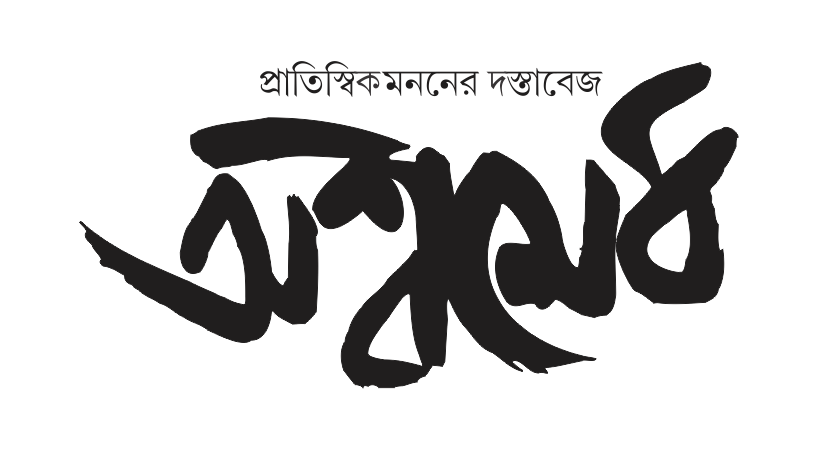তাঁর নিজের তৈরি মঞ্চে বহুজনকে আলো ফেলতে দিলেও, নিজের জীবনে আলো ফেলে, নেপথ্য থেকে সামনে নিয়ে আসতে যাঁরাই উদ্যোগী হয়েছেন, অধিকাংশ সময়ই তাঁদেরকে নিরাশ করেছেন—তা, নিরুচ্চারের বাস্তব কারণ হতে পারে বটে, কিন্তু একজন আপসহীন ব্যক্তি, শিল্পসমর্পিত হওয়ার পরেও সমাজের দায়পালনে যিনি আশৈশব উদ্যোগী, যাঁর নির্মোহ-নিবেদনশীলতা যেখানে দৃষ্টান্তযোগ্য, প্রেরণাবহ, তাঁকে—তাঁর একান্ত নেপথ্যচারিতা সত্ত্বেও—আমাদের নিজ-প্রয়োজনেও তো নানামুখী মূল্যায়নে সামনে-নিয়ে-আসা উচিত ছিল; অথচ, আমাদের জানা মতে, প্রায় ছয় যুগের শিল্পীজীবনে খালেদ চৌধুরীকে নিয়ে যতুটুকু আলোচনা হয়েছে, তা তাঁর প্রতিভার পক্ষে একেবারেই অকিঞ্চিৎকর আর আমাদের জন্যে অতি অবশ্যই লজ্জার।
তাঁর প্রতিভা সম্পর্কে ‘আশ্চর্য’ বিশেষণটি যুক্ত করেছেন, তাপস সেন, মঞ্চে আলো-ফেলার শিল্পে নানা উদ্ভাবনী ক্ষমতা দেখিয়ে, যিনি নিজেই এক কিংবদন্তিতুল্য প্রতিভার দৃষ্টান্ত। খালেদ চৌধুরী ও তাপস সেন—দুজনেই নেপথ্যের শিল্পী। একজন মঞ্চ তৈরি করলে—সেখানে আলো ফেলেন অন্যজন। এই দুটো কাজই পরস্পরস্পর্শী; এবং মঞ্চ নির্মাণ ও আলো প্রক্ষেপণের কাজ যেহেতু যেখানে-সেখানে আসবাব বসিয়ে-দেওয়া আর যেনতেন আলো-ফেলে যাওয়াই শুধু নয়—যেখানে একাধিক চরিত্র এবং বহু বিষয় নিয়ে ভাবনারও একটা ব্যাপার রয়ে যায়—তাই একজন সম্পর্কে অন্যজনের মন্তব্য গুরুত্বের দাবি রাখতেই পারে।
বহুরূপী এবং বহুরূপী-র বাইরে অনেক কাজ একসঙ্গে করে তাপস সেন জানিয়েছেন, কাজের জীবনে অনেকের সঙ্গেই তো তাঁর পরিচয় হয়েছে, কিন্তু সকলকে ছাপিয়ে যে দুজনের নাম আলাদাভাবে তাঁর মনে থাকবে, তাঁদের একজন বংশীচন্দ্র গুপ্ত, অন্যজন খালেদ চৌধুরী; বহু চলচ্চিত্রে কাজ করে, বিশেষত ‘পথের পাঁচালী’-তে শিল্পভাবনার পরিচয় দিয়ে, এবং সেই ছবিটির জগজ্জোড়া সাফল্যের সুবাদে বংশীচন্দ্র বরাবরই এক উচ্চারিত নাম, কিন্তু খালেদ চৌধুরী? তাঁর নেপথ্যচারণই কি এই নিরুচ্চারের কারণ?
ভাবতে অবাকই লাগে, আসামের করিমগঞ্জ জেলার প্রায় সাত-আট কিলোমিটার দূরবর্তী চেপরা গ্রামের চিররঞ্জন, পরবর্তী জীবনে যিনি খালেদ চৌধুরী নামে সংগীত-চিত্রকলা- মঞ্চচিত্রণ-ধ্বনি-সংযোজন প্রভৃতি ক্ষেত্রে শিল্পকুশলতার পরিচয় দিয়ে, বাংলায়, ভারতবর্ষে স্বনামখ্যাত হয়ে উঠবেন; অল্পবয়সে মা’কে হারানো সেই ছেলেটিকেই প্রায়শ জন্মদাতার ত্রাসে কাটাতে হত। এই ভয় কি বয়সসুলভ কোনো চাপল্যের জন্যে? নিজের সম্পর্কে প্রগলভ হতে অনাগ্রহী খালেদের মাধ্যমে এই বিষয়ে বিস্তারিত জানা যায় না, শুধু তাঁর নিজের জবানিতে এইটুকু শুনি—মাঝেমধ্যে স্কুল পালাতেন আর চলে যেতেন নানা পরব-অনুষ্ঠান দেখতে; একবার শুনলেন, তাঁর স্কুলের পাশের গ্রামে ‘নৌকোপূজা’ হবে, ব্যাপারটি কেবল তাঁর নয়, অন্যদেরও অভিনব মনে হলো; তাই তিনি স্কুল পালিয়ে নৌকোপুজো দেখতে গেলেন; এরপর তাঁর গ্রামের চারপাশে যে যাত্রাগান, মনসামঙ্গল-পদ্মাপুরাণ পালা প্রভৃতি হত, তা-ও দেখবার অনুমতি ছিল না; কেউ-যাতে-না-দেখে এমন সতর্কতা সহ লুকিয়ে চুরিয়ে সেগুলো দেখতে যেতেন; শুধু এইসবই যদি কারণ হয়ে থাকে, তাহলে, অনুমান করা যায়, এইসব নিষিদ্ধ এলাকার প্রতি তাঁর আগ্রহের কারণেই একসময় তাঁকে তাঁর প্রিয় গ্রাম, তার ভূমিচিত্র-নদীতীর-যাত্রাপালা-পূজা ও পরব-লোকসংগীত আর ধামাইল গান শোনা-র অতৃপ্ত বাসনা ছেড়ে, বরাক নদী পার হয়ে সিলেটে, সুরমাপারে চলে আসতে হয়।
সিলেটে আসা মানে তো নিষেধ-বিড়ম্বিত চিররঞ্জনের জন্যে ‘পৃথিবীর পথে’ পা-দেওয়া, পরে যেখান থেকে তিনি পৃথিবীর পাঠশালায় পৌঁছে যাবেন; কিন্তু আমাদের কাছে তাঁর সিলেট-পূর্ব নিষিদ্ধ যাতায়াতের যে-জগৎ, তা ঐতিহাসিক মূল্যের কারণে তো বটেই, তাঁর শিল্পজীবন বোঝার জন্যেও গুরুত্বপূর্ণ। খালেদ চৌধুরী নিজেই জানিয়েছেন (‘থিয়েটারে শিল্পভাবনা’)—
আমার ছেলেবেলা থেকেই শুরু করা ভালো। কারণ অনেক কিছু আমার চারপাশে ঘটত, অনেক কিছু শুনতাম, জানতাম যেগুলোর অনেকটাই বুঝতে পারতাম না; অথচ তার একটা পরোক্ষ প্রভাব আমার ওপর কাজ করে যেত। সেই প্রভাবটা আমি বহু পরে বুঝতে পারি। যে জিনিসগুলোর প্রভাবের কথা বলছি, তার মধ্যে ছিল লোকসঙ্গীত, লোকশিল্প, বিশেষ করে আমাদের দেশে যেটা খুবই হয়, সেই পুতুলজাতীয় জিনিশ, মেলার মধ্যে যা আমরা দেখতে অভ্যস্ত; আর মূর্তি। মূর্তি সম্পর্কে একটা কথা বলে রাখা ভালো যে, মূর্তিশিল্প আমার ওপরে একটা প্রচণ্ড দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব বিস্তার করে এসেছে—যেটা তখন আমি বুঝতে পারিনি, বুঝেছি বহু পরে।
ছেলেবেলার বিচিত্র জগতের অভিজ্ঞতা কীভাবে সংগীত, চিত্রকলা ও মঞ্চচিত্রণে ভূমিকা রেখেছে, তার বর্ণনা তাঁর বিভিন্ন লেখা ও সাক্ষাৎকারে প্রকাশ করেছেন খালেদ চৌধুরী। এক্ষেত্রে উল্লেখ করা যায়, শোলমারা গ্রামে এক বর্ধিষ্ণু চাষির দেওয়া সেই ‘নৌকোপুজো’-র কথা, যা তাঁর কাছে ছিল একেবারেই অচিন্তিত; দেখলেন—প্রায় চারতলা উঁচু এক বিশাল বাড়ির মতো ঘর, ঘরটির দুই দিকে বের হয়ে আছে দুইটি গলুই; প্রায় দেড়শ, দু-শো ফুটের দুই গলুইওয়ালা বিশাল ঘরটিকে দেখলে মনে হয়, একটি বিশাল ছইওয়ালা নৌকো; এখানেই শেষ নয়, ঘরটি তাক-তাক করা, শুরুর দিকের তাকে খাজুরাহোর মিথুনমূর্তির মতো নানা ভঙ্গিতে নানারকম উলঙ্গ প্রেতের সারি; বিস্ময় আরো আছে, তার পর পরই নানা অবতার, এই নামগুলি বালক খালেদের তখনও একেবারেই অজানা: কূর্ম-বামন-বরুণ-অগ্নি; তাঁর কাছে অদ্ভুত লাগার কারণ হলো নৃসিংহ হলো অর্ধেক মানুষ, অর্ধেক সিংহ; বরুণ: অর্ধেক মানুষ, অর্ধেক কচ্ছপ—দুটি চরিত্রের এমনতরো মিশ্রণ যে হতে পারে, তা কোনোদিন কল্পনাই করেননি; কারণ, হয়তো মানুষ দেখেছেন, নয়তো জীবজন্তু—এর বাইরে কিছু নয়। নৌকোপূজা দেখতে এসে এই প্রথম তিনি দেখলেন, উপরে উলঙ্গ প্রেত, আর নীচে এক উলঙ্গ রাখাল—এইসব উলটোপালটা কাণ্ড সেই বালক বয়সে তাঁকে এতটাই ভাবিয়ে তুলেছিল যে, তার প্রভাবে তিনি মূর্তি-আঁকা শুরু করে দিলেন। একতাল কাদা দিয়ে, সারি সারি—যেমন-যেমন দেখেছেন ঠিক তেমন-তেমন করে, ভুল হলে সঙ্গে সঙ্গে ‘রেকটিফাই’ করে আসতেন; এরপর মিনিয়েচার করে সেগুলিকে সাজিয়ে রাখতেন। এখানেও পিতার চোখ: তিনি দেখে ফেলে বললেন—’এগুলি বানাবে না’; খালেদ ভাবলেন, এগুলিও বোধহয় খারাপ কাজ, তাঁকে তাকিয়ে থাকতে দেখে, পিতা আবার বললেন, ‘বানালে পুজো করতে হয়’; পিতার কথা শুনে মনে-মনে ভাবলেন, আদলটা তাহলে একই হচ্ছে, কিন্তু দায়বন্ধনের ব্যাপারটি যখন দেখলেন—তখন মূর্তি বানানোটা একদমই ছেড়ে দিলেন, তবে, তাঁর এই হাতেখড়ির অভিজ্ঞতা মনের মধ্যে রয়ে গেল, এবং পরে এর সঙ্গে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন স্থানে দেখা পুতুল ও মূর্তিকে মিলিয়ে-দেখা সম্ভব হলো।
এছাড়া নদীর পারে বাড়ি থাকায়, নদী দিয়ে যাঁরা গান গেয়ে যেত, তাঁদের নানাপ্রকারের গান তাঁর মনে ঢুকে পড়ত; তার সঙ্গে আছে প্রতি বর্ষায় নৌকাবাইচের ধুম—বাইচালদের উদ্দাম নাচ আর গান; খালেদ চৌধুরী একটু বিশেষভাবে একটি নাচের কথা বলেছেন, যে-কোনো উৎসবে নানা বর্ণের মেয়েরা এই নাচটি করত, সেটি হলো ধামাইল নাচ। এখানে ঐতিহাসিক মূল্যের কারণে তাঁর নিজের বর্ণনাটি পড়া যাক (‘থিয়েটারে শিল্পভাবনা’)—
কথাপ্রসঙ্গে বলে রাখি যে আমার দিদিমা এই নাচের একজন প্রবক্তা ছিলেন। আমার দিদিমা ছিলেন গুরুসদয় দত্তের বড়দি। ওই বয়সে তাঁকে, আমি নাচতে দেখেছি, আমার ছোটবেলায়—তখন তো তাঁর যত বয়স, প্রায় তখন ষাটের কাছাকাছি বয়স হবে—তখন তাকে দেখে আমার মামীমা বলতেন যে, তিনি যখন নাচতেন তখন তাঁকে দেখে মনে হত ষোল বছরের মেয়ে। আমি নিজে তাঁর নাচ দেখেছি। সেই পরিবেশে শুধু তিনিই নন; আমাদের সমস্ত গ্রাম নমঃশুদ্র পরিবেষ্টিত; তাঁদের বাড়ির মেয়েরাও একই সঙ্গে নাচত।
বলা হয়েছে যে, তাঁর এই অভিজ্ঞতা ছোটবেলার, কারণ একটু বড় হলেই সে-আসরে আর থাকবার অধিকার থাকত না; খালেদ পরে অনুমান করেছেন, উদ্দাম নাচের তালে—বিশেষ করে বিজয়া দশমীতে—মেয়েরা, কাপড় অবিন্যস্ত হয়ে পড়ত বলেই হয়তো পুরুষদের ঘর থেকে বের করে দিত। এইসব অভিজ্ঞতা নিয়েই খালেদ চৌধুরী ধামাইল নাচের ওপর তাঁর অতি পরিচিত ছবিটি এঁকেছিলেন, যেখানে দেখা যায় যে, মেয়েরা গোল হয়ে নাচছে, করতাল হাতে একজন, সে-ই এই নাচের নেতৃত্ব দিচ্ছে (‘মাটির সুরের খোঁজে’, রণজিৎ সিংহ)। খালেদের অভিজ্ঞতাটির বর্ণনা দিতে গিয়ে ঐতিহাসিক মূল্যের প্রসঙ্গটি এজন্যেই আনা হয়েছে যে, বিখ্যাত ব্রতচারী আন্দোলনের নেতা গুরুসদয় দত্ত লিখেছেন, কায়স্থ-ব্রাহ্মণরা নাকি এগুলো করে না, অথচ খালেদ নিজের চোখে দেখে বলেছেন যে, গুরুসদয় দত্ত-র বড়দি কাত্যায়নী পুরকায়স্থ ছিলেন এই নাচের একজন প্রবক্তা।
সিলেটের এক মুসলিম পরিবারে লজিং নিয়ে উঠে ‘চিররঞ্জন’ নামটি চিরদিনের মতো ফেলে দিয়ে, খালেদ চৌধুরী নামে যখন পরিচিত হয়ে উঠবেন, সেখানকার অবস্থা তখন উত্তাল; ১৯৩৭ থেকে ১৯৩৯—এই দুই বছর রুজিরোজগারের জন্যে নানা চেষ্টা করলেও, খেয়ে না-খেয়ে কাটল তাঁর। এরপর শুরু হলো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, একটু-আধটু কাজ পেতে শুরু করলেন। হাতের লেখা ভালো থাকায় সাইনবোর্ড লিখে, হোর্ডিং-লেটারিং ইত্যাদি করে কোনোরকমে পেট চালাচ্ছেন, এই সময় বিনোদবন্ধু দাস, যিনি ধাঙড় ইউনিয়ন করতেন, খালেদ চৌধুরীর কাছে স্তালিনের প্রতিকৃতি আঁকার প্রস্তাব নিয়ে এলেন; খালেদ যেহেতু মিত্রপক্ষের লোক, স্তালিন কীভাবে এগোচ্ছে, লড়াই করছে—সে-বিষয়ে কৌতুহলী, তাই ‘সানন্দে রাজি হয়ে ঘরের দরজা-টরজা বন্ধ করে লুকিয়ে-চুরিয়ে’ কাজটা করলেন। যুদ্ধের কারণে গোটা বাংলাদেশ জুড়ে তখন দুর্ভিক্ষ, সকলেই পীড়িতদের জন্যে কিছু একটা করতে আগ্রহী—এই অবস্থায় দুর্ভিক্ষ-তহবিলের জন্যে টাকা তুলতে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন হবে, তাতে চিত্রকর হিসেবে খালেদকেও ডাকলেন বিনোদবন্ধু দাস; সেই অনুষ্ঠানে কেউ গান গাইছে, কেউ বাজনা বাজাচ্ছে, আর একটু দূরে দেখা গেল কয়েকটি ছবিও টাঙানো। হঠাৎ খালেদ চৌধুরীর আঁকা স্তালিনের প্রতিকৃতি সম্বন্ধে একজন বলে উঠলেন—‘আপনারা ভাবতে পারেন এই ছবিটা বোধহয় কলকাতা থেকে আনা। তা নয় এটা এখানকার একটি ছেলের আঁকা’—এই মন্তব্যটি একটু দূর থেকে শুনে-নেওয়া খালেদ চৌধুরীর অল্পবয়সের রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার কথাটি জানাচ্ছেন, সুদেষ্ণা বসু, তাঁর ‘খালেদদা’ নামের বইতে—
আমার গায়ের লোমটোম খাড়া হয়ে গেল। পরক্ষণেই মনে হল, এটা কি সত্যিই আমার আঁকা সেই ছবিটা? কিন্তু এত ছোট করে তো আমি আঁকিনি। সেটা তো বড় ছবি ছিল। আসলে বসেছিলাম শেষ বেঞ্চিতে। দূর থেকে দেখছি বলে মনে হচ্ছিল ছোট। পার্সপেকটিভের জন্য যে একটা জিনিসকে ছোট দেখায় সেই বোধটা পর্যন্ত তখনও তৈরি হয়নি।
এই অনুষ্ঠানে তাঁর পরিচয় হলো বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে, পরে যিনি শ্ৰমিক-নেতা হিসেবে খ্যাতি পাবেন; তিনি কলকাতা থেকে এসেছিলেন, আর লোক-ধারণা যেহেতু ‘কলকাতার লোক সব জানে’, তাই তাঁর শংসাবাক্য, এবং তাঁকে ছবি-আঁকা চালিয়ে যেতে বলায় এখানে তাঁর বেশ কদর বাড়ল, তিনিও তাঁর স্কুলের ক্লাসে সবসময় দশে-দশ পাওয়া অঙ্কন-অভিজ্ঞতা নিয়ে পুরোদমে ছবি আঁকা শুরু করে দিলেন। এই সময় ওই বিনোদবন্ধু দাসই তাঁকে ধরে নিয়ে গিয়ে হেমাঙ্গ বিশ্বাস ও নির্মলেন্দু চৌধুরীর সঙ্গে তাঁর যোগসূত্র বেঁধে দিলেন।
হেমাঙ্গ বিশ্বাসের জবানিতে স্পষ্ট যে—এই অঞ্চলের সবচেয়ে সংগঠিত সাংস্কৃতিক সংগঠনের অপরিহার্য ব্যক্তিত্ব খালেদ চৌধুরীর তিনটি গুণ তখনই প্রকাশিত হয়ে গিয়েছিল—চিত্রকর, গায়ক ও মঞ্চচিত্রক। সিলেটে অঙ্কনশিল্পে যখন আদৃত হচ্ছিলেন তিনি, তখন,—যেহেতু নিজে যেচে প্রকাশ করবার পাত্র নন—হেমাঙ্গ বিশ্বাস যেদিন আবিষ্কার করলেন, খালেদ শুধু আঁকেনই না, গানও গেয়ে থাকেন; সেই থেকে তাঁর গায়কজীবনও শুরু হয়ে গেল। তখন একসঙ্গে দুটোই শুরু হলো—সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত ছবি আঁকা, বিকেল হলেই গান; একসময় এমনই দাঁড়িয়ে গিয়েছিল যে, নির্মল আর খালেদই হয়ে গেলেন আসল গাইয়ে, কখনও নির্মল অসুস্থ হলে গানের দায়িত্বটা পড়ে যেত খালেদের ওপর— এইভাবেই কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে খালেদ চৌধুরীর জড়িয়ে পড়া; এ প্রসঙ্গে হেমাঙ্গ বিশ্বাস লিখেছেন (‘উজান গাঙ বাইয়া’)—
পার্টির অন্তর্ভুক্ত নন অথচ একজন শক্তিশালী শিল্পীর সন্ধান পেয়ে তাঁকে টেনে আনলাম আমাদের এই স্কোয়াডে। ইনি হলেন খালেদ চৌধুরী। আঁকা ছাড়া এর মাঝে আবিষ্কার করলাম একজন সম্ভাবনাময় গায়ককে। ইনি তখন উর্দু গজল ও কাওয়ালী গাইতেন। যদিও তিনি তখন পার্টির সভ্য নন, তথাপি বারীন দত্তের অনুমতি নিয়ে পার্টির নিয়মের ব্যতিক্রম করে তাঁকে সর্বক্ষণের পার্টিসভ্যদের কমিউনে নিয়ে এলাম। আমাদের চলমান দলের মঞ্চ স্থাপনা ও সজ্জায় তিনি হয়ে উঠলেন অপরিহার্য। এভাবে আমাদের দলটি হয়ে উঠল বাংলা বা আসামের মফঃস্বল জেলার মধ্যে পার্টির নেতৃত্বে সবচেয়ে সংগঠিত একটি সাংস্কৃতিক জাঠা।
কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে জড়িত হওয়ার পর গায়ক খালেদ চৌধুরীর সঙ্গে চিত্রকর খালেদ চৌধুরীর কর্মক্ষেত্র আপাতত সীমাবদ্ধ হয়ে থাকল দুর্ভিক্ষের ছবি আঁকার মধ্যে; জয়নুল আবেদিন, চিত্তপ্রসাদ ও সুনীল জানার দুর্ভিক্ষের ছবি, আর রেডিও ও খবরের কাগজ পড়ে যে-অভিজ্ঞতা হত, তার ওপর ভিত্তি করে, পার্টি থেকে যে-থিম দেওয়া হয়, সেই অনুযায়ী ছবি আঁকতেন খালেদ। হেনা দাস তাঁর ‘স্মৃতিময় দিনগুলো’ বইয়ে এই সময়কার অভিজ্ঞতা জানিয়ে লিখেছেন—“পোস্টার শিল্পেও এই সময় নতুনত্ব, বৈচিত্র্য ও উন্নতমানের প্রকাশ ঘটে। আমাদের জেলার চিত্রশিল্পী খালেদ চৌধুরীর নেতৃত্বে পোস্টার শিল্পে বিস্ময়কর অগ্রগতি সূচিত হয়। পোস্টার হয়ে দাঁড়ায় শক্তিশালী প্রকাশমাধ্যম।” পরে সেই পোস্টারগুলোর একটি এগজিবিশনও হয়, তাঁর শিল্পী মাত্র একজন—খালেদ চৌধুরী। অথচ সেই সময় আরো দুজন শিল্পী ছিলেন সিলেটে। এ প্রসঙ্গে খালেদ চৌধুরীর সবিনয় ভাষ্য তুলে ধরা উচিত (‘থিয়েটারে শিল্পভাবনা’)—
পরে দেখা গেল আর্টিস্ট আছেন আরো দুজন। তাঁরা আমার চেয়ে অনেক বেশি শিক্ষিত, অনেক বেশি জানেন বলেই বোধহয় তাঁরা এগিয়ে আসতেন না। আর আমি জানি না বলেই বেশি তড়পাতাম। এর মধ্যে একজন দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীর ছাত্র; তিনি আবার রণেন রায়চৌধুরীর দাদা, রাধিকাবল্লভ রায়চৌধুরী। এখনো আছেন এখানে, ডানলপের কাছে থাকেন। আর একজন ত্রিপুরায় আছেন, তাঁর নাম হেমন্ত দাস। হেমন্ত দাস কোথায় শিখেছিলেন তা জানি না, তবে তিনি পোস্টার করতেন, এবং আমার চেয়ে অনেক ভাল করতেন, আমার মতে। কিন্তু আমার আদরটা বেশি ছিল। কেন আমার আদরটা বেশি ছিল, তা আমি জানি না।
শিক্ষা ও জানার বিষয়টি ঠিক কী অর্থে বলেছেন তিনি তা আমরা বুঝতে পারি বাড়ি-পালানো খালেদকে দেখে, কিন্তু এই কারণটি তাঁকে অঙ্কনপটু হতে সমস্যাগ্রস্ত যে করেনি, তার প্রমাণ আমরা পেয়ে যাই তাঁর কলকাতায় পৌঁছে যাওয়ার পর—যখন আঁকা শিখবার জন্যে জয়নুল আবেদিনের কাছে গেলেন। সেদিন সেখানে কামরুল হাসানও উপস্থিত, খালেদ তাঁর কিছু ছবি বের করলেন; ছবি দেখে জয়নুল বললেন—‘এ তোমার আঁকা তো?’ তিনি বললেন, ‘হ্যাঁ’; ‘আর্ট স্কুলে ভর্তি হবার দরকার নেই’—জয়নুলের এই স্বতঃস্ফূর্ত স্বীকৃতির মধ্যে, সিলেট থাকাকালে তাঁর আদৃত হওয়ার কারণটি বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না। এছাড়া প্রগতি লেখক সংঘ কর্তৃক আয়োজিত কনফারেন্সে যখন এসেছিলেন, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তখন তাঁর গান শুনে এবং ছবি দেখে মন্তব্য করেছিলেন—’গান গাইছ গাও কিন্তু ছবি আঁকা ছেড়ো না।’
এরপর, সিলেটে বেশিদিন আর মন টিকল না তাঁর—এক ফার্নিচার ব্যাপারির ক্যাটালগ করে, তার সম্মানি-বাবদ যে সামান্য ক’টি টাকা পেয়েছিলেন তাই সম্বল করে একদিন কলকাতার পথ ধরলেন খালেদ।
ছবি পছন্দ হওয়ায়, কলকাতায় জয়নুল আবেদিন তাঁকে এটা-ওটা আঁকার কাজ দিতেন, তখন একই রকম কাজ করতেন কামরুল হাসানও; কাজ করতেন, সেই সঙ্গে শেখাও হয়ে যেত অনেক কিছু; কিন্তু অচিরেই দাঙ্গা শুরু হলো, জয়নুল চলে গেলেন বাংলাদেশে, আর খালেদ পড়ে গেলেন মহা দুর্ভাবনায়।
‘তখন তো আমাকে খেতে হবে! কী করা যায়’—ভাবলেন খালেদ; সিদ্ধান্ত নিলেন প্রচ্ছদ আঁকবেন, এক্ষেত্রে, শুরুর দিকে পোস্টার আঁকার অভিজ্ঞতাটি কাজে লাগল, পোস্টারের মধ্যে যেমন নির্ধারিত পরিসরে পুরো একটি ঘটনাকে তুলে নিয়ে আসতে হয়, বইয়েও তেমনি একটি ক্ষুদ্র মলাটের মধ্যে বিষয়-নির্যাসকে ছবিতে ফুটিয়ে তুলতে হয়। এমন ভাবনার মধ্য দিয়ে জীবনের প্রথম প্রচ্ছদ আঁকলেন—ডাইসন কার্টারের সোভিয়েত বিজ্ঞান, এর অনুবাদক ছিলেন চিন্মোহন সেহানবিশ; সম্মানি-বাবদ পেয়েছিলেন দশ টাকা; এই বইয়ের প্রচ্ছদটি এঁকেই তাঁর মনে হয়েছিল ‘প্রচ্ছদ আঁকাই বোধহয় পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শিল্পকর্ম’। এরপর নানা ধরনের বইয়ের প্রচ্ছদ তিনি করেছেন, নানান পরীক্ষানিরীক্ষা করে উতরে গিয়ে সেখানে প্রতিষ্ঠাও পেয়েছেন। বর্তমান কম্পিউটার গ্রাফিক্সের বদৌলতে প্রচ্ছদ নির্মাণের ক্ষেত্রে নানা চোরাপথ বেরিয়ে যাওয়ার পর আমাদের চোখ এতটাই ধাঁধাগ্রস্ত যে, উক্ত প্রচ্ছদগুলিকে হয়তো এখন আর তেমন গুরুত্বপূর্ণ মনে হবে না বর্তমান প্রজন্মের। কিন্তু যুগ-পরিপ্রেক্ষিত মাথায় রেখে, তার বিষয়ানুগ কল্পনা ও বিন্যাস বিচার করলে খালেদের স্বাতন্ত্র্য ও প্রতিষ্ঠার কারণ বোঝা যাবে।
এরপরও নিয়ত নতুনত্ব সন্ধানী ছিলেন বলে, অঙ্কিত প্রচ্ছদগুলি নিয়ে তাঁর দ্বিধা ও অতৃপ্তির শেষ ছিল না; ‘জীবনে অনেক ভালো প্রচ্ছদ করেছেন’—এরকম মন্তব্যের মুখে সাক্ষাৎকারীকে তাই বলেছেন (‘খালেদদা’, সুদেষ্ণা বসু)—
এখন তুমি যেটা বলছ—যে আমি খুব ভালো বইয়ের কাভার করেছি, হয়তো এটা আমার অজ্ঞাতে। কারণ আমি জানি না, তার মধ্যে খুব একটা কোনো রিমার্কেবল কাজ হয়েছে কী না। কিন্তু আমার কিছু কাজ নিয়ে, যদি বলো যে কিছু দুর্বলতা ছিল কী না, তাহলে বলব যে হ্যাঁ, একটু আধটু দুর্বলতা ছিল, কিছু কিছু ছবির ক্ষেত্রে—যেমন ওমর খৈয়ামের ইলাস্ট্রেশন করেছিলাম আমি।

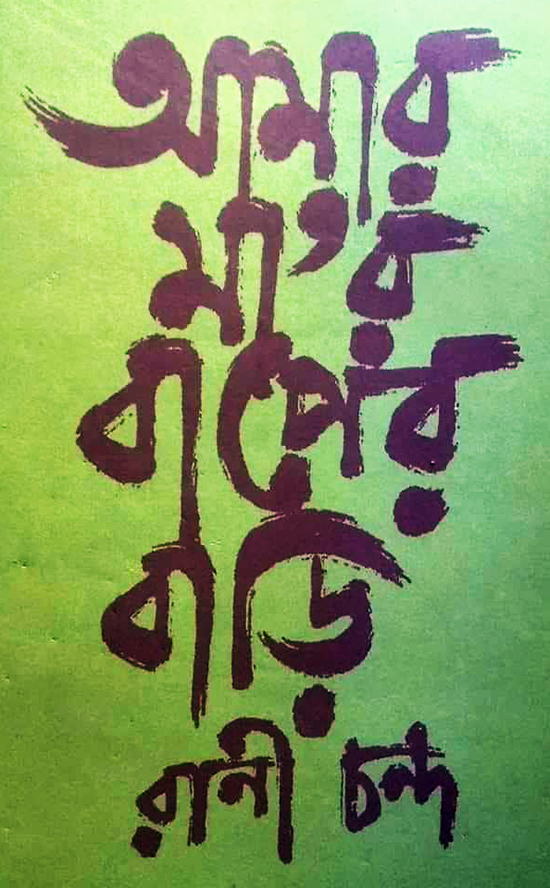

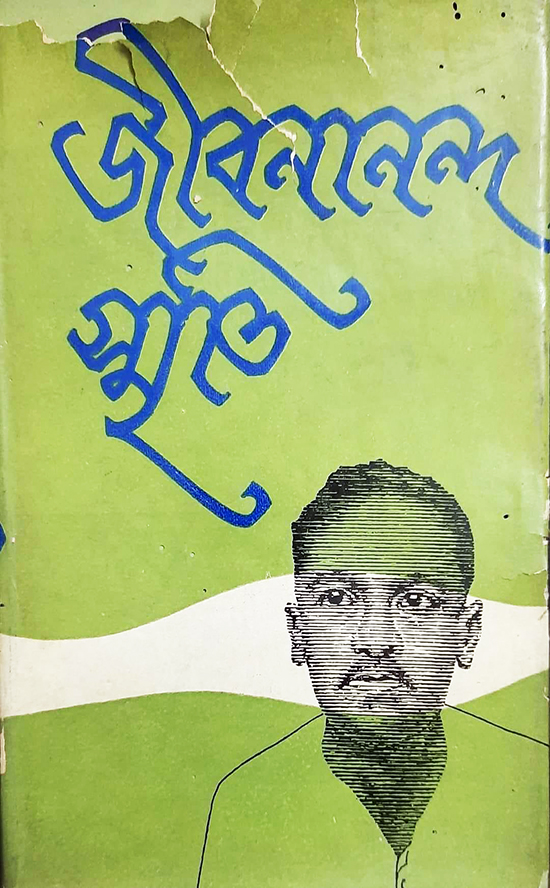
বইয়ের প্রচ্ছদে নিবিষ্ট হওয়ার জন্যে খালেদ চৌধুরীর সংগীতমনস্কতা কি ব্যাহত হলো—এ প্রসঙ্গে তিনি জানিয়েছেন—তিনি নিজে শুরুতে লোকসংগীত—লোকসুরের গান গাইতেন, কিন্তু গলা নষ্ট হয়ে যাওয়ায় একসময় তাঁকে গাওয়া ছেড়ে দিতে হলো, এরপর কিছুদিন তবলা বাজালেন; পরে ভাবলেন, পার্টির কাজ তো লোকসমাজকে সংস্কৃতিগতভাবে শিক্ষিত করে তোলা, অথচ তিনি নিজেই প্রাতিষ্ঠানিকভাবে শিক্ষিত নন; তাই সলিল চৌধুরীর পরামর্শে পাশ্চাত্য মিউজিক শিক্ষার উদ্দেশ্যে ভায়োলিন শিখতে গেলেন, এবং ক্রমশ জানলেন—বাজনার বিজ্ঞান, ব্যাকরণ আর সংগীতের কাঠামো। এর মধ্য দিয়ে পাশ্চাত্য সংগীত বিষয়েই যে শুধু অবহিত হলেন তা নয়, নিজেদের সংগীত বিষয়েও সচেতন হতে পারলেন; বুঝতে পারলেন: লোকসংগীত আর মার্গসংগীতের তফাতটা ঠিক কোন জায়গায়। এই চেতনা অর্জনের পর সংগীত ও ধ্বনি নিয়ে নতুন কিছু ভাববার, পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবার অবকাশ মিলল, ক্ষতি হলো একটাই—না ভেবে দুম করে কিছু করার সাহসটা কমে গেল। হতে পারে তা ক্ষতি, কিন্তু এই অভিজ্ঞতার কারণে সংগীত—বিশেষত লোকসংগীত বিষয়ে যে বিচারবোধ তৈরি হলো, তার পরিচয় আমরা পেলাম ‘লোকসংগীতের প্রাসঙ্গিকতা ও অন্যান্য প্রবন্ধ’ বইটিতে।
শেখার সময়টাতে যখন প্রতিদিন আট ঘণ্টা ভায়োলিনের চর্চা করতেন, তখন তাঁর মেহের আলী রোডের বাড়িতে বাজনা শোনার জন্যে আসতেন শম্ভু মিত্র, তিনিও শম্ভু মিত্রের নাসিরউদ্দিন রোডের বাড়িতে যেতেন; ওই সময় শম্ভু মিত্র ‘ছেঁড়া তার ও চার অধ্যায়’ নিয়ে করা ফেস্টিভালের জন্যে পোস্টার করিয়ে নেন। এর কিছুদিন পরে নাটক করার প্রস্তাব দিলে, খালেদ তা ফিরিয়ে দেন; শম্ভু মিত্র এবার টাকা উপার্জনের প্রসঙ্গ তোলায় তিনি তার আইপিটিএ-এর অভিজ্ঞতার কথা তুলে বললেন যে, নাটক করে টাকা আসে না। এরপরও শম্ভু মিত্র দমেননি, ‘রক্তকরবী’ করার আগে খালেদ চৌধুরীকে বললেন—’তুমি পড়েছ রক্তকরবী?’—জবাবে জানালেন যে, তিনি শুধু ‘রক্তকরবী’ পড়েনইনি, দেবব্রত বিশ্বাস যখন পার্টির টাকা তুলতে ‘মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি’র ব্যানারে শ্রীরঙ্গম-এ ‘রক্তকরবী’র শো করলেন, তাতে ছবি রায়ের সঙ্গে তিনি সেট-এর কাজও করেছিলেন।
খালেদ চৌধুরী এইভাবে ‘রক্তকরবী’-র মাধ্যমে জড়িয়ে পড়লেন শম্ভু মিত্রের সঙ্গে; প্রথম শো-এর পর যথেষ্ট সম্ভাবনাময় মনে হওয়া সত্ত্বে, আবার তিনি সংগীতমগ্ন হতে চাইলেন, কিন্তু শম্ভু মিত্রের অনুরোধ তাঁকে নাটকে জড়িয়ে পড়তে বাধ্য করল; এবং ক্রমশ মিউজিক, সেট, কস্টিউম—সবকিছুরই দায়িত্ব পড়ে গেল তাঁর ওপর। খুব একটা আকস্মিকতা না থাকলেও, যেহেতু আগে কখনও ভাবেননি এইভাবে জড়িয়ে যাবেন, তাই, সবকিছু নিয়ে নতুনভাবে ভাবতে শুরু করলেন। শৈশব ও কৈশোরে দেখা প্রকৃতি, লোকসংগীত-লোকশিল্প, মূর্তি-পোস্টার এবং বিশেষ করে প্রচ্ছদ চিত্রণের অভিজ্ঞতা একাকার করে দিয়ে তাঁর বিস্ময়কর শক্তিকে মঞ্চে ঢেলে দিলেন। দর্শক-সমালোচকদের কাছে ঐতিহাসিক ও উল্লেখযোগ্য মঞ্চ বলে বিবেচিত ‘রক্তকরবী’ মঞ্চায়নের ব্যাপারে খালেদ চৌধুরীর অনিবার্যতা বোঝা যায় শম্ভু মিত্রের জবানিতে (‘সন্মার্গ সপর্যা’), তিনি লেখেন—
আমাদের রক্তকরবী ভালো লাগে। যেমন অনেকেরই লাগে। অনেকবারই আমাদের মনে হয়েছে যে ওটা অভিনয় করি। আবার প্রত্যেকবারই মনে হয়েছে যে আমরা পারব না। আমাদের পক্ষে এ কাজ অত্যন্ত কঠিন। তারপর একদিন খালেদ চৌধুরী বহুরূপীতে এলেন। এবং রয়ে গেলেন।— লোকটির অস্বাভাবিক ক্ষমতা। আঁকতে পারেন, যে-কোনো বাজনা বাজাতে পারেন, গান শেখাতে পারেন, আর যত নতুন জিনিষ উদ্ভাবন করতে পারেন। তাঁকে পেয়ে আবার আমাদের মাথায় রক্তকরবীর চিন্তা পেয়ে বসল।
শম্ভু মিত্রের বক্তব্যে এইটুকু স্পষ্ট যে, রক্তকরবী মঞ্চস্থ করার কথা অনেকদিন ধরে ভাবলেও তাঁদের মনে হচ্ছিল এইরকম করে সংগীতসহ সর্ববিষয়ে তাতিয়ে দিয়ে শম্ভু মিত্র খালেদ চৌধুরীর যাবতীয় জড়তা মোচন করলেন যেন। খালেদ অবশ্য তাঁর নিজের গেঁতোমি বিষয়ে নিজেই সচেতন, কেউ চাপ সৃষ্টি না করলে কোনো কিছুতে যেতে চান না; আর গেলে, ভালোভাবেই যান। শম্ভু মিত্র খালেদ চৌধুরীর বিস্ময়কর উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দিতে গিয়ে লিখেছেন (“রক্তকরবী’তে সঙ্গীত প্রয়োগ”)—
যক্ষপুরীতে সুরকে খণ্ডিত করে বেসুরের প্রতাপ দেখাতে খালেদ কীভাবে টিউনিং ফর্ক নিয়ে পুরোনো লোহালক্করের দোকানে গিয়ে ভাঙা লোহার পাত সংগ্রহ করলেন, যেগুলো পর্দায় বাজবে, বাজনার ছন্দে মাঝে-মাঝে নাকাড়ার উপর ঝাঁটা মারা হবে, আর কাঠের টুকরোর উপরে কাঠি মেরে একসঙ্গে একটা যন্ত্রের আওয়াজ সৃষ্টি হবে; অন্যদিকে বাজবে বাঁশি; বাঁশি জীবনের উৎসারিত সুর, আর অন্য আওয়াজ জীবনের বেসুরত্বেরই ব্যঞ্জনাবহ, যে-আওয়াজ বাঁশির সুরকে ছাপিয়ে উঠতে চায়।
এই বর্ণনার পর তিনি বলেছেন যে, নাট্যাভিনয়ের ক্ষেত্রে, চেনা যন্ত্রের চেনা আওয়াজে মন বিশ্লিষ্ট হয়ে যায় বলে কখনও নতুন যন্ত্রের দরকার পড়ে, সে-ক্ষেত্রে খালেদ চৌধুরী অবিকল্প। এরকম এক প্রয়োজনে তিনি একটি যন্ত্র বানান, যার নাম দেন ‘ঘড়ঘড়ি’, তার আওয়াজ মোটা শেকলের মতো, তার উপর ঝাঁঝ, নাকাড়া ও বাঁশি বাজবে; যখন নন্দিনী ‘বিশু পাগল, পাগল ভাই’ বলে ডাকতে শুরু করবে, তখন বাঁশি সেই আর্তনাদকে সুরে তুলে নেবে; এইরকম আরো একটি যন্ত্র তৈরি করেছিলেন, যার নাম রাখা হয় ‘কাট্টুকুটুম’, তার সঙ্গে প্রয়োজনানুসারে বাঁশি-বেহালার সুর, যার মাধ্যমে নাটকে তৈরি হয় ‘রঙ আলো কথা সুর সব মিলিয়ে একটা অখণ্ড সত্তা’।
এই সময়কার অসাধারণ অভিজ্ঞতার কথা আমাদেরকে জানিয়েছেন শঙ্খ ঘোষ তাঁর ‘ইশারা অবিরত’ বইটিতে— ‘অভিনয় যে কেবল মঞ্চের উপরে কয়েকটি মানুষের অভিব্যক্তিময় চলাচলটুকুই নয়, তার সঙ্গে যে জড়ানো আছে দৃশ্যের আলোর সুরের ঘনিষ্ঠ অনেক সংযোগ, তারই একটা ধারণার দিকে পৌঁছলাম আমরা’—যার ফলে তাঁর মনে এই জিজ্ঞাসা তৈরি হলো যে, ‘এ সংযোগ ঘটান কারা?’— ছেলেবেলায় মঞ্চে অভিনেতাকে দেখতেন, পরে এর আড়ালে একজন পরিচালক যে আছেন তাও জানলেন, ফলে, চার অধ্যায়, দশচক্র, বা পুতুল খেলার মঞ্চ দেখতে-দেখতে শুরুতে ভেবেছেন শম্ভু মিত্রের কথা, পরে ভেবেছেন—কিন্তু শুধু শম্ভু মিত্রই কি? একটু একটু করে কি জানতে হয়নি যে, পরিচালকের আছেন অনেক সহায়ক, মঞ্চদৃশ্যের জন্য আলোর জন্য বা সুরের জন্য আরো অনেকের সৃষ্টিকাজকে ব্যবহার করতে হয় তাঁদের আর এভাবে এ শিল্প হয়ে ওঠে এক যৌথশিল্প? আমরা জেনেছিলাম শম্ভু মিত্রের তেমন এক সহায়কের নাম খালেদ চৌধুরী।
কিন্তু নাটকে শম্ভু মিত্রকে কতটুকু সহায়তা করেন খালেদ, তা কি সাধারণ কোনো দর্শকের পক্ষে বোঝা সম্ভব? খালেদ চৌধুরী বিষয়ে শম্ভু মিত্রের লেখাটি পড়বার আগে তার কোনো ধারণা করতে পারেননি স্বয়ং শঙ্খ ঘোষও। শম্ভু মিত্র খালেদ চৌধুরীর মধ্যে এমন মৌলিক বোধশক্তি আর অনন্য দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পেলেন—যা না থাকলে নাটক সফল হয় না। কিন্তু তাঁর বর্ণনাটি তো শুধু ‘রক্তকরবী’-র বিষয়ে; এর বাইরে যে আটটি নাটকে সংগীত প্রয়োগ আর ষাটটি নাটকের মঞ্চচিত্রণ করেছিলেন খালেদ চৌধুরী তার বিবরণ তো অলিখিতই রয়ে গেল। এ কারণেই শম্ভু মিত্র আক্ষেপ করেছিলেন, ‘দুর্ভাগ্যবশত আমাদের দেশে এত বিশৃঙ্খল অবস্থা যে এইসব অনন্য সৃষ্টির কোনো দলিল রাখা হয় না’ আর শঙ্খ ঘোষ লিখেছিলেন, ‘নেপথ্য প্রস্তুতির এইসব দলিলের অভাবে আমাদের থিয়েটারের কোনো ঠিক-ঠিক ইতিহাস তৈরি হতে পারল না এ পর্যন্ত।’
শিল্পের, সৃষ্টির এইসব ক্ষেত্রে খালেদের সাফল্য আর তাঁর কাজ সম্পর্কে শিল্পবোদ্ধাদের এমনতর শংসার কারণ হচ্ছে তাঁর প্রস্তুতি, উপলব্ধি ও চিন্তার মৌলিকতা—এই গুণ নিয়ে তিনি যে-মাধ্যমের সঙ্গে যুক্ত হতেন, প্রাণ নিয়ে যুক্ত হতেন; যা বোঝেন না, বা যে-বিষয়ের সঙ্গে প্রাণের যোগ তৈরি হয় না, তার সঙ্গে যুক্ত হতেন না কিছুতেই। কাজ নেওয়ার আগে সব কিছুকে তিনি নিজের চিন্তা, দৃষ্টিভঙ্গি ও সাহিত্যবোধের সাহায্যে পরখ করে নিতে চাইতেন; এই কারণে, রবীন্দ্রনাথের নাটক হওয়া সত্ত্বেও ‘দাদাঠাকুর’ চরিত্রটি না বোঝার কারণে ‘অচলায়তন’-এ কাজ করার প্রস্তাব ফিরিয়ে দেন, যে-কাজটি পরে বাধ্য হয়ে তাপস সেনকেই করতে হয়। খালেদের যুক্তি ছিল: এই নাটকটি পড়তে ভালো লাগে ঠিকই, এবং আইডিয়ার দিক থেকেও দাদাঠাকুরকে মানা যায়, কিন্তু বিশ্বাসযোগ্যতার দিক থেকে সেটিকে মেনে নেওয়া বেশ মুশকিল।
কাজের জায়গায় তাঁর এমনতর স্বচ্ছ চিন্তা ও ব্যাখ্যা থাকা সত্ত্বেও, ভাবনাগত স্বাতন্ত্র্যর কারণে তা সবসময় সকলের পক্ষে বোঝা সম্ভব হত না, আর তিনি সর্বস্থানে সেটা প্রকাশ করার পক্ষপাতী ছিলেন না, তাই মাঝে-মাঝে, কারো কারো সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝি হত। কিন্তু তিনি যখন নিজের চিন্তা সরাসরি প্রকাশ করতেন, তখন সেখানে শ্রোতাদের ঋদ্ধ হওয়ার মতো উপাদান থাকত। তার পরিচয় পাচ্ছি শম্ভু মিত্রের ‘অভিনয় নাটক মঞ্চ’ বইটির ভূমিকায়, তিনি লিখেছেন—’খালেদ চৌধুরী ছাড়া এই বই বেরুত না। প্রবন্ধের মধ্যে এমন অনেক জায়গা আছে, যা তাঁরই আলোচনা থেকে আহরণ করা। তাঁর প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা অশেষ।’
থিয়েটার বিষয়ে কথাবার্তা শম্ভু মিত্র ছাড়া হাতে গোনা দু-একজনের সঙ্গেই করতেন খালেদ চৌধুরী, এছাড়া বাকি সময় নিজের মতো করে থাকতে পছন্দ করেন। এই কারণেই, ‘পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি’ তৈরি হওয়ার পর অনেক অনুরোধ সত্ত্বেও প্রথমে সেখানে যোগ দিতে চাননি তিনি। কিন্তু তাপস সেন, বিভাস চক্রবর্তী এবং ইন্দ্রনাথের চাপাচাপিতে রাজি হয়ে, পরপর কয়েকটি প্রশিক্ষণ শিবিরে প্রশিক্ষক হিসেবে ক্লাস নেন। তাপস সেন এই প্রশিক্ষণ শিবিরের বর্ণনা দিয়েছেন (‘অন্তরঙ্গ আলো’) এভাবে—
আমরা দলবেঁধে ওর ক্লাসগুলো শুনতাম মন্ত্রমুগ্ধের মতো। আসলে ও যখন কথা আরম্ভ করে তখন তার প্রসার, ব্যাপ্তি তা তো সহজে পরিমাপ করা যায় না। অথচ আমাদের অমনোযোগিতায় ওর এসব অসাধারণ বক্তব্যগুলো আমরা কোনোভাবেই ধরে রাখতে পারি না। এ যে কত বড় ক্ষতি তা বলে বোঝানো যায় না।
পরে, কাগজ-কলমে সহ-সভাপতি থেকে গেলেও, খালেদ চৌধুরী তাঁর স্বভাবগত কারণেই সেখান থেকে নীরবে সরে এলেন। এই সহ-সভাপতিত্বের কারণেই, তিনি সংস্থার দেওয়া ‘দীনবন্ধু মিত্র পুরস্কার’টি গ্রহণ করেননি; তাঁর মতে, এই পুরস্কার গ্রহণ করা মানে, নিজেই নিজেকে পুরস্কার দেওয়া; আরেকটা কারণ অবশ্য তিনি জানিয়েছেন—এর আগে এই পুরস্কার যাঁরা পেয়েছেন, তাঁদের প্রায় সকলেই ছিলেন নাট্যকার, অতএব এই পুরস্কার তিনি নিতে পারেন না। প্রচলিত অর্থে যা সম্মান, তা প্রত্যাখ্যানের আরো কিছু ঘটনা অবশ্য তাঁর জীবনে আছে।
নিজের সম্পর্কে তাঁর মন্তব্যটি স্মরণ করা যেতে পারে—
আমি বেসিক্যালি নিজের সম্পর্কে জটিল ধারণার বিরুদ্ধে, যাকে বলে একনিষ্ঠ অথবা একগুঁয়ে। যা বিশ্বাস করি সেই জায়গাতেই দাঁড়িয়ে থাকতে ভালবাসি। যা বিশ্বাস করি না তা থেকে বেরিয়ে আসতে দু-মিনিটও লাগে না। ‘আইপিটি এ’ ছেড়েছিলাম ওদের মতাদর্শের সঙ্গে নিজেকে মেলাতে পারিনি বলে। ‘বহুরূপী’-র বেলায়ও তাই। শম্ভু মিত্রের ভাবনাচিন্তার সঙ্গে শেষদিন অবধি আমার অসম্ভব মিল ছিল শিল্পগত ভাবনার ক্ষেত্রে। গণ্ডগোল বাধল পাবলিসিটির ব্যাপারটি নিয়ে। উনি চাইলেন আমার নাম দিতে, আমি চাইলাম না।
খালেদ চৌধুরী এরকমই, আপসহীন, জেদি আর মোহহীন; মহাশ্বেতা দেবী, সুদেষ্ণা বসু-র ‘খালেদদা’ বইয়ের মুখবন্ধে তাঁদের একসময়ের ‘সম্প্রসারিত পরিবার’-এর বর্ণনা দিয়ে বুঝিয়ে দেন যে, তাঁরা যে-জীবন কাটিয়ে এলেন, তারপরে, আজ রাজনীতি যখন দুর্বৃত্তায়িত তখন খালেদের মতো মানুষের পক্ষে বহু বিষয়ে নির্মোহ না হয়ে উপায় নেই; কারণ, এখন বিশ্বাস ন্যস্ত রাখা কঠিন।
কিন্তু তাঁর কাছ থেকে কোনোকিছু গ্রহণ করার কি আর আমাদের দরকার নেই কারো? বলা বাহুল্য পরিণত বয়সে এসে যিনি ভাবতে পারেন, কবিতা-উপন্যাস-নাটক-ভাস্কর্য-নৃত্য-সংগীত সবকিছু যার যার মতো করে কথা বলতে চাইছে—তাঁর কাছ থেকে আমাদের পাওয়ার এখনও অনেক কিছুই আছে। অনেকের মতো গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে দিয়ে নিজেকে সমর্পণ করেননি তিনি। এবং তাই তিনি অনেকখানিই আমাদের থেকে আলাদা; সকলের সঙ্গে একসঙ্গে নিবিড়ভাবে থেকেও তবু বিশেষ এক ব্যতিক্রম খালেদ চৌধুরী। এই মানুষটিকে নিজেদের প্রয়োজনের জন্যে হলেও—আমাদের শ্রদ্ধা জানানো উচিত, তাঁকে না জানিয়ে, অস্বস্তির মধ্যে ফেলে না দিয়ে।
প্রচ্ছদচিত্র, স্কেচ সৌজন্য: শিল্পী সুবর্ষা চক্রবর্তী।
খালেদ চৌধুরীকৃত গ্রন্থ প্রচ্ছদ সৌজন্য: ফেসবুক গ্রুপ ‘প্রচ্ছদনামা’ ও ‘মলাটচিত্র’।