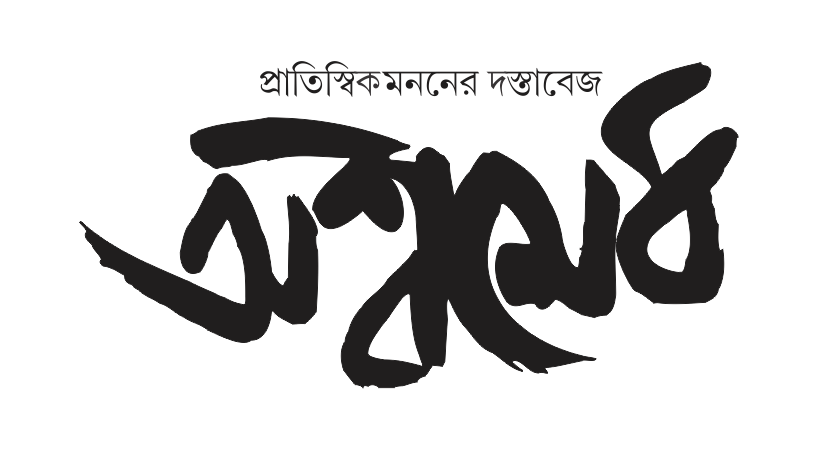ভারতীয় জনতা পার্টির নানা মাপের নেতারা দাবি জানাচ্ছেন উত্তরবঙ্গ-কে পৃথক রাজ্যে করার। এ দাবি নতুন নয়, বারে বারে নানা কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে ‘বিচ্ছিন্নতাবাদী’ আন্দোলন সূত্রে।
বর্তমান রাজ্য সরকার ‘উত্তরবঙ্গ’ বিষয়ে যে ‘সংবেদনশীল’ তা বলা বাহুল্য। বিগত কয়েক বছরে কামতাপুরী বা রাজবংশী ভাষা আকাদেমি গঠন তার সাক্ষ্য। রাজবংশী ভাষা আকাদেমি গঠনের সিদ্ধান্তর পর, ২০১৬ সালে কামতাপুর প্রোগ্রেসিভ পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্ত থেকে যেমন জানা যায়, বিধানসভা ভোটে রাজ্যের বর্তমান শাসক-গোষ্ঠীকে সমর্থন দেওয়া হবে ‘ভাষাভিত্তি চুক্তি’ অনুযায়ী। অবশ্য ২০১৭ সালে কামতাপুরী ভাষা আকাদেমি গঠনের সরকারি ঘোষণার পর রাজবংশী ভাষার বুদ্ধিজীবীরা (যেমন, নিখিলেশ রায়, দীপক রায়, গিরিজাশঙ্কর রায়, সত্যেন বর্মন প্রমুখ) প্রতিবাদ-স্বরূপ রাজ্য সরকারকে চিঠি দিলেন উক্ত ঘোষণাকে অনৈতিহাসিক জানিয়ে।
পশ্চিমবঙ্গের সাম্প্রতিক ইতিহাসে বাংলা ভাগের প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে গোর্খাল্যান্ড-কে চিহ্নিত করে ‘বাংলা ও বাংলা ভাষা বাঁচাও কমিটি’র সভাপতি মুকুন্দ মজুমদার বলছেন,—জিটিএ-র মাধ্যমে স্বায়ত্তশাসন ও সে-ই সঙ্গে বিপুল আর্থিক প্যাকেজ পেলেও দার্জিলিং-তরাই-ডুয়ার্স এবং জলপাইগুড়ির বিস্তীর্ণ এলাকার বাঙালি, রাজবংশী, আদিবাসী ও অন্যান্য জনজাতির মানুষ নেপালিদের সঙ্গে বসবাস করেও নেপালিদের তুলনায় সবদিক থেকে বঞ্চিত, তাঁদের জীবনযাপনের মান নেপালিদের তুলনায় অনুন্নত। এই বৈষম্য তৈরি হওয়ার অন্যতম কারণ হিসেবে তিনি উল্লেখ করছেন—কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষপাতিত্বকে।
১৯৪৭ পূর্ব বা পরবর্তী সময়েও উচ্চশিক্ষা হোক বা জীবিকা এমনকি চিকিৎসার প্রয়োজনেও প্রান্তবাসীর কলকাতা-মুখী হওয়ার নিয়মে কোনও ছেদ পড়েনি। পাশাপাশি সংস্কৃতির পীঠস্থান হিসেবেও ‘পশ্চিমবঙ্গ ও কলকাতা’ পরিপূরক এই অলিখিত ধারণা ধীরে ধীরে রূপ পেয়েছে। অলিখিত এই ধারণার বিপরীতে শহর কলকাতার বাইরের যে পশ্চিমবঙ্গ স্বাভাবিকভাবেই স্থানীয় সমস্যাগুলি নিয়ে ক্ষোভ-বিক্ষোভ সেখানে বেড়েছে, যে অসন্তোষগুলিকে একবাক্যে খারিজ করা সবক্ষেত্রে সম্ভবপর হয়তো নয়। এই প্রতর্কের ভালোমন্দর ভেতর প্রবেশ করার উদ্দেশ্যে এ নিবন্ধ নয়। বরং যে বিষয়টি নিয়ে ভাবার তা হলো সাম্প্রতিক সময়ে জঙ্গলমহল-কেও এই ভাবে স্বতন্ত্র রাজ্যের স্বীকৃতি দেওয়ার মনোবাঞ্ছা জাহির করেছেন এক নেতা।
পিলচু বুড়ি আর পিলচু হামামের সাত সন্তান। তারপরেও পাঁচটি টোটেম গোষ্ঠীর যোগ দেওয়ায় সংখ্যাটা হলো মোট বারো। পণ্ডিতরা বলেন এঁরা দক্ষিণ-ভারতীয় নৃগোষ্ঠীর শাখা। লর্ড টেইঙ মাউথের বিবরণ থেকে যেমন জানা যাচ্ছে, আঠারো শতকের শেষভাগ থেকে এই গোষ্ঠীর বসতির সন্ধান মিলেছে বাংলাদেশের এই অংশে। যাঁদের ‘সাঁওতাল’ হিসাবে অভিহিত করা হয়। এমনটা মনে করা হয় যে, সতেরোশো সালের দুর্ভিক্ষ একটি মূল কারণ; কিরাতকে ভূমিপুত্রে, কৃষকে পরিণত করার ক্ষেত্রে। ১৭৯৩-এর চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মধ্যেই বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম ভূখণ্ডের একটা বিরাট অংশের দখল নিল এই ভূমিপুত্রেরা। যে ভূখণ্ডের নাম জঙ্গলমহল। এই সাবেক জঙ্গলমহল এবং পরবর্তী মানভূমের অনেকাংশ আজ বিহার তথা ঝাড়খণ্ডের অধীন। প্রান্তিক, অনুন্নত অঞ্চল হিসাবে বাম আমলের ‘অবজ্ঞা’ কাটিয়ে, সরকারি উন্নয়নের দাগ খতিয়ানে জঙ্গলমহল-এর অন্তর্ভুক্তিরও অনেকগুলি দিন পার হলো।
ভাষা-বিভ্রাট দক্ষিণবঙ্গে বা জঙ্গলমহলে কিছু কম নয়। রঘুনাথ মুর্মু কৃত অলচিকি হরফকে বাম আমল-এর তপশিলি ও আদিবাসী মন্ত্রী ড. শম্ভু মান্ডির ব্যবস্থাপনায় সরকারি স্বীকৃতি দেওয়া হয় (বিহার ও উড়িষ্যায় সে-ই সময়ে এই হরফকে সরকারি স্বীকৃতি যদিও দেওয়া হয়নি)। সরকারি নির্দেশে স্কুল-কলেজে অলচিকি পড়ানোর কথা বলা হলেও, বাংলার সাঁওতালরা যে বাংলা ভাষাটি ‘প্রায় মাতৃভাষার’ মতোই বলতে পারেন এ কথা জানিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা। একইভাবে অন্য রাজ্যের বাসিন্দা হিসাবে ওড়িয়া বা হিন্দি বলতে, পড়তে ও লিখতে তাঁরা অভ্যস্ত। বাংলাদেশের মুণ্ডা, ভূমিজ, লোঠা, খেড়িয়া, বীরহড়, মাহালি, সবর, হো, মালপাহাড়ি, বেদিয়া প্রভৃতি জনজাতিগুলির বহু মানুষ নিজস্ব ভাষার পাশাপাশি মিশ্র বাংলা ভাষা ব্যবহার করে। কুর্মি সম্প্রদায়ের ভাষা কুড়মালি বলা হলেও কুর্মিরা সাধারণত বাংলা ভাষাতেই কথা বলেন। বাংলাদেশে কোনও কোনও জাতি নিজেদের ভাষা সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে এই মিশ্র বাংলা ভাষায় অভ্যস্ত হয়েছে। ১৮৯১ সালে জনগণনার ভিত্তিতে গ্রিয়ারস্ন যে ভাষা সমীক্ষা করেছিলেন, তাতেও বলা হয়েছে যে—ছোটনাগপুর অঞ্চলে বিহারি ভাষার চল থাকলেও মানভূম অঞ্চল বাংলাভাষীদের।
অলচিকি ভাষা বিষয়ে সাঁওতালদের নিজেদের ভেতরেই মতভেদ রয়েছে, বিরোধিতা হয়েছে বিদ্যালয়ে অলচিকি ভাষা পড়ানোর সরকারি সিদ্ধান্তেরও। এক্ষেত্রে মিশনারিদের প্রভাবকেও অস্বীকার করা যায় না। যে কারণে ‘সাঁওতালি লিটারেসি সোসাইটি’ শিক্ষার ক্ষেত্রে বাংলা ও রোমক লিপির পক্ষে ছিল। রাজ্যের শতাধিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অলচিকি ভাষা শিক্ষার সরকারি নির্দেশ যেমন রয়েছে, তেমনই রয়েছে আদিবাসী সংগঠনগুলির তরফে শিক্ষক নিয়োগের দাবি ও সরকারি ঔদাসীন্যের প্রতি অভিযোগ। সাঁওতালি ভাষা আন্দোলনের এক দীর্ঘ ইতিহাস এদেশে থাকলেও, এযাবৎকালে সরকারি উদ্যোগে ‘ভাষা আকাদেমি’ জাতীয় ‘সংঘ’ গঠনের কোনও প্রস্তাব-পরিকল্পনার কথা আমাদের জানা নেই। উত্তরবঙ্গে যে দুটি ‘ভাষা আকাদেমি’ গঠন করা হয়েছে, ভাষা চর্চার নিরিখে তার ভূমিকা সম্পর্কেও সন্দিহান বহু স্থানীয় মানুষই।
স্বাধীনতার ৭৫ বছরে, পুরুলিয়ার ‘বঙ্গভুক্তি’রও ৬৫তম বছরে পদার্পণ। বর্তমানের এই ‘বঙ্গভঙ্গ’-র রাজনৈতিক দড়ি টানাটানির আবহে, কেন্দ্র সরকারের ‘এক দেশ’ প্রকল্পে, ‘এক দেশ এক ভাষা’-নীতি প্রয়োগ পরিকল্পনার দিনে, আমরা আরও একবার ফিরে পড়া বা দেখা প্রয়োজন মনে করলাম এই মানভূম ভাষা আন্দোলনকে।
২.
ভারতবর্ষের স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পরের বছরই মানভূম জেলায় ভাষা আন্দোলন শুরু হয়েছিল। জেলার যাঁরা স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতা ছিলেন, তাঁরা ভাষা আন্দোলনেরও নেতা হলেন। প্রকৃতপক্ষে মানভূমের ভাষা আন্দোলন ছিল এই জেলার ক্ষেত্রে দ্বিতীয় স্বাধীনতা আন্দোলন। সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের চেয়েও হিন্দি সাম্রাজ্যবাদীরা মানভূমের মাতৃভাষার জন্য আন্দোলনকারীদের উপর নৃশংস অত্যাচার করেছিল, হীন চক্রান্ত ও মিথ্যার আশ্রয় তো তারা পদে পদে নিতো।
বিহার প্রাদেশিক কংগ্রেস সহ জাতীয় কংগ্রেসের সমুদয় জেলা নেতৃত্ব মানভূমের ভাষা যে বাংলা তা মানতে অস্বীকার করেছিল। বাংলা ভাষায় পড়াশোনার অধিকারটুকুও তারা কেড়ে নিয়েছিল। বৃটিশ আমল থেকেই মানভূমের জনসাধারণ জমির দলিল লেখার কাজ, বিচারালয় ও সরকারি অফিসে বাংলা ভাষার ব্যবহার করতেন, স্বাধীনতা-প্রাপ্তির পরপরই সে অধিকারও কেড়ে নেওয়া হয়। মানভূমের গৃহ-পরিবেশে, সামাজিক আচার অনুষ্ঠানে, চিঠিপত্রাদিতে, পুথি রচনা সহ সর্ববিধ সারস্বত-চর্চায়, এমনকি মন্দিরে উৎকীর্ণ শ্লোকগুলিতে যে বাংলা ভাষা ব্যবহৃত হতো তা তাঁরা অস্বীকার করলেন। এমনকি টুসু ভাদু করম ঝুমুর সহ সমৃদ্ধ লোকগানের ভাণ্ডারও যে বাংলা ভাষায় রচিত হয়নি তা প্রমাণ করতে তাঁরা সচেষ্ট হলেন। বিহারে বসবাসকারী সমস্ত বাঙালিদের জন্য ‘ডোমিসাইল সার্টিফিকেট’ দাখিল করা জরুরি ছিল, এই আইনকেও কঠোরভাবে বলবৎ করা হলো স্বাধীনতার পর।
১৯৪৬ সালে ’গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং’ নামে কুখ্যাত দাঙ্গার পালটা হিসেবে বিহার প্রদেশের ভয়ংকর দাঙ্গায় সংখ্যালঘুদের উপর নৃশংস অত্যাচার হয়েছিল, সে সময় সে-ই দাঙ্গা দমনের জন্য ‘জননিরাপত্তা আইন ১৯৪৬’ তৈরি হয় এবং বিহার সরকার ১৯৪৮ থেকে শুরু হওয়া— মানভূমবাসীদের ভাষা আন্দোলনকে দমন করার জন্য ওই আইনটিকেও প্রয়োগ করতে শুরু করে। প্রশাসনের সর্বোচ্চ পদগুলিতে যেমন—পুলিশ প্রশাসন, ডিসি, ডিএফও, ডিআই প্রভৃতি পদে বাংলা ভাষা বিদ্বেষী হিন্দিভাষী আধিকারিকদের নিয়োগের মাধ্যমে মানভূমের বাংলাভাষীদের উপর নির্বিচার নিপীড়ন চালানো হতো। সে-ই সঙ্গে মানভূম কংগ্রেসের বাংলাভাষী অথচ বিহার-প্রেমী নেতাদের সহযোগিতায় বাঁধ, কুয়া প্রভৃতির জন্য প্রভূত সরকারি আর্থিক অনুদান বিলি করে এলাকাবাসীকে বিহার প্রদেশে রাখার জন্য প্রচেষ্টারও শুরু হয়।
হরিপদ সাহিত্য মন্দির কর্তৃপক্ষের কাছেও প্রস্তাব আসে—’মানভূমের ভাষা হিন্দি’—এই প্রস্তাবের পক্ষে মত দিলে অনুদান পাওয়া যাবে। হরিপদ সাহিত্য মন্দির সে-ই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলে, তার প্রতিক্রিয়ায় বিহার সরকার নির্মাণ করে হিন্দি সাহিত্যের গ্রন্থাগার ‘স্টেট লাইব্রেরি’ যা বর্তমানে পুরুলিয়ার জেলা গ্রন্থাগার।
প্রাথমিক স্তরের সর্বনিম্ন শ্রেণি থেকে হিন্দি ভাষায় পড়া বাধ্যতামূলক করা হলো, পুরুলিয়া জেলা স্কুলে বাংলা বিভাগ কার্যত তুলে দেওয়া হলো। টেক্সট বুক কমিটি হিন্দি ছাড়া অন্য কোনও ভাষায় বই ছাপাবে না এই নির্দেশ জারি হলো। প্রতিটি বিদ্যালয়ে কালো জমিনের উপর সাদা রঙে হিন্দি ভাষায় সাইনবোর্ড টাঙানো এবং প্রার্থনার সময় রামধূন গাওয়া বাধ্যতামূলক করা হলো, প্রত্যেক সার্কেলের এসআই-দের ১৯৪৮ সালের ৩১ মার্চের মধ্যে হিন্দি ভাষায় সমস্ত হিসাবপত্র এবং রিপোর্ট ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করার নির্দেশ দেওয়া হলো। যেসব স্কুল-পড়ুয়া বাংলা ছাড়া অন্য ভাষায় কোনও পাঠ নেয়নি তারা যেমন সমস্যায় পড়ল, যে শিক্ষকরা হিন্দি পড়তে-লিখতে অভ্যস্ত নন তাঁরাও পড়লেন দুর্বিপাকে।
ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম তিন দশকে এতদঞ্চলে দুটি জেলা তৈরি হয়েছিল—একটি জঙ্গলমহল (১৮০৫) অন্যটি মানভূম (১৮৩৩)। জঙ্গলমহলের সদর শহর ছিল বাঁকুড়ায় এবং মানভূমের সদর শহর ছিল প্রথমে মানবাজার পরে পুরুলিয়া (১৮৩৮)। বিশেষজ্ঞরা বলেন: মানভূম জেলা তৈরির কারণ ছিল—শেষ চুয়াড় বিদ্রোহ (১৮৩২)—যাকে ইংরাজ ঐতিহাসিকগণ ‘গঙ্গানারায়ণ হাঙ্গামা’ বলে চিহ্নিত করেছেন। জঙ্গলমহল জেলা হিসাবে প্রশাসনিক দিক থেকে কোনও সুবিধে ব্রিটিশদের যে দেয়নি তা বলা বাহুল্য। মানভূম জেলা তৈরির পর এই এলাকায় বহুতর কৃষক সংগ্রাম মাথা তুলেছিল যেমন—সাঁওতাল বিদ্রোহ (১৮৫৫), সিপাহি বিদ্রোহ (১৮৫৭) প্রভৃতি; সাঁওতাল বিদ্রোহের কেন্দ্রস্থল সাঁওতাল পরগণা হলেও তার আঁচ এই অঞ্চলেও পড়েছিল স্বাভাবিকভাবেই। আর সিপাহি বিদ্রোহে এই এলাকার সাঁওতাল আদিবাসী জনজাতিদের অংশগ্রহণের কাহিনি পণ্ডিতরা সকলেই স্বীকার করেন।
মানভূম জেলা তৈরির সময় জেলাটির এলাকা ছিল ৭৮৯৬ বর্গমাইল। যদিও জেলা গঠনের এক দশক পেরোতে না পেরোতেই জেলাটিকে খণ্ডন করার প্রয়াস শুরু হয়েছিল। দ্বাদশ বর্ষে (১৮৪৫) ধলভূম পরগণা বিচ্ছিন্ন করা হলো। পরের বছর (১৮৪৬) ছাতনাকে বাঁকুড়া জেলার সঙ্গে যুক্ত করা হলো। ১৮৭১-এ পাণ্ড্রা-পোদ্দারডিকে মানভূম থেকে বাদ দেওয়া হলো এবং শেষে ১৮৭৯ সালে সুপুর, অম্বিকানগর, সিমলাপাল ভেলাইডিহা, ফুলকুসমাকে বাঁকুড়া জেলার সঙ্গে যুক্ত করা হলো। মানভূমের আয়তন কমে দাঁড়াল ৪১১২ বর্গমাইলে; ১৮৩৩-এ জেলা তৈরি হওয়ার ৪৬ বছরের মধ্যেই অর্ধেক রাজত্ব শেষ।
বিংশ শতাব্দীর সূচনায় বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ আন্দোলন ছিল বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন। তখনকার বাংলাদেশ ছিল আকবর বাদশার তৈরি করা—বাংলা সুবা; সকলে একে সুবা বাংলা বলতো। বাংলা-বিহার-উড়িষ্যা মিলে ছিল এই সুবা। লর্ড কার্জন এই বাংলা সুবা ভাগ করার প্রস্তাব করেন ১৯০৫ সালের ১৯ জুলাই। বলা হলো—রাজশাহী, চট্টগ্রামের সঙ্গে মালদহ জেলা, পার্বত্য ত্রিপুরা ও আসামকে নিয়ে তৈরি হবে পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশ, রাজধানী হবে ঢাকা। অবশিষ্ট বাংলা বিহার ও উড়িষ্যাকে নিয়ে প্রস্তাবে বলা হয়—ঢাকা হবে বাংলা প্রদেশ, রাজধানী হবে কলকাতা। ১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর এই সিদ্ধান্ত কার্যকর করার দিন ধার্য হয়। সারা বাংলাদেশে আন্দোলন শুরু হয়, অবশেষে ব্রিটিশ সরকার এই সিদ্ধান্ত কার্যকর করা থেকে বিরত থাকে। এর এক যুগ পরে ১৯১১ খ্রিস্টাব্দের ১২ ডিসেম্বর দিল্লিতে ‘দরবার উৎসব’ পালন করা হয়। পঞ্চম জর্জ ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে কয়েকটি সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। সিদ্ধান্তগুলি ছিল এরকম—(১) বাংলাদেশকে ভাগ করার সিদ্ধান্ত রদ হলো (বঙ্গভঙ্গ রদ), (২) কলকাতা থেকে ভারতের রাজধানী দিল্লিতে স্থানান্তরিত হবে, (৩) সুবা বাংলাকে নিম্নলিখিত দুটি প্রদেশে ভাগ করা হবে (ক) বাংলাদেশ (রাজধানী কলকাতা) ও (খ) বিহার-উড়িষ্যা (রাজধানী পাটনা)। চতুর্থ সিদ্ধান্তটি সম্পূর্ণতই মানভূম জেলার জন্য—মানভূম জেলা বিহার-উড়িষ্যা রাজ্যের অন্তর্ভক্ত হবে। ১৯১২ খ্রিস্টাব্দর ১ এপ্রিল এই প্রস্তাবগুলি কার্যকরী হবে।
মানভূম জেলাকে বিহার-উড়িষ্যা রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করার বিরুদ্ধে সেদিন প্রবল আন্দোলন বিক্ষোভ হয়েছিল, মূলত রজনীকান্ত সরকার ও শরৎচন্দ্র সেন এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। বাংলাভাষী মানভূম কেন বিহার ও উড়িষ্যা রাজ্যের মধ্যে যাবে সে বিষয়ে মানভূমের বাইরের বহু বুদ্ধিজীবীও প্রশ্ন তুলেছিলেন।
রাঁচীর শরৎচন্দ্র রায়, যাঁকে ভারতবর্ষের ‘ফাদার অব অ্যানথ্রোপোলজি’ বলা হয়, তিনিও এই সিদ্ধান্তের তীব্র প্রতিবাদ করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে যুগ যুগ ধরে বাংলাদেশের মধ্যে থেকে ভাষা শিক্ষা সংস্কৃতি খাদ্যাভ্যাস আচার-আচরণ সামাজিক রীতিনীতি অর্থনীতি রাজনীতি সমস্ত বিষয়ে বাংলাদেশের আবহাওয়ায় বেড়ে উঠেও কী কারণে মানভূমবাসীদের বিহার-উড়িষ্যা রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করা হলো তার কোনও যুক্তিগ্রাহ্য কারণ ব্রিটিশ শাসকরা দিতে পারেনি। ভাষা বিচারে সমগ্র মানভূমই ছিল বাংলাভাষী; শুধু মানভূম নয় গিরিড়ি, হাজারিবাগ, রামগড় সহ সুবর্ণরেখার ওপারে রাঁচী পর্যন্ত সমগ্র এলাকাটিই বাংলাভাষী বা ‘গ্রেটার বেঙ্গল’ নামে পরিচিত। জামশেদপুরের ক্ষেত্রেও একই যুক্তি প্রযোজ্য। তা সত্ত্বেও কেন এবং কী বিচারে মানভূমের অবস্থান হলো বিহার-উড়িষ্যায় তার যুক্তিগ্রাহ্য উত্তর মিলল না। উক্ত অঞ্চলগুলিতে মানভূম ভাষা আন্দোলনের প্রভাব বিষয়ে বিস্তৃত তথ্য সেভাবে উপলব্ধ নয় এখনও, গবেষকগণ এ বিষয়টির যথাযথ সন্ধান করলে সে তথ্য নিশ্চয় পাঠকের সামনে আসবে। এক্ষেত্রে শুধু এটুকুই বলার—এই সমগ্র অঞ্চলে বাংলা ভাষার জন্য আন্দোলনে মানভূমই অগ্রজ।
১৯১২ থেকে মানভূম জেলা প্রথমে বিহার-উড়িষ্যা রাজ্যে, পরে ১৯৩৬-এ উড়িষ্যা রাজ্য তৈরি হলে বিহার রাজ্যের মধ্যে থাকতে বাধ্য হলো। স্বাধীনতা আন্দোলনের সে-ই উথালপাতাল দিনে বিহার রাজ্যের মধ্যে থেকেই মানভূম স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশ নিল। মানভূমের স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ সারা দেশেই শ্রদ্ধা পেয়েছেন। ঋষি নিবারণচন্দ্র দাশগুপ্ত, অতুলচন্দ্র ঘোষ, বীরবাঘব আচারিয়া, গিরিশচন্দ্র মজুমদার, অন্নদাপ্রসাদ চক্রবর্তী, বিভূতিভূষণ দাশগুপ্ত, লাবণ্যপ্রভা ঘোষ, ললিতকিশোর মিত্র, জীমূতবাহন সেন প্রমুখ নেতৃবৃন্দ সারা দেশের যে-কোনো এলাকার মানুষের তুলনায় যোগ্যতায় কৃচ্ছ্রসাধনায় ন্যূন ছিলেন না। কংগ্রেসের সভাপতি ও সম্পাদক হিসাবে প্রথমে নিবারণচন্দ্র দাশগুপ্ত ও অতুলচন্দ্র ঘোষ; পরে ১৯৩৫ সালে নিবারণবাবুর মৃত্যুর পর—অতুলচন্দ্র ঘোষ ও বিভূতিভূষণ দাশগুপ্ত গভীর শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন।
স্বাধীনতা-প্রাপ্তির পরপরই গোটা ঘটনার পরিপ্রেক্ষিত দ্রুত পরিবর্তিত হলো। বিহার প্রাদেশিক কংগ্রেস ও সর্বভারতীয় কংগ্রেস নেতৃত্বের নিকট বারেবারে মানভূমের ভাষা-সমস্যা সমাধানের জন্য আবেদন করেও মানভূম জেলা কংগ্রেস ব্যর্থ হয়ে চরম রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়। বিহার সরকার মানভূমবাসীর স্বার্থের পরিপন্থী নানাবিধ সিদ্ধান্ত সার্কুলার আকারে পাঠাতে থাকল। যার ফলে মানভূমের জনমানসে স্বাধীন সরকারের সদিচ্ছা সম্পর্কে প্রশ্ন দেখা দিল। এর মধ্যেই মানভূম জেলা কংগ্রেস অধিবেশন ডাকা হলো, বান্দোয়ান থানার জিতান গ্রামে (৫ মে, ১৯৪৮)। সেখানে একটি প্রস্তাব এল—মানভূমের ভাষা বাংলা। মানভূম জেলার দুটি মহকুমা পুরুলিয়া সদর ও ধানবাদ। ধানবাদের প্রতিনিধিরা ওই প্রস্তাব সম্পর্কে আলোচনার জন্য অন্য দিন ধার্য করার আবেদন জানালে ২৫ মে ও ৩০ মে (১৯৪৮) যথাক্রমে জেলা কার্যকরী কমিটি ও জেলা কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন বসল। মানভূমের ভাষা বাংলা—সভাপতির এই প্রস্তাব ৪৩-৫৫ ভোটে পরাজিত হলো। হিন্দিভাষী ধানবাদ মহকুমার প্রতিনিধিদের সঙ্গে পুরুলিয়া সদর মহকুমার প্রতিনিধিরাও সভাপতির প্রস্তাবের বিপক্ষে ভোট দেওয়ায় প্রস্তাবটি ১২ ভোটে পরাজিত হয়। ওই সভাতেই জেলা কংগ্রেসের সভাপতি অতুলচন্দ্র ঘোষ, সম্পাদক বিভূতিভূষণ দাশগুপ্ত সহ পুরুলিয়া সদর মহকুমার ৩৪ জন ও ধানবাদ মহকুমার একজন মোট ৩৫ জন জেলা কমিটির সদস্য একযোগে জেলা কমিটি ও কংগ্রেসের সাধারণ সদস্যপদ থেকে ইস্তফা দিলেন। ১৩ ও ১৪ জুন পুঞ্চা থানার পাকবিড়রা গ্রামের কর্মীসভায় কংগ্রেস থেকে পদত্যাগী কর্মী-নেতৃত্বে ‘লোকসেবক সংঘ’ নামক নতুন গান্ধিবাদী আঞ্চলিক রাজনৈতিক দলের প্রতিষ্ঠা হলো।
৩.
মানভূম ভাষা আন্দোলন পরিচালিত হয় লোকসেবক সংঘের নেতৃত্বে। এই আন্দোলনের সময়কাল ছিল ১৯৪৮ সাল থেকে ১৯৫৬ সাল—এই নয় বছর ব্যাপী। দেশের মধ্যে প্রথম ‘ভাষাভিত্তিক’ রাজ্য গঠনের দাবিতে আন্দোলন শুরু হয়েছিল মানভূমে। স্বাধীনতার আগের ও পরের বিভিন্ন অধিবেশনে পশ্চিমবাংলার প্রতিনিধিবৃন্দ সর্বভারতীয় কংগ্রেস নেতৃত্বের নিকট মানভূম জেলাকে পশ্চিমবাংলায় ফেরত দেওয়ার জন্য আবেদন করে; সর্বভারতীয় নেতৃত্বও বিবেচনার আশ্বাস দেয়, কিন্তু কার্যকরী কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয় না।
লোকসেবক সংঘ-র নেতৃত্ব ও কর্মীরা ১৯১২ সালে বাংলাদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া সম্পূর্ণ মানভূম জেলার সঙ্গে আরও বহুতর বাংলাভাষী এলাকাকে পশ্চিমবাংলায় ফেরত দেওয়ার দাবিতে যে আন্দোলন গড়ে তুলল চরিত্রে তা বহুমাত্রিক। মানভূমের জাতীয় কংগ্রেসের ভূমিকা ছিল সমগ্র মানভূম জেলাকে বিহার প্রদেশের মধ্যেই রাখার পক্ষে। কংগ্রেসের নবনির্বাচিত সভাপতি মহেশ্বর মাহাত (মাগুড়িয়া) সহ সমস্ত কংগ্রেস দলটিই এই ভূমিকা পালন করত। অপরদিকে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি সহ সমস্ত বামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলি মানভূমের বঙ্গভুক্তির পক্ষে হওয়া এই আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিল। এছাড়া পুরুলিয়া বারের একদল প্রবীণ উকিল-ব্যারিস্টার-মোক্তার এই আন্দোলনের প্রধান প্রচারক সমর্থক ও সহমর্মী ছিলেন। হরিপদ সাহিত্য মন্দির, পুরুলিয়া পৌরসভা, জেলা বোর্ড সহ বহু সাবেকি প্রতিষ্ঠান এই আন্দোলনের সমর্থক ছিল। এর মধ্যেও বেশ কিছু বুদ্ধিজীবী সহ রাজনৈতিক কর্মী ও প্রবীণ নাগরিক মানভূমের বিহার প্রদেশে থাকা সমর্থন করতেন। পুরুলিয়ার বঙ্গভুক্তির অর্ধশতক পেরিয়ে এখনও এই মতের প্রচ্ছন্ন সমর্থক যে আছেন তা বলা বাহুল্য।
দু-দফায় অসহযোগ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে লোকসেবক সংঘের নেতৃত্ব ভাষা আন্দোলনকে সারা জেলার দূরতম প্রান্তে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। ১৯৪৯ সালের ৬ এপ্রিল থেকে ১৬ এপ্রিল পর্যন্ত পুরুলিয়া সদর মহকুমার ২১টি থানার ৬৪টি গ্রামে অসহযোগ আন্দোলনের প্রথম পর্যায়টি সম্পন্ন হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ের আন্দোলনে জেলার ২২টি স্থানে বৃহৎ জমায়েত করে সরকারের জনবিরোধী কর্মসূচীর বিরূদ্ধে ধিক্কার জানানো হয়। ১৯৫১ সালের ৯ মার্চ থেকে ১১ মে পর্যন্ত এই কর্মসূচীটি পালিত হয়। এ সময় মানভূম জেলায় অনাবৃষ্টির ফলে ফসল ফলেনি, কাপড়ের সরবরাহ কম থাকায় কাপড়ের সংকট শুরু হয়। খাদ্যের জোগান কম থাকায় চালের দর হয় আকাশ-ছোঁয়া। সে-ই কারণে ১৯৪৯ সালের মে মাস থেকে ১৯৫১ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত প্রায় দু-বছর আন্দোলনের সমস্ত কর্মসূচীই স্থগিত রাখা হয়। বিহার সরকার জঙ্গলের পাতা ফুলফল তুললেও সাধারণ মানুষের উপর জরিমানা করত। কেস দিয়ে কোর্টে চালান করত। এমনকি দাঁতনের জন্য গাছের ডাল ভাঙলেও বন দপ্তরের কঠোর আইনের জালে পড়তে হতো স্থানীয় মানুষদের। সে-ই কারণে প্রতিবাদ-স্বরূপ লোকসেবক সংঘ ‘হালজোয়াল’ আন্দোলন শুরু করল। জজ কোর্টের চত্বর ও তৎসংলগ্ন ফাঁকা জায়গায় গ্রামের মানুষ বনের কাঠ কেটে হাল ও জোয়াল তৈরি করে বিক্রি করত। পুলিশের চোখের সামনেই এই কাজ হতো—এই প্রতিবাদী আন্দোলনের নাম—হালজোয়াল আন্দোলন।
ভাষা আন্দোলনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় ছিল—টুসু সত্যাগ্রহ। টুসু গান মানভূম তথা ছোটনাগপুরের জনপ্রিয় লোকগান। সারা পৌষ মাস জুড়ে মেয়েরা এই গান গায়। পৌষ পার্বণের দিন চৌদল নিয়ে মেয়েরা নদীতে টুসু ভাসাতে যায় গান গাইতে গাইতে। এই লোকগানকে সংঘের নেতারা অতীব দক্ষতায় রাজনৈতিক আন্দোলনের বিষয় করে তুললেন। টুসু গান গাইলে পুলিশ গায়কদের বিরুদ্ধে কেস দিত। বিখ্যাত টুসু গানগুলির দু-একটির প্রথম কলির উল্লেখ করা যাক—’ও বিহারী ভাই, তোরা রাইখত্যে লারবি ডাঙ্গ দেখাই’ (ভজহরি মাহাত), ‘মানভূমবাসী থাইকব্যে সতরে, ধলভূমবাসী থাইকব্যে সতরে’ (জগবন্ধু ভট্টাচার্য), ‘বাংলা ভাষা প্রাণের ভাষারে’ (অরুণ চন্দ্র ঘোষ) ইত্যাদি। এই সময়ে প্রায় লক্ষ কপি ‘টুসু গানে মানভূম’ বইটি বিক্রি হয়েছিল। অজস্র কর্মী-নেতা-নেত্রী টুসু সত্যাগ্রহে এক-দেড় বছর পর্যন্ত জেল খেটেছেন বা জরিমানা দিয়ে পুলিশি হেনস্তার শিকার হয়েছিলেন। ১৯৫৪ সালের ৯ জানুয়ারি থেকে ৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত এই টুসু সত্যাগ্রহ চলেছিল।
মানভূমের ভাষা আন্দোলনের সর্বশেষ পর্যায় ছিল বঙ্গ সত্যাগ্রহ অভিযান। ১৯৫৬ সালের ২০ এপ্রিল থেকে ৬ মে পর্যন্ত ১০০৫ জন সত্যাগ্রহী (দশজন মহিলা সত্যাগ্রহী সহ) পুঞ্চা থানার পাকবিড়রা থেকে কলকাতা পর্যন্ত পদযাত্রা করে কলকাতায় আইন অমান্য করেন। বাঁকুড়া, বর্ধমান, হুগলি, চন্দননগর ও হাওড়ার জনগণের অকুণ্ঠ-সহযোগিতায় স্নাত হয়ে পদাযাত্রীরা কলকাতায় পৌঁছান। কলকাতায় পদযাত্রীদের সংবর্ধনা সভায় অতুলচন্দ্র গুপ্ত, সুরেশচন্দ্র ব্যানার্জি, জ্যোতি বসু, মোহিত মৈত্র, হেমন্তকুমার বসু প্রমুখ নেতৃত্ব দেন। ৭ মে সত্যাগ্রহীরা সত্যাগ্রহ কোরে কারাবরণ করেন, ১৩ দিন পর ১৯ মে সকলে কারামুক্ত হন। ওইদিন জেল-ফটকে তাঁদের সংবর্ধিত করেন অতুলচন্দ্র গুপ্ত। দেশপ্রিয় পার্কের এক মহতী জনসভায় তাঁদের আপ্যায়িত করা হয়। ২০ মে ভোরে স্পেশাল ট্রেনে যাত্রা করে পদযাত্রীরা পুরুলিয়া প্রত্যাবর্তন করেন। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায় ও বিহারের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী কৃষ্ণ সিংহের যৌথ ঘোষণায় বিহার রাজ্য ও পশ্চিমবঙ্গকে সংযুক্তিকরণ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে এই বঙ্গ সত্যাগ্রহ হয়েছিল। সীমা কমিশনের রায় অনুযায়ী মানভূম জেলার একটি অংশকে ‘পুরুলিয়া জেলা’ নাম দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্তিকরণের প্রক্রিয়াকে বাতিল করার জন্য এই ঘোষণাটি করা হয়েছিল। জনগণের সার্বিক প্রতিরোধে বিধান চন্দ্র রায় ওই প্রস্তাব থেকে সরে আসতে বাধ্য হন। বিধানচন্দ্র রায়ের ’পশ্চিমবঙ্গের রূপকার’ ইমেজটিকে বজায় রাখতে এই ইতিহাস ফাইল-বন্দি হয়ে থেকে যায়।
এ সময় সারা দেশে ভাষাভিত্তিক রাজ্য গঠনের জন্য আন্দোলনের চাপে, বিশেষত পৃথক অন্ধ্রপ্রদেশ গঠনের দাবিতে ৫১ বছর বয়সি শ্রীরামুলুর ৫৮ দিন অনশন শেষে মৃত্যুজনিত কারণে ১৯৫৩ সালের ২৩ ডিসেম্বর লোকসভায় রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন গঠিত হয়। উড়িষ্যার গভর্নর সৈয়দ ফজল আলি, রাজ্য পরিষদ সদস্য পণ্ডিত হৃদয়নাথ কুঞ্জরু ও মিশরের রাষ্ট্রদূত সর্দার কে. এম. পানিক্কর এই কমিশনের সদস্য ছিলেন। চেয়ারম্যান ছিলেন সৈয়দ ফজল আলি। কমিশনের সেক্রেটারি হিসেবে নিযুক্ত হন পি. সি. চৌধুরী। পুরুলিয়া কোর্টের জজ হিসাবেও দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন একসময় শ্রী চৌধুরী।
এই কমিশন ১৯৫৪ সালের ২৪ এপ্রিলের মধ্যে লোকসেবক সংঘর নেতৃত্বকে দাবিপত্র পেশ করার নির্দেশ দেয়, পরে ওই তারিখ ৩১ মে পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়। লোকসেবক সংঘ ১৯৫৪ সালের ৩১ মে ১২০০ পৃষ্ঠার স্মারকলিপি কমিশনের নিকট জমা দেয়, পরে আরও ২০০ পৃষ্ঠার দাবিপত্র সংযোজিত করলে মূল দাবিপত্রটি হয় ১৪০০ পৃষ্ঠার। লোকসেবক সংঘ ছাড়া সদর লোকাল বোর্ড, মাঙ্গলিক সাহিত্য বীথি, পুরুলিয়া বার অ্যাসোসিয়েশন, মানভূম বাঙালি সমিতি, সংযুক্ত প্রগতিশীল ব্লক, মানভূম নাগরিক সংঘ, হরিপদ সাহিত্য মন্দির, মানভূম জেলা মাধ্যমিক শিক্ষক সংঘ (এমডিএসএসটিএ) এবং ধানবাদের জনসাধারণ কমিশনের কাছে স্মারকলিপি জমা দেয়। বাংলাদেশের বহু প্রতিষ্ঠানও মানভূম ও ধলভূমকে পশ্চিমবঙ্গ ভুক্ত করার জন্য স্মারকলিপি জমা দিয়েছিল। এগুলি হল: পশ্চিমবঙ্গ সরকার, বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি, ভারতীয় হিন্দু মহাসভা, ভারতীয় জনসংঘ, ভারতীয় প্ল্যান্টার্স অ্যাসোসিয়েশন প্রভৃতি।
৪.
সীমা কমিশন পুরুলিয়ার সার্কিট হাউসে এসে সকলের সাক্ষ্যগ্রহণ করেছিল। ১৯৫৫ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি বিকেল চারটে থেকে পরদিন বিকাল ৬টা পর্যন্ত কমিশন পুরুলিয়ায় ছিল। পুরুলিয়া আসার আগে এই কমিশন মাইথন ও ধানবাদে সাক্ষ্যগ্রহণ করেছিল। কমিশনের চেয়ারম্যান সৈয়দ ফজল আলি যদিও পুরুলিয়ায় আসেননি। সাক্ষ্য নিয়েছিলেন হৃদয়নাথ কুঞ্জরু ও সর্দার কে. এম. পানিক্কর। লোকসেবক সংঘের বারোজন প্রতিনিধি অতুলচন্দ্র ঘোষের নেতৃত্বে সাক্ষ্যদান করেছিলেন। সাতটি ট্রাংক বোঝাই তথ্য, দলিল, রেকর্ড সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল প্রতিনিধি দলটি। সেক্রেটারি পি. সি. চৌধুরী প্রতিনিধি দলকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—ট্রাংকে স্বাক্ষর রাখা আছে কিনা—এই প্রশ্ন করার কারণও ব্যাখ্যা করে বুঝিয়েছিলেন। দুমকায় ড. অনুগ্রহ নারায়ণ সিংহ (বিহারের মন্ত্রী) তিনখানা স্বাক্ষরের বাঁধানো খাতা নিয়ে কমিশনকে দেখালে—কমিশন বলে এগুলি লাইব্রেরিতে রাখা হবে। পি. এম. বাগচীর একটি পঞ্জিকা ট্রাংক থেকে তুলে কমিশনের সদস্যরা জিজ্ঞাসা করেছিলেন—সমস্ত মানভূমে এই পঞ্জিকা চলে কি-না। প্রায় ৭০ মিনিট সময় ধরে প্রতিনিধি দলের সঙ্গে কমিশনের আলোচনা চলে। ১৪০০ পৃষ্ঠার স্মারকলিপিতে বর্ণিত পুরুলিয়া, ধানবাদ, ধলভূম সহ বিহারের অন্যান্য বাংলাভাষী এলাকাগুলির পশ্চিমবঙ্গ-ভুক্তির যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করে কমিশনকে বোঝানো হয়। লোকসেবক সংঘের নির্বাচিত বিধায়ক ও লোকসভার সব সদস্যই কমিশনের নিকট সাক্ষ্য দিতে গিয়েছিল, কেবল মাত্র বিধায়ক সমরেন্দ্রনাথ ওঝা সে সময় টুসু সত্যাগ্রহ করে হাজারিবাগ জেলে বন্দি ছিলেন বলে ওই দলে থাকতে পারেননি। সমরবাবু কমিশনের নিকট সাক্ষ্য দেওয়ার আবেদন জানালে বিশেষ পুলিশি প্রহরায় তাঁকে হাজারিবাগ থেকে রাঁচী নিয়ে যাওয়া হয়। তিনি বঙ্গভুক্তির পক্ষে তাঁর সাক্ষ্য দেন। পণ্ডিত হৃদয়নাথ কুঞ্জরু সমরবাবুকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—মৈথিল হয়েও আপনি বাংলার পক্ষে বলছেন কেন? সমরবাবু বলেছিলেন—‘তাহলেই বুঝুন আমার বর্তমান বাসস্থান কোন সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে অবস্থিত।’ সমরবাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র অরবিন্দবাবুও টুসু সত্যাগ্রহে যোগ দিয়ে জেলে বন্দি হয়েছিলেন, সে সময় তিনি ছিলেন কলেজের ছাত্র।
অন্তর্ভুক্তির পক্ষে অন্যান্য যাঁরা সাক্ষ্য দেন তাঁরা হলেন—সংযুক্ত প্রগতিশীল ব্লকের তরফে: বীররাঘব আচারিয়া, অশোক চৌধুরী, মিহিরকুমার চট্টরাজ, মহাদেব মুখোপাধ্যায়, অলক চৌধুরী, সীতারাম মাহাত। লোকাল বোর্ড: শ্যামকিঙ্কর ভট্টাচার্য, জগদীশ চট্টোপাধ্যায়, গঙ্গাধর সিং মোদক, সহদেব চক্রবর্তী, মথন চন্দ্র মাহাত। নাগরিক সংঘ: ভোলানাথ মজুমদার, গোপাল নন্দী। হরিপদ সাহিত্য মন্দির-এর পক্ষে সাক্ষ্য দেন অশোক চৌধুরী। পুরুলিয়া বার অ্যাসোসিয়েশন: জগদীশ মুখোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র বসু, যতীন্দ্রমোহন দত্ত, দ্বারিকানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্যোর্তিময় দাশগুপ্ত, অর্ধেন্দুশেখর চট্টোপাধ্যায়, নলিনবিহারী সরকার, প্রমোদ ঘোষ, অহিভূষণ ঘোষ। বেঙ্গলি অ্যাসোসিয়েশন: ধীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। মাঙ্গলিক সাহিত্য বীথি: মৃগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও চারুচন্দ্র দাস। এবং ভূতপূর্ব পার্লামেন্ট সেক্রেটারি (বিহার) জীমূতবাহন সেন।
মানভূম জেলাকে বিহারে রাখার পক্ষে যেসব সংগঠনের সদস্য/সমর্থকরা সাক্ষ্য দিয়েছিলেন—তৎকালীন জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান। জিলা কংগ্রেস, জিলা পঞ্চায়েত, কুর্মক্ষত্রিয় সংঘ, জমিদার সংঘ, মৈথিলী সংঘ ও মহিলা সংঘ—এদের অনেকগুলিই ছিল ভুয়া সংগঠন। উৎকল সমাজের কয়েকজন ভুয়া রাজনৈতিক দল তৈরি করেও বিহারের পক্ষে সাক্ষ্য দিয়েছিল। মহিলা সংঘের সদস্যরা বিহারি মহিলাদের মতো সাজসজ্জায় কমিশনের নিকট নৃত্যগীত পরিবেশন করেছিলেন। গানের বিষয় ছিল লোকসেবক সংঘের মানভূম ভাষা আন্দোলনকে হেয় করা।
দেশ স্বাধীন হওয়ার পর প্রথম জনগণনায় বিহার সরকার পরিকল্পিত ভাবে এনুমারেটর ও সুপারভাইজারদের নির্দেশ দিয়েছিল—মাহাতদের ভাষা কুড়মালি, ভূমিজদের ভাষা মুণ্ডারী, সাঁওতালদের মাতৃভাষা সাঁওতালি এবং আদিবাসী ও হরিজনদের ভাষা হিন্দি লিখতে হবে। অথচ ব্রিটিশ শাসকদের সমীক্ষায় এটি স্পষ্ট বলা হয়েছিল যে, মানভূমবাসীদের ভাষা বাংলা। এমনকি সাঁওতালেরও। জনগণনায় এই ইচ্ছাকৃত তথ্য বিকৃতি পরবর্তীকালে কাজে লাগিয়েছিল হিন্দিভাষীরা। মানভূমের বিহার প্রদেশের অন্তর্ভুক্তির পক্ষে যাঁরা তাঁরা।
৩০ সেপ্টেম্বর ১৯৫৫ রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন সরকারের নিকট পেশ করে তাঁদের রিপোর্ট যা জনগণের জ্ঞাতার্থে ১০ অক্টোবর প্রকাশ করা হয়। এই রিপোর্টে বলা হয় পুরুলিয়া ও ধানবাদ এই দুই মহকুমার পুরুলিয়া সদরের ২১টি থানার ভেতর চাষ ও চন্দনকিয়ারিকে বাদ দিয়ে ১৯টি থানার অন্তর্গত যে অঞ্চল তা ‘পুরুলিয়া জেলা’ হিসাবে পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। ধানবাদের ১০টি থানাই বিহারে রাখার পরামর্শ দেওয়া হলো। ১৯৫১ সালের জনগণনায় চাষ ও চন্দনকিয়ারী থানার অন্তর্গত মানুষদের হিন্দিভাষী হিসাবে দেখানো হয়েছিল। পাশাপাশি মানচিত্রে গুয়াই নদীকে দামোদর হিসেবে চিহ্নিত করাও ইচ্ছাকৃত। কেননা দামোদরের অবস্থান চাষের বহু পরে, ধানবাদের কাছাকাছি। যদিও ভাষা ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলই কমিশনের নিকট প্রধান বিবেচ্য ছিল তবু ভৌগোলিক অবস্থান বিচারের বাইরে ছিল না। পশ্চিমবাংলার অন্যতম প্রধান তিনটে নদী কাঁসাই শিলাই ও দ্বারকেশ্বরের উৎসস্থলটি পশ্চিমবাংলার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করাও কমিশনের লক্ষ্য ছিল।
জল সরববাহের সুবিধার জন্য টাটা কোম্পানি বিধানচন্দ্র রায়ের নিকট জামশেদপুর সংলগ্ন ইঁচাগড়, চাণ্ডিল, পটমদা এই তিনটি থানা বিহারে রাখার আবেদন জানায়। বিধান চন্দ্র রায় উক্ত তিনটি থানা বিহারকে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। তিনটি থানার অন্তর্গত ৫৯৪ বর্গমাইল এলাকা এভাবে বিহারকে দান করার প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেন কমিশনের সদস্য হৃদয়নাথ কুঞ্জরু।
কমিশন পুরুলিয়াকে পশ্চিমবাংলায় অন্তর্ভুক্তিকরণের প্রস্তাব করলেও, বিহার রাজ্য তা সহজে মেনে নিল না। বিহারের একখণ্ড জমি গেলেও রক্তগঙ্গা বইবে—এই ঘোষণা করা হলো। সেইজন্য দিল্লিতে রাজ্য পুনর্গঠন সাব কমিটি গঠিত হলো। এই কমিটি তাঁদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে ১৬ জানুয়ারি ১৯৫৬। বিহার প্রদেশ তার পরদিন সারা রাজ্যে হরতাল পালন করে। হিন্দীপন্থীরা ঝালদা, পুরুলিয়া প্রভৃতি জায়গায় ১৭-২০ জানুয়ারি (১৯৫৬) হরতাল করে। দিল্লিতে পুরুলিয়াকে বঞ্চিত করার সমস্ত কৌশলই বজায় রইল, লোকসভায় পুরুলিয়ার বঙ্গভুক্তি বিষয়টি সিলেক্ট কমিটিতে পাঠানো হয়। ধানবাদ থেকে জামশেদপুর যাবার রাস্তার ডানদিকের থানাগুলি অর্থাৎ জয়পুর, ঝালদা, বাঘমুণ্ডি আড়ষা, বলরামপুর ও পুরুলিয়াকে বিহারে রেখে রাস্তাটিকে জাতীয় সড়ক হিসাবে ঘোষণা করতে হবে এই দাবি করা হলো। এই দাবি মেনে নিলে পুরুলিয়া শহর ও বলরামপুর শহরের অর্ধেকাংশ বিহারের অন্তর্ভুক্ত হয়।
১৯৫১ সালের জনগণনার রিপোর্টকে সামনে রেখে ‘ল্যাঙ্গুয়েজ হ্যান্ডবুক’ নামে একটি পুস্তিকা বিলি করে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করা হয়। তাতে দেখানো হয় উল্লেখিত থানার অধীন মানুষেরা সবাই মূলত হিন্দিভাষী। যার ফলস্বরূপ লোকসভায় আলোচনা চলাকালীন স্বারাষ্ট্রমন্ত্রী গোবিন্দবল্লভ পন্থ সরাসরি পশ্চিমবঙ্গ ও মানভূমের ভাষা আন্দোলনের বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখেন। পঞ্জাবের এমপি ঠাকুরদাস ভার্গব প্রাথমিকভাবে পুরুলিয়ার বঙ্গভুক্তির পক্ষে থাকলেও ‘ল্যাঙ্গুয়েজ হ্যান্ডবুক’-এর কারণে নিজেকে ‘নিরপেক্ষ’ ঘোষণা করেন। এমন অনেক নেতাই ছিলেন যাঁরা নিজেদের নিরপেক্ষ বললেও আসলে চেয়েছিলেন মানভূম বা পুরুলিয়া বিহারে থাকুক। ১৬ আগস্ট লোকসভায় ভজহরি মাহাত পুরুলিয়ার বঙ্গভুক্তির পক্ষে বক্তব্য রাখেন। ১৭ আগস্ট মানভূমের পক্ষে বক্তব্য রাখেন হিন্দু মহাসভার নেতা নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়ের পিতা)। এছাড়াও লোকসভায় যাঁরা পুরুলিয়ার বঙ্গভুক্তির পক্ষে বক্তব্য রাখেন তাঁরা হলেন—হীরেন মুখার্জি, কমল বসু, মহারাষ্ট্রের নেতা গ্যাডগিল, লোকসেবক সংঘের চৈতন্য মাঝি প্রভৃতি।
১৭ আগস্ট লোকসভায় ‘বাংলা-বিহার সীমান্ত নির্ধারণ বিল’ পাস হলে রাজ্যসভায় বিলটি পেশ হয় ২৮ আগস্ট। রাজ্যসভায় বিলের পক্ষে বক্তব্য রাখেন ভূপেশ গুপ্ত, কে. পি. সিংহ। রামস্বামী মুদালিয়র বিলের পক্ষে বক্তব্য রেখে বলেন,—”গত ৪০ বছর ধরে বাংলাভাষী জনগণ স্বভাষাভাষীদের সংঘবদ্ধ করেছেন (১৯১২-৫৬ পর্যন্ত)। দেশভাগের ফলে পশ্চিমবঙ্গকে যেভাবে খণ্ড বিখণ্ড করা হয়েছে আমাদের তাও ভাবা দরকার। অথচ আজ সীমা কমিশন বাংলাতে তাঁদের দাবির এক ক্ষুদ্র অংশ দেওয়াতেও চরম অশান্তি সৃষ্টি হচ্ছে—এটা দুঃখজনক।” ১ সেপ্টেম্বর ১৯৫৬ ড. রাজেন্দ্রপ্রসাদ ‘বাংলা-বিহার ভূমি হস্তান্তর’ বিলে সই করেন। ১ নভেম্বর ১৯৫৬ একটি নতুন জেলা পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হলো—পুরুলিয়া। মানভূম ভিক্টোরিয়া ইনস্টিটিউশনে সাতদিন ধরে এই বঙ্গভুক্তির উদ্যাপন অনুষ্ঠান হয়েছিল। নবনির্মিত পুরুলিয়া জেলার আয়তন হলো ২৪০৭ বর্গমাইল; থানার সংখ্যা ১৬টি, জনসংখ্যা ১১,৬৯০৯৭ জন। লক্ষ্যণীয় যে, ভাষা কমিশনের নিকট পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৩,৯৫০ বর্গমাইল এলাকা (৬৭ লক্ষ জনসংখ্যা বিশিষ্ট) দাবি করেছিল। কিন্তু সীমা কমিশন সাকুল্যে ২৫০০ বর্গমাইল (১৩ লক্ষ জনসংখ্যাবিশিষ্ট) এলাকা বঙ্গভুক্তির জন্য সুপারিশ করে, তার মধ্যে পুরুলিয়ার এলাকাটিই ২৪০৭ বর্গমাইল। এছাড়া পূর্ণিয়া জেলায় মহানন্দার পূর্বতীরস্থ ৭০-৮০ বর্গমাইল এলাকা বাংলার ভাগ্যে জুটেছিল। প্রায় সমসংখ্যক জনসংখ্যা নিয়ে পূর্বতন মানভূমের একাংশ বাংলাভাষী এলাকা বিহারেই থেকে গেল। পূর্বতন বিহার, বর্তমান ঝাড়খণ্ডের অধীন এই অঞ্চলের বাংলাভাষী জনগণের মুখের ভাষা বাংলা হলেও তাঁদের সন্তানরা বাংলা ভাষায় বিদ্যালয়ের পাঠ নেবার সুযোগ পায় না। এছাড়াও বাংলাভাষী জনগণের অন্যবিধ বহু সমস্যা তো আছেই।
ভারতবর্ষের মধ্যে সর্বপ্রথম সংগঠিত ভাষা আন্দোলনের এই ফলাফলে জয়ী হলো পুরুলিয়ার মানুষ হিসাবে বাংলাভাষীরা, জয় হয়েছিল লোকসেবক সংঘর নেতৃত্বর। পশ্চিমবঙ্গে বিধানচন্দ্র রায়, অতুল্য ঘোষের মতো নেতা থাকা সত্ত্বেও এ প্রাপ্তির শ্রেয় তাঁদের নয়। কেননা অন্যান্য অনেক বিষয়ে পশ্চিমবাংলার প্রাপ্তি ছিল চাহিদার চেয়ে অনেক কম—এক্ষেত্রেও প্রায় শূন্য। দুর্ভাগ্য এও যে, অর্ধশতাব্দী পেরিয়ে এসে আমরা দেখলাম, ১৯৫৬ সালের ১ নভেম্বর যে নিবারণ পার্কে আড়াই হাজার প্রদীপ জ্বলেছিল সেখানে পঞ্চাশতম বর্ষে একটি প্রদীপও জ্বলেনি। সাধারণ মানুষের মধ্যে, নবীন প্রজন্মের মধ্যে সামান্যতম আগ্রহ উদ্দীপনা নেই এই দিনটিকে নিয়ে। বিস্মৃতির ধোঁয়াশায় ঢেকে গিয়েছে অতীত গৌরব।
দোষের ভাগ আমাদেরও কিছু কম নয়; আমরা যারা ‘সচেতন’ নিজেরাই বা কতটা এ ইতিহাসকে চর্চায় স্থান দিয়েছি? পুরুলিয়া শহরে কোনও কোনও সংগঠন ‘ভাষা দিবস’ হিসেবে ২১ ফেব্রুয়ারি পালন করে—সেখানেও পুরুলিয়ার কোনও কৃতবিদ্য মানুষ মানভূমের ভাষা আন্দোলনের কথা স্মরণ করে না। এর অন্যতম কারণ হয়তো পশ্চিমবঙ্গের বাঙালির এই ঐতিহাসিক আন্দোলনের মর্মবাণীকে আত্মস্থ করতে না-পারা। সামগ্রিকভাবে পুরো রাজ্যেই এই চিত্র। এখন চারপাশে, সোশ্যাল মিডিয়ায়, ‘সমাজ-সচেতন’ বাঙালি আবার ‘গোবলয়’, হিন্দি ভাষা/সাংস্কৃতিক আগ্রাসন বিষয়ে নানান কথা বলছেন দেখছি। বায়বীয় আখড়ায় ‘একমাত্রিক’ কথা-প্রতিকথা বিলীন হয়ে যাচ্ছে সময়-স্রোতে! যেমনটা গিয়েছে বিগত দশকগুলিতে, বছর বছর ঘটা করে কেবল ‘বাংলা ও বাংলা ভাষা বাঁচাও কমিটি’র অনুষ্ঠান পালন হয়েছে কোলকাতার কার্জন পার্কে। গান, আবৃত্তির প্রভাতী বা সান্ধ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান মফস্সলে—দোকানের হোর্ডিংয়ে কালি লেপে বাংলা ভাষাকে বাঁচানোর উদ্যোগ জনজীবনে কোনও প্রভাব ফেলেছে বলে আমাদের জানা নেই। পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি বাংলা ভাষাকে রক্ষা করার জন্য কিছুই না করে তামিলদের আন্দোলনের ফলে অর্জিত ‘ত্রি-ভাষা’ নীতির সুফল পেয়েই সন্তুষ্ট।
বঙ্গভূমের প্রান্তসীমায় সংগঠিত বাংলা ভাষা আন্দোলন বিষয়ে অজিত রায় লিখিত ‘ধানবাদ ইতিবৃত্ত’ (প্রথম প্রকাশ: জুন ১৯৯৬) নিশ্চিতভাবে একটি উল্লেখনীয় গ্রন্থ।
হরিপদ সাহিত্য মন্দির-কে পুরুলিয়া শহরের ‘যাদুঘর’ বলা হয়। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হুমায়ুন কবীর এই সংগ্রহশালার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন ৭ জুলাই ১৯৬০-এ। এই সংস্থার কার্যনির্বাহী সদস্য তথা পুরাতাত্ত্বিক সংগ্রহশালার তত্ত্বাবধায়ক, লোকগবেষক শ্রী দিলীপকুমার গোস্বামীর ‘মানভূমের ভাষা আন্দোলন ও পুরুলিয়ার বঙ্গভুক্তি’ (২০১১) শীর্ষক বইটি এই ভাষা আন্দোলনের রূপরেখাকে বোঝার ক্ষেত্রে অপর একটি পাঠ-সহায়ক গ্রন্থ। বলা বাহুল্য ব্যক্তিগত উদ্যোগে প্রকাশিত গ্রন্থটি মুষ্টিমেয় পুরুলিয়াবাসী ব্যতিরেকে, বৃহত্তর পাঠকসমাজের হাতে সেভাবে পৌঁছয়নি।
মানভূম ভাষা আন্দোলনের গুরুত্বকে খাটো না-করলেও এ কথা বলতেই হয়—দক্ষিণবঙ্গের বা জঙ্গলমহলের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির (এমনকি কলেজের) যে চিত্র আমরা পাই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় বা সংবাদমাধ্যমের সূত্রে, তার কারণে আমরা জানি, কেবল সাঁওতাল নয়, আন্যান্য জনজাতি এমনকি কুর্মি সম্প্রদায়ের স্কুল-পড়ুয়া বালকবালিকার ক্ষেত্রেও মাতৃভাষার সঙ্গে স্কুলের পাঠ্যবইয়ের মান্য বাংলা ভাষার ‘সামান্য’ হলেও যে ফারাক তাকে ডিঙোতে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়। আর এ সমস্যা কেবল প্রথম প্রজন্মের, প্রথম শ্রেণির বিদ্যার্থীদের ক্ষেত্রে নয়। সপ্তম বা অষ্টম শ্রেণির পড়ুয়াও যে একটি বাক্য গুছিয়ে লিখতে পারে না বা শব্দের বানান কিংবা অর্থ সম্পর্কে সম্যক ওয়াকিবহাল যে সে নয় এর কারণ কি কেবল রাজ্যের বেহাল শিক্ষাব্যবস্থা? সব জেনেবুঝেও সরকারি ঘোষণার হাততালিতে চাপা পড়ে যায় এভাবেই বারেবারে ভাষা সমস্যার রুখাশুখা বাস্তব।
ছবি সৌজন্য: আনন্দবাজার পত্রিকা আর্কাইভ। হাওড়া ব্রিজ অতিক্রম করছে মানভূমবাসীদের মিছিল।