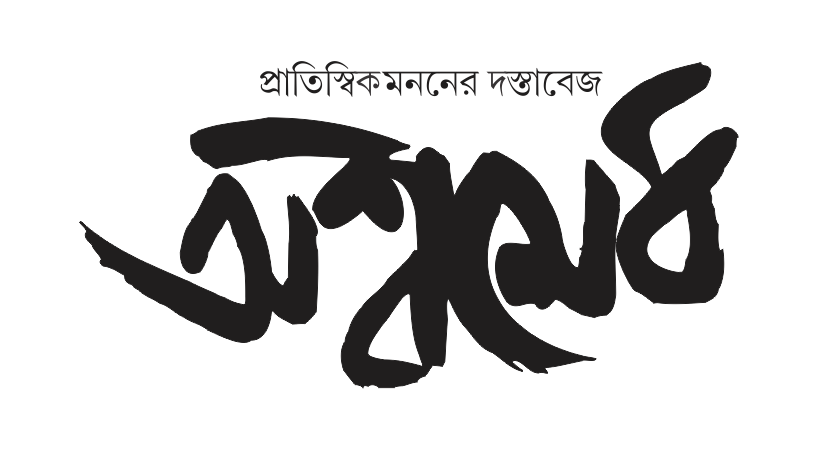এখন যা লিখছি তার জন্য দায়ী প্রবাল দাশগুপ্তর তিনটে ঘুম-ভাঙানিয়া খোঁচা। জিমেইল দেখাচ্ছে, প্রথম খোঁচার সময়-তারিখ : Fri, Oct 25, 2019, 5:58 PM, “Fwd: LINGUIST List Daily Summary for Thu Oct 24 2019”—এই শিরোনামে তাঁর কাছ থেকে আসা ই-মেইলে লেখা স্রেফ দুটো বাক্য— “/Yao krito Blommaert reviewtxaa porxo. Boitxaar pdf paao to setxaao porxe dekhte paaro/” (= ‘ইয়াও কৃত ব্লোমার্ট রিভিউটা পোড়ো। বইটার পিডিএফ পাও তো সেটাও পড়ে দেখতে পারো।’) অর্থাৎ, গ্রন্থের নাম : ‘Dialogues with Ethnography: Notes on Classics, and How I Read Them’, লেখকের নাম : Jan Blommaert (ইয়ান ব্লোমার্ট, ব্লোমার্ট নিজে এইভাবেই উচ্চারণ করেন দেখেছি), সাল : ২০১৮, প্রকাশক : Multilingual Matters, ‘Linguist List’ নামের এক অনলাইন সংস্থায় বইটা রিভিউ করেছেন, মেলবোর্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক Xiaofang Yao (এঁর নামের উচ্চারণ সম্ভবত জিয়াওফ্যাঙ ইয়াও-এর কাছাকাছি কিছু)।
হঠাৎ, এমন নির্দেশ! তাও আবার কোনোরকম, পূর্বাপর বিবৃতি-ব্যাখ্যা ছাড়া! আমার কাছে প্রবাল দাশগুপ্তর পড়ানোর এটাই চেনা কায়দা। তাছাড়া আমার মতো বনের-পাখি মার্কা শিক্ষার্থীর জন্য এছাড়া আর কী-ই বা তাঁর করার আছে! তিনি জানেন, আমায় হাতে ধরে শেখানো যায় না। এর আগেও, এইরকমই, ই-মেইলে বা বইমেলায় কাগুজে সান-গার্ডের পেছনে বইয়ের নাম লিখে, অথবা নেহাতই গল্পের ছলে, তিনি আমায় এমন সমস্ত কাজের কথা বলেছেন, যা আমার কাছে দীর্ঘদিন ধরে খুঁজে না-পাওয়া উত্তরের মতন। অথচ, প্রশ্ন যে সরাসরি আমি করতে শিখিনি, সেটা কোনোভাবে তিনি জানেন। তিনি আমার মনের অভাবটা কী করে যেন বুঝে ফেলেন—জানি না!
ভাবতে অবাক লাগে, এইভাবেই তাঁর বলার সূত্র ধরে আমি পেয়েছি—ই. ই. কামিঙ্স, গার্ট্রুড স্টেইন, য়্যুরি লৎমান, ড্যান এভারেট, লিকোলা যুর্য়ে প্রমুখের কাজের হদিশ। প্রত্যেকবারই চমক থাকে, থাকে ক্লু। ফলে, Fri, Oct 25, 2019, 5:58 PM-এ আসা ই-মেইলটা আমার কাছে যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল, সে-কথা আর বলার অপেক্ষা রাখে না! ওই নির্দেশের ‘রিভিউ’-টা পড়া ছাড়া, আর কিছু অবশ্য আজ অবধি করা গেল না, কেননা আমি ‘Dialogues with Ethnography’ বইটা জোগাড় করতে পারিনি, ও-বইয়ের বিস্তর দাম। কিন্তু ওই ই-মেইল পেয়ে অবধি, আমি ব্লোমার্টের অন্যান্য কাজ ও বক্তৃতা পড়তে ও শুনতে শুরু করেছিলাম। দেখতে পেলাম, আমি যেন এরকম সূত্রই বেশ কয়েক বছর ধরে খুঁজে বেড়াচ্ছি। আটপৌরে ভাষায়, সাহিত্যে, সংকেত তত্ত্বের প্রয়োগ করতে গিয়ে বারবার ফিরে আসছি—নানান নিত্যনতুন বয়ান দেখে, কথা বলা ও লেখার নতুন-নতুন ধরন দেখে। ভাষ্য-রচনা করবার মতো সামগ্রিক কোনো তল খুঁজে পাচ্ছি না। ব্লোমার্টে গিয়ে যেন খানিকটা স্বস্তি মিলল। যখন এই বহুমুখী সময়টাকে আমি কিছুতেই কোনো নির্দিষ্ট একটা সামগ্রিক অবয়বে ধরতে না-পেরে, ‘নিছক’ ভাষাভিত্তিক কাজ করতে পারছি না, তখন সেই জায়গায় ব্লোমার্ট পথ দেখাচ্ছেন।
প্রবাল দাশগুপ্তর দ্বিতীয় খোঁচা, এখানেও ই-মেইল (সময়-তারিখ : Dec 9, 2019, 5:51 PM) “praSonggik aro EkTa lekha, ingrijite ar banglaY”—এই শিরোনামে, এবং এক্ষেত্রেও ‘এমনিই’ বলা,—Sibansu, EkTa kono SomOYe kaje lagte pare. ebong tomar Ocena bole amar dharona. (= ‘শিবাংশু, একটা কোনো সময়ে কাজে লাগতে পারে। এবং তোমার অচেনা বলে আমার আমার ধারণা।’)—ব্যস্! এইটুকু বলে পাঠানো তাঁর দুটো লেখা, বাংলায়, ‘নাটক আর ভাষাতত্ত্ব’ আর ইংরিজিতে—‘THE THEATER AND CLASSICAL INDIA: SOME AVAILABILITY ISSUES’,উল্লিখিত বাংলা লেখাটা এবং প্রবাল দাশগুপ্তর তৃতীয় খোঁচা হিসেবে এর আগে পাওয়া তাঁর আর একটা লেখা—‘শান্তির পথে মার্কসীয় সম্বল’। সব মিলিয়ে আমায় এই কাজে হাত দিতে একরকম বাধ্য করল। প্রবালদার লেখা দুটোর যে কাজ, আর বর্তমান রচনার যা অভীষ্ট—সে দুটো এক জিনিস নয়। কিন্তু আজকাল বাংলায় ‘অনুপ্রেরণা’ বলে একটা কথা চালু হয়েছে। তাই, এই কথাগুলো বলে রাখা।
বর্তমান রচনায় যে রিস্ক আমি নিচ্ছি তার জন্য প্রবাল দাশগুপ্তর খোঁচাগুলোকে দায়ী করলেও, এই রচনার সবরকম মন্দের দায় আমার। কারণ আমি নিজেও জানি, এই কাজ বেশ দুরূহ এবং বেশিরভাগটাই আমার ক্ষমতার বাইরে। তবু কাজের উদ্দেশ্য মাথায় রেখেই ‘শিরোনাম’ নির্বাচন। শুধু একটা সূত্র বলে রাখা দরকার। রচনার বয়ানে, কথায়-কথায় যে ইংরিজি Expression লেখা হয়েছে, সেগুলো কোনো বই থেকে নেওয়া নয়। লক্ষ করে দেখবেন; আমরা, আমাদের নিজেদের ভাবনাতেই এইরকম মিলিয়ে মিশিয়ে ভাবতে শিখেছি আজকাল। এই লেখা সেইরকম ভাবনারই কিছু পরিকল্পিত আর কিছু স্বতঃস্ফূর্ত নমুনা মিলিয়ে মেরে দেওয়া। উদ্ধৃতির জন্য তো আলাদা করে বলেইছি, কোথায় কী দিচ্ছি!
SRU C TURE
এই রচনার SRU C TURE-টা একটু ‘অন্যরকম’। এ-যুগে বসেও যাঁরা conventionally written and duly printed #classicaltexts like #fiction, #novel, #article ইত্যাদি পাঠ করতে অভ্যস্ত, তাঁদের কাছে এ লেখা—‘#কিম্ভুতকিমাকার’ ঠেকবে! কোন জিনিসটা ভূমিকায় বলব, কোনটা পর্যালোচনা করব, আর উপসংহারে পৌঁছে কী সিদ্ধান্ত নেব—এগুলোর কোনোটাই আমি আগে থাকতে ঠিক করিনি, in fact এখনও জানি না। মনে মনে কেবল ঠিক করেছি—contemporary and coming era of an undefined #socialcommunicationdynamics-এ ভাষার ভূমিকা কী দাঁড়িয়েছে এবং কী দাঁড়াবে, এবং সেইসব ভাষিক ভূমিকাবলির ভাষ্য লিখতে চাইলে কোন ধরনের অভ্যেসের কথা মাথায় রেখে কাজে হাত দেওয়া প্রয়োজন, ইত্যাদি। Undefined বলার কারণ, ভাষা ও সংস্কৃতির ভূমিকার বিচারে আজ অবধি এই যুগের কোনো নামকরণ হয়েছে বলে জানি না।
প্রাচীন-মধ্য-আধুনিকের গল্পটা অন্য। কিন্তু এই মুহূর্তে আমার সবচেয়ে বড়ো কাজ বলে মনে হচ্ছে, এই যুগটাকে অর্থাৎ ‘contemporary and coming era’-কে চিহ্নিত করা। কারণ; কেন জানি না, এ-যুগের নানান সাংস্কৃতিক অর্পণ (Cultural performance-এর performance-কে বাংলায় ‘অর্পণ’ বললাম ‘নাটক ও ভাষাতত্ত্ব’ রচনা থেকে ধার নিয়ে) এবং social practice নিয়ে একটা অস্বস্তি, এক ধরনের দুশ্চিন্তা সর্বক্ষণ মনের ভেতরে #ছুঁচোরকেত্তন করছে। ভাষাচর্চার কয়েকটা এলাকা, যেমন বক্তব্য তত্ত্ব (#Pragmatics), সংকেত তত্ত্ব (#Semiotics), ভাষিক বাস্তুতন্ত্র (Linguistic Ecology) এবং স্বাভাবিক ভাষা-বৈচিত্র্যের প্রয়োজনীয়তা (Necessity of ‘Natural’ Linguistic Diversity)—এইসব নিয়ে ভাবনাচিন্তা করতে করতে দেখতে পাচ্ছি, বেশ ক’দিন হলো, মন বড়োই উদ্বিগ্ন এবং কখনও কিংকর্তব্যবিমূঢ়। ‘এই কাজ’ ‘এই সময়’ কেন করব—এই অতি সাধারণ প্রশ্নটারই যেন কোনো সুরাহা খুঁজে পাচ্ছি না মনের ভেতরে। যেন, ভাষার যে-এলাকায় আমার কাজ, সেই-এলাকাকেই কেমন অচেনা ঠেকছে।
অভ্যেসের তাগিদে যা-যা করে যাচ্ছি—সেইসব কাজগুলোকে যেন ‘কাল্পনিক’ এবং ‘আংশিক’ বলে মনে হচ্ছে। আটপৌরে ভাষার পীঠস্থান ঘর। সেই ঘরের মধ্যেও চরিত্ররা যেন নিজেদের মধ্যে ‘কথা বলা’-র পরিসরকে যথাসম্ভব আনুষ্ঠানিক ও সংক্ষিপ্ত করে তুলেছে। এবং সেই ঘরোয়া আনুষ্ঠানিকতার মধ্যেও মোবাইল ফোনের সৌজন্যে ডেকে আনা হচ্ছে ঘরের বাইরের অন্য অনেকরকম কথা বলাকে। ঘরের কথার মধ্যে মোবাইল-মারফত ঢুকে পড়ছে অসংখ্য চেনা/অচেনা বক্তা/শ্রোতার সঙ্গে ঘরের লোকের কথোপকথনের বিভিন্ন পর্ব।
এই প্রত্যেকটা কথোপকথন আলাদা আলাদা জাতের (জাত এই অর্থে Genre)। ভিন্ন ভিন্ন জাতের অসংখ্য #discourse ঢুকে ঘরের কথার পরিসরকে কোণঠাসা করে দিচ্ছে এবং সেই সংক্ষিপ্ততর ‘নমনীয়’ ঘরোয়া সংলাপের ভেতরে এতরকম conversational crossing and overlapping zones তৈরি হচ্ছে যে, আটপৌরে ভাষার পরিসরে, আর আগের মতন locution-illocution-perlocution-এর ত্রিস্তরীয় #SpeechAct-এর কাজকে ‘আদর্শ কাজ’ বলে ধরা যাচ্ছে না। দেখছি, নানারকম নতুন নতুন সংকেত, নতুন নতুন অভিব্যক্তি এসে জড়ো হচ্ছে ঘরোয়া কথায়/লেখায়। শুধু শহরে বা আমার মফস্সলের ঘরে বলে নয়, গ্রামাঞ্চলেও অল্পবয়সি ছেলে/মেয়েরা ওই একই সংকেত, একই অভিব্যক্তি আয়ত্ত করে নিয়েছে—যে অভিব্যক্তি, তাদের নিজস্ব ভাষার নয়, যে সংকেত তাদের নিজস্ব সংস্কৃতির নয়। তারাও—online transaction, text, messaging, #, @, forwarding, sending, poor network—ইত্যাদি সংকেত বা অভিব্যক্তি অবলীলায় ব্যবহার করছে। একজন আদিবাসী ছেলে T-shirt আর হাফ-প্যান্ট পরে, #Fade&Taper ধরনের চুল কেটে, কানে মোবাইলের হেডফোন লাগিয়ে, আমার সামনে এসে দাঁড়াচ্ছে। তাকে আদিবাসী বলে চেনা যাচ্ছে না। আবার এও দেখছি, কোনো আদিবাসী ছেলে খাঁটি মান্য বাংলায়, বাংলা হরফে আমাকে text/message করে আমার কুশল জানতে চাইছে। এসব কী হচ্ছেটা কী? এই বিরক্তিমূলক প্রশ্নের উত্তর খুঁজতেই এই রচনায় হাত দেওয়া!
শহরে T-shirt আর হাফ-প্যান্ট পরিহিত, #Fade&Taper ধরনের চুল কাটা হিন্দু ব্রাহ্মণের ছেলের প্রসঙ্গ তুলিনি বলে, আমার কথাগুলো আপাত অর্থে ‘উন্নয়ন’-বিরোধী মনে হতে পারে অনেকের। কিন্তু তা নয়। শহরের, মফস্সলের, এমনকি আমার নিজের ঘরের কথা দিয়েই তো এখন শুরু করেছি কথা বলতে। কেবল ‘হাইBrid’ বলে দিলেই সমস্যা মিটে যাচ্ছে না—সেটা দেখতে পেয়েই কাজে হাত দিয়েছি! ভাষার কাজ করতে গিয়ে, বা নিদেনপক্ষে ভাষায় অংশগ্রহণ করতে গিয়ে, কোথায় কোথায় অসহায় লাগছে—সেটা বলছি। আরও অনেক অনেক আছে দৃষ্টান্ত। অনলাইনে ‘খবর’ (ওরফে ‘ভাইরাল’) পরিবেশনের দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখলে সকলেই দেখতে পাবেন—কীভাবে #Fakenews অথবা ‘telling the truth’-এর মাধ্যমে #Sadism বা #masochism-এর প্রবণতা কতগুণ বেড়েছে। কাজ করতে গিয়ে পদে পদে ঠেকছে। অথবা কাজ করার এলাকা এত প্রসারিত হয়ে উঠেছে যে, কোত্থেকে শুরু করব ভেবে উঠতে পারছি না। অথচ, ‘বেঁচে থাকা’-র মতো ‘কাজ করতে হবে’-টাও মনের মধ্যে গেঁথে আছে, যুগ-যুগ ধরে। কিন্তু পারছি না। কেন পারছি না? আমার আশপাশ থেকে আমার বন্ধু-পরিজনদের তো কাউকে এ কথা বলতে শুনছি না! তাহলে কি অসুবিধেটা শুধুই আমারই? ‘অসুবিধেটা শুধু আমার’—এটাই আপাতত ধরে নিয়ে কাজ এগোতে হচ্ছে। কেন এমন হচ্ছে, অসুখটা মনের ঠিক কোথায়—সে সব জানার জন্য নিজের ওপরেই একরকম psychoanalysis চালাতে হচ্ছে। বর্তমান রচনাটির ভাবনা সূত্র প্রাক্-রচনা পর্বে উল্লিখিত তিন খোঁচার মধ্যে নিহিত এবং বলা বাহুল্য, মেথড স্বনির্মিত। তাই এখানে প্রখ্যাত #SaintLucian কবি Derek Walcott-এর কবিতার মতো শুরুতেই বলতে হয় :
“The time will come
when, with elation,
you will greet yourself arriving
at your own door, in your own mirror,
and each will smile at the other’s welcome,
and say, sit here. Eat.
You will love again the stranger who was your self.
Give wine. Give bread. Give back your heart
to itself, to the stranger who has loved you
all your life, whom you ignored
for another, who knows you by heart.”
আমার রোগের পটভূমি—যে যুগ, ওরফে সময়, আক্ষরিক অর্থে সেই সময়ই আমাকে সুযোগ করে দিল : to greet myself at my own door—অপর কোনো বনলতা সেন নয়, এ যুগে খুঁজে পেতে হবে নিজেকে, খুঁজে নিয়ে মুখোমুখি বসতে হবে তার সঙ্গে, I and the stranger, my self, who knows me by heart;—‘নাটক ও ভাষাতত্ত্ব’ লেখাটায় অর্পণশিল্পের মঞ্চে দাঁড়িয়ে ‘ছায়াসঙ্গী’-র প্রসঙ্গ তুলেছেন, প্রবাল দাশগুপ্তও। যেখানে নাটকের একজন অভিনেতা, দর্শকের জন্য নয়, নিজের জন্যও নয়, মঞ্চে অভিনয় করেন তাঁর নিজেরই ওই ছায়াসঙ্গীর জন্য। মন তবুও খুঁতখুঁত করে। দুজনে মুখোমুখি বসে কী নিয়ে কথা বলব?
কিছু কথাবার্তা বলে তো দেখলামও, সমস্যাটা ‘সমাজ-বিচ্ছিন্ন আমি’র নিজেকে নিয়ে নয় কেবল। সমস্যাটা আসলে আমার পটভূমি বা সোজা কথায় বললে, আমি ও তার মঞ্চ (locus) নিয়ে। অর্থাৎ, এই যুগে আমার খেলার মাঠ ও খেলার নিয়ম চিনতে এবং বুঝতে না পারা এবং তার ফলশ্রুতিরূপে contemporary practices-এ মানিয়ে নিতে না পারাটাই প্রধান সমস্যা। আশা করি, এই সমস্যা আমার মতো অনেকেরই। অসুবিধেটা বিশেষ করে তাঁদের, যাঁরা চোখ-কান খোলা রেখে এ-যুগের transition-কে একদিকে বুঝতে চেয়েছিলেন অথচ অন্যদিকে, তথ্যের চোখ ধাঁধানো সমাবেশে, এক ডিসকোর্সের মধ্যে অনেক ডিসকোর্সের অনুপ্রবেশের ফলে, তৈরি হওয়া ডিসকোর্সের সাপ-লুডোর গোলকধাঁধায় পড়ে, যাঁরা transition-এর বিন্দুবিসর্গ বুঝতে না-পেরে অধৈর্য হয়ে উঠেছেন। ফলে ‘ব্যাপারটা কী’, বুঝে নেওয়ার পর্বেই খামতি থেকে যাচ্ছে আমাদের।
দোষটা আসলে ঠিক আমাদেরও নয়। এখনকার ‘যুগ’ অতি দ্রুত পরিবর্তনশীল। ফলে তাকে বোঝা বা ব্যাখ্যা করার বেশি সময় পাওয়া যাচ্ছে না, একটা অভ্যেসে ধাতস্থ হতে না হতেই ঘাড়ের ওপর আরেকটা অভ্যেস এসে পড়ছে। অথচ না-বুঝে দু-তিনটে যুগ পার হয়ে যাওয়ার ফলে—মনে অতৃপ্তি এবং উদ্বিগ্নতা ক্রমবর্ধমান।
Online-এ চট করে ‘জানকারি’ মেলে। ওইটুকু এই প্রজন্মের কাছ থেকে শিখে নিয়েছি একটু একটু করে। সুতরাং চট করে, এই যুগটাকে (যে যুগটাকে আমার যাবতীয় অসুখের কারক বলে কাঠগড়ায় তুলেছি) কী বলে, google-এ দেখে নেওয়া যেতে পারে। এমন বন্ধু নাকি আর কেউ নেই! বন্ধুও খানিকটা confused, আমার What is this current era called? প্রশ্ন পেয়ে! সে প্রথমেই ধরে নিলে, আমি বোধহয়, Geological era-এর কথা বলছি! তারপর অনেক কষ্টে, searchable string of words নিয়ে নানান রকম পরীক্ষানিরীক্ষা করবার পর—একটা কিছু পাওয়া গেল। তাও কি সহজে মেটে, যা-যা পাওয়া গেল তার একটা flowchart বানিয়ে তারপর একটা মোটামুটি যা নিয়ে খোঁজখবর করছি, এবং তাকে কীভাবে, কোন নজরে দেখব—তার মোটামুটি একটা Title ও Subtitle দেওয়া গেল।
যা যা পেয়েছিলাম এবং প্রাথমিক বাছাই পর্বের শেষে যেগুলোর দিকে চোখ রেখেছিলাম, সেগুলো এইরকম—(১) Phanerozoic eon, Cenozoic era, Quaternary period, Holocene epoch, Meghalayan age, Anthropocene (২) Post-capitalist Society, Surveillance Capitalism (৩) Online-Offline nexus (৪) Translingualism, Transculturalism, Transethnic (৫) Superdiversity, Supervernacularism ইত্যাদি। (১)-এর পরিসরটা দেখে সম্পূর্ণ আলাদা মনে হলেও—সূত্র ওর মধ্যেও আছে। ওই শেষোক্ত শব্দটায় বলা আছে, এই Geological era-র নিয়ন্ত্রক মানুষ। সে প্রকৃতির নিজস্ব নিয়মের ভেতরে ছাপ ফেলছে তাঁর কর্মকাণ্ডের। সে-ই ‘প্রকৃতি-নিয়ন্ত্রণ’ এবং বাকি সংজ্ঞাগুলোর ভেতর থেকে ঠিক জিনিস বেছে, নিজের রোগমুক্তির পথ হিসেবে ওই Title-Subtitle শিরোধার্য করতে বেশ বেগ পেতে হলো।
#Postdigital
If you’re not careful, the newspapers will have you hating the people who are being oppressed, and loving the people who are doing the oppressing. —Malcolm X
Post-অনুসর্গটা মানবিক বিদ্যাচর্চায় এক ‘বিশেষ ব্যঞ্জনা’ বয়ে নিয়ে বেড়ায়। Postmodernism-Postcapitalism-Postcolonialism ইত্যাদির কোনোটার ক্ষেত্রেই Post-অনুসর্গের মানে ‘পরবর্তী’ নয়। উলটে সেটা বিশিষ্ট বিগ্রহের (paradigm) মুখের ওপর তর্জনি নেড়ে সেই বিগ্রহেরই অন্য আরেক প্রস্থান রচনা করে। Post-Digital মানেও তেমনি, ডিজিটাল-পরবর্তী নয়। আরেকরকম ডিজিটাল। Post-Digital যুগটা কেমন সেটা বুঝতে গেলে, Accenture-এর Chief Technology & Innovation Officer, #Paul Daugherty-র একটা জরুরি ঘোষণা ও প্রশ্নের দিকে তাকানো দরকার : ‘The post-digital era is coming: Are you ready?’[১] বোঝা যায়, এই ঘোষণা ও প্রশ্ন করা হয়েছে, ক্রেতা সমাজকে অথবা ক্লায়েন্টদের। ঘোষণাটা করা হয়েছে ২০১৯ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি।
সেই ঘোষণায় ছিল—বাণিজ্য এবং সমাজে প্রযুক্তির স্বরূপ পরিবর্তনের দুর্নিবার গতি সর্বক্ষণ আমাদের টানটান উত্তেজনার মধ্যে রাখে। এই বুঝি আরও নতুন নতুন ফিচার এল নতুন ও দামি মোবাইলে, আমার মোবাইলে সে সব ফিচার নেই। ফলে আমি উদ্বিগ্ন এবং আমি একইসঙ্গে সে-ই সামাজিক ও বাণিজ্যিক উত্তেজনার অংশ। প্রযুক্তির স্বরূপ পরিবর্তনের নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হতে চলেছে। আমরা সেই দিগন্তের দিকে যাত্রা করব : প্রযুক্তিই আমাদের নিয়ে যাবে, from the digital age towards a new reality, Accenture-এর prediction সেই ‘নতুন বাস্তব’ হবে post-digital era, কেন post-digital era? তার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে ডগার্টি বলছেন : আমরা এখন কোথায় (কোন যুগে) বাস করছি—সেটা একবার ভাবুন! কীরকম যুগ সেটা? সেই যুগে, ২০১৯-এ, গোলক জুড়ে (Globally) ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশন খাতে খরচা হবে ১.২৫ ট্রিলিয়ন ডলার। International Data Corporation (IDC)-এর হিসেব অনুযায়ী, সেই আকাশছোঁয়া খরচা ২০২২-এ গিয়ে দাঁড়াবে ১.৯৭ ট্রিলিয়ন ডলারে। Digitally-enhanced offerings, operations, and relationships ইত্যাদির ওপর নির্ভর করে থাকা প্রত্যেক industry-র বৃদ্ধি ও বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে Global GDP-র ষাট শতাংশ digitized হয়ে যাবে।
মানবসভ্যতায় এই উত্তরণ নিঃসন্দেহে নতুন এক অধ্যায়ের সূচনা করবে, যেখানে সকলেই বলবে—they are going digital, সেই নতুন অধ্যায়ে দরকার পড়বে নতুন set of rules-এর, যাতে Post-Digital যুগে মানুষ Digital প্রযুক্তিকে আরও গভীরভাবে, আরও ব্যাপকভাবে ব্যবহার করতে পারে। কেমন দেখতে হবে সেই যুগ? পল ডগার্টি বিবৃত করছেন, সেই যুগ হবে—“A world where individualization and instant on-demand capabilities will make it possible for businesses to capture and deliver on momentary markets.”—নজরটানগুলো তাঁরই দেওয়া। এখন কথা হচ্ছে, যখন ‘Global GDP-র ষাট শতাংশ digitized হয়ে যাবে’ বলে ঘোষণা করা হচ্ছে, তখন, মানবিক বিদ্যার কর্মীদের কাজ কী হবে—সেটা যেমন ভাবনার বিষয়, তেমনই নতুন (আগত) Post-Digital যুগে ‘এমনি’ মানুষ কীভাবে কাজ করবে, সক্রিয় সামাজিক প্রাণী হিসেবে নিজেদের ঘরে-বাইরে তারা কীভাবে communication চালাবে, কী হবে তার phenomenology of understanding—এসব হিসেবনিকেশও আগেভাগেই ভেবে রাখার কথা।
হিসেবের একাধিক আভাস পাই ব্লোমার্টের কাজে (দ্রষ্টব্য : ব্লোমার্ট ২০১৮ক, ২০১৮খ)। ব্লোমার্ট বিশেষত তাঁর শেষের দিকের কাজে কথা বলার যে পরিসরটা বেছে নিয়েছেন, সেটা হলো, Online-offline Nexus (দ্রষ্টব্য : ব্লোমার্ট ২০১৮খ)। এখন এই নেক্সাসটা একটু বুঝে নিলে আপনাদের মতো আমারও সুবিধা হওয়ার কথা। এখনকার যুগে মানুষের যে সামাজিক নড়াচড়া তা ওই online-offline Nexus-এর দড়িতে বাঁধা। গোলোকায়নের এ এক নতুন গ্যাঁড়াকল। যেখানে ডিজিটাল প্রযুক্তি মানুষের প্রতিদিনের উল্লেখযোগ্য বলিষ্ঠ এবং অবিকল্প offline কাজকে সংগঠিত করে রাখে। সেখানে সেই কাজ মুক্তি খুঁজে পায় online-এ। ‘বক্তব্য’ তার শ্রোতা পায়, ‘লেখা’ তার পাঠক পায়, ‘মন্তব্য’ পায় বোঝদার মানুষ, ‘বার্তা’ তার প্রেরিতকে খুঁজে পায়। ব্যক্তি-মানুষের ‘ডিজিটাল’ পরিচয়েই মানুষকে চেনা। তার সঙ্গে বন্ধুত্ব। এ-যুগের কর্মকাণ্ডের ‘কুরুক্ষেত্র’ হচ্ছে—online-offline nexus—এই nexus, Post-digital যুগে মানব সম্বন্ধের দুই dimension (online-offline)-কে সমন্বিত করে। মানুষের সেই সামাজিক জীবন নতুন, বাস্তব অভূতপূর্ব।
অফিস যাবার নতুন যান হবে বৈদ্যুতিন মাধ্যম। মানুষ অশরীরে অফিস যাবে, তাকে আর তিরিশ মাইল দূরে—ট্রেন-ট্রাম-বাস ঠেঙিয়ে, ভিড়ে চিঁড়েচ্যাপটা হয়ে, গলদঘর্ম অবস্থায় অফিস যেতে হবে না। বাড়িতে বসে সে আট ঘণ্টার জায়গায় চোদ্দ ঘণ্টা কাজ করবে। তারও লাভ, কোম্পানির ভি লাভ। সেই ব্যক্তি খেয়ালও রাখবেন না তাঁকে চোদ্দ ঘণ্টার কাজে বেতন দেওয়া হচ্ছে দৈনিক বারো ঘণ্টা হারে। বাড়িতে বসে কাজ করে, ‘আগের চেয়ে বেশি মাইনে’—এইটেই তার কাছে বড়ো হয়ে উঠবে। দপ্তরের হলদে লতপতে ফাইল হয়ে উঠবে বর্ণহীন ই-ফাইল, দপ্তরির সাক্ষর হয়ে উঠবে ই-সিগনেচার। হাতে নোট লেখা তো ছেড়ে দেওয়া হয়েছে কবেই! কাজের offline আর interactivity-র online—এই হলো, online-offline nexus-এর মোদ্দা কথা। যদিও পরিসর হিসেবে online অনেক বেশি dynamic এবং expandable, এবং post-digital সমাজে সেই পরিসরের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি, তবুও সেই সমাজ offline-কে একবারে অস্বীকার করতে পারে না, কারণ offline-ই তো online-এর শিরদাঁড়া।
তবে অনলাইনের সবচেয়ে বড়ো অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে তার ভাষার খেলা ও তার নিত্য নতুন নিয়ম। সেই নিয়ম অফলাইনের ভাষায় নেই। কারণ অফলাইনে সময় দীর্ঘ ও স্থায়ী, অনলাইনে সময় কম ও ডাইনামিক।
উদ্বেগ
বিগত কয়েক দশকের মধ্যেই ঘটনাটা ঘটল। আমাদের সকলের সামনে দিয়ে, সকলকে জানিয়ে। অথচ আমরা কেউ টের পেলাম না কী ঘটল! এই সময়টাতে মানুষের জীবন একেবারে ‘অন্যরকম’ হয়ে গেল এবং এই জীবন যে আরও দ্রুত ‘অন্যরকম’-ই হতে থাকবে, সেই কথা অনুমান করা শক্ত কাজ নয়। তার ওপর ডগার্টির ঘোষণা তো রয়েইছে! সমাজের গঠন, মানুষের জীবনধারা, চর্চা ও চর্যার মূল সূত্রগুলো চিরকালই তো সদা-পরিবর্তনশীল! এবং মানবসভ্যতার ইতিহাসে কোনো এক পর্ব থেকে এই পরিবর্তনের সবচেয়ে বড়ো ও একমাত্র কারণ পুঁজির বিকাশ এবং পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থায় প্রযুক্তির উন্নতি। এবং সমাজবিজ্ঞান, অর্থনীতি, ইতিহাস, ইত্যাদি মানবিক বিদ্যার নানান শাখায় মানুষের সমাজ ও মনের সদা-পরিবর্তনশীলতা নিয়ে চিরকালই আলোচনা হয়ে এসেছে। তাহলে এখনকার পরিস্থিতির ‘অন্যরকম’ হয়ে যাওয়া নিয়ে আমি গৌরবে ‘আমরা’ কেউ কেউ উদ্বিগ্ন কেন? আমাদের কারুর কারুর মনে হয়েছে, মানবসভ্যতার ইতিহাসের অন্যান্য পরিবর্তনগুলোর সঙ্গে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য দেখিয়ে আজকের যুগলক্ষণগুলো এই মুহূর্তে চিহ্নিত করে ভাষার বৃত্তে আমাদের আশু কর্তব্যগুলোর দিকে তাকাতে হবে।
অন্যান্য অনেকের মতোই, আমাদের সেই কারুর কারুর হিসেবে, বিগত কয়েক দশকে এবং অদূর ভবিষ্যতের দিনগুলোতে—সমাজের গঠনের, মানুষের কামনা-বাসনার, অভ্যেসের, অভিজ্ঞতার, অনুশীলনের, অর্পণের, interaction-এর ক্ষেত্রে, এই পরিবর্তনকে—বিশেষভাবে নজর দেওয়া প্রয়োজন। সভ্যতার ইতিহাসের অন্যান্য বদলগুলোর সঙ্গে তুলনামূলক সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য দেখিয়ে, এই অর্বাচীন ‘যুগ’-টাকে $objectify করা দরকার। কারণ, আমরা অনেকেই উপলব্ধি করছি সভ্যতার ইতিহাসের অন্যান্য ‘বিশেষ’ অর্থনৈতিক পরিবর্তনগুলোর সঙ্গে এই ‘অন্যরকম’ পরিবর্তনের প্রকৃতিগত ফারাক রয়েছে।
প্রত্যেকটা পরিবর্তনের সঙ্গেই প্রত্যেকটা পরিবর্তনের ফারাক ছিল, আগেও ছিল। কিন্তু এখনকার পরিবর্তনের লক্ষণগুলো বিচার করে দেখা যেতে পারে আমার বা আমাদের কারুর কারুর মনের অসুখের পটভূমিটা ঠিক কী? যে সমস্ত পরিবর্তন ইতিহাসের বৃহৎ অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তন বলে চিহ্নিত, সেটার শুরু ধরে নেওয়া যেতে পারে জমি-দখলের অন্যতম কৌশল হিসেবে, উপনিবেশ বিস্তারের সূচনা হওয়ার মধ্যে দিয়ে। দ্বিতীয়ত; আরেকটু অন্যভাবে বলতে গেলে, বাজার, বিপণন ব্যবস্থা, বাণিজ্য ব্যবস্থার সঙ্গে প্রযুক্তির নানান আবিষ্কারের ঘটনার বরাবরই যোগ রয়েছে। এখনও রয়েছে। যোগের প্রকৃতিও প্রত্যেকবারেই পালটেছে—প্রযুক্তির বিকাশের ধরন এবং পুঁজিবাদের নীতির সাপেক্ষে। কিন্তু তবু যেন মনে হচ্ছে, এখনকার পুঁজিবাদের স্বরূপ এবং প্রযুক্তির বিকাশের সঙ্গে পুঁজিবাদের সম্পর্ককে নতুন করে বিচার করা প্রয়োজন।
কারণ বর্তমানের ওই সম্পর্ক মানুষের জীবনধারায় শুধু প্রভাব ফেলছে—তাই নয়, এমন এক জায়গায় সক্রিয় হচ্ছে, যেখানে সাংস্কৃতিক মানুষের বাস্তব-জীবনের সত্তাগত ওরফে #ontological এবং physical অস্তিত্ব বিপন্ন হচ্ছে। এখনকার পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থায়—মানুষের মন, ও ব্যক্তিগত পরিসর ‘কাঁচামাল’ হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে দেখতে পাচ্ছি। এইসবের কেতাবি প্রমাণ পরে দিচ্ছি। এই যে বস্তু/দ্রব্যের Replacement হিসেবে মানুষের ‘মন’, বর্তমান উৎপাদন ব্যবস্থার অন্যতম কাঁচামাল—এই Replacement-টাই বিশেষভাবে ভাবাচ্ছে আমায় বা আমাদের।
কীভাবে ঘটছে ঘটনাটা? আরেকটু বিশদে বোঝার চেষ্টা করি। এ-যুগের ‘বদল’ আমাকে ‘আমি’-ই থাকতে দিচ্ছে। আমাকে আমার যাবতীয় সাংস্কৃতিক অভ্যাস বজায় রাখতে দিচ্ছে। আমাকে বরং আগের চাইতে অনেক বেশি সৃজনশীল করে তুলছে। এইখানে, এই যে বেশি করে পাওয়ার মধ্যেই যেন সন্দেহটা বেশি করে জন্মায়। আমার সমস্ত রকম কাজকর্ম যেন অবচেতনে ভেতরে-ভেতরে অন্যরকম হয়ে উঠছে। কীরকম ‘অন্যরকম’, সেটা সবার প্রথমে জানা প্রয়োজন। শুধুমাত্র অনুভূতি বা উপলব্ধির ওপর বসে কাজ করাটা, এই ক্ষেত্রে কাজের কথা নয়।
এই কাজ করতে গেলে, একসঙ্গে বসতে হবে সকলকে। অর্থনীতি, ভাষাতত্ত্ব, জীববিজ্ঞান, ইতিহাস, মনস্তত্ত্ব, পরিবেশ বিজ্ঞান এবং বাস্তুবিজ্ঞানের কর্মীদের। এছাড়াও আরও অন্যান্য চর্চার কর্মীদেরও সম্মিলিত করতে হবে। এই সমন্বয়ের কাজ এই মুহূর্তে কেবল কঠিনই নয়, অসম্ভব। এ-যুগে সময়ের যখন এত অভাব, তখন ‘অসম্ভব’-এর কাজে হাত দেওয়াটা বোকামি। তাই আপাতত নিজের নিজের আর্থসামাজিক পরিসরে দাঁড়িয়ে, নিজের-নিজের চর্চার উঠোনে দাঁড়িয়ে, আপনাকে-আমাকে, আলাদাভাবেই আপাতত কাজ করতে হবে, এই কথা জানিয়ে রাখছি। কখনও আমাদের দেখা হলে হাত ধরে বলতে হবে, আমরা একই কাজের বিভিন্ন অংশ এক-একজনে করছি। সেই কাজ শুরুও করেছেন অনেকে। মনে রাখতে হবে আমাদের ‘মঞ্চ’ একটাই। সে মঞ্চ পারস্পরিক কথা-বিনিময়ের জায়গা, গণতন্ত্রের জায়গা।
মঞ্চটা অনেকদিনের। মঞ্চে কখনও ধীরে কখনও চটজলদি কাজ হয়ে চলেছে। কিন্তু একটা মুশকিল নিয়ে আজকাল বাজার বেশ সরগরম হতে দেখছি। মঞ্চের নীচে জড়ো হওয়া মানুষের মধ্যে থেকে দাবি উঠতে দেখছি—‘কী করে বাঁচবে লোকে/ কেউ যদি বলে দিত।‘ এখন এই দাবির ভেতর একটা প্রাতিষ্ঠানিক উসকানিও থাকতে পারে, আমাদের সমাবেশ ভেস্তে দেওয়ার প্রকল্প হিসেবে। সে-কথা উড়িয়ে দিচ্ছি না। কিন্তু দাবি যখন একবার উঠেছে—তা মানুষের মধ্যে সংক্রমিত হতে বেশি সময় নেবে না। সংক্রমণের যা গতি হয়েছে আজকাল! কেবলমাত্র ওই মঞ্চে উপবিষ্ট মানুষ পরস্পরের এই সমস্ত কাজগুলোকেই যে কেবল জরুরি মনে করছেন তা তো নয়! কিন্তু যারা দাবি করছেন, ‘কেউ যদি বলে দিত’, তাদের দাবিও ফেলে দেওয়ার মতন নয়।
সোজা কথায় প্রযুক্তি ও পুঁজিবাদের জোটকে যদি বিরোধীপক্ষ ভাবি তাহলে টাকায় ও কৌশলে আমাদের বিরোধীপক্ষ আমাদের চাইতে পাল্লায় অনেক ভারী। তাই আমাদের কাজ, আমাদের দায়দায়িত্ব অনেক বেশি ওদের তুলনায়। এই বিভাজন কিন্তু কেবলমাত্র স্ট্র্যাটেজিক, সেটা মনে রাখুন দয়া করে। শুধুমাত্র পরিস্থিতির একটা চটজলদি ছবি আঁকার চেষ্টা। এখন আমাদের মঞ্চের আশপাশ থেকে ওঠা দাবির ‘কেউ’ কারা হতে চাইবেন সেটা দেখা সবচেয়ে আগে দরকার। এইসব দরকারের কথা মাথায় রেখে আমি মঞ্চে উঠবার চেষ্টা না করে, আপাতত নেমে দাঁড়াচ্ছি। কিন্তু মঞ্চেরও নিজস্ব কিছু কাজ থাকে, সেই কাজ ছেড়ে দিলে কাজের বৃত্ত অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। কথাটা অপূর্ণতা নিয়ে নয়। ‘কোনোকিছুই পরিপূর্ণ হয় না’—কথাটা মনে মনে বিশ্বাসের মতো আঁকড়ে ধরেছি কবেই তো! ভয়টা কাজের অবিচ্ছিন্ন পরম্পরার সূত্রটা পাছে ছিঁড়ে যায়, তার! আমার কাজ শিখবার জায়গা ভাষাতত্ত্ব, সংকেত তত্ত্ব আর ভাষা-বৈচিত্র্যের চরিত্র ব্যাখ্যা তত্ত্ব। আমিও এই মুহূর্তে ভেবে নিয়েছি, আমাকেও কাজ চালিয়ে যেতে হবে, আমার নেতাদের সঙ্গে একই মঞ্চে না থেকে, মঞ্চের নীচে দাঁড়িয়ে দুয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে হাতে হাত রেখে কিংবা একা!
আমি আমার শিখবার জায়গাতেই দাঁড়িয়ে দেখতে পাচ্ছি, যে—‘অন্যরকম’-এর কথা দিয়ে আমি এখনকার ‘What is to be done’ লিখতে বসেছি, সেই অন্যরকমের প্রমাণ—ভাষা ইত্যাদির অস্তিত্বের মধ্যেও প্রচ্ছন্নভাবে অথবা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। প্রথমদিকে মনে একটু দ্বিধা ছিল। রাষ্ট্রীয় অর্থনৈতিক স্তরে একইসঙ্গে ‘ভাষা-বৈচিত্র্য’-কে, ‘ভাষার বিপন্নতা’-কে ডিফাইন করার কাজ চলছে—জোর কদমে। আবার সেই সঙ্গে তৈরি হচ্ছে #translingual space, একদিকে rural diversity অন্যদিকে metropolitan super-diversity আমাকে confuse করে দিচ্ছে।
ইদানীং সেই দ্বিধা খানিকটা কেটেছে। তৈরি হতে হচ্ছে, অন্যান্য অনেক মানুষের ontological dualism-এর মতো ভাষারও একাধিক অস্তিত্বের জায়গা নিয়ে, crossing and convergence of discourses নিয়ে। এক জিনিসের ভেতর সেই একই জিনিস। যার ফাংশনগুলোও এক। অথচ ফাংশনগুলো নিজেরাই ভীষণভাবে এক অদৃশ্য নজরে বন্দি। এই অবস্থায় একটা গোড়ার প্রশ্ন নিয়ে বেশ কিছুদিন ধরে নাড়াচাড়া করেছি। ভাষা ঠিক কোথায় অন্যান্য প্রাণীর in-group ও out-group communication-এর নিরিখে আলাদা? এই প্রশ্নটা এখনও এই অন্যরকম পরিস্থিতিতেও কাজে লাগবারই তো কথা। লাগবেও হয়তো। এখুনি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি না। এখন কথা হচ্ছে যে, ওই ‘অন্যরকম’ তো সমস্ত সমাজে-রাষ্ট্রে অর্থনৈতিক-ব্যবস্থা নিরপেক্ষ নয়। ফলে ‘সমস্যা’-র যতটা ভাবতে পারছি, সে তার চেয়েও অনেক বেশি জটিল। আমার চেনাজানা বৃত্তেই তো কতরকম মানুষ। তার ওপর ডিজিটাল-বিশ্বে মানুষের আনাগোনার সূত্রে বিষয়ীর পরিচয়ের বৈচিত্র্য যেভাবে বেড়েছে তাতে যে-কোনো একটা সূত্র দিয়ে আদর্শ বক্তা-শ্রোতা বা আদর্শ লেখক-পাঠক, ইত্যাদি বর্গ তৈরি করা যাবে না।
সোজা ও অল্প কথায় বলতে গেলে, মানুষের ভাষিক আদানপ্রদানের পরিসরের (ক) প্রাগৈতিহাসিক চেহারা অর্থাৎ মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কথা বলা বা কথা লেখা/আঁকা—যেখানে বক্তা বা ধারাভাষ্যকারের সঙ্গে এক বা একাধিক শ্রোতা/পাঠক/দর্শকের সম্বন্ধ গড়ে উঠত, (খ) এই সম্বন্ধের ঐতিহাসিক পুঁজিবাদী মোচড় ও মুদ্রণের বন্দোবস্ত, যেখানে শ্রোতা/পাঠক/দর্শকের সংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মামুলি বক্তা বা ধারাভাষ্যকারের পাশাপাশি তৈরি হলো, লেখক এবং (গ) ভাষিক আদানপ্রদানের পরিসরকেই তৃতীয় একপ্রকার সক্রিয় ও গতিশীল ব্যবস্থার (যাকে এখানে Post-digital Online-Offline Nexus বলেছি) হাতে তুলে দেওয়া এবং তার মাধ্যমে অজস্র বক্তা-শ্রোতা অথবা লেখক-পাঠকের সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা করা। এই (ক), (খ) এবং (গ) তিনটে সূত্রই মোটামুটি এখনকার ভাষিক পরিবেশে সক্রিয়। বলা বাহুল্য, (গ) ক্রমপ্রসারমান এবং (খ)-কে ইতিমধ্যেই সে প্রায় সম্পূর্ণ গিলে ফেলেছে। (ক) মানুষের দীর্ঘদীনের আদিম অভ্যেস—তাই তাকে গিলতে (গ)-এর সময় লাগবারই কথা! আমি একজন ভাষী হিসেবে তাহলে এখন কীরকম পরিসর পাচ্ছি? আটপৌরে কথা বলার পরিসর পাচ্ছি —যেখানে অনবরত হানা দিচ্ছে Online-Offline Nexus, ফলে আমি প্রথাগত ভাষিক উপলব্ধি এবং বোঝাপড়ার জায়গাটায় থিতু থাকতে পারছি না। আর সরাসরি পাচ্ছি Online-Offline Nexus-এ অংশগ্রহণ করার সুযোগ। সেখানে বক্তা-শ্রোতা, লেখক-পাঠক চিনতে পারছি না, তারা পরস্পরের থেকে অনেকটা দূরে সরে গেছে—এখন আমার সঙ্গে সবার হয়ে কথা বলছে এক বুদ্ধিমান ব্যবস্থা। তাতে গণ্ডগোলটা কোথায় হচ্ছে? তাতে আমি একইসঙ্গে—আটপৌরে-আনুষ্ঠানিক, সত্যি-মিথ্যে, ভাষার চেহারা দেখতে পাচ্ছি, যে-চেহারা খণ্ডিত অভিব্যক্তি-নির্ভর সাংকেতিকও বটে আবার আনুষ্ঠানিক মানে ‘উৎপাদনকারী’ ‘অখণ্ড পাঠ্য’ও বটে।
আমার সকল রসের ধারা
শিরোনামে, (আমি) যুগটাকে Post-Digital, পরিসরকে Online-Offline Nexus এবং সেই পরিসরে আদানপ্রদানের ভাষার চেহারাকে #Translingual বলেছি। কিন্তু উল্লিখিত যুগ এবং পরিসরে ভাষার কাটাকুটি খেলার চরিত্রকে বুঝব কী করে? ভাষাতত্ত্ব বা সংকেত তত্ত্বের চেনা ছক ধরে এগোলে কাজ হবে না—সেটা বোঝা যায়, শিরোনামে ব্যবহৃত ওই প্রত্যেকটা পরিভাষার কাজের আসল জায়গার উল্লেখ করলে। শুরু থেকে মনের অসুখের প্রসঙ্গটা তো এমনি তুলিনি। তুলেছি এই কথার ইঙ্গিত দিতে—যে এই সময়টা কাজ করছে সরাসরি মানুষের মনকে নিয়ে, যে ‘মন’ ভাষার ভোক্তার ভূমিকায় সদা নিয়ত। তাই এ-যুগে ভাষার ওই কিম্ভুতকিমাকার চেহারার সামনে দাঁড়িয়ে কাজ করবার জন্য, আমিও এমন এক অদৃশ্য কার্যক্রমের পালটা প্রসঙ্গ টেনে আনছি—যা কোনো ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একাধিক মনের এলাকায় কাজ করে এবং ‘মন’গুলো, ওই ঘটনা এবং কার্যক্রমের সূত্রে পরস্পরের মধ্যে গভীর সম্বন্ধে বাঁধা। অদৃশ্য কার্যক্রম বলে আমি এখানে ‘রস’-এর কথা তুলতে চাইছি। ঠিকই ধরেছেন সাহিত্যের আলোচনায় যে রসের উল্লেখ পান, এ সেই রস। ভাষা তার নিজের চেহারা পালটে ফেললেও, কিংবা তার কাজ করবার জায়গায় তৃতীয় একপ্রকার সক্রিয় ও গতিশীল ব্যবস্থার অনুপ্রবেশ সহ্য করলেও—সে মানুষের মন ও সমাজের লৌকিক-অলৌকিক, বাস্তব-অলীক—এসব খেলার নিয়ম আজও ভুলে যায়নি—এইটুকুই যা ভরসা। ওই ভরসার জায়গা থেকেই রসের কথা তোলা!
বাংলা সাহিত্যের আলোচনার জগতে, বিশেষ করে কাব্যের আলোচনায় এই ‘রস’ জিনিসটাকে বেজায় প্রাধান্য দেওয়া হয়। এই রসের কথা আমরা প্রথম পড়েছিলাম, অতুলচন্দ্র গুপ্তর (১৯৯১) ‘কাব্যজিজ্ঞাসা’ বলে একটি চটি বইতে। তখন আমাদের পরীক্ষায় লিখতে হতো, ‘কাব্যরসের আধার কাব্যও নয়, কবিও নয়—সহৃদয় কাব্য-পাঠকের মন’—এই বক্তব্যের (ওই বইয়েরই উদ্ধৃতি) ব্যাখ্যা। রস ব্যাপারটা কী? সে-কথা খুব সংক্ষেপে বলি। যেহেতু, ভারতীয় কাব্য ও নাট্যশাস্ত্রের তরফ থেকে রসের ভাষ্য আমরা প্রথম পাচ্ছি, সেহেতু, রসের প্রাথমিক পরিচয় দেওয়ার কথা ওই সমস্ত শাস্ত্রের ভেতরে বসেই। তবে ক্রমশ তার কাজ করবার এলাকা নিয়ে প্রশ্ন তুলে তাকে মুক্তি দেওয়ার চেষ্টা তো করতেই হবে।
রস হচ্ছে এমন এক অলৌকিক জিনিস যা কাব্যের পাঠক বা নাটকের দ্রষ্টার মনের লৌকিক ভাবকে উসকে দিয়ে তাকে কাব্য বা নাটকের উপলব্ধির স্তরে নিয়ে যায়। তাই অলৌকিক হলেও রস একধরনের মানসিক অবস্থা (গুপ্ত ১৯৯১ : ২৫)। তাই বলে, রসকে মানুষের মনের নির্বিশেষ অবস্থা বলা হয়নি কিন্তু। কাব্য বা নাটকের রস সকল মনে নির্বিশেষ ভাবে দাগ কাটে না। তার জন্য চাই, এক বিশেষ ধরনের মন। ভারতীয় আলংকারিকরা যে মনকে বলেছেন, ‘সহৃদয়হৃদয়সংবাদী’ (প্রাগুক্ত : ২৪)। অর্থাৎ রসের প্রধান উপাদানই হলো মানুষের মন, এবং কাজ হলো সেই মনকে বিশেষ করে তোলা। রসের আরেকটা উপাদান আছে, সেটা হলো বাহ্যিক। এই ক্ষেত্রে বাহ্যিক মানে আক্ষরিক অর্থে বাহ্যিক নয়। রসের বাহ্যিক উপাদান আসে কবির সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে, তাঁর কৃতিত্বের মধ্যে দিয়ে।
“লৌকিক জগতের বাহ্যিক কারণে মনে শোক জেগে মানুষ শোকার্ত হয়। কিন্তু শোকার্ত লোকের মনের ‘শোক’ তার কাছে ‘রস’ নয়, এবং সে শোকের কারণটিও কাব্য নয়। কবি যখন তাঁর প্রতিভার মায়াবলে এই লৌকিক শোক ও তার লৌকিক কারণের এক অলৌকিক চিত্র কাব্যে ফুটিয়ে তোলেন, তখনই পাঠকের মনে রসের উদয় হয়, যার নাম ‘করুণ রস’।” (প্রাগুক্ত: ২৬ এবং নজরটান সংযোজিত)
সুতরাং, দুটো কথা এখানে মনে রাখা দরকার। এক, রস জিনিসটা নিজে অলৌকিক হলেও, তার জন্মের ভিত্তি লৌকিক এবং দুই, রস প্রতিভার মায়াবলের অধিকারী কবি বা নাট্যকার ও সহৃদয়হৃদয়সংবাদী পাঠক বা দ্রষ্টার মধ্যে আদানপ্রদানের এক কার্যক্রম, যে কার্যক্রমের পরিসর কাব্য অথবা নাটক। প্রসঙ্গত, উল্লেখ করে রাখলে ক্ষতি নেই যে, সংস্কৃত অলংকার শাস্ত্রে নয় রকমের স্থায়ী রসের কথা বলা হয়েছে : শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস, অদ্ভুত ও শান্ত। ওই প্রত্যেক প্রকার রসই কিন্তু জন্মসূত্রে লৌকিক বা বাস্তবের উত্তরসূরী।
এবার Post-Digital Online-Offline Nexus-এ মানুষের মনের অবস্থা, ভাষার #Translingual চেহারা নিয়ে কথা কইতে গিয়ে হঠাৎ আমরা রসের প্রসঙ্গ কেন পেড়ে আনলাম, বর্তমান রচনার পাঠক ইতিমধ্যেই হয়তো তার ক্লু পেয়ে গেছেন। ও-প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনায় যাবার আগে, ‘রস’ নিয়ে রবীন্দ্রনাথের তিনটে বক্তব্য একটু বিশদেই উল্লেখ করছি, যাঁরা এখনও ক্লু পাননি, তাঁদের কথা ভেবে। এই বক্তব্যের মধ্যে কিছু অংশে পাঠকের নজর টানবারও চেষ্টা করছি।
(১) প্রথম বক্তব্য তাঁর ‘সাহিত্য’ গ্রন্থের ‘ঐতিহাসিক উপন্যাস’ [২] প্রবন্ধ থেকে—
“ব্যক্তিবিশেষের সুখদুঃখ তাহার নিজের পক্ষে কম নহে, জগতের বড়ো বড়ো ঘটনা তাহার নিকট ছায়ায় পড়িয়া যায়, এইরূপ ব্যক্তিবিশেষের অথবা গুটিকতক জীবনের উত্থানপতন-ঘাতপ্রতিঘাত উপন্যাসে তেমন করিয়া বর্ণিত হইলে রসের তীব্রতা বাড়িয়া উঠে; এই রসাবেশ আমাদিগকে অত্যন্ত নিকটে আসিয়া আক্রমণ করে। আমাদের অধিকাংশেরই সুখদুঃখের পরিধি সীমাবদ্ধ; আমাদের জীবনের তরঙ্গক্ষোভ কয়েকজন আত্মীয়বন্ধুবান্ধবের মধ্যেই অবসান হয়।”
(২) রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় বক্তব্য, ‘সাহিত্য’ গ্রন্থের ‘পরিশিষ্ট’ [৩] থেকে—
“সাহিত্যেও তেমনি মানুষ আষাঢ়ের মেঘের মতো যে রসের ধারা এবং যে জ্ঞানের ভার নিজের প্রয়োজনের মধ্যে আর ধারণ করিয়া রাখিতে পারে না তাহাকেই বিশ্বমানবের মধ্যে বর্ষণ করিতে থাকে। এই উপায়েই সাহিত্যের দ্বারাই হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয়, মনের সঙ্গে মন, মিলিত হইয়া মানুষ ক্রমাগত স্বকীয়, এমন-কি স্বজাতীয়, স্বাতন্ত্র্যের ঊর্ধ্বে বিপুল বিশ্বমানবে পরিণত হইবার অভিমুখে চলিয়াছে।”
(৩) তৃতীয় বক্তব্য তুলে আনছি রবীন্দ্রনাথের ‘শান্তিনিকেতন’ প্রবন্ধাবলির ‘ভাবুকতা ও পবিত্রতা’ [৪] প্রবন্ধ থেকে। ওই প্রবন্ধের শুরুতেই আছে—
“ভাবরসের জন্যে আমাদের হৃদয়ের একটা লোভ রয়েছে। আমরা কাব্য থেকে, শিল্পকলা থেকে গল্প গান অভিনয় থেকে নানা উপায়ে ভাবরস সম্ভোগ করবার জন্যে নানা আয়োজন করে থাকি।…
এইরকম ভাবের পাওয়াকেই পাওয়া বলে ভুল করা মানুষের দুর্বলতার একটা লক্ষণ। সংসারে নানাপ্রকারে আমরা তার পরিচয় পাই। এমন লোক দেখা যায় যারা অতি সহজেই গদ্গদ হয়ে ওঠে, সহজেই গলা জড়িয়ে ধরে মানুষকে ভাই বলতে পারে—যাদের দয়া সহজেই প্রকাশ পায়, অশ্রু সহজেই নিঃসারিত হয় এবং সেইরূপ ভাব-অনুভব ও ভাব-প্রকাশকেই তারা ফললাভ বলে গণ্য করে। সুতরাং ওইখানেই থেমে পড়ে, আর বেশিদূর যায় না।
এই ভাবের রসকে আমি নিরর্থক বলি নে। কিন্তু একেই যদি লক্ষ্য বলে ভুল করি তা হলে এই জিনিসটি যে কেবল নিরর্থক হয় তা নয়, এ অনিষ্টকর হয়ে ওঠে। এই ভাবকেই লক্ষ্য বলে ভুল মানুষ সহজেই করে, কারণ এর মধ্যে একটা নেশা আছে।”
আপাতত, রস নিয়ে এই-ক’টা ক্লু উল্লেখ করে আলোচনায় ফিরছি। কোথায় ক্লুগুলো কাজে লাগছে সেটা বলা বাহুল্য ক্রমশ প্রকাশ্য।
এখন রাবীন্দ্রিক-চিন্তার সূত্র ধরে, কাব্য, সাহিত্যের পরিসর থেকে টেনে বের করে এনে যদি আমরা রসকে আরও বড়ো কোনো পরিসরে কাজ করতে দিই, ধরা যাক আমাদের জীবনের সাধারণ কথাবার্তার পরিসরে! তাহলে ব্যাপারটা কীরকম দাঁড়ায়! আলংকারিকরা হয়তো এতে আপত্তি জানিয়ে বলবেন, রস ব্যাপারটার আধার যদি সহৃদয় চর্চিত পাঠকের মনই হয়ে থাকে, তাহলে তাকে অচর্চিত আটপৌরে মনে কাজ করতে দিলে কোনো ফল পাওয়ার আশা একেবারেই নেই! ও চেষ্টা বৃথা! কিন্তু আমি তাঁদের আরেকটু উদার হতে আবেদন জানাব—এই কথা বলে যে, আমরা যখন নিত্য আটপৌরে কথোপকথনে অবলীলায় অংশগ্রহণ করি তখন, আমরাও কি বক্তার বক্তব্যের মারপ্যাঁচ, মিথ্যে কথা, ঘুরিয়ে নাক দেখানো, কিছু না বলে অনেক কথা বলা বা অনেক কথা বলে কিছু না বলা, নিবেদন, আবেদন—ইত্যাদি সহৃদয়হৃদয়সংবাদী হয়ে পড়তে চেষ্টা করি না? সে সব কথা লেখা না-ই বা হলো। পড়তে চেষ্টা করলে তো সেইসব আটপৌরে কথা থেকেও রস পাবার কথা পাঠক অর্থে শ্রোতার! রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যকে মঞ্চে টেনে আনার কারণও তো সেইটাই।
আসলে রসের কারবার তো মানুষের মন নিয়ে। তাই তাকে কাব্যের বাইরেও কাজ করতে হবে বইকি। এই রস সংস্কৃত অলংকার শাস্ত্রে বর্ণিত রস ঠিকই কিন্তু তাকে যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে মানুষের মন জুগিয়ে চলতে হয়েছে বলে সে-ও আজ আর শুধু কাব্যের বাগানে ফুটতে চায় না। তার কারবার যে মানুষের মনে সে মানুষের তো নিত্য যাতায়াত, কথার আটপৌরে বৃত্তে। এখানে হ্বিটগেনস্টাইনের language game-এর কথা মনে করিয়ে দিতে চাই। রস ভাষার সেই একই নিয়মে কাজ করে, যে নিয়মের কথা হ্বিটগেনস্টাইন বলেছেন, ভাষার মামুলি দৃষ্টান্ত দিয়ে। ‘ভাষা’ নিজে বাস্তবের থেকে আলাদা হয়ে বাস্তবকে বিবৃত করে—এমন ধারণাকে হ্বিটগেনস্টাইন খারিজ করে দেন। ভাষার নিজের মধ্যেই থাকে ভাষা এবং অ্যাকশন। আবার সেই অ্যাকশনের মধ্যেই থাকে ভাষার বীজ। তাঁর language game খুব সহজ ও সরল। একজন শিশুকে যেমন প্রথমে ভাষার সহজ ব্যবহার দিয়ে ভাষা শেখানো হয়, language game তেমন। প্রত্যেকটা আঞ্চলিক ভাষার খেলার নিজস্ব নিয়ম আছে এবং প্রত্যেকটা খেলার মধ্যে নিয়মের একটা সম্বন্ধ আছে। আমরা যে আটপৌরে ভাষা ব্যবহার করি—সেটা আসলে language game-গুলোর পরিবারের মতো।
Reading the online (translingual) texts
১.
এই ছোট্ট বিভাগটাকে অন্যান্য নানান নামে ডাকা যেত। বলা যেত, OR, Understanding the Online SUBJECT—বা—Understanding the infinite multiplicity of expressions—যান্ত্রিক অনুরণনের রসাস্বাদন, ইত্যাদি। বলা বাহুল্য, আমি যখন Offline-এ তখন আমার আর TEXT(s)-এর সম্পর্কটা অনেকাংশেই পাঠক আর পাঠ্যের মতো। কিন্তু যে-দুটো জিনিসকে ডিজিটাল যুগে সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করা হয়েছে এবং (অথচ) ভোক্তা বা গ্রহীতা হিসেবে আমি যে-দুটো জিনিসকে নিরন্তর underestimate করে গেছি, সেই দুটো জিনিস হলো, use of time এবং multiplicity of expressions অথবা অনুরণন। কারণ আমার মনে রাখা দরকার ছিল, আমার আর TEXT(s)-এর মধ্যে যে মধ্যস্থতা করছে, সে মুদ্রিত গ্রন্থের মতো Static interface নয়। সে Semi-human dynamic interface, ফলে আমার ওই ভুলের মাশুল আমাকে গুনতে হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে।
আসলে ‘আমি’ নিজেও, user/reader/listener/observer/consumer—হিসেবে অনেকদিন ধরেই নিজেই ভীষণ dynamic—তাই, Semi-human dynamic interface-এর dynamicity আমার নজর এড়িয়ে গেছে। আর আমি ভেবেছি, একই গান বহুবার শোনা বা একই পদ্য বহুবার পড়া মানে আসলে Static interface থেকেই আমার স্থান-কাল-পরিস্থিতির গতিশীলতার সাপেক্ষে বহু ভাষ্য নির্মাণ করা।
এবার ডিজিটালোত্তর যুগে, আমি যখন Online-এ অংশগ্রহণ করছি, তখন আমার আর TEXT(s)-এর physical coordination-টা কেমন দাঁড়াল—সেটা ভেবে দেখবার সময় এসেছে। আর যেহেতু এই ভেবে দেখার কাজ আমাকে দিয়ে স্থগিত ‘রাখানো’ হয়েছিল, তাই এ-যাত্রায় কাজের পরিমাণ অনেকটা বেড়েও গেছে। এই বেড়ে যাওয়াটা মনে রেখেই কাজে হাত দিতে হবে। কাজের পরিমাণ বেশি ভেবে পিছিয়ে গেলে চলবে না! কারণ কাজ করার মানেই তো—আমরা যারা, খানিকটা ideological state apparatus-এর ঢঙে বর্তমানে ক্ষমতা বলবৎ করবার প্রক্রিয়ার মধ্যে, state-capitalism nexus, stakeholders, consumers/users ও economic polarization and exploitation-এর victim-দের দেখতে পাচ্ছি, তাদের নিজের নিজের দায়িত্বটুকু পালন করে যাওয়া। না হলে, মানবিক বিদ্যার শপথের প্রতি সুবিচার করা হবে না। মানবজমিনের পুরোটাই ব্যবহার করবে economic polarization-এ তৈরি হওয়া dominant class—যেখানে মানুষের সংখ্যা মুষ্টিমেয়, যাঁরা monogamous এবং violent!
Post-digital যুগে মনে রাখতে হবে, এই যুগকে কেউ কেউ নাম দিয়েছেন—‘The age of surveillance capitalism’ (দ্রষ্টব্য: Zuboff 2018)। সেই নাম দেওয়ার পেছনে যে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে সেটার দিকে তাকানো জরুরি। Shoshana Zuboff এই যুগের নামে তাঁর গ্রন্থের নামকরণ করেছেন। দ্বিতীয়ত; তিনি অত্যন্ত বিচক্ষণ হয়ে—‘surveillance capitalism’-এর একটা আভিধানিক সংজ্ঞা বইয়ের শুরুতে টাঙিয়ে দিয়েছেন। সংজ্ঞা প্রথমে বলে দেওয়া, deductivism-এর লক্ষণ। পাঠের ক্ষেত্রে deductivism-কে অগ্রাধিকার দেওয়ার মধ্যে একটা Anti-reading-কে উসকে দেওয়ার অভিসন্ধি থাকে। যে-সমস্ত পাঠক ইতিমধ্যেই এই যুগের লক্ষণ অন্যান্য পন্থায় চিনে নিতে শুরু করেছিলেন তাঁদের সঙ্গে প্রথমেই এই গ্রন্থ মিতালি পাতিয়ে নেবে—যাতে নতুন পাঠকের সঙ্গে ওই টেক্সটের সেতু বাঁধার কাজটায় অভিজ্ঞ পাঠক চটজলদি হাত দিতে পারে। আবারও বলছি, এ-যুগে কাজ করবার সময় কম পাওয়া যাবে—এটা ধরে নিতেই হবে। আর কাজ করবার দরকারের কারণটা তো আগেই বলেছি। সেই কথাটা আবার মনে করিয়ে দিচ্ছি, আপনারা কেউ কেউ বারবার ভুলে যাচ্ছেন বলে। মুখে বললে দেখেছি অনেক সময় কাজ কম হয়। তাই জ়ুবফের উৎসর্গ পত্রে—ওই গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্যকে যেভাবে ‘লেখা’ হয়েছে তাকেই আপাতত মনে রাখুন :
“…In honor of my children,
Chloe Sophia Maxmin and Jacob Raphael Maxmin—
I write to fortify your futures and the moral cause of your
generation.”
ফলে বুঝতেই পারছেন কোন জায়গাটায় দাঁড়াতে হচ্ছে এখনকার মানবিক বিদ্যার কর্মীদের। তাঁদের কাজে যদি সার্বিক সহযোগিতার হাত আমরা না বাড়াই তাহলে সমস্তই ভেস্তে যাবে।
‘Surveillance capitalism’-এর আভিধানিক সংজ্ঞায় জ়ুবফ (২০১৮) উল্লেখ করেছেন : (এক) এ-যুগের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, মানুষের ব্যক্তিগত তথ্য, ব্যক্তিমানুষের প্রকৃতি ও চাহিদা, এবং ওই দুইয়ের মধ্যে দিয়ে তাকে পণ্য বিক্রি করার এক প্রচ্ছন্ন বাণিজ্যিক প্রক্রিয়ার উদ্দেশ্যে মানুষের অভিজ্ঞতাকে কাঁচামাল হিসেবে বিনামূল্যে ব্যবহার করা। (দুই) পণ্যদ্রব্য এবং পরিষেবা উৎপাদনের পরজীবী অর্থনৈতিক যুক্তিকে তার স্থান থেকে নামিয়ে এনে, মানুষের আচরণের নতুন global architecture-কে অগ্রাধিকার দেওয়া। (তিন) মানবসভ্যতার ইতিহাসে যা পূর্বে অযাচিত ছিল, সেইরকম উপায়ে পুঁজিবাদের দুর্বৃত্তায়নে ব্যবহার করা হচ্ছে—সম্পদ, জ্ঞান এবং ক্ষমতাকে। (চার) নজরদারিত্বের লক্ষ্যকে সামনে রেখে পুঁজিবাদের কাঠামো নির্মাণ। (পাঁচ) ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে যেমন industrial capitalism প্রাকৃতিক সম্পদের যথেচ্ছ ব্যবহার করে তাকে বিপন্ন করে তুলেছিল, তেমনই একবিংশ শতাব্দীতে surveillance capitalism মানুষের মন ও তার প্রকৃতিকে যথেচ্ছ ব্যবহার করে তাকে বিপন্ন করে তুলবে। (ছয়) বাণিজ্যিক গণতন্ত্রকেও ‘এই যুগ’ বিপন্ন করবে, সেই সঙ্গে মানুষের ওপর ক্ষমতা বিস্তারের নতুন যন্ত্রোপযোগী ক্ষমতার জন্ম হবে। (সাত) সামগ্রিক নিশ্চয়তার আবহে একটা নতুন সামগ্রিক বিন্যাস মানবসমাজের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হবে। (আট) এই যুগে মানবাধিকারের কথা সবচেয়ে বেশি বলা হবে, ওপর থেকে, আসলে মানুষের সার্বভৌমত্বকে হত্যা কোরে।
‘Surveillance capitalism’ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন জ়ুবফ (২০১৮)। এখানে সেই বিস্তারে পৌঁছোনো লক্ষ্য নয়। কিন্তু যুগলক্ষণ মিলিয়ে তাকে চিনিয়ে দেওয়ার কাজটুকু তো করতেই হবে। সকলেই বুঝবেন, (এবং) অনেকেই বিরক্ত হবেন এটা শুনলে যে—Google-কে প্রায় ‘Surveillance capitalism’-এর জনকতুল্য বলা হয়েছে জ়ুবফের কাজে। জ়ুবফ দেখাচ্ছেন : কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তায় ‘reverse engineering’—বলে একটা কথা চালু আছে। কথাটাকে লেন্স হিসেবে ব্যবহার করলে ‘Surveillance capitalism’-এর উৎপাদন ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য খানিকটা বোঝা যাবে। দরকার : data, তাই—mechanism to build data is automatic extraction, প্রক্রিয়া—data analysis through the machine learning—তাই মেকানিজম—‘predictive analytics’ or ‘artificial intelligence’ যা মানবমনের রসকে খুঁচিয়ে তুলতে পারে। জ়ুবফ (২০১৮) বলেছেন—
“These machine intelligence operations convert raw material into the firm’s highly profitable algorithmic products designed to predict the behavior of its users. The inscrutability and exclusivity of these techniques and operations are the moat that surrounds the castle and secures the action within.”
এই হচ্ছে নজরদারিত্বের জায়গা। এখানে ‘means of production’ serves the ‘means of behavioral modification’—আসলে, জ়ুবফের কাজটা এতটাই interesting যে, ওই কাজটা নিয়ে অনেক কথা বলতে ইচ্ছে করে। জরুরি কাজের সময়, মনের সব ইচ্ছেকে গুরুত্ব দিতে নেই।
এবার সরাসরি বসা দরকার—Post-digital যুগে, আমি যখন Online-এ TEXT(s)-এর মুখোমুখি হচ্ছি তখন—আমার TEXT(s)-এর physical coordination নিয়ে, TEXT(s)-এর এপারে ‘আমি’ নামক user, আর অপর পারে ‘তুমি’ নামক producer-এর মধ্যেকার সম্পর্কটা-ই বা কী, TEXT(s)-এর ভাষ্য ভেঙে নতুন ভাষ্য তৈরির প্রক্রিয়ার তালটা (তাল মানে সময়ের টুকরো) কেমন, ভাষ্য তৈরির মেকানিজমটা-ই বা কী—এইসব প্রশ্ন নিয়ে। এখানে রস নিয়ে রবীন্দ্রনাথের একটা যুক্তি প্রণিধানযোগ্য। তবে মনে রাখতে হবে Online TEXT(s), সাহিত্যের বেশ কয়েক কাঠি বাড়া। ওই-যে রবীন্দ্রনাথ বলছেন, পাঠ্যের রস মানুষ একা বহন করতে পারে না, ফলে সে অগণিত প্রাপকের কাছে সেই রস পৌঁছে দেয়। Online-এই তাই এখন “হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয়, মনের সঙ্গে মন, মিলিত হইয়া মানুষ ক্রমাগত স্বকীয়, এমন-কি স্বজাতীয়, স্বাতন্ত্র্যের ঊর্ধ্বে বিপুল বিশ্বমানবে পরিণত হইবার অভিমুখে চলিয়াছে।” এখন বিশ্বমানবের সংজ্ঞা যদি কেউ গোলোকায়নের মধ্যে দাঁড়িয়ে, তার নেটওয়ার্কি কৌশলের বশবর্তী হয়ে দিতে চায়, তাহলে তো হিসেবটা পালটে যাবেই!
এই বিভাগের শুরুতেই বলেছি যে, এই পরিসরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো, use of time এবং multiplicity of expressions কিংবা অনুরণন। Use of time-এর ক্ষেত্রে application হলো— expansion of the concept of ‘present’ (অথবা মেরে-কেটে বলা যায়—Synchronic inclusion of diachrony)। অনুরণন সেদিক দিয়ে self-explaining protocol। এখন তাহলে বলতে হয়, আমার আর টেক্সটের মধ্যে যে বুদ্ধিমান ব্যবস্থা মধ্যস্থতা করছে সেই ব্যবস্থার বাস্তবায়নের মেশিন কখনও ‘আমি’, কখনও আমার সমতুল ‘অপর’। যে আমায় কেবল হাড়ে-হাড়ে নয়, মনে-মনেও চেনে। আগেকার দিনের কথকদের মতো সে কেবল ’বলতে’ পারে না, ’লিখতে’-ও পারে। তবে তার খচরামিটা আরও সাংঘাতিক। সে বেশিরভাগ সময় নিরপেক্ষ কথকের ভূমিকা পালন করে। যেন, আমি আগের মতোই, সোস্যুর, পার্স, বার্ত, পঁটি, লৎমান, একো, প্রমুখের ভাষ্যে তৈরি হওয়া সরঞ্জামগুলো দিয়ে এখনও static text/narrative-এর বহুবাচনিক ভাষ্য তৈরি করতে পারি।
মুশকিলটা ধরতে আমাদের একটু সময় লেগেছে ঠিকই, তবে ওই আমার সমতুল ও আমার সঙ্গে ওতপ্রোত মেকানিক জন্তুগুলোর খচরামি আজকাল অনেকটাই প্রকাশ্যে এসে পড়েছে। কারণ গোলোকায়নের এই নতুন পন্থায় মানবিক আচরণকে এক ধরনের নকল স্বাধীনতা ভোগ করতে দেওয়া হয়, তার পার্সোনাল ইনফরমেশনের বিনিময়ে। আর যেহেতু মানুষ এখনও তার আচরণের কিছু সাবেকি ধারা বজায় রেখে চলে, সেহেতু সে উদ্বিগ্ন হয়, টেক্সটের সঙ্গে সঙ্গে তারও টেনশন বাড়ে। রসের কারবারি মানুষ তো তার বাহ্যিক জ্ঞানের জগতেই বাস করে। তাই একসঙ্গে এক সময়ে অসংখ্য সময়-নিরপেক্ষ multiple meaning generating text on same discourse, user-কে বিভ্রান্ত করে। সে একইসঙ্গে পরস্পরবিরোধী ঘটনাকে সত্যি বলে ভাবে। সেখানে সংকেতায়নের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক (অপেক্ষাকৃত জটিল ও বহুমুখী) প্রক্রিয়ার বাইরে বেরিয়ে এসে রসিক তার সাবেকি অভ্যেসেই টেক্সটকে পড়তে শুরু করে।
কারণ বুদ্ধিমান মেশিন যে online texts, exhibit করে তা আসলে, একরকম transtemporal, online-offline dualism-driven, expression-duplexes (ED)—এখন এই ED-তে থাকতে পারে, পুরোনো-নতুন, ভুয়ো-আধভুয়ো, অর্ধসত্য-পূর্ণসত্য গালগল্প, বিবৃতিমূলক আখ্যান, সুখবর-দুঃসংবাদ, আতঙ্ক-ভয়-উদ্বেগ সৃষ্টিকারী sadist বিবৃতি, emails, reply-emails, comments, tweets, retweet, posts, updates, smses, messages, texts—আরও কত কী, যাকে বলে—multiplicity of ED অথবা দ্বিতলীয় অভিব্যক্তির অনুরণন! ED-র ক্ষেত্রে আমাদের মনে রাখতে হবে যে, Transgression of meaning-কে সামলাতে গেলে দরকার বেশ কিছু নতুন সরঞ্জাম। অথবা আপাতত পুরোনো সরঞ্জামগুলোকে ঘষে মেজে নতুন করে তোলা। তাই নতুন করে ভারতীয় কায়দায় রসের ভাষ্য নিয়ে বসেছি এ যাত্রায়। আগেই বলেছি এই কাজে হাত লাগিয়েছেন বেশ কয়েকজন সহকর্মীও। তাঁদের সকলেরই নিজস্ব কায়দা-কানুন রয়েছে। এখন আমাদেরও সেই কাজে হাত দেবার পালা। দেরি করলে আমাদেরই ক্ষতি। কারণ মানুষের মন নানান রকম expression পড়তে জানে। তার রস উপলব্ধি করতে জানে। বলা বাহুল্য, এই জানা তার খানিকটা আদি, এবং বেশ খানিকটা সাংস্কৃতিক অভ্যেসের ফল। তবে এখনও তার মন ED-কে সম্পূর্ণ পড়তে পারার সক্ষমতা অর্জন করতে পারেনি।
মনের বিবর্তন ঘটেছে অনেকটাই। খোদ শহরে যাদের বয়স, এই ধরা যাক, ১২/১৩, তাদের মধ্যে ED-র এসেনশিয়াল দর্শনে অভ্যস্থ হওয়ার প্রবণতা রয়েছে ঠিকই কিন্তু Post-digital leap-টা সংখ্যাগুরু মানুষের মনের সঙ্গে খাপ খায়নি। অর্থাৎ রসগ্রহণের পুরোনো অভ্যেস দিয়ে পাঠক বা শ্রোতা আজকাল এই Post-digital Online Text পড়ার সম্পূর্ণ কাজ সারতে পারছে না। অথচ, যে ভাবরসের লোভের কথা রবীন্দ্রনাথ তুলেছেন, সেই লোভ তার এখনও ষোলোআনা বজায় আছে। তাই মনের অসুখের প্রকোপ বাড়ছে, আরও বাড়বে। এখন প্রশ্ন হলো, তাহলে কি আমাদেরও নিজেদের মিলিয়ে নেওয়ার জন্য লাফ মেরে এগিয়ে যেতে হবে, না-কি সকলে মিলে ’দাও ফিরে সে অরণ্য’ বলে পেছন পানে ফিরব! কিন্তু চরম ভোগ-সর্বস্ব জীবনে তো মানুষের শরীর এবং মনের যে-দিকগুলো ওই বিষবৃক্ষের ফল, সেই দিকগুলো গিয়ে সম্মিলিত হয়ে বসে আছে ক্ষমতার বৃত্তে এবং ‘Surveillance capitalism’-এর সংজ্ঞার পাঁচ নম্বর যুক্তি অনুযায়ী বাকি মানুষের মনকে কাঁচামালের মতো ব্যবহার করা হচ্ছে—তার হাত থেকে বাঁচবার উপায় কী?
তাছাড়া দেখতে হবে, আমরা Online-এ আবির্ভূত হওয়া ব্যক্তিবিশেষকে কী চোখে দেখি! এবং আগামী দিনে সবচেয়ে জরুরি কাজ হলো—how to read ED texts-এর পন্থা বের করা। বেশ কয়েক দশক ধরেই গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক প্রমুখরা how to read a text—নিয়ে কথা বলে আসছেন। সেক্ষেত্রে Reading-কে তাঁরা রাজনীতি-অর্থনীতি-নিরপেক্ষ প্রক্রিয়া হিসেবে দেখতে নারাজ। সংবাদ মাধ্যম যখন মুদ্রণ মাধ্যমে মানুষের কাছে প্রথম পৌঁছেছিল, তখন তাকে সেই রসেরই দ্বারস্থ হতে হয়েছিল। এদিকে মুদ্রণের তো খরচা আছে, ফলে সংবাদ মাধ্যমকেও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান হিসেবে নিজেকে তৈরি করে নিতে হলো। তাই অবস্থানগত পরিবর্তন ঘটিয়ে, রাষ্ট্র ও বাণিজ্যের প্রকল্পে সামিল হওয়া ছাড়া, তার কাছে আর কোনো রাস্তাই ছিল না।
সাহিত্যকে কখনও মানুষের বাহ্যিক জ্ঞানের কারক হয়ে লৌকিক হতে হয়নি। লৌকিক জগতের মানুষ সাহিত্যের রস উপভোগ করেছে লৌকিক-অলৌকিকের সম্পর্কের ভেতর দিয়ে। ফলে সাহিত্য বাস্তবের থেকে আলাদা জিনিস—সেই নিয়ে পাঠকের মনে বিভ্রান্তি ছিল না। কেবল সে মনে রাখত সাহিত্যে যা ঘটে বাস্তবেও তার সমতুল ঘটনা ঘটতে পারে। এবং সাহিত্যে লেখক-পাঠককে beyond reality যেতে হবে—এই কথা দু-পক্ষই জানত। ফলে সাহিত্যের text-এর পাঠক, প্রাথমিক পর্যায়ে, robust literal meaning খুঁজবে না—সে কথাই তো স্বাভাবিক। কিন্তু সাহিত্যেরও তো নানান পর্যায় আছে, তারও মুদ্রণের সঙ্গে সম্পর্ক আছে। যদিও সে-সম্পর্ক সংবাদ মাধ্যমের সঙ্গে মুদ্রণের সম্পর্কের সমতুল নয়। তবুও সাহিত্য বাস্তবের কোনো ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় তৃতীয় স্বর হিসেবে নিজের robust literal meaning generating protocol-কে প্রতিষ্ঠা করেছে পরের দিকে। ওই একই protocol-এ সংবাদপত্র খবর ছাপিয়েছিল।
২.
আরেকবার মনে করিয়ে দিই। রসের কারবার মানুষের মনকে নিয়ে। মানুষের মনের জিনিস ভাব। এই ভাবকে সহজে চিনতে গেলে ইমোশনগুলোর দিকে তাকাতে হয়। বাস্তবে কারুর দারিদ্র্য দেখলে মনে দুঃখের বা কারুণ্যের ভাব হয়। ওই ভাব হলো রসের মানসিক উপাদান। জ্ঞানের সঙ্গে রসের পার্থক্য হলো, রসের বাহ্যিক উপাদান বাহ্যিক জগত থেকে আসে না। তা ‘আসে কবির সৃষ্ট জগত থেকে’ (দ্রষ্টব্য: গুপ্ত: ১৯৯১: ২৬)। সুতরাং রসের একদিকে কবি, আর অন্যদিকে সহৃদয় পাঠক। রস হচ্ছে দুই বিষয়ীর মধ্যে একটা abstract collaborating device (ACD) যা দুজনের মানসিক বৃত্তকে জুড়ে দেবার কাজ করে। অর্থাৎ আমাদের প্রথমের দিকে বলা কথার মতো যদি রসকে বৃহত্তর যোগাযোগের পরিসরে কাজ করতে দিই তাহলে ACD-র একপাশে থাকবে প্রেরক অন্যপাশে থাকবে প্রেরিত। রস তো বড়ো জায়গায় কাজ করবার সময় কেবল রসিক খোঁজে না, না-রসিক, বেরসিকও খুঁজে নেয়। ED-তে বেরসিকের ভিড়ে ঠাসাঠাসি অবস্থা!
এবার ACD যখন ED-র মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয় তখন দুই বা অসংখ্য বিষয়ীর হাতে ACD-র নিয়ন্ত্রণ থাকে না। সেই নিয়ন্ত্রণ চলে যায় Online-Offline Nexus-এর এলাকার নেতাদের হাতে।
এই বৃহত্তর পরিসরের মধ্যে প্রত্যেক উপাদানই একইসঙ্গে বাস্তবের অন্যান্য পরিসরেও যাতায়াত করে। তবে এই inter-space movement-এর ক্ষেত্রে সেই উপাদানগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি active ব্যক্তিমানুষ ওরফে বিষয়ী অথচ সে নিয়ন্ত্রণহীন। কারণ, বিষয়ী সপ্রাণ, তার উইল, উইশ, ডিজায়ার থাকলেও Online-Offline Nexus-এ তার ক্ষমতা বেঁধে দেওয়া। বিষয়ীর ওই অতকিছু থাকার ওজন এবং Online-Offline Nexus-এর কেন্দ্রীয় টানে একের ওপর আরেক পরিসর এসে মিলেমিশে গিয়ে Hybrid space তৈরি করে। আমরা যখন বাস্তব বলে একটা কিছুর মানচিত্র আঁকি সেটা আসলে ওই Hybrid space-এর বিবরণ ও ব্যাখ্যামূলক এক পরিসর যাকে Meta-real বলা যায়। সেই Meta-real Hyper-real-এ পৌঁছোয়—অনুরণনের মধ্যে দিয়ে। তাই এখনকার ভাষার পরিসরে—mode of production of language implies that the language itself is multiplied by infinite interactions, subject to ED!
তর্কের খাতিরে এই ED linguistic space-কে translingualism বলছি, যেখানে mode of production depends not only on the conventional monetary transaction but also includes other transactions where the object of transaction is invisible, for example, invisible money as EMI operation, use of private information and individual’s time as the transactions. The space of translingualism is elaborated and extended over the communities although there is some remaining, which once was defined as “inner domain” for a separate “reason” by Partha Chatterjee. Thus, the concept of inner domain is not the same as ED domain of the translingual space for the linguistic communities. Therefore, the basic interactional features and the concept of context in Rasa are supplemented by the various functions of Translingualism in ED. As a result, Rasa has majorly lost its internal value system although some inner domains still hold the same as their primacy.
Online-Offline nexus-এ ED-কে বসিয়ে দেখলে লক্ষ করা যায় অজস্র অভিব্যক্তির পৌনপৌণিক ব্যবহার আদর্শ বক্তা-শ্রোতার ওপর ছায়া ফেলে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা লাগানো semi-human interface নিজে বক্তা বা শ্রোতার ভূমিকা নিয়ে নেয়। সেই ভার্সানটাকে আলোর এত কাছে আনে যে, বক্তা-শ্রোতার বাকি ভূমিকার ওপর গ্রহণ লাগে। সেগুলো ছায়ার অন্তরালে চলে যায়। ফলে আমরা যে ভাষাতত্ত্ব করি সেটা ছায়াচ্ছন্ন ভাষাতত্ত্ব।
সেখানে ক্ষমতার বিন্যাস সাংঘাতিক জাগরুক। যে ED-র কথা বলেছি, তার নীচের তলে থাকে ভাষার আদি চেহারা। আর দোতলায় থাকে ভাষার নতুন চেহারা। এই নতুন চেহারা দরকার মতো expression তুলে আনে এক তলা থেকে। কিন্তু তাদের কাউকেই সে নিজের কাজ করতে দেয় না। এদিকে যে user তারও তো ওই domain-গুলোতে যাতায়াত রয়েছে—ফলে সে সেই expression-গুলোকে সঠিকই মনে করে। মনে করে, কই এতে তো কোনো সন্দেহ নেই! এ তো আমার সংস্কৃতির বলয় থেকেই নেওয়া! কিন্তু সে যে privacy এবং time-কে currency হিসেবে নিজের অজান্তেই ব্যবহার করে ফেলেছে, সেটা তার খেয়াল থাকে না। সে একই সঙ্গে translingual space-এ সক্রিয় থাকে আবার inner domain of speaking-এও তার স্মৃতি পড়ে থাকে। ফলে monolingual space-এ তার অবস্থানও ছায়ার অন্তরালে চলে যায়।
সেই জন্য নিগ্রো ফরাসি পতাকা দেখে স্যালুট করছে—এই ঘটনা থেকে মিথের চেহারা যারা ধরতে পারছিল, তারা বর্তমান বিশ্বেও, কালো মানুষের বঞ্চনার ইতিহাসের সঙ্গে, আমাদের দেশের দলিত নিগ্রহের ঘটনার ইতিহাসের মধ্যে থেকে এখনকার কালো মানুষ হত্যার ঘটনার প্রতিবাদ করার component খুঁজে পেল, রসের সূত্র ধরেই। উপরন্তু তাদের আর লিখিত বা ছাপা মিথের অপেক্ষাকৃত জটিল বিন্যাস দেখতে হলো না, তারা সরাসরি খুন দেখল। কেবল বেশিরভাগ প্রতিবাদ হলো, সোশ্যাল মিডিয়ায় সাক্ষরদানের মধ্যে দিয়ে।
Emergence of social networking–explosion of linguistic data and event—এদিকে মস্তিষ্কের ক্ষমতা তো সীমিত। Expression dependability এবং Expression-based allocation of utterance এত বাড়তে থাকল যে, মানুষ, স্বাভাবিক সংকেতনের বা আলংকারিক সংকেতনের হিসেবটাকে ঘেঁটে ফেলল। কারণ—ED allows, rather it instigates always switching from one expression to another expression paradigmatically associated with each other not by virtue of equivalence but by the domination of the mode of production in translingualism or transculturalism where the “online” is another universality measure for the ethnic groups playing in the same ground of translingualism (occupied in the collective human mind). This space exhibits: Lacking of the ideal speaker-hearer nexus, lacking to hold the basic semiosis, Contextlessness, Since it takes expressions from the default paradigmatic field governed by the power, Constraints on the linearity of discourse thus syntactic rules lack temporality, Unspecific interaction between real and virtual, Shadowing the basic assumptions in semiosis, sign has collapsed, Myth is over generated, meaning also is over generated arbitrarily, etc.
কলকাতা-ইছাপুর nexus and beyond
ইছাপুর থেকে কলকাতা যেতে গেলে লোকাল ট্রেনে চেপে যাওয়াটাই হচ্ছে একমাত্র সোজা পথ। বাসে যেতে গেলে অনেকটা ঘুরপথ। শিয়ালদাগামী ট্রেনে যাত্রীরা বেশিরভাগই বাংলায় কথা বলেন। অনেকেরই বাংলা উচ্চারণ শুনে মনে হয়, তাঁরা জন্মসূত্রে বাঙালি নন। কলকাতায় কাজ করেন, এরকম ভিন রাজ্যের ভিন-ভাষার অনেক মানুষ। তারা অনেকেই কাঁকিনাড়া, টিটাগড়, ব্যারাকপুর, খড়দহ, ইত্যাদি জায়গা থেকে কলকাতা, আমার মতোই ডেলি-প্যাসেঞ্জারি করেন। শহরতলিতে থাকলে রোজকার যাতায়াতের হাঙ্গামা থাকে বটে, কিন্তু বাড়ি-ভাড়া বেজায় কম পড়ে। যেতে-আসতে আড্ডা দিতে দিতে বেশ চলেও যাওয়া যায় কলকাতায়। এক-আধ ঘণ্টার পথ। ফলে যাতায়াতের কষ্টটা গায়েও লাগে না। ট্রেনে যাবার সময় তারা কখনও বড়ো বড়ো দলে বিভক্ত হয়ে আড্ডা মারেন। সেখানে মূলত বাংলা ভাষায় কথা হয়। কিন্তু মূল কথার মধ্যেও যখন তারা সহ-ভাষীর সঙ্গে নিজেদের ভাষায় কথা বলে ওঠেন, তখন বিভিন্ন ভাষার এক আশ্চর্য কোলাজ তৈরি হয়। অন্যদিকে সরাসরি কলকাতায় বসবাস করেন অন্তত বিশ-তিরিশ রকম ভাষার মানুষ। বাঙালির সংখ্যা বেশি—এ নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু সব মিলিয়ে কলকাতার মেট্রোপলিটন ভাষিক-চরিত্র বিচিত্র। কিন্তু এর আগে আমি বলেছিলাম, যে কলকাতার বিভিন্ন ভাষার সহ-অবস্থানকে ভাষা-বৈচিত্র্য বা Linguistic diversity বলা যায় না। কেন বলা যায় না তার ব্যাখ্যাও আমি দিয়েছিলাম (দ্রষ্টব্য: মুখোপাধ্যায় ২০২০ক)। কলকাতার বিভিন্ন ভাষা, ধর্ম, সংস্কৃতি, নৃতাত্ত্বিক কৌমের সহাবস্থানকে অপর এক পরিভাষায় বলা হয়—Superdiversity (দ্রষ্টব্য: Vertovec 2007, Blommaert 2013a, 2013b, প্রমুখ)।
কলকাতায় রকমারি ভাষার সহাবস্থানকে যেমন ভাষা-বৈচিত্র্য বলা যায় না, বলতে হয় Superdiversity ধরনের কিছু, তেমনই সেই Superdiversity-কে বহুভাষিক ওরফে Multilingual পরিস্থিতিও বলা যায় না, অতিবিচিত্র ভাষার এই পরিস্থিতিকে আজকাল Translingualism (Kellman 1996, Schwarzer et al 2006, Tung-Chiou 2010, Blommaert 2018b) নামে ডাকা হয়, Translingualism শব্দটা সম্ভবত স্টিভেন কেলম্যানই (১৯৯৬) প্রথম ব্যবহার করেছিলেন। তবে সেই ব্যবহারের হেতু ছিল আলাদা। কেলম্যান বলেছিলেন, একজন লেখক যখন একাধিক ভাষায় সাহিত্য রচনা করেন, যখন নিজের ভাষার একাধিপত্য ছেড়ে, নিজের linguistic identity ছেড়ে বেরিয়ে আসতে পারেন, তখন সেই ঘটনাটা—Translingual, পরে ব্লোমার্ট (২০১৮খ) Online-Offline nexus-এ Translingual পরিসরের ব্যাখ্যা দিলেন অন্যভাবে।
বাস্তব জীবনে Translingualism-এর গুরুত্ব আছে। সেখানে সম্মিলিত অধিবাসের ফলে এক ভাষার লোক আরেক ভাষায় (যে ভাষা dominant) আত্মপ্রকাশ করে। সেখানে ভূমির অধিকারের প্রসঙ্গ থাকে। এখনও তো লোকে গলা উঁচিয়ে বলে, ‘আমরা টোটো’, ‘আমরা কোঁড়া’, ‘আমরা তামাং’, ইত্যাদি। সে যেভাবেই বলুক, বলে তো। কিন্তু কলকাতায় ভূমির অধিকারের প্রশ্ন নড়বড়ে। কলকাতা কাদের বাসভূমি? ’বাঙালির’ বলে দিলেই মিটে গেল না কথাটা। কলকাতার মেট্রোপলিটন মন, সেই ভূমির অধিকার ছাপিয়ে যায়। কলকাতা সকলের। বাঙালি, বিহারি, তেলুগু, মালায়ালি, মারাঠি, পঞ্জাবি, গুজরাটি, চাইনিজ, ব্রিটিশ, অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান, আর্মেনিয়ান, আরও অনেকের। এরা সবাই বাংলা জানেন হয়তো। ঊষা উত্থুপ নিজেকে বাঙালি বলে পরিচয়ও দেন। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এখনও, অনেক ভাষাভাষী, যাদের ভাষার মর্যাদা বাংলার চাইতে রাষ্ট্রীয় পরিসরে কোনো অংশে কম নয় তাঁরা প্রায় সকলেই নিজের নিজের সংস্কৃতি ও ধর্মের নানান রীতি-রেওয়াজ বজায় রেখেই বাঙালি সমাজে অংশগ্রহণ করেন। বরং রাষ্ট্রীয় মর্যাদাবোধে হীনম্মন্য যে-সমস্ত ভাষাভাষী রয়েছেন, তাদের অনেকেই আজ বাঙালির মতো জীবনযাপন করছেন, যদিও নিজেদের ঘরে তারা নিজের ভাষায় কথা বলেন এবং (অনেক সময় ঘরেও তারা বাংলা ভাষাতেই কথা বলেন ফলে) তাদের নতুন প্রজন্ম নিজেদের ভাষা অনেক ক্ষেত্রে শিখছে না, কারণ তারা সমাজের মূল স্রোতেই থাকতে চান। এমতাবস্থায় Diaspora-ও ভেঙে যায়। আবার অন্যান্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে সেটা টিকেও থাকে।
ইছাপুর তো বটেই, এমনকি বীরভূম, পশ্চিম মেদিনীপুরের গ্রামে গিয়েও দেখেছি, সেখানে নতুন প্রজন্ম বাংলাতেই কথা বলে। কখনো-কখনো কোনো শব্দের আদিম জ্ঞান হয়তো বাংলার পেটে ঢুকিয়ে দেয় আঞ্চলিক communication-এর তাগিদে। আমি নিজে কোনো এক আদিবাসী ’মা’-কে কিঞ্চিৎ প্রশ্রয়ের সুরে, মৃদু হেসে বলতে শুনেছি, ’জানেন আমার মেয়ে এসে চুপি চুপি আমায় এসে জিগেস করবে, মা, এই কথার (ওর নিজের ভাষার শব্দ) মানে কী, ওই কথার মানে কী?’ স্যামুয়েল বেখেটের একাধিক ভাষায় সাহিত্য রচনার সঙ্গে এই বদলে যাওয়ার তফাত আছে নিশ্চয়ই। আর এই নতুন প্রজন্মের রাষ্ট্রীয় ভাষায় অংশগ্রহণ করার ঘটনার অন্য ব্যাখ্যা আছে। তাই নিয়ে বিস্তর আলোচনাও আছে। তাই এখানেই ও-প্রসঙ্গের ইতি টানছি। সঙ্গে এও বলে রাখছি—ওই বদলে যাওয়া পরিসর Translingual space নয়। আবার ওই পরিসরেরও বটে, কারণ ওই পরিসরেই তো একটা নতুন কথা চালু হয়েছে—supervernacularization (Blommaert 2012)। ‘Supervernaculars and their dialects’ প্রবন্ধের শুরুতেই, ব্লোমার্ট, Supervernacular বলতে কী বুঝিয়েছেন, সেটা দেখা যাক : Supervernacular-কে দেখা হচ্ছে—
“…as a descriptor for new forms of semiotic codes emerging in the context of technology-driven globalization processes. Supervernaculars are widespread codes used in communities that do not correspond to ‘traditional’ sociolinguistic speech communities, but are deterritorialized and transidiomatic communities that, nonetheless, appear to create a solid and normative sociolinguistic system.”
সুতরাং, মোবাইল ফোন, ইন্টারনেট-মারফত যে জগতে আমরা অংশগ্রহণ করি সেটা আমার hypo-language-কে supervernacular-এ পরিণত করে। একজন রাজবংশী-ভাষা ব্যবহারকারী সে ওই Translingual game-এ অংশগ্রহণ করে নিজের ভাষাকে Supervernacular করে তুলবে। কিন্তু সেই সঙ্গে translingual খেলার নিয়ম শিখে তার মনটাকে জুড়ে দেবে সেই ’মানসভূমি’-র সঙ্গে, যার অধিপতি অদৃশ্য। কিন্তু অধিপতির উপনিবেশ গোলকজোড়া ’মানসভূমি’।
খেয়াল করলেই দেখা যাবে, আমরা যখন মোবাইল ফোনে মেসেজ লিখি তখন আমরা কী ভাষায় লিখি? আত্মসচেতন, আত্মগর্বী, অতি-সাবধানি এবং কলকাতা-ঢাকার নেক্সাসে মুদ্রণ-পুঁজিতে অংশগ্রহণকারী কিছু বাঙালি, যারা কম্পিউটারে-মোবাইলে ‘বাংলা’ হরফে, পশ্চিমবঙ্গীয় সিপিএম-কর্তৃক ‘অনুমোদিত’ বানানবিধি মেনে বাংলা লেখেন, তাদের বাদ দিয়ে—অনলাইন-অফলাইন নেক্সাসে মোটামুটি সক্রিয় বাঙালি—যে ভাষায় কথা ‘লেখেন/বলেন’ সেটা বরং Translingualism-এর দৃষ্টান্ত।
সাবধানি বাঙালির দুটো রূপ। একটা প্রযুক্তি-নির্ভর স্ববিরোধী রূপ আরেকটা প্রযুক্তি-নির্ভর সাধারণ রূপ। স্ববিরোধী রূপের যে পরিচয় ওপরে দিয়েছি সেটা তো প্রথম প্রকার। দ্বিতীয় প্রকার বাঙালি কম্পিউটারে-মোবাইলে ইংরিজিতেই লেখেন সরাসরি। কিন্তু ওপরের উদাহরণগুলো ‘সাবধানি’ বাঙালির সৃষ্টি নয়। ওগুলো, যারা translingual space-কে শিরোধার্য করে নিয়েছেন, ভবিতব্যের মতো, তাদের। যেখানে ’আমার সোনার বাংলা’-র নতুন signifier ‘AmarSonarBangla’ এবং ‘#’ এক বিশেষ সংকেত—যার মানে ওই সংকেতকের আধারটাকে iconic করে তোলে—যেখানে ওই signifier-এর—conceptual boundary-র মধ্যে ঢুকতে কারুর (কোনো) বাধা নেই। (এবং) অন্যান্য ডিসকোর্সও অবলীলায় ঢুকে পড়তে পারে কেবল #AmarSonarBangla-এর মধ্যে দিয়ে। আরও জিনিস আছে খেয়াল করবার মতো—(গ)-এ ‘remembering’-এর equivalent ‘Rem’bering’, (ক) এবং (খ)-এ একই প্রতিমা—‘#আমারসোনারবাংলাআমিতোমায়ভালোবাসি’-র ভেতরে দু-রকম ডিসকোর্স। গোলকায়নে ভাষার একধরনের নতুন associativeness তৈরি হয়েছে। (আর) তাই নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হওয়া দরকার।
Online-এ বুদ্ধিমান ব্যবস্থার মধ্যস্থতার ফলে মানবমনের চরিত্র বদলে যেতে শুরু করেছে। সেখানে cognitive entity-গুলোকে one-to-one marking-এ রাখে বুদ্ধিমান ব্যবস্থা। একদিকে multiplicity of event (ও) কর্মকাণ্ডের পরিমাণগত বৃদ্ধি, অন্যদিকে—physical cognitive isolation, (যদিও) Online Isolation-এ কেউ নিঃসঙ্গ নয়। কারণ, আমি থাকা মানে যেমন আমার ছায়ারও থাকা, তেমনই Online-এ প্রত্যেক ‘আমি’র চিরসখা বুদ্ধিমান ব্যবস্থা। এটা গদ্যের কোনো আলংকারিক ব্যবহার নয়। সোজা কথা, আক্ষরিক কথা। অর্থাৎ মুদ্রণের কালে, বুদ্ধিমান ব্যবস্থার মডেলে গণমাধ্যমের এপারে ছিল জনতা পাঠক আর ওপারে কর্তা বা বিষয়ী সংবাদদাতা। এখন ‘ওপার’ আর দেখা যায় না। বুদ্ধিমান ব্যবস্থার মডেলে dynamic interface হিসেবে যে-কোনো আকারে উপস্থিত থাকে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা।
ধরা যাক স্মার্টফোন তার একটা আকার। ওপারের সংবাদদাতারা এখন আড়ালে, বুদ্ধিমান ব্যবস্থা এখন নিজেই বিষয়ীর ভূমিকায় নামে। আমার মনের সবচেয়ে যা গোপন কথা—তা একমাত্র আমার মোবাইল ফোনই তো জানে। কত হাজার পাসওয়ার্ড তাকে জানিয়েছি, তার হিসেব নেই। পাসওয়ার্ড কি মনের সেই গোপন কথা? না, তা বলিনি। তবে, পাসওয়ার্ডও গোপন কথা। এমন গোপন কথা যা, আমার সহজীবীদের থেকে, আমার সবচেয়ে প্রিয় মানুষের থেকে, আমাকে বিচ্ছিন্ন করে cognitive isolation-এ রাখে। বুদ্ধিমান ব্যবস্থা আমার cognitive trend জানে। আপনিও পরীক্ষা করে দেখতে পারেন। কোনো বন্ধুকে বলুন না, আপনাকে তার যাবতীয় পাসওয়ার্ড বলতে। বলার পরে (না-হয়) তিনি আবার নিজের মতো করে পালটে নিন। কিন্তু এ-যাবৎ তিনি যা-যা পাসওয়ার্ড দিয়েছেন— তার একটা বিগ্রহী তালিকা গঠন করলে, আপনিও বুঝে নিতে পারবেন, আপনার ওই বন্ধুর cognitive trend-টা কী ও কেমন! পাসওয়ার্ডে কেউ হয়তো সংখ্যা বা অন্যান্য গাণিতিক সংকেত ব্যবহার করেন। কেউ হয়তো নিজের nick name বা নিজের পোষ্যের নাম ব্যবহার করেন। আবার পাসওয়ার্ড কতটা সাংকেতিক হবে, সেই বিষয়ে তো নানান Online রেজিস্ট্রেশনের সময় নির্দেশিকাই আসে। সেখানে বলা থাকে, অন্তত একটা upper case থাকতে হবে, numeric থাকতে হবে, symbol অর্থাৎ, @ বা #—এই ধরনের চিহ্ন থাকতে হবে।
এই নির্দেশিকা দেখেই তো বোঝা যায়, Online-এর ওপার থেকে কেউ বা কারা আপনার cognitive trend জানার চেষ্টাই শুধু করছে না, cognitive trend-এর একটা ছক বানাতে চাইছে। আপনাকে আপনার ইচ্ছেমতো পাসওয়ার্ড বানাতে দিয়ে সে দেখেছিল, ওই #plurality সে সামলাতে পারছে না। অন্যদিকে মানুষের আটপৌরে কথোপকথনে যে নিবেদনের গুরুত্ব ছিল, তাকে কেবল বিবৃতি এবং নির্দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হলো। ফলে পারলোকিউশন বা প্রালব্ধির জায়গাকে বুদ্ধিমান ব্যবস্থা ক্ষমতার কাজে লাগাল ওই দুই মেজাজের ভিত্তিতে (প্রালব্ধির ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে পড়তে হবে ’নাটক ও ভাষাতত্ত্ব’)।
ফিরে দেখা
আমাদের ছোটোবেলায় জীবনবিজ্ঞানের ক্লাসে জার্মান পণ্ডিত আর্নস্ট হ্যাকেলের (Ernst Haeckel) বিখ্যাত উক্তি ‘ontogeny recapitulates phylogeny’ প্রবচনের মতো বলা হতো। এই কথার মানে হচ্ছে, কোনো #organism-এর জৈবিক গঠন ও বিকাশ সেই #organism-এর বিবর্তনের ইতিহাসের সমান্তরাল এবং তার সংক্ষিপ্তসার। বলা বাহুল্য, বিজ্ঞানের ইতিহাসে হ্যাকেলের এই উক্তি ধোপে টেকেনি। কিন্তু এই কথার খেই থেকে গেছে আমাদের বিভিন্ন ভাবনায়। বিভিন্ন #organism-এর বিবর্তনের #diachronic বা archaeological clue খুঁজে পাওয়া না গেলে এখনও (কিন্তু) তার নিজস্ব বিকাশের স্তরগুলোর দিকে তাকানো ছাড়া কোনো উপায় থাকে না। আমি নিজেও ওই উক্তির আক্ষরিক বক্তব্য বিশ্বাস করি না, কিন্তু ওই প্রবচনের যে একটা semiological effect মনের মধ্যে থেকেই গেছে, সে-কথাও অস্বীকার করতে পারি না। বিশেষ করে কোনো জৈবিক অস্তিত্বের বিবর্তনের সর্বজনস্বীকৃত প্রমাণ হাতে না পেলে মনের মধ্যে ওই প্রবচনের সামগ্রিক তাৎপর্য মনের মধ্যে আনাগোনা করতে থাকে। যেমন, মানুষের বিবর্তনে টিকে থাকা একমাত্র প্রজাতি হোমো স্যাপিয়েন্স এবং সেই প্রজাতির বর্তমান চেহারার অজস্র বৈচিত্র্য ও তাদের মধ্যে একইভাবে ’ভাষা’ ব্যবহারের উদ্ভব, বৈচিত্র্য এবং সেই ভাষার ক্রমশ জটিলতর হোয়ে ওঠার বৃত্তান্তের ক্ষেত্রে (বলা বাহুল্য) এখনও (অবধি) archaeological clue-র যথেষ্ট অভাব রয়েছে। মানুষের ও মানুষের ভাষার আজকের বৈচিত্র্য, বিবর্তনের কোনো (এক) সময়ে (archaeologically) মানুষের বিভিন্ন প্রজাতির interbreeding-এর ফলস্বরূপ admixture-এর ভবিতব্য কিনা সে-কথাও আমরা পুরোপুরি জানি না (এ বিষয়ে, একাধিক মত এবং আলোচনার জন্য পাঠক চোখ রাখতে পারেন—Renfrew 1994; Hauser, Chomsky and Fitch 2002; Fitch et al 2005; Ackermann et al 2016; Castro et al 2004; Everett 2016; 2017; Berwick and Chomsky 2016)।
এই রচনার মূল উদ্দেশ্য মানুষের ভাষার বিবর্তন ও তার প্রকৃতিগত বৈচিত্র্য বিষয়ে প্রত্নতাত্ত্বিক অনুমান বা বিতর্কে অংশগ্রহণ (মুখোপাধ্যায় ২০১৮; ২০২০) করা নয়। মানুষের ভাষার বিশিষ্ট বিশ্বজনীনতা তার ভাষার রিকার্সিভ চরিত্রের মধ্যে নয় বরং সংকেত ব্যবহারের মধ্যেই রয়েছে সেই বিশিষ্টতার চাবি—এই মতের পক্ষে সওয়াল করার মধ্যে ভাষার বর্তমানের চেহারা ও ব্যবহারের ভাষ্য তৈরির ক্ষেত্রে এক বিশেষ পক্ষপাত থাকে ঠিকই, কিন্তু এই রচনায় সেই সওয়াল প্রত্যক্ষভাবে জরুরি নয়, পরোক্ষভাবে দরকারি। এখানে কথা বলছি, মানুষের ভাষা ব্যবহারের পরিসর নিয়ে। যে পরিসরে ব্যবহৃত ভাষার দৃষ্টান্তের ভিত্তিতেই ’আদর্শ দৃষ্টান্ত’ তৈরি করে নিতে হয় আকরবাদী (formalist) ভাষাবিজ্ঞানীদের। কেন এই প্রকল্পে হাত দিতে হলো—সে বিষয়ে (বলতে হলে) বেশ খানিকটা বাক্যব্যয় করা দরকার। এক-কথায় সে প্রশ্নের জের টানতে গেলে, বলে নিতে হয়, ভাষার পরিসরকে এতটা উদাসীন, নির্লিপ্ত, নিষ্ক্রিয়, নিপাট ও নৈর্ব্যক্তিক ভাবার সময় ফুরিয়েছে। যে পরিসরটাকে ভাষার নিরপেক্ষ খেলা করার জায়গা ভাবা হচ্ছিল—সেই পরিসরটাকে চিহ্নিত না করতে পারলে, ফরমুলা মুখস্থ করার মতো তামাদি হয়ে যাওয়া ফোনোলজি-মরফোলজি-সিনট্যাক্স-সেম্যানটিক্স আউড়ে যেতে হবে, সেইসব ফরমুলা কোথায় কাজ করে, কেন দরকারি বা আদৌ দরকারি কিনা—সে বিষয়ে পরের প্রজন্মের সন্দেহ কাটবে না। এদিকে হাতে সময় কম, তাই দেরি না-করে পরের প্রজন্মকে বিষয়-আশয় বুঝিয়ে দেওয়ার কাজে হাত দিতে হবে।
সোস্যুর এবং পার্স যখন ভাষাকে সংকেত তন্ত্র হিসেবে বিবেচনা করে সংকেতের যথাক্রমে দ্বিমাত্রিক ও ত্রিমাত্রিক ভাষ্য দিচ্ছেন তখন মানুষ ঊনবিংশ থেকে বিংশ শতকে পা দিচ্ছে। মুদ্রণ প্রযুক্তি তার সম্পূর্ণ শক্তি কায়েম করেছে মানুষের ওপর। এঁদের গুরু মেনে তৈরি হচ্ছে ব্যাকরণ ও সংকেত তত্ত্বের নানান ভাষ্য। এই সমস্ত ভাষ্যগুলোর মধ্যে, যেমন ধরা যাক, বিশেষ করে সোস্যুর কথিত ভাষ্যের উত্তরসূরী ভাষ্যগুলোর মধ্যে একটা contradiction ছিল, সেটা হয়তো অনেকেই খেয়াল করে থাকবেন। সেটা হলো, সোস্যুরের ভাষ্য থেকে একই সঙ্গে গ্রন্থনবাদী সংকেত তত্ত্ব এবং আকরণিক ব্যাকরণের দিকে যাত্রা। সোস্যুরের কাজের পরবর্তী চর্চার ধারায় ইউরোপ-আমেরিকা মিলিয়ে এই নিয়ে একটা পরস্পর বিরোধিতা ছিল।
একদিকে ভাষাকে দেখতে বলা হচ্ছিল beyond the basic communication system এবং culture-driven paradigmatic association—হিসেবে এবং অন্যদিকে বলা হচ্ছিল—universally structured society-driven formal system বা syntagmatic set of rules হিসেবে। ওই দ্বিতীয় ধারাটা গেল আকরণিক ব্যাকরণের দিকে। ভাবা হলো, ভাষার গঠন যে syntagmatic set of rules দিয়ে তৈরি সেই set of rules সম্পর্কে জানতে পারলে মানবসত্তার বিশ্বজনীন চরিত্রকেও বোঝা যাবে। কারণ ভাষাই মানুষের পূর্ণাঙ্গ ও অন্তরঙ্গ আত্মপ্রকাশের জায়গা। ওই যে বলেছিলাম, স্থাবর সম্পত্তির অধিকার, জমির অধিকার, এমনকি মানুষকে বন্দি করে তার দেহের ওপর অধিকার—অর্থাৎ যা-কিছু ধরাছোঁয়া যায় এমন সমস্ত কিছুকে মানুষ বিংশ শতকের আগেই জেনে ফেলেছে। বিংশ শতকে তৈরি হচ্ছে স্পর্শযোগ্য বস্তুর নানান জটিল আইনকানুন। এবং ক্ষমতার জোরে, আইনের জোরে জোর কদমে চলছে colonization, আর একই সঙ্গে অন্যদিকে চলছে যা স্পর্শযোগ্য নয়, মানুষের মন, সময়, আলো, ইত্যাদিকে গণিতের সাহায্যে ব্যাখ্যার চেষ্টা। কারণ তখন, Colonial Power বুঝে গেছে আমায়, ওই অসীমকেও বাঁধতে হবে সীমার মাঝে। নইলে, colonization সম্পূর্ণ হবে না। কারণ মানুষকে আটকে রেখে, তার ওপর নির্মম অত্যাচার চালিয়েও যে তাকে বশ করা যায়নি—তার প্রমাণ তো ইতিহাসে অজস্র রয়েছে। ভাষার সেই গাণিতিক ব্যাখ্যাই ভাষাতত্ত্বে প্রাধান্য পেল। আমাদেরও আধুনিক ভাষাতত্ত্বের কোর্স তৈরি হলো সেদিকে হেলেই। কেবল বুড়ি ছোঁয়ার মতো ছুঁয়ে রাখা হলো—সোস্যুর, ইয়াকবস্ন, প্রমুখদের। (তবে) আমরা এখনকার আলোচনায় সেই গণিতের দিকটাকে টেনে আনছি না, বরং তাকাচ্ছি (সেই দিকে) যেখানে ভাষা—beyond the basic communication system!
বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি ভাষা দিয়ে যে কাব্য তৈরি করা যায় সেটা চোখে আঙুল দিয়ে দেখানোর শুরু হয়েছে এই বলে যে, ভাষার একটা গুণ হচ্ছে কাব্যগুণ। সে গুণ বিশেষ কিছু নয়। আটপৌরে ভাষাতেই সেই গুণ থাকে। থাকে বলেই, আটপৌরে ভাষার মাল ব্যবহার করে কাব্য বানানো যায়, বার্তা দেওয়া যায়, আবেগ-অনুভূতি প্রকাশ করা যায়, নির্দেশনা দেওয়া যায়, আভিধাধিক অর্থ প্রকাশ করা যায়, ইত্যাদি। সুতরাং আটপৌরে ভাষার গুণাবলির মধ্যেই এমন কিছু থাকে যা দিয়ে নানা রকম হাইপো-ভাষা বানানো যায়। এদিকে বিশ্বে তখন উপনিবেশবাদের পরিণত অবস্থা, মুদ্রণ-পুঁজিবাদের মধ্যে দিয়ে সেই সময়ে ভাষার নানান বৃত্তিকে কাজে লাগান হচ্ছে, উপনিবেশ ও বাণিজ্যের স্বার্থে। শিক্ষিত মানুষের জীবনে মুদ্রিত সংবাদ-মাধ্যম প্রভাব ফেলছে। মানুষ দেখতে পাচ্ছে, ভাষা দিয়ে ‘জনমত’ তৈরি করা যায়। বিজ্ঞাপন দিয়ে মানুষকে কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যর প্রতি আকৃষ্ট করা যায়।
Syntax
“So syntax is a language, and we study it so that we can live in a bigger noetic universe. Not for any utilitarian purpose. We study it as we study the fugue, because if we do not know what is going on in a crab fugue (the one that has one Satz that goes backwards from the way another one goes) we will not be able to hear it, we will miss the beauty.”
রবার্ট রসের[৫] এই কথার মধ্যে একটা ফ্রাস্ট্রেশন আছে। বিশেষত, তিনি এই কথাগুলো বলার আগেই বলেছেন, “But for some reason this (obvious to me) truth had never sunk into my heart of linguistic hearts–in the depths of the syntactic Big Woods.” তিনি নিজেও হয়তো বুঝতে পারেন, এখনকার যুগে ‘utilitarian purpose’ কথাটারই কোনো একক মানে নেই। ‘utility?’— কার, আমি বক্তা/শ্রোতা, ইন্টারনেটের মাধ্যমে আমার ই-জগতে আমি কথা বলি, যেখানে আমি কাউকে বাস্তবে চিনি, কাউকে অপার্থিব বাস্তবের বাইরে চিনি না, সেখানে আমার কথা বলার ইউটিলিটি একরকম নয়। আর আমাদের কথা বলাচ্ছে যারা, আমাদের ব্যক্তিগত, সামাজিক, রাজনৈতিক ’কথা’ যাদের কাছে কাঁচা মাল, তাদের কাছে ইউটিলিটি অন্যরকম। ‘syntax is a language’—সেই ভাষা এখন ছায়াচ্ছন্ন।
শুধু এইটুকু বলে দিলেও মিটে যায় না। সেই ভাষা ও ছায়াভাষা মিলিয়ে যে ED পরিসর তৈরি করে, সেখানে অভিব্যক্তির তাৎপর্যের চাবিকাঠি থাকে ব্যবহারকারীর প্রতিগ্রহী সম্পর্কের চয়ন থেকে। সব সম্পর্ক সমান নয়। প্রতিগ্রহী সম্পর্কের ভেতরেও উচ্চনীচ ভেদ আছে। Dominant relationship ওপরে থাকবেই। যদি ধরে নিই, মানুষের আটপৌরে ভাষাই ’ছায়াচ্ছন্ন’ তাহলে, মনে রাখতে হবে যে ভাষা প্রতিগ্রহের উপরিতলে তার ক্ষমতা কায়েম করছে—সে কিন্তু ওই ছায়াচ্ছন্ন স্বাভাবিক ভাষাকে বাঁচিয়ে রাখে নিজের স্বার্থে। কারণ তাকে ভাষার ওই আটপৌরে এলাকা থেকেই অভিব্যক্তির বিভিন্ন একক, উপাদান ধার করে আনতে হয়। ED-র উপরিতলের ভাষা বেঁচে থাকতেই পারবে না যদি সে ছায়াচ্ছন্ন আটপৌরে ভাষার পরিসরকে বাঁচিয়ে না রাখে।
অথচ, তার নিজের চরিত্র সে কবেই পালটে ফেলেছে। যেহেতু তার লক্ষ্য, বিশ্বের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ এবং তাদের খুব সহজে পাওয়া যায় তাদের ভাষায়—সেহেতু, সেই বিপুল জনগণের ভাষা-গরিমার ভাবাদর্শের মন্দির বানিয়ে দিয়ে, মন্দিরের বাইরে পুরোনো খেলার কিছু নিয়ম বজায় রেখে আর কিছু নতুন নিয়মের synthesis ঘটিয়ে, প্রধান ভাষার প্রত্যেকের ক্ষেত্রে এক-একটা নতুন চরিত্রের পিজিন তৈরি করছে। যার নাম দেওয়া হয়েছে—translingualism, যদি খুব ভুল না করি, তাহলে ED পরিসরে এই খেলা তৈরির মানে হচ্ছে ওই কতিপয় local translingualism-গুলোকে, GLOBAL-Tanslingualism-এ integrate করা। মানবাধিকারের প্রশ্নে Archive তো আছেই। সেই Archive-এ আমি-আমরা, তুমি-তোমরা, আপনি-আপনারা, সে-তারা, তিনি-তাঁরা—সকলেই ঠাঁই পাবেন।
ম্যালাই ও ব্লোমার্ট (২০১৯) দেখিয়েছেন, আমরা এই সময়ে দাঁড়িয়ে, প্রতিবেশীর সামাজিক সক্রিয়তার অনলাইন-অফলাইন সংগঠিত পরিসরে নিজেদের ও নিজেদের নৃ-পরিচয়কে নিয়ে যেতে পেরেছি। ওই পরিসরে, superdiverse প্রতিবেশীর মধ্যে আমি আমার local বাঙালিয়ানাকে খুঁজে পাই। যখন superdiversity-কে আমরা interactivity-র global চেহারা বোঝবার জন্য লেন্সের মতো ব্যবহার করি, আমরা অনেক বেশি কিছু দেখতে পাই। এই অনেক বেশি কিছুর মধ্যে মানের পরিবর্তিত হতে থাকা দিগন্তও থাকে। ডিজিটাল মাধ্যম এই interactivity-র ভেতরে উপস্থিত থেকে মানুষের সামাজিক ভূমিকার প্রকৃতিকে পরিবর্তন ঘটায় কারণ সে মানে পরিবর্তন প্রক্রিয়ার ভেতরে বসে কাজ করে। আমরা এই পরিসরটাকেই ED বলেছি, যেখানে local translingualism-গুলোকে, GLOBAL-Tanslingualism integrate করার নিরন্তর কাজ চলে। প্রিন্ট মিডিয়াতেও Subjects of Interaction বা Channels of Interaction-এর এত পরস্পরবিরোধী multiplication ছিল না। প্রিন্টের এপারে বক্তা, লেখক, সম্পাদক, প্রকাশক, সাংবাদিক, বিজ্ঞাপনদাতা সংস্থা, প্রতিবাদী মানুষ—যিনিই থাকুন না কেন তার কাজের জায়গা ছিল কম ডাইনামিক। লেখবার/বলবার নিয়ম মানুষের কথোপকথনের আটপৌরে পরিসরের চাইতে জটিল হলেও, সেই কম ডাইনামিক জায়গায় তার সূত্রগুলো মোটামুটি বোঝা যেত। কিন্তু এখন মাধ্যমের ভূমিকা অন্যরকম।
’কে/কারা বলছে’ আর ’কাকে/কাদের বলছে’—এই প্রশ্ন দুটোর কোনো সোজা উত্তর (কিন্তু) নেই অনলাইন ডিজিটাল মাধ্যমে। সবচেয়ে মজার কথা হলো, যুগ যত এগোয়, means of production বাড়তে থাকে। কোনো কিছুকেই এই নতুন পুঁজিবাদ (surveillance capitalism) ফেলে দিচ্ছে না। সে পুরোনো পাঁচ-দিনের টেস্ট ক্রিকেটও রাখছে, অপেক্ষাকৃত দ্রুতগতিসম্পন্ন একদিনের ৫০ ওভারের ক্রিকেটও রাখছে, আবার টি-টোয়েন্টির সুপারফাস্ট ২০ ওভারের খেলাও রাখছে। প্রত্যেকটা খেলাই আগের চেয়ে নিয়ম বদলেছে। কিন্তু তারা একসঙ্গে exist করছে। ভাষার খেলাতেও তাই। সবই আছে একসঙ্গে। অর্থহীন প্রবাদ, প্রবচন, আটপৌরে গালিগালাজ, ঠোনা মারা, আদেশ, অনুজ্ঞা, রিকোয়েস্ট, বিবৃতি, বর্ণনা, প্রশ্ন—অর্থাৎ বলা, লেখা, সাহিত্য, চিঠি, অ্যাপ্লিকেশন, সব রয়েছে।
তার সঙ্গে তৈরি হয়েছে নতুন নতুন, খেলার ধরন—offline typing, emailing, messaging, texting, blogging, vlogging, chatting, trolling, posting, video conferencing, viral, আরও কত কী! এই এতরকম চ্যানেলে ব্যক্তিমানুষের অনলাইন-অফলাইন আইডেন্টিটির চেহারা বদলে গেছে। কারুর নাম, thecrazybull, কারুর নাম misscrazybong, অথবা peak_of.love, কিংবা aroyfloyd, এইরকম আরও কতরকম! এই নামগুলো সংকেত তত্ত্বের কর্মকাণ্ডের বাইরে নয়। ধরে ধরে দেখলে, সমস্ত কিছু ব্যখ্যা করবার ক্ষমতা আছে ওই বিদ্যার হাতে। কিন্তু, নানারকম চ্যানেল দিয়ে এসে অভিব্যক্তি যে ED-তে জমা হচ্ছে—সেদিকে নজর রেখেই এখন সংকেত তত্ত্বের কাজে হাত দেওয়া দরকার। কারণ এত প্রতিমা ওরফে আইকনের ব্যবহার, কয়েক দশক আগের অভিব্যক্তিতেও ছিল না। এখন বক্তা-শ্রোতা বা লেখক-পাঠকের আদিম নেক্সাসে মধ্যস্থতা করছে এমন এক মাধ্যম যেটা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার জোরে একইসঙ্গে বক্তা, শ্রোতা, লেখক, পাঠক, দ্রষ্টা, স্রষ্টা—সমস্ত রকম মানবিক ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। ফলে, বক্তা-শ্রোতা বা লেখক-পাঠকের আদিম নেক্সাসের চরিত্র তো বদলাবেই। এখনকার ভাষার ভাষ্যকারদের সেদিকটায় তো নজর রাখতেই হবে।
সুতরাং, রবার্ট রসের সতর্কতা—‘we will miss the beauty’ (কে), পালটে বলতে হয়—we are already missing the beauty। একটু ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে কাজ করছেন ব্লোমার্ট। তিনি কেবল তাকাচ্ছেন, ওই superdiverse, translingual space-এর দিকে। তাঁর কাজে ‘what is to be done’-এর আংশিক কথা বলা আছে। ম্যালাই ও ব্লোমার্ট (২০১৯)-এর কাজে রয়েছে—
“People’s interaction with interfaces (and algorithms) potentially script their online and offline practices–taking pictures from barista coffees, gourmet hamburgers or fancy cocktails–before drinking and eating so that ‘good life pictures’ can be posted as ‘stories’ and posts on Facebook, Instagram or Snapchat using hashtags, and tagging friends and infrastructures and liking posts and reviews. All those practices in the offline/online nexus together create meaning.”
অর্থাৎ তাঁদের কাজে—নিরপেক্ষতা রয়েছে। আমার ক্ষেত্রে যেটার অভাব সবচেয়ে বেশি। আমি সক্রিয় কণ্ঠে বলছি, সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং-কে ওভার পাওয়ার করুন। কম্পিউটার আপনার ভৃত্য হোক, প্রভু নয়। ঠিক যেমন প্রিন্ট মিডিয়াকেও আমরা কাজে লাগিয়েছিলাম। প্রিন্ট মিডিয়া কেবল মাত্র প্রিন্ট-ক্যাপিটালিজমের অস্ত্র হয়ে থাকেনি। যারা পুঁজিবিরোধী শ্রেণিহীন সমাজের, সমবায়ের, শান্তির, যৌথখামারের স্বপ্নে বিভোর হয়েছিলেন, এমনকি যারা ’দাও ফিরে সে অরণ্য’-এর ভঙ্গিতে প্রকৃতিচেতনার কথা বলতেন তারাও ’কাগজ তৈরি করতে গেলে গাছ কাটতে হয়’-এর মতো বিশ্বাসকে এক ফুঁয়ে উড়িয়ে না দিয়েই প্রিন্ট মাধ্যমকে কথা বলবার জায়গা করেছিলেন। ফলে আমাদের বর্তমান প্রস্থানেও তেমনই, ভাষ্য তৈরির, সমালোচনার, কঠোর অভিজ্ঞার কাজ করে যেতে হবে, মিডিয়ার অনলাইন-অফলাইন চরিত্রে ভাষা ED-র পরিসরকে মাথায় রেখে।
ব্লোমার্টদের মতো কেবল বলে দিলেই চলবে না যে, linguistic landscape-কে সবচেয়ে ভালো বোঝা যাবে—‘(online/offline) network of texts, mediated practices, artifacts, experiences and semiotics’-এর পার্ট হিসেবে ভাবলে। তাঁদের ভাবনার গুরুত্ব আছে। সেটা এই যে, ED-নামক জায়গাটায় কী ঘটছে সেটা কেবলমাত্র পুরোনো ভাষাতত্ত্ব বা সংকেত তত্ত্ব দিয়ে জানা যাবে না। দ্বিতীয়ত, মানুষের আটপৌরে ভাষার পরিসর এখন ছায়াচ্ছন্ন। ফলে সেই আটপৌরে ভাষাকে সামনে রেখে যে ভাষাতত্ত্ব সে-ও ছায়াচ্ছন্ন ভাষাতত্ত্ব। কিন্তু ওখানে (যদিও) একটা মুশকিল আছে, ওই যে surveillance capitalism কোনো কিছুকে বাদ দেয় না বলেছি, সে-কথা ঠিক। শুধু বাদ দেয় না-ই নয়, সে নিজের ওই ED-র পরিসরে এনে সমস্ত কিছুকে নতুন করে codify করে। কিন্তু প্রথমত; মানবমনের অজানা অনেক রহস্যের সমাধানসূত্র তার হাতে এখনও আসেনি, দ্বিতীয়ত; অনুন্নত অর্থনৈতিক দেশগুলোতে এখনও অনেকখানি cognitive landscape ও তার সমান্তরাল physical landscape খাপছাড়া ভাবে তার বাণিজ্যের বাইরে থেকে গেছে। সেখানে ক্রেতার সংখ্যা কম। আমাদের কাজ—একই সঙ্গে superdiversity, remaining linguistic diversity, এবং procurement of cultural principles by the new generation—এই সমস্ত এলাকাগুলোর দিকে তাকানো, (এবং) Transmission কোথাও কোথাও ঘটছে কিনা সে সব বিবেচনা করা, ইত্যাদি।
এই প্রজন্ম, যারা মোবাইল ফোনে অনলাইন ক্লাস অ্যাটেন্ড করছে, তাদের দিকে তাকানো বিশেষ জরুরি। স্কুল যাওয়া, ক্লাসরুম ইন্টার্যাকশন, মাঠেঘাটে খেলতে যাওয়া প্রভৃতির যে শারীরিক ও মানসিক প্রক্রিয়া ছিল, সেই প্রক্রিয়া অনলাইনে ব্যাহত হচ্ছে—এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। এই তফাতকে বলা হচ্ছে ‘participation gap’ (দ্রষ্টব্য: Boyd 2014)। কিন্তু এই পরিবর্তনে তাদের এথনোগ্রাফিক পরিচয় কোন জায়গায় দাঁড়াচ্ছে সেই কথা বিবেচনা করতে গিয়ে এই প্রজন্মকে বলা হয়ছে—’ডিজিটাল নেটিভ’ (দ্রষ্টব্য: Boyd 2014), Boyd দৃষ্টান্ত (2014: 194) পেশ করে বলছেন—
“a teen who uses a library computer with filtered access for an hour a day has a very different experience with the internet than one who has a smartphone, laptop, and unrestricted connectivity.”
Boyd আরও বলছেন—
Rather than fighting to reclaim the places and spaces that earlier cohorts had occupied, many teens have taken a different approach: they’ve created their own publics. Teens find social media appealing because it allows them access to their friends and provides an opportunity to be a part of a broader public world while still situated physically in their bedrooms. Through social media, they build networks of people and information. As a result, they both participate in and help create networked publics (2014: 201)
এখন আমাদের দেখতে হবে, Boyd (2014) যে পরিসর এবং স্থানের পরিপ্রক্ষিতে তাঁর বক্তব্যকে সাজিয়েছেন, সেই পরিসর কোথায় কোথায় আজও ঢুকতে পারেনি। সেখানে এলাকা বা স্থানের গুরুত্ব বুঝতে হবে। এবং এ কথাও সত্য যে, ওই পরিসর কাউকেই ছেড়ে কথা বলতে নারাজ। এবং তার এমন এক পরিসর দরকার, যে পরিসর, দেশ-কালের গণ্ডি অতিক্রম করে মানুষের মনকে আনুভূমিক নিরন্তর এক কলোনিতে পরিণত করবে।
Expanding Transition
প্রশ্ন তুলে বা প্রশ্নের ওপর প্রশ্ন করে কথা শুরু করা মুশকিল। ধরা যাক যদি প্রশ্ন তোলাও হয়, তাহলেও তো সেই প্রশ্নের মধ্যেই পূর্ববর্তী কোনো আপ্তবাক্যের বীজ থাকে। যেমন, যদি আলোচনা, ’ভাষা জিনিসটা কী?’—এই প্রশ্ন দিয়ে শুরু করি, তাহলেও ’ভাষা বলে একটা জিনিস যে আছে’ সেটা ওই প্রশ্নের মধ্যেই প্রাক্সিদ্ধের মতো বসে থাকে। একেবারে মৌলিক প্রশ্ন বলে কিছু হয় না। তবে ’আমার এই ভাবনায় কোনো প্রাক্সিদ্ধ নেই’—এ কথা বলার মধ্যে শূন্য থেকে শুরু করার যে ভঙ্গি থাকে সেটা অর্জন করা খুব শক্ত কাজ। ’যা শিখেছ ভুলে যাও’-এর মতো শক্ত। আমরা যেমন মনে করি কিছু শিখতে গেলে পরিশ্রম করতে হয়, তেমনই শিখে ফেলা জিনিস ভুলতে গেলেও ততধিক পরিশ্রম করতে হয়। শেখার প্রাতিষ্ঠানিকতার পাশে যথারীতি শেখা জিনিস ভুলে যাওয়ারও প্রাতিষ্ঠানিকতা থাকে। ঠিক একই রকম প্রশ্ন সেই এলাকাতেও ঘোরে ’সঠিক পন্থায় ভুলতে পারলাম কি?’ কিন্তু এ-যুগে মানবিক বিদ্যার বিভিন্ন চর্চার ক্ষেত্রে ওই সঠিক পন্থায় ভুলতে পারাটা খুব জরুরি। কোথাও কোথাও নতুন করে শুরু করার অগ্রিম বায়না নিতে হয়েছে!
তাই এই নতুন করে শুরু করার কাজে রসের ধারণাকে কাজে লাগাতে চেষ্টা করছি। ভারতীয় শাস্ত্রে বলা হয়েছে, কবি কাব্যে ’মায়াজগৎ’ সৃষ্টি করেন (গুপ্ত ১৯৯১: ২৮)। এখন আমরা যে ED-র প্রসঙ্গ তুলেছি সে-ও তো আরেক ’মহামায়া’-র জগৎ। রসের প্রাতিষ্ঠানিক ব্যাখ্যাতেই তো বলা আছে যে, ওই ন’টা স্থায়ী রস ছাড়াও বহু রকম রস থাকতে পারে। কারণ মানুষের মনের যে লৌকিক ভাব তার এমনিতেই স্থিরতা নেই। সেই ভাব যুগের ছন্দে নেচে বেড়ায়। তাই কবিরা তাদের কাব্যে একক রসকে বেশি গুরুত্ব দিলেও, কাব্যের পরতে-পরতে নানারকম অন্যান্য রসের আমদানিও ঘটানো হয়। যাদের রসের নানান শাখাপ্রশাখায় বিচরণকারী রসিক বাস্তব ওরফে লৌকিক জগতে বসেই কাব্য পাঠে অবিরাম অংশগ্রহণ করতে পারেন। সুতরাং রসের আলোআঁধারির খেলায় অংশগ্রহণ করার অভ্যেস রসিকের অনেক দিনকার। এখন যিনি রসিক তিনি আটপৌরে মানুষও বটেন। ফলে রসগ্রহণের মুনশিয়ানা তার জাগরুক থাকে আটপৌরে ভাষার ঘর-দালান সর্বত্র। এখন সহৃদয় পাঠকের মনে রস সঞ্চারিত করা অবধি কবির কাজ। তার অতিরিক্ত কিছু কবির কাম্যও নয়, সেই ক্ষমতাও তার নেই।
”কারণ কাব্য কোনো পাঠকবিশেষের মনে রসের উদ্রেক করবে কি না, তা কেবল কাব্যের ওপর নির্ভর করে না, পাঠকের মনের ওপরেও নির্ভর করে। কবি যে ভাবকে রসমূর্তি দিতে চান, যদি পাঠকের মন সে ভাব সম্বন্ধে কতকটাও কবির মনের সহমর্মী না হয়, তবে সে পাঠকের কাছে কাব্য ব্যর্থ ।” (প্রাগুক্ত: ৪৭)
শঙ্খ ঘোষও (১৯৯৪) ’কবির অভিপ্রায়’ নিয়ে বলতে গিয়ে জিজ্ঞেস করছেন, কী বলতে চান কবিরা?
“নিজের কথাটুকু বলা, এই নিশ্চয়। কিন্তু সে-কথা বলবার মুহূর্তে সমকালীন জীবনতথ্যের সঙ্গে মিশে যায় কত বহুকালীন অনুভব-অভিজ্ঞতার রেশ, মুহূর্তটাকে ছুঁয়ে থেকে পুঞ্জে পুঞ্জে ভরে আসা কত অজস্র মুহূর্তের টান, তার কি কোনো হিসেব আছে?” (প্রাগুক্ত: ৫১)
কিন্তু আমরা যেহেতু রবীন্দ্রনাথের হাত ধরে, রসকে টেনে এনে কাব্য বা নাট্যের বাইরে পা রাখতে বলেছি—সেখানে তো তার জগৎ অসীম। Online-Offline Nexus-এর যে পাঠ্য, সে যে মানুষের সেই অসীম ভোগের সুযোগ নেবে—এ কথা তো জানাই। ফলে সেই অসীমের জগতে পাঠক হিসেবে কারুর ব্যর্থতার সুযোগ পর্যন্ত নেই। কারণ রবীন্দ্রনাথ বলছেন, ’এইরকম ভাবের পাওয়াকেই পাওয়া বলে ভুল করা মানুষের দুর্বলতার একটা লক্ষণ।‘—এই কথাটাতে খেয়াল করে দেখবেন, আমি নজরটান দিয়ে রেখেছি। Online-Offline Nexus-এর মাঝে যে বুদ্ধিমান ব্যবস্থা তৈরি করা হয়েছে, সেই ব্যবস্থায় মানুষের সেই দুর্বলতারই সুযোগ নেওয়া হয়। রবীন্দ্রনাথ সেইরকম ব্যক্তিমানুষের ছবি এঁকেছেন—
“এমন লোক দেখা যায় যারা অতি সহজেই গদগদ হয়ে ওঠে, সহজেই গলা জড়িয়ে ধরে মানুষকে ভাই বলতে পারে—যাদের দয়া সহজেই প্রকাশ পায়, অশ্রু সহজেই নিঃসারিত হয় এবং সেইরূপ ভাব-অনুভব ও ভাব-প্রকাশকেই তারা ফললাভ বলে গণ্য করে।”
কেবল রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যে একটা বিরোধিতা করা যায়—এই বলে যে, ‘এইখানেই সে থামিয়া পড়ে না’ এবং সেই ব্যক্তিমানুষ এখন তাঁরই কথায় বিশ্বমানবে সম্মিলিত হয়েছে। বাকি কি নেই কিছুই? আছে, নজর রাখুন ওই inner domain-গুলোর দিকে। তাহলেই আমার সব কথা পরিষ্কার হবে। অধিক বলা বাহুল্যমাত্র।
[কৃতজ্ঞতা স্বীকার: এই রচনায় রসের প্রসঙ্গ এনে হাজির করার সূত্রও প্রবাল দাশগুপ্তর ধরিয়ে দেওয়া। তিনি রচনার খসড়া পড়ে তাঁর মতামতে সেই কথা জানিয়েছিলেন। তাঁর পরামর্শ অনুযায়ী রচনাটি যথাসাধ্য সংশোধন করলাম। তাঁর প্রতি আরও একবার কৃতজ্ঞতা জানাই।]
উদ্ধৃতি
URLs:
১. https://www.accenture.com/us-en/blogs/technology-innovation/daugherty-digital-transformation
২. https://rabindra-rachanabali.nltr.org/node/7498
৩. https://rabindra-rachanabali.nltr.org/node/7529
৪. https://rabindra-rachanabali.nltr.org/node/9210
৫. Ross, Haj.* Why to syntax. http://www-personal.umich.edu/~jlawler/haj/Whytosyntax.pdf
#Bibliography অথবা গ্রন্থপঞ্জি
ইংরিজি:
Ackermann, R.R., Mackay, A., Arnold, M.L., 2016. The Hybrid Origin of “Modern” Humans. Evolutionary Biology 43 (1 https://doi.org/10.1007/s11692-015-9348-1.
Berwick, R. C. and Chomsky, N. 2016. Why Only Us. Cambridge: The MIT Press.
Blommaert, J. 2012. Supervernaculars and their dialects. Dutch Journal of Applied Linguistics, 1(1), 1–14.
Blommaert, Jan. 2013a. Citizenship, Language, and Superdiversity: Towards Complexity. Journal of Language, Identity, and Education, 12: 193–196. DOI: 10.1080/15348458.2013. 797276.
Blommaert, Jan. 2013b. Ethnography, Superdiversity and Linguistic Landscapes. UK: Multilingual Matters. Print.
Blommaert, Jan. 2018a. Dialogues with Ethnography: Notes on Classics, and How I Read Them. London: Multilingual Matters.
Blommaert, Jan. 2018b. Formatting online actions: #justsaying on Twitter. International Journal of Multilingualism. https://doi.org/10.1080/14790718.2019.1575832.
Boyd, Danah. 2014. it’s complicated. New Haven: Yale University Press.
Castro, L., Medina, A., Toro, M., 2004. Hominid cultural transmission and the evolution of language. Biology & Philosophy 19 (5), 721-737. https://doi.org/10.1007/s10539-005-5567-7.
Dasgupta, Probal. 2020. The Theatre and The Classical India: Some Availability Issues. Soft Copy (P.C)
Everett, D. L. 2017. How Language Began: The Story of Humanity’s Greatest Invention. WW Norton & Co.
Everett, D. 2016. Grammar Came Later: Triality of Patterning and the Gradual Evolution of Language. lingbuzz/002948.
Fitch, W. T., Hauser, M. D., Chomsky, N., 2005. The evolution of the language faculty: Clarifications and implications. Cognition 97, 179-210.
Hauser, M. D., Chomsky, N., Fitch, W. T., 2002. The faculty of language: What is it, who has it, and how did it evolve? Science 298, 1569-1579.
Kellman, Steven. 1996. “J. M. Coetzee and Samuel Beckett: The Translingual Link”. Comparative Literature Studies. 33 (2): 161–172.
Maly, Ico & Blommaert, Jan. 2019. Digital Ethnographic Linguistic Landscape Analysis (ELLA 2.0). Tilburg Papers in Cultural Studies. Paper 233. Print.
Renfrew, C. 1994. World Linguistic Diversity. Scientific American, January 1994, 116 – 123.
Schwarzer, David, Melanie Bloom, Sarah Shomo. (2006). Research as a Tool for Empowerment: Theory Informing Practice. (Research in Second Language Learning). Charlottesville, NC: Information Age Publishing.
Tung-Chiou, Huang. 2010. The Application of Translingualism to Language Revitalisation in Taiwan. Asian Social Science. 6(2): 44-59.
Vertovec, Steven. 2007. “Super-diversity and its implications”. Ethnic and Racial Studies. 30 (6): 1024–1054. doi:10.1080/01419870701599465.
Wittgenstein, Ludwig. 2009. Philosophical Investigations (4th edn). P.M.S. Hacker and Joachim Schulte (eds. and trans.), Oxford: Wiley-Blackwell.
Yao, Xiaofang.2019. Review: Anthropological Linguistics; Sociolinguistics: Blommaert (2018). LINGUIST List 30.4050. https://linguistlist.org/issues/30/30-4050.html.
বাংলা:
গুপ্ত, অতুলচন্দ্র। ১৯৯১। কাব্যজিজ্ঞাসা। কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ।
ঘোষ, শঙ্খ। ১৯৯৪। কবির অভিপ্রায়। কলকাতা: রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়।
দাশগুপ্ত, প্রবাল। ২০১৯। শান্তির পথে মার্কসীয় সম্বল। আলোচনা চক্র। Soft Copy (P.C).
দাশগুপ্ত, প্রবাল। ২০২০। নাটক আর ভাষাতত্ত্ব। পরিকথা। Soft Copy (P.C).
মুখোপাধ্যায়, শিবাংশু। ২০১৮। মানুষের ভাষার বিশেষত্ব। আলোচনা চক্র, ৩২(২), পৃ. ২৮০ – ২৯৮।
মুখোপাধ্যায়, শিবাংশু। ২০২০খ। বিশ্বজনীন ব্যাকরণের সার এবং মানুষের ভাষার বাস্তব।
মুখোপাধ্যায়, শিবাংশু এবং চিরঞ্জীব শূর সম্পাদিত, নোয়াম চমস্কি: বহুরূপে সম্মুখে তোমার। কলকাতা: আলোচনা চক্র। পৃ. ১০৯ – ১৩০।