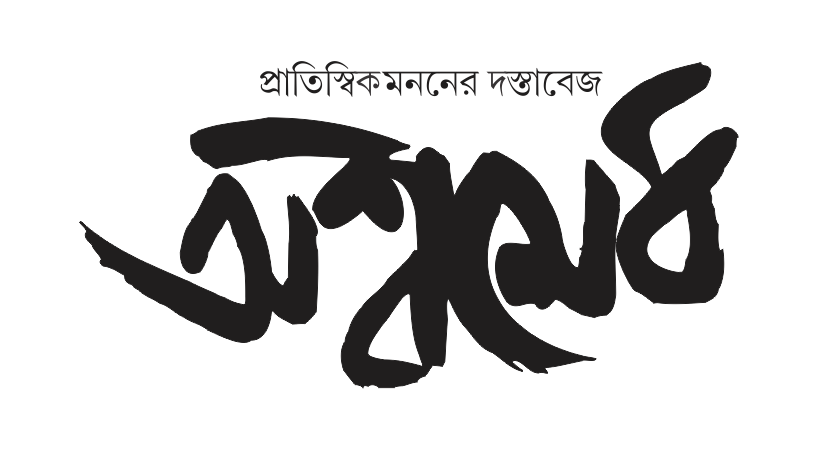বিবর্তনবাদের জনক চার্লস ডারউইনের তত্ত্ব অনুযায়ী প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে জীবের গাঠনিক ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের যে ক্রমপরিবর্তন তা বিবর্তন হিসাবে পরিচিত। জীবের জিনরাশি বংশধরদের মধ্যে যে বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করে তাতে জীবের নতুন করে কোনও বৈশিষ্ট্যের উদ্ভব হতে পারে বা পুরানো বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন ঘটতে পারে। যদিও একটি প্রজন্মে জীবের বৈশিষ্ট্যের যে পরিবর্তন সাধিত হয় তা খুবই সামান্য কিন্তু কালক্রমে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধিত হয়। এমনকি তা নতুন প্রজাতির উদ্ভবের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এই ভাবে আমাদের সকল প্রজাতির প্রাণীই এক ধারাবাহিক পরিবর্তনের মাধ্যমে ধীরে ধীরে উৎপত্তি লাভ করেছে।[১] অর্থাৎ বলা যায় জীবজগতের যা কিছু এখন বর্তমান তা সুনির্দিষ্ট বিবর্তনেরই পথ ধরে আজকের পৃথিবীতে বিরাজ করছে। আর সে-ই বিবর্তনের পথে চলতে গিয়ে কত কিছুর ঘটেছে চির অবলুপ্তি। তবুও পাহাড় কন্দরে তাদের যে ছাপ থেকে গেছে তা যেমন সে-ই পুরানো পৃথিবীকে মনে করায় তেমনি ভাবিয়ে তোলে সে-ই পর্যায়কে যেখানে পরিবর্তনের পথে যখন দুই রকম বৈশিষ্ট্যই বর্তমান ছিল তার কথা। মিসিং লিংক হিসেবে যেমন সেগুলির কথা অনস্বীকার্য তেমন ভবিষ্যৎ পরিবর্তনের মাত্রা কীরূপ হতে পারে তার ধারণাও তৈরি হয়ে যায় তার সঙ্গে সঙ্গে।
সাহিত্যের ক্ষেত্রেও বিবর্তনের কথা সমান ভাবে প্রযোজ্য। যদিও সেখানে জীব বিবর্তনের মতো কোটি কোটি বছর সময় লাগে না। এক প্রজন্মের মধ্যেই তা সীমায়িত হতে পারে। এমনকি মুহূর্তেও ঘটতে পারে সে-ই পরিবর্তন। কেননা সাহিত্যের যে বিবর্তন তা মূলত ভাবনার বদল বা দৃষ্টিভঙ্গির বদল। এক ভাবনা থেকে আর এক ভাবনার জন্য লেখক যেমন পূর্ববর্তীর ধারণাকে বহন করে নিয়ে চলেন তেমন সে-ই ভাবনা জারিত হয়ে নতুন ভাবনারও জন্ম হয়। আর সৃষ্টিশীল লেখক মাত্রই সে-ই ধারণাকে পরিস্ফুট করে তোলেন সর্বাধিক। সামাজিক রাজনৈতিক পটপরিবর্তন বাংলা সাহিত্যের বিবর্তনকে ত্বরান্বিত করেছে সবথেকে বেশি। সে কারণে কাব্য সাহিত্যে প্রকাশভঙ্গিরও বদল ঘটেছে বারে বারে। প্রাচীন চর্যাপদের যে সমাজ-চিত্র আর মধ্যযুগের কাব্যের যে সমাজ তার অনেক বদল ঘটে গেছে। কেননা মধ্যযুগে যে রাজনৈতিক সংঘাত বাংলার মাটিতে হয়েছে তা তুর্কি আক্রমণের পূর্বে ছিল না। তাই দেখা যায় মধ্যযুগের কবিরা বেশি মাত্রায় সময় সচেতন এবং তাঁদের কাব্য কবিতায় সে-ই সময়ের সমাজ-চিত্র বেশি মাত্রায় উল্লেখিত। রাজসভার আনুকূল্য পেলেও কবিরা তৎকালীন সমাজ ও সময়কে কৌশলে লিখে রেখে গেছেন। মঙ্গলকাব্যগুলিতে দৈব বিশ্বাসের পাশাপাশি দেবতাদের চরিত্রে মানুষের ছাপ পড়তে থাকে। ভারতচন্দ্র তো শিবকে ভাঁড়ের পর্যায়ে নামিয়ে সে-ই সময়ের সাধারণ মানুষের অবস্থা নির্দেশ করে গেছেন। ব্যতিক্রমী ধারা হিসাবে চৈতন্যজীবনী বিবর্তনবাদের নতুন উদ্ভবকে স্মরণ করায়, যেখানে মানুষই দেবতার আসন পেতে থাকে।
অন্যদিকে আর এক পরিবর্তনের কারণ হয়ে দাঁড়ায় উনিশ শতক। ভিন্ন জাতি ধর্মের সংস্পর্শে, ভিন্ন সাহিত্যের আস্বাদনে বাঙালি হৃদয় আর একবার পরিবর্তিত হয়। ইংরেজি শিক্ষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য ধ্যান-ধারণার সঙ্গে যুক্ত হবার ফলে শিক্ষত ভারতবাসীর মনে নবজাগরণের সৃষ্টি হয়। গতানুগতিক আলোচনার চেয়ে সাহিত্যিক প্রশ্নের সম্মুখীন হয় সমাজ। কবি সাহিত্যিকদের লেখনীতে তাই উনিশ শতকের সাহিত্যে সমাজের নানান ছবি প্রকাশিত হতে থাকে। ঈশ্বর গুপ্ত, রঙ্গলাল, মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, দীনবন্ধু মিত্র, বঙ্কিমচন্দ্র, বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ ছিলেন সে-ই পর্যায়ের লেখক। বিহারীলাল চক্রবর্তী এই সময়ের হলেও তিনি ছিলেন স্বতন্ত্র; সৌন্দর্যানুরাগ, প্রকৃতিমুগ্ধতা ও আত্মমগ্নতার লিরিক কবিতা ছিল তাঁর স্বাতন্ত্র্যের মূল। অপরদিকে আর এক পরিবর্তনের দিক নির্দেশ করলেন রবীন্দ্রনাথ, যার প্রভাব থেকে পুরোপুরি মুক্ত হতে পারেনি কোনও কবিই। সমাজভাবনা, সাহিত্যভাবনা, প্রকরণগত ভাবনা, কবিতা, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ, ছোটগল্পের মতো বহুমুখী ধারা সৃষ্টিতে তিনি একাই হয়ে উঠলেন সর্বকালের প্রতিনিধি। সংশয়ের ঊর্ধ্বে প্রতিষ্ঠিত তাঁর মন ঐশী অনুভবের স্পর্শে মানুষের শুভচেতনা ও পরম মঙ্গলকেই ধ্বনিত করে তুলেছে সমগ্র রচনার মধ্যে। কিন্তু পরাধীনতার গ্লানি, ইংরেজদের অত্যাচার, মন্বন্তর, বিশ্বযুদ্ধ, অন্নাভাব, শোষণ, শাসন, মূল্যবোধের অবমূল্যায়ন বিশ শতকের কবি লেখকদের ভাবিয়ে তোলে। কবিতা তখন শুধুই শুভ বোধের বাহক নয় তার দেহে ঢুকতে থাকে সন্দেহের বিষ। সত্যেন্দ্রনাথ, মোহিতলাল, যতীন্দ্রনাথ, নজরুলের কবিতায় প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর শোনা গেলেও ‘আধুনিক মানুষের সামাজিক সংকট, ব্যক্তিক নৈরাশ্যবোধ, নতুন ও পুরানো মূল্যবোধের সংঘাতজনিত অনিশ্চয়তা—এসব দিক প্রধান হয়ে ওঠেনি।’[২] সেদিক থেকে জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, অমিয় চক্রবর্তী, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের কবিতায় উঠে এল পরিবর্তিত সময় ও বিশ্বচেতনার ছাপ। উপমা, চিত্রকল্প ও শব্দের প্রচলিত ধারা ভেঙে কবিতায় এল ডিম, যোনি, স্তন, নষ্ট শশা, পচা চালকুমড়োর মতো নানাবিধ শব্দবন্ধ, আভিধানিক অপ্রচলিত শব্দের প্রয়োগ লক্ষ করা গেল আর আধুনিক মানুষের ক্লান্তি বোঝাতে এল অতীতচারিতা, মৃত্যুচেতনা ও প্রকৃতির অকৃত্রিমতার কাছে আশ্রয় নেবার কথা। যদিও রবীন্দ্র-কবিতায় মৃত্যুর ছবি আছে অনেক কিন্তু আধুনিক কবিদের কাছে তা শুধু মঙ্গলময় ঈশ্বরের পরশ নয় তা যেন জীবনের টুকরো টুকরো মৃত্যুর বিপরীতে এক দৃঢ় প্রতিবাদ। তাই জীবনানন্দের ‘আট বছর আগের এক দিন’ কবিতায় দেখা যায় লাসকাটা ঘরে লোকটি নিশ্চিন্তে শুয়ে আছে কেননা অর্থ কীর্তি সচ্ছলতার থেকেও ‘আরো এক বিপন্ন বিস্ময় আমাদের অন্তর্গত রক্তের ভিতর খেলা করে,/ আমাদের ক্লান্ত করে’ আর লাসকাটা ঘরে সে-ই ক্লান্তি নেই। যুগের ক্লান্তির চেয়ে লাসকাটা ঘর তাই তাকে শান্তি দেয়।
বিবর্তনের পথে চলতে চলতে কবিতার মধ্যে এসেছে সমকালীন রাজনৈতিক আবহাওয়া। চারের দশকে কবিরা সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করেছিলেন। অরুণ মিত্র, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, দীনেশ দাশ, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সুকান্ত ভট্টাচার্যের কলমে শ্রমজীবী মানুষের জয়গান লেখা হতে থাকে। কবিতার অভিমুখ বদল ঘটতে থাকে। সমাজ বদলের আহ্বান শোনা যায় কবির কণ্ঠে, সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের বিখ্যাত ‘মে-দিনের কবিতা’ সে-ই দিক বদলের ইঙ্গিতকে স্পষ্ট করে—’শতাব্দীলাঞ্ছিত আর্তের কান্না প্রতি নিঃশ্বাসে আনে লজ্জা;/ মৃত্যুর ভয়ে ভীরু বসে থাকা, আর না—/ পরো পরো যুদ্ধের সজ্জা।’
কবিতার বিবর্তনের পথে পাঁচের দশক আরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। দাঙ্গা, খণ্ডিত স্বাধীনতা, দেশভাগ, উদ্বাস্তু সমস্যা, প্রভৃতি ঘটনা মানবিক সুস্থ সম্পর্কগুলোকে ভেঙে তছনছ করে দেয়। ফলে কবিতায় সমাজজীবনের পাশাপাশি কবির ব্যক্তিজীবনের সুখ-দুঃখ আশানিরাশাও স্পষ্ট ভাবে উঠে আসে। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, শঙ্খ ঘোষ, বিনয় মজুমদার, মণীন্দ্র গুপ্ত, দিব্যেন্দু পালিত প্রমুখ বিভিন্ন কবি এই পর্যায়ে প্রতিনিধিত্ব করেছেন। আর এই পর্যায়ের কবি মণীন্দ্র গুপ্তের কবিতার সেই বিবর্তনের গতিশীল ক্রিয়া আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। যদিও মণীন্দ্র গুপ্ত নিজেকে ‘চল্লিশ ও পঞ্চাশের মাঝামাঝি সময়ের কবি’[৩] বলে চিহ্নিত করেছেন। ১৯৪৯ সালে ‘আমরা তিনজন’ নামে যৌথ কাব্য সংকলনের মাধ্যমে মণীন্দ্র গুপ্তের আত্মপ্রকাশ আর ‘নীল পাথরের আকাশ’ থেকে এককভাবে পথচলা। বিদ্রোহ, উচ্চকিত কলরব, উদ্দামতা থেকে দূরে তাঁর কবিতা নিবিড় শান্ত মগ্ন সুরে নিঃশব্দে ঐতিহ্যের প্রতি আনুগত্য রেখে নিজস্ব পরিসরে ও স্বতন্ত্রভাবে পরিবর্তিত হয়ে পথ সৃষ্টি করে চলেছে, যেখানে প্রেম প্রীতি ভালোবাসা শুধুমাত্র মানুষের মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকে না, প্রকৃতির মধ্যে বিস্তার লাভ করে চলে। মনুষ্যেতর প্রাণীর কথাও তাঁর কবিতায় উঠে এল, কেননা তিনি চেয়েছেন—”লোকসংখ্যা কমুক, বৈভব তৈজস কমুক, শব্দ বাক্য কমুক। মাছ পাখি পশু বাড়ুক, বন বাড়ুক। পৃথিবী শান্ত সৌন্দর্যে টলমল করুক। মানুষের মুখরতাকে চাপা দিয়ে বয়ে যাক বনমর্মর।”[৪] মানুষের শুভ বুদ্ধি যেখানে অবমূল্যায়িত হয় সেখানে প্রকৃতিই নবচেতনায় এগিয়ে যেতে ভরসা দেয়। প্রকৃতির সরলতা ভরা গভীর স্পর্শ সেই বিবর্তনেরই সূচনা করে, যেখানে দুঃখকে অতিক্রম করা যায়, কেননা নিসর্গের মধ্যে আছে মুক্তি সেখানে ‘কোনো দুঃখ ব্যক্তিগত নয়’ (‘নিসর্গে: মুক্তি’, লাল স্কুলবাড়ি)। কবিতায় বিবর্তন মূলত দুই প্রকার—প্রকরণগত ও ভাবনাগত। প্রকরণগত দিক থেকে মণীন্দ্র গুপ্তের কবিতায় খুব একটা জটিলতা নেই। ভাষা সজহজবোধ্য ও আড্ডার মেজাজে কথা বলা, সে কারণেই সাদামাটা ভাষা ভাবনার গভীরতাতে পৌঁছাতে পেরেছে। স্লোগানধর্মিতা বাদ দিয়ে প্রাতিষ্ঠানিকতার বিপরীতে দাঁড়িয়ে জীবনের রহস্য উন্মোচন করে গেছে কবিতাগুলি।
বিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে পৃথিবী যখন উত্তপ্ত হচ্ছে, নদ নদী মজে যাচ্ছে, পশুপাখি ধ্বংসের মুখে, মরুভূমি বেড়ে চলেছে, মানুষ নিজের লালসায় নারীকে পণ্য করে তুলছে, নাগরিক বর্জ্য পদার্থে বিষিয়ে উঠছে সভ্যতা—ঠিক সে-ই সময় মানসিক বাস্তুতন্ত্রকে ঠিক করে দিতে কবি লেখনী ধারণ করেছেন। শব্দ প্রয়োগের যে বিরাট পরিবর্তন জীবনানন্দ করে গেছেন, তার উত্তরাধিকার বয়ে চলেছে মণীন্দ্র গুপ্তর কবিতায়। বিজ্ঞান, গ্যালাক্সি, ইতিহাস, প্রেম, প্রকৃতি, কর্মবাদ, পুরাণ, মিথ সবকিছুই তাঁর কবিতায় ভাষারূপ পেয়েছে। সৌন্দর্যবোধের বিস্ময় ফোটাতে কবিকে দুর্বোধ্য ভাষা ব্যবহার করতে হয় না। যেমন (‘চিন্ময় বসন্ত’, লাল স্কুল বাড়ি)—
ঘুরন্ত বাতাসে কাঠিকুটি, শুকনো পাতা নাচুনে হরিণের মতো
চক্কর খেতে খেতে চলে যায়—মাঠের শেষ সীমার চেয়েও
দূর কোনো দেশে নিশ্চয় ফুটেছে।
পুঞ্জ পুঞ্জ আকাশকুসুম।
মণীন্দ্র গুপ্ত কবিতার ক্যানভাসে ফুটিয়ে তুলেছেন জীবনের বিচিত্র ছবি। জীবনানন্দের কবিতায় যে চিত্রকল্প পাওয়া যায় তা নিছক সাদৃশ্যকে বোঝায় না, তার মধ্যে থাকে বুদ্ধিদীপ্ত মনন, চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য এবং অভিজ্ঞতার আভাস যেমন ‘মোরগ ফুলের মতো লাল আগুন’ বা ‘বাঘের ঘ্রাণের মতো হৃদয়ে জাগায়ে যায় ত্রাস’। সুধীন্দ্রনাথের কবিতায় সেই ধারা বইতে থাকে ‘কুলায় বিমুখ চিলের মতো মুক্তাকাশে প্রসার ক’রে ডানা’ বা ‘মাৎস্যন্যায় প্রাচীর স্বস্তি কাড়ে’ প্রভৃতি বাক্যবন্ধ। অপর দিকে পরবর্তী সময়ের কবিদের রচনা সহজবোধ্য চিত্রকল্পের দিকে ঝোঁক নেয়। ছেঁড়া জুতোয় ফিতে বাঁধতে বাঁধতে মনে বেঁধে নেওয়া বা পূর্নির্মার চাঁদকে রুটির সঙ্গে তুলনায় কবিরা আরও বেশি করে স্পষ্ট ভাবে ছড়িয়ে দিতে চাইছেন তাঁদের ভাবনাকে। আর সেই ধারাবাহিকতা বজায় রেখে কবিতা আরও বিস্তৃত ও প্রাঞ্জল হয়ে উঠল মণীন্দ্র গুপ্তের কবিতায়। তাই চিত্রকল্পে উঠে আসে তেপান্তরের পথ, অপদেবতার খুলি, কাটা মুণ্ড, স্ত্রী নাভি, বাঘের বাচ্চার মতো রোদের ছবি। এছাড়াও বিজ্ঞান, কলা, দর্শন, ধর্মশাস্ত্র এবং বিভিন্ন কাহিনি উপকাহিনির সংযোগে গড়ে উঠে কাব্যের শরীর। ‘মৃত্যুর পরে’ কবিতায় বিজ্ঞান ও মিথকে এক করে সুন্দর একটা চিত্রকল্প তৈরি হয়েছে (‘মৃত্যুর পরে’, ছত্রপলাশ চৈত্যে দিনশেষ)—
আমার মৃত্যুর পরে বৃষ্টি নামল:
ভয়ংকর তেজস্ক্রিয় বিষ ধুয়ে আদি শ্যাওলা জাগাতে যেমন
প্লিস্টোসিন যুগে হাজার বছর ধরে বৃষ্টি হয়েছিল।
সেই অকালসন্ধ্যায় আমার মেঘের মুণ্ড রক্তাকাশে
রাহুর মুণ্ডের মতো ভাসমান হলে
হূ হূ করে কোথা থেকে বাতাস নামক বস্তু তৈরি হয়ে এসে
তাকে আরো উঁচুতে ওঠায়।
ছন্দের দিক থেকে আধুনিক কবি হিসাবে গদ্য ছন্দ হয়েছে প্রধান তবে কিছু সমিল ছন্দের কবিতাও আছে। জীবনানন্দের মতো অক্ষরবৃত্ত রীতি তাঁর কবিতার বৈশিষ্ট্য। কিন্তু কবির ভাবনা যেখানে মুখ্য সেখানে এই সমস্ত প্রকরণ গৌণ হয়ে যায়।
দিক বদলের ভাবনা যে সমস্ত কবিদের লেখায় থাকে, সে-ই কবিরাই উপেক্ষিত থেকে যান অনেক সময়। প্রাতিষ্ঠানিকতা, বিজ্ঞাপনধর্মীতা ও জনপ্রিয়তার বাইরে দাঁড়িয়ে মণীন্দ্র গুপ্তের কবিতা নব যুগের সৃষ্টি করেছে। তাঁর কবিতায় নিহিত ভাবনা ও চেতনার অনুরণন পাঠকের মনে চলতেই থাকে। কবিতার জীবনশক্তি প্রসঙ্গে তিনি বলছেন (কবিতার জীবন ও দুষ্প্রবেশ্যতা: বৃদ্ধি: চাঁদের ওপিঠে) —“উৎকৃষ্ট কবিতার দুর্মর জীবনশক্তি অনেকটা যেন সেই বিশুষ্ক পদ্মবীজের মতো, যা হাজার বছর পরেও অনুকূল ক্ষেত্রে পুঁতলে আবার বেঁচে ওঠে, ফুল ফোটায়।” ক্ষণকাল পেরিয়ে চিরকালের পথে কবিতার পথ চলায় তিনি বিশ্বাস করেন। সৃষ্টির অন্ধকার থেকে কবিতা ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ে চেতনার আলোকে। আপাত তুচ্ছ বিষয় অনন্তের ভাবনায় দ্যোতিত করে পাঠক হৃদয়কে। ‘নীল পাথরের আকাশ’ কাব্যগ্রন্থের ‘চৈতন্যময় ভাষা’ উপলব্ধি ও অনুভূতির স্তরে পৌঁছে যায়। ‘আমার রাত্রি’ কাব্যগ্রন্থে আধুনিক মানুষের দাম্পত্য সম্পর্ক নিয়ে কবি চিন্তিত। তাই ‘দম্পতি’ নামে একাধিক কবিতা দেখা যায়। ‘দম্পতি ৩’ কবিতায় বলছেন—’তারা ভুল করেছিল। ভেবেছিল:/ ভালোবাসা অনপেক্ষ এবং দুর্মর।/ কখনো ভাবেনি তারা অভিজ্ঞতা মানে জন্মান্তর’। ‘লাল স্কুলবাড়ি’ কাব্যের আত্মজৈবনিক সুর কবিকে মৌলিকত্ব দান করে—’সন্ধ্যাবেলা তালা খুলি। ঘর নয়, বোবা কালা মা-মরা সন্তান/ ঢলে আছে। থাক।—ক্লান্ত লাগে’…[৫]
‘Poets are the unacknowledged legislators of the world’—শেলির[৬] এই কথার আভাস পাওয়া যায় ‘ছত্রপলাশ চৈত্যে দিনশেষ’ কাব্যগ্রন্থের ‘প্রথম মণীন্দ্র গুপ্ত’ কবিতায় ‘শরৎমেঘ ও কাশফুলের বন্ধু’ কাব্যে পৌরাণিক শিব একাধারে নির্লিপ্ত থাকেন, কিন্তু শিব চতুর্দশীতে বিবাহযোগ্যা মেয়েরা ছুঁলে ‘ভিতরের আগুন ধক ধক করে’ জ্বলে ওঠে। আবার ‘নমঃ শিবায়’ কবিতায় দেখা যায় বম্বে রোডে সারারাত ট্রাক চালানোর পর ক্লান্ত দেহমনে ধাবায় যখন ঘুম আসে তখন তিন নম্বর চোখ খুলে যায়। এই শিবকে চিনে নিতে আমাদের কষ্ট হয় না। বিবর্তনের পথে শিব আমাদের সঙ্গী হয়। কালচেতনা ও পৌরাণিক কাহিনিকে আধুনিক ভাবনার আলোকে বিশ্লেষণের দৃষ্টান্ত ‘ভবতারিণী’ কবিতাটিতে ফুটে উঠেছে; কামাতুর হয়ে রমণসঙ্গিনীকে মুখ কপাল চেটে দিতে বলায় ভবতারিণী ‘চাটতে লাগল আর পুঁছে পুঁছে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে লাগল/ আমার চোখ নাক গাল ঠৌট।’—এই ভাবে মহাকালকে দেবতার পৌরাণিক অনুষঙ্গে জুড়ে দেওয়ায়, কবিতার গতিমুখ পরিবর্তন হয়ে গেল।
জীবন ও মৃত্যু কবির কাছে অবস্থাগত রূপান্তর শুধুমাত্র। আর মৃত্যু পরবর্তী পরলোক তাঁর কাছে বাপের বাড়ির সমার্থক—’পরলোক আর বাপের বাড়ি তো একই পাড়ায়’। তাই মৃত্যুতে জীবনের সব শেষ বলে তিনি মনে করেন না। মরণ থেকে সোনা গড়িয়ে আনতে তিনি চলে যান দেশান্তরী হয়ে। ‘যেন মরণের পরে’ কবিতার শাোনা যায়—’আমি এখন ব্যথাবিহীন, হাত পা কলের, চলে যাচ্ছি—/ কপালময় আঁকা:/ চক্রপাতা গাছের মাথায় বুকের ধন, বাংলা দেশের রাকা।’ ‘মহারাত্রি’ কবিতায় সেই পথ চলা আরও স্পষ্ট হয় (‘মহারাত্রি’, মৌচুষি যায় ছাদনাতলায়)—
রাত্তিরে মারা যাবার পর বোঝা গেল রাত্রি কী দীর্ঘ!
কোটি কোটি মাইল রাত্রির মধ্যে যাবার পরও
রাত্রি ভোর হয় না।
জীবনানন্দ পরবর্তী কবি হিসাবে তাঁর ভাবনার স্বকীয়তা এর থেকেই প্রমাণিত হয়।
বিবর্তনের পথে চলতে চলতে কবিতায় তার ছাপ ধরা পড়ে। ক্ষণকাল থেকে শাশ্বতের দিকে যেতে গেলে পূর্বসূরির অভিজ্ঞতা ব্যতীত তা কখনোই সম্ভব নয়। অনেক সময় সে-ই অভিজ্ঞতা অন্ধ অনুকরণে পর্যবসিত হয়ে যায় কবিতার শরীরে তখন তা থেকে আর নতুন কিছু সৃষ্টি হয় না। আবার সে-ই অভিজ্ঞতাকে সঙ্গে নিয়ে ভাবনায় ঋদ্ধ হয়ে যাঁরা নতুন পথের সন্ধান দেন তাঁরা বিবর্তনের সূচনা করেন। কবিতার বীজ-কে উপযুক্ত ক্ষেত্রে বপন করার জন্য তাই কবিকে চেষ্টা চালিয়ে যেতে হয়। কেননা—“কবিতার মধ্য দিয়েই কবির চেতনা সঞ্চারিত হয় পাঠকের চেতনায়। আর, কবিতার সেই আপাত-নির্জীব দেহের মধ্যগত সংহরিত জীবনবীজই সঞ্জীবিত হয়ে ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকে পাঠক-চিত্তের আকাশে।”[৭] মণীন্দ্র গুপ্তের কবিতা সেই বীজকেই বহন করে চলেছে।
সূত্রনির্দেশ:
১. https://bn.m.wikipedia.org/wiki/বিবর্তন
২. সুমিতা চক্রবর্তী, ‘আধুনিক কবিতার দ্বিতীয় পর্যায়’, কলকাতা; প্রজ্ঞাবিকাশ, ২০১০, পৃষ্ঠা ৩।
৩. গৌতম মণ্ডল (সম্পাদনা), ‘আদম’ (ত্রৈমাসিক কবিতা পত্রিকা), নদিয়া, ত্রয়োবিংশ বর্ষ, মার্চ ২০১৮, পৃষ্ঠা ৫৬।
৪. মণীন্দ্র গুপ্ত, ‘কবিতা সংগ্রহ’, নদিয়া; আদম, ২০১৬, প্রথম প্রকাশের ‘ভূমিকা’ অংশ।
৫. মণীন্দ্র গুপ্ত, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৮৩।
৬. www.poetryfoundation.org/articles/69388/a-defence-of-poetry
৭. মণীন্দ্র গুপ্ত, ‘গদ্যসংগ্রহ ১’, কলকাতা; অবভাস, ২০১৩, পৃষ্ঠা ১৬।
প্রচ্ছদ ছবি সৌজন্য: অহিরা পত্রিকা ও অরণি বসু