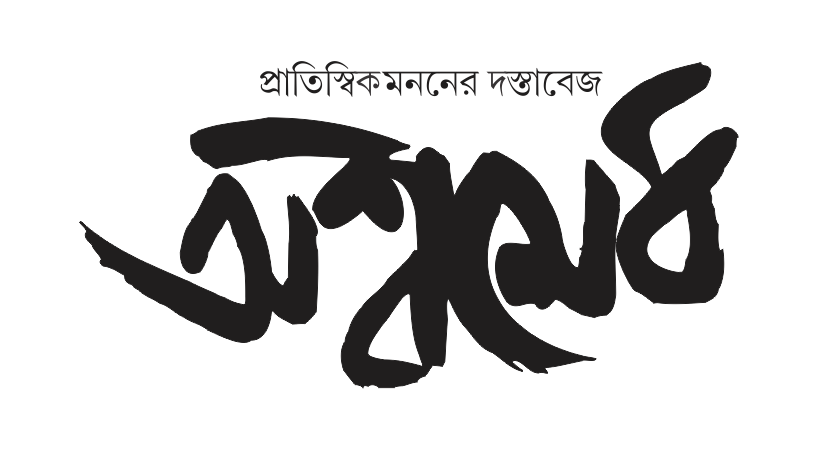উত্তর চব্বিশ পরগনা প্রাচীন এবং ঐতিহ্যমণ্ডিত এলাকা। তবে সমগ্র চব্বিশ পরগনা থেকে এ জেলার প্রশাসনিক বিচ্ছেদ অতি সাম্প্রতিক কালের ঘটনা (১৯৮৩)। প্রশাসনের অনুশাসনে ভূগোল এবং ইতিহাসের উত্তরাধিকার এবং পরম্পরাকে সবসময় খণ্ডন বা লঙ্ঘন করা যায় না। তাই দুটি জেলার জীবন-সমীকরণে এক অকৃত্রিম সহজ সমন্বয় ও সম্পর্কের স্রোত থেকেই গেছে। এ জেলা নদীবহুল, সাগর জলে স্নাত, অরণ্যের আশীর্বাদপূত, মৃত্তিকার উর্বতায় ধন্য। কৃষি, শিল্প, স্বাধীনতার সংগ্রাম, শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে অতুলনীয় উৎকর্ষ অর্জনেরও কৃতিত্ব আছে জেলার। যে গাঙ্গেয় বদ্বীপের উল্লেখ প্রাচীন মহাকাব্য মহাভারত-এ অথবা রঘুবংশ-এ পাওয়া যায়, যার পৌনঃপুনিক প্রসঙ্গ পুরাণ কাহিনিমালায় বিধৃত তা নিঃসন্দেহে এই অঞ্চল। খ্রিস্টপূর্বাব্দ প্রথম শতক থেকে আনুমানিক তৃতীয় খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়কালে গ্রীক নৌচালকদের সমুদ্রাভিযান কাহিনি, ভৌগোলিক বা ভ্রমণ-বিবরণে এই অঞ্চলের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। প্লিনি এবং টলেমির রচনা, অজ্ঞাত লেখকের ‘The Periplus of the Erythraean Sea’-তেও আমাদের এই আলোচ্য পরগনা প্রসঙ্গায়িত হয়েছে।
পুরাতাত্ত্বিক উৎখননের ফলে বেড়াচাঁপা-দেগঙ্গা-চন্দ্রকেতুগড়ের সন্নিহিত বিশাল অঞ্চলে আনুমানিক চতুর্থ শতাব্দীর সমৃদ্ধ সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ মিলেছে। চতুর্থ থেকে দশম খ্রিস্টাব্দ অর্থাৎ গুপ্ত যুগ থেকে পাল শাসকদের রাজত্বকাল পর্যন্ত বেড়াচাঁপা দেগঙ্গায় গ্রাম-বৃত্তায়িত বন্দর ও নগরজীবনের অস্তিত্ব ছিল। দেগঙ্গা হয়তো বা দ্বিতীয় গঙ্গার অপভ্রংশ এবং জনগোষ্ঠী ‘গঙ্গারিদি’ নামে পরিচিত ছিল।
ইখতিয়ারউদ্দীন মহম্মদ বখতিয়ার খিলজির অভিযান এবং নদিয়া দখলের সূত্রে মধ্যযুগে বাংলার ভাগ্য পরিবর্তন ঘটে। পরিবর্তনের অভিঘাত উত্তর চব্বিশ পরগনাও এড়াতে পারেনি। রাজা চন্দ্রকেতুর সঙ্গে গোরাই গাজি-র সংঘাতই এর প্রমাণ। যদুনাথ সরকার তাঁর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত ’হিস্ট্রি অব বেঙ্গল’-এর দ্বিতীয় খণ্ডে বলেছেন, বাংলার ছোট বড় রাজা-মহারাজা-ভূমিপতিরা এ সময়ে গৌড়ের সুলতান আলি মর্দান-কে রাজস্ব এবং নজরানা পাঠানো শুরু করে। পরে প্রতাপাদিত্য মুঘল সেনাপতি মান সিংহের কাছে পরাস্ত হলে, বাংলার প্রাচীন শাসনব্যবস্থার সম্পূর্ণ পতন ঘটে। ১৪৯৫ খ্রিস্টাব্দে বিপ্রদাস পিপলাই চাঁদ সদাগরের সমুদ্র-যাত্রা নিয়ে ‘মনসাবিজয়’ কাব্য রচনা করেন, তাতে গঙ্গার প্রবাহ-পথের উল্লেখ আছে। উত্তর চব্বিশ পরগনার একাধিক অঞ্চল এই প্রবাহ-পথে অবস্থিত। ড. ব্লকম্যান, ১৫৮২-তে রচিত মুঘল রাজস্ব তালিকায় এ অঞ্চলের উল্লেখ পেয়েছেন বলে একটি গবেষণাপত্রে দাবি করেন। টোডরমল এই তালিকার প্রণেতা, পরে এটি আবুল ফজল-এর ‘আইন-ই-আকবরি’তে সংযোজিত হয়।
শিল্পবিপ্লবের ওপর নির্ভর করে গোটা ইওরোপে নবযুগের সূচনা হয়। ইংরেজ, পোর্তুগিজ, ফরাসি, স্পেনীয় নানা দেশের বণিককুল ব্যাবসা, বাজার, কাঁচামালের খোঁজে বেড়িয়ে পড়ে এশিয়া, আফ্রিকা সহ নানা অনুন্নত অঞ্চলে। বিদেশী বণিক ও রাজন্যবৃন্দের কাছে ভারতবর্ষ অবশ্যই উল্লেখনীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ গন্তব্য ছিল। তারা অস্ত্রের আঘাতে, রক্তক্ষয়ের মধ্যে আপন আপন কর্তৃত্ব কায়েম করার উদ্যোগ নিয়েছে। মুঘল সাম্রাজ্যের পড়ন্ত বেলায় ক্ষীয়মাণ শক্তি ও ক্রমবর্ধমান কলহের সুযোগে বাংলার প্রান্তে মুর্শিদাবাদের পলাশি যুদ্ধক্ষেত্রে সারা ভারতবর্ষের ভাগ্য বিপর্যয়ের সূচনা হলো। ১৭৫৭-র ১৫ জুলাই মুর্শিদাবাদের পুতুল নবাব মীরজাফর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গে একটি অসম ও অসম্মানজনক চুক্তিতে চব্বিশ পরগনার জমিদারি স্বত্ব কোম্পানির হাতে তুলে দিলেন। যেহেতু মুর্শিদাবাদ এবং কলকাতার সংযোগ-পথে বারাসাত অবস্থিত, তাই বাণিজ্যিক এবং সাম্রাজ্য সম্প্রসারণের প্রাথমিক প্রক্রিয়া—প্রতিযোগিতা-য়, উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার গুরুত্ব অস্বীকার করার কোনও উপায় ছিল না। জেলার ইতিহাসে আরম্ভ হলো আর এক অধ্যায়। ইতিহাসকারেরা এই সময়কে জল বিভাজিকা রেখা হিসাবে নির্দিষ্ট করে ভারতে আধুনিক যুগের প্রবর্তনকে চিহ্নিত করেছেন। এক লহমায়, উত্তর চব্বিশ পরগনার প্রাচীন থেকে আধুনিক যুগে বিবর্তনের এই হলো সংক্ষিপ্ত রূপরেখা।
সুদূর অতীত থেকেই উত্তর চব্বিশ পরগনার ইতিহাসে শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রাণময় স্পর্শ লেগেছে। রমেশচন্দ্র মজুমদার, যদুনাথ সরকার, সরসীকুমার সরস্বতী, সুকুমার সেন, অধ্যাপক বিনয়চন্দ্র সেন, দেবপ্রসাদ ঘোষ প্রমুখ বিভিন্ন রচনায় এ প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন। চন্দ্রকেতুগড়ে প্রাপ্ত প্রত্নসামগ্রী, ডায়মন্ডহারবারের হরিনারায়ণপুরে উদ্ধার করা পোড়ামাটির কাজ, ‘দিব্যাবদান’-এ পাওয়া চতুর্থ শতাব্দীর অতি আধুনিকা মহিলার বিবরণ, ‘মহাভারত’-এর বনপর্বের কাহিনি, পাল-সেন যুগের ধ্বংসাবশেষ, শিল্প ও চিত্রকলা, বারাকপুরে বিজয় সেনের তাম্রপত্র, সুন্দরবনে লক্ষ্মণ সেনের তাম্রফলক, বৌদ্ধ এবং জৈন নিদর্শনসমূহ, মন্দির স্থাপত্য, ভাস্কর্য ইত্যাদি অভ্রান্তভাবে এই সিদ্ধান্তে আমাদের পৌঁছিয়ে দেয় যে, প্রাচীন কালে গুপ্ত সাম্রাজ্য অথবা তার অগ্রবর্তী কাল থেকেই বাংলাদেশের এই অঞ্চলে সমৃদ্ধ শিক্ষা ও সংস্কৃতির চল ছিল। এমনকি চৈনিক পরিব্রাজক তথা অন্যান্য সূত্র থেকেও প্রমাণিত যে, তাম্রলিপ্তের প্রাণস্পন্দিত শিক্ষা সংস্কৃতির সঙ্গে জল ও বন্দর পথে চন্দ্রকেতু রাজ্যের পরিচয় ও সংযোগ হয়। নীহাররঞ্জন রায় ‘বাঙালীর ইতিহাস’-এর আদি পর্বে এর ইঙ্গিত করেছেন। সুন্দরবনে বিষ্ণু ও গরুড় মূর্তি-সহ যে অভিনব তাত্রপত্রটি পাওয়া গেছে তাতে শিক্ষার জন্য আর্থিক প্রসঙ্গ রয়েছে। খ্যাতনামা বিশেষজ্ঞ বিনয়চন্দ্র সেন এবং দেবপ্রসাদ ঘোষ ‘ইন্ডিয়ান হিস্টোরিকাল কোয়ার্টার্লি’ পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে এই দুই মূর্তির রেখাঙ্কনের সঙ্গে ব্রহ্মদেশ এবং নেপালের চিত্রশৈলীর সাজুয্য লক্ষ করেছেন। এমনকি তাঁদের মত—তৎকালীন জাভা এবং বালির অনুপম ‘ওয়াং’ চিত্রাবলীর সঙ্গে, প্রত্যক্ষ না হলেও দূরতম, পরোক্ষ সম্পর্ক রয়েছে এই মূর্তির। এসব নিদর্শন ও মতামত নিশ্চিত ইঙ্গিত করে যে, প্রাচীনকালে বিদ্যাচর্চার বিভিন্ন শাখায় এই জেলা অগ্রগামী ভূমিকায় ছিল। তবে এ কথা স্মরণ রাখা জরুরি যে, সেকালে শিক্ষার সর্বজনীনতার সংজ্ঞা প্রায় অজ্ঞাতই ছিল। শিক্ষা ও সংস্কৃতিচর্চা নির্দিষ্ট শ্রেণির স্বল্পতম অংশে সীমাবদ্ধ ছিল। তার প্রসাদে সম্পূর্ণ সমাজ আলোকিত হয়ে ওঠার অবকাশ পায়নি।
মধ্যযুগে বঙ্গে মুসলমান বিজয়ের প্রাথমিক অবস্থায় নৈরাজ্য ও শৃঙ্খলাহীনতা চোখে পড়ে। বলা বাহুল্য প্রশাসন-সহ সমগ্র ব্যবস্থার পরিবর্তনের সময়ে স্থিতি ও শান্তির অভাব তো ঘটবেই! শিক্ষা ও সংস্কৃতির আঙিনাতেও তখন অস্থিরতার প্রভাব পড়েছে। কিন্তু চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীতে বেশ কয়েকজন আলোকপ্রাপ্ত শাসক গৌড়ের সিংহাসনে বসেন। যদুনাথ সরকার এ প্রসঙ্গে ইলিয়াস শাহী এবং হুসেন শাহী বংশের উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে আলাউদ্দীন হুশেন শাহ আরবি, ফারসি ছাড়াও বাংলা, পালি, প্রাকৃত ও সংস্কৃতের প্রতি আগ্রহশীল ছিলেন। হয়তো এই কারণে নবদ্বীপ, বিষ্ণুপুর ও মালদহে সংস্কৃত শিক্ষার প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে শুরু করে। অপর একটি মতে, মুসলমানি শাসনের বিরোধিতায় হিন্দু জনসাধারণ তাদের আত্ম-স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠার জন্য উত্তরোত্তর সংস্কৃত চর্চায় মন দেয়। রমেশচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত বহু খণ্ডের ‘The History and Culture of the Indian People’ গ্রন্থমালার ষষ্ঠ খণ্ডে উল্লেখ করা হয়েছে, এই সময়ে ভাগীরথীর পূর্বতীর বরাবর ব্রাহ্মণ গ্রামগুলি যেমন, মূলাজোড় ভাটপাড়া নৈহাটি হালিশহর ইত্যাদি সংস্কৃতচর্চা ও মন্দ্রিত বেদোচ্চারণে জেগে উঠতে লাগল। টোল, চতুষ্পাঠী ও গুরুগৃহ-কেন্দ্রিক গুরুকুল শিক্ষার প্রসারিত আয়োজন উত্তর চব্বিশ পরগনাকে ভারতের সনাতন শিক্ষাব্যবস্থার মানচিত্রে উজ্জ্বল স্থান করে দেয়।
ন্যায়, কাব্য, স্মৃতি, ব্যাকরণ ইত্যাদির উচ্চতম সোপানের নিরবচ্ছিন্ন পঠনপাঠনের জন্য ভট্টপল্লী বা ভাটপাড়া সারা ভারতবর্ষে স্বীকৃতি লাভ করে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সহ-সভাপতি এবং বঙ্গীয় সাহিত্যসম্মেলন-এর সভাপতি অমৃতলাল বসু ভাটপাড়াকে ‘দ্বিতীয় নবদ্বীপ’ হিসেবে উল্লেখ করেন। দীনবন্ধু মিত্র-র ‘সুরধনী’, পি. ভি. কানের ‘History of Dharmasastra’, ম্যাক্স মুলারের ‘India, what Can it Teach Us?’ এবং লুই রোনো (Louis Renou)-র ‘Sanskrit et Culture’ প্রভৃতি গ্রন্থে ভাটপাড়ার পণ্ডিত সমাজের বিবরণ পাওয়া যায়। হলধর তর্কচূড়ামণি, যদুরাম সার্বভৌম, মহামহোপাধ্যায় রাখালদাস ন্যায়রত্ন, তারাচরণ তর্করত্ন, মহামহোপাধ্যায় শিবচন্দ্র সার্বভৌম, মাণিক্যচন্দ্র তর্কভূষণ প্রমুখের নাম ভারতের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। মূলাজোড়ে একটি সংস্কৃত কলেজও প্রতিষ্ঠিত হয়। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি রাজা, মহারাজা, জমিদার ও অর্থবান শিষ্যদের দানে চলত। এইসব প্রতিষ্ঠান থেকে মহৎ কিছু কাব্য, নাটক ও শাস্ত্রগ্রন্থ রচিত হয়েছে যার স্থায়ী মূল্য সংস্কৃত ভাষায় স্বীকৃত। William Ward তাঁর ভারতত্ত্ব গবেষণায় ভাটপাড়া সহ প্রতিবেশী হালিশহর, মূলাজোড় ইত্যাদি টোলের উল্লেখ করেছেন। লক্ষণীয় গঙ্গার পশ্চিমপাড়ে শ্রীরামপুর, চুঁচুড়া, ব্যান্ডেলে মিশনারিদের প্রচারিত আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষার অভিঘাতেও সংস্কৃতচর্চা-কেন্দ্রগুলির গৌরব ক্ষুণ্ণ হয়নি। বিপ্রদাস পিপলাই-এর ‘মনসাবিজয়’ কাব্যের উল্লেখ আগেই করা হয়েছে। সুকুমার সেনের অনুমান ইনি উত্তর চব্বিশ পরগনার বাদুড়িয়ার সন্তান। তাঁর কাব্যাংশ বিভিন্ন পুথিতে সুললিত হস্তাক্ষরে লিপিবদ্ধ করে দেন—দত্তপুকুর-ছোট জাগুলিয়া অঞ্চলের একাধিক ব্যক্তি। অর্থাৎ এ কথা বলা চলে যে, সে সময় দত্তপুকুর, নিবাধই, ছোট-জাগুলিয়া, বারাসাত, বাদু-গুস্তিয়া, বাদুড়িয়া ও বসিরহাট অঞ্চলে শিক্ষার চল স্বল্প হলেও ছিল।
হুসেন শাহী রাজত্বকালে চৈতন্যদেবকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশে ভক্তিবাদ ও ভক্তি আন্দোলনের প্লাবন বয়ে যায়। এর যেমন একটি মানবিক সহজিয়া রূপ ছিল, ঠিক তেমনি গভীর অধ্যাত্মবাদ ও দর্শন চর্চারও দিক ছিল। শ্রীচৈতন্যের ক্ষমা, ভালোবাসা এবং অনুকম্পা, সর্বজীবে সম-প্রেমের আদর্শ পূর্ব-ভারতের সংস্কৃতিচেতনায় উদার মানবিকতার স্বচ্ছন্দ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে ন্যায়, নব্যন্যায়, মীমাংসা, সাংখ্য ইত্যাদি পঠনপাঠনের দ্বারও উন্মুক্ত করে। ষোড়শ শতকের প্রথমার্ধে শ্রীচৈতন্যদেব শান্তিপুর থেকে নীলাচল যাওয়ার পথে কুমারহট্টে বা বর্তমান হালিশহরে তাঁর যাত্রা ভঙ্গ করেন। তিনি গঙ্গা তীরবর্তী খড়দহ, পানিহাটি, বরানগর ইত্যাদি অঞ্চলেও সাময়িক কালের জন্য অবস্থিতি করেন। আমরা পরিচয় পাই শ্রীচৈতন্য-এর গুরু ঈশ্বরপুরীর অপরিসীম প্রজ্ঞার। শ্রীচৈতন্যের পরম স্নেহাস্পদ ছাত্র শ্রীনিবাস পণ্ডিত কুমারহট্টে চতুষ্পাঠী স্থাপন করে বিদ্যাদানে ব্রতী হন। প্রখ্যাত ভাগবত-শাস্ত্রী আচার্য রঘুনাথ, যিনি ‘কৃষ্ণতরঙ্গিনী’ কাব্যের রচয়িতা, বরানগরে থাকতেন। শ্রীচৈতন্যের শিষ্য নিত্যানন্দ খড়দহে শ্রীপাট স্থাপন করে বৈষ্ণব শাস্ত্রের পঠনপাঠন ও প্রচারে মন দেন। কাঞ্চনপল্লী বা বর্তমান কাঁচড়াপাড়ায় বাস করতেন চৈতন্যভক্ত শিবানন্দ সেন। তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র পরমানন্দ, ‘কবিকর্ণপূর’ নামেই পরিচিত। প্রকৃত তথ্য না পাওয়া গেলেও অনুমান করা হয় যে, পরমানন্দের জন্ম সম্ভবত ১৫১৬ থেকে ১৫২০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে। বালক বয়সেই তিনি মহাপ্রভুর দর্শন লাভ করেন। সংস্কৃত ভাষায় রচনা করেন ‘চৈতন্যচন্দ্রোদয়’, ‘চৈতন্যচরিতামৃত’ প্রভৃতি নাটক ও কাব্যগ্রন্থ।
মধ্য-সপ্তদশ শতক থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত, বাংলা সাহিত্য সৃষ্টিতে উত্তর চব্বিশ পরগনায় নবযুগের উচ্ছ্বসিত প্রাণস্পন্দন ধরা পড়ে। প্রচলিত লোককথা ও পাঁচালি নামের সংকীর্ণ পরিসর থেকে ষষ্ঠী, শীতলা, দক্ষিণরায়ের বহুশ্রুত কাহিনিকে মঙ্গলকাব্যে উন্নত করেন বেলঘড়িয়ার অন্তর্গত নিমতা গ্রামের কবি কৃষ্ণরাম দাস। তাঁর রচিত ‘কালিকামঙ্গল’, ‘ষষ্ঠীমঙ্গল’, ‘রায়মঙ্গল’, ‘শীতলামঙ্গল’ এবং ‘লক্ষ্মীমঙ্গল’ বাংলা মঙ্গলকাব্যে অক্ষয় সংযোজন হিসাবে আদৃত হয়। মাত্র কুড়ি বছর বয়সে কবিতা রচনায় হাত দিয়ে মূল্যবান সামাজিক এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও সম-ভাবনার উত্তরাধিকার রেখে গেলেন কবি কৃষ্ণরাম দাস ‘রায়মঙ্গল’ কাব্যে। কবির কল্পনায় বিশ্বকে বাঁচাতে শ্রীকৃষ্ণ এবং মহম্মদ একসাথে ধরাধামে অবতীর্ণ হয়ে অন্যায়, অসাধুতা ও হিংসার বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন। লোক-প্রচলিত উপায়ে তখনকার চিন্তাশীল ব্যক্তিরা সামাজিক সুস্থতা ও সাম্প্রদায়িক মিলন সাধনের উদ্দেশ্যে কাজ করেছেন। হিন্দুর সত্যনারায়ণ এবং মুসলমানের মানিক পির এই উদ্যোগের ফলেই সত্যপির-এ রূপান্তরিত হয়ে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের পূজা পেয়েছেন। উত্তর চব্বিশ পরগনা পাঁচালি, লোককথা ও মঙ্গলকাব্যের আঙিনায় ধর্মভেদশূন্য অখণ্ড মানবিকতার স্বপ্ন সৃষ্টি করেছে।
অষ্টাদশ শতকের অসামান্য কবি রামপ্রসাদের জন্ম হালিশহরে ১৭১৮ খ্রিস্টাব্দে। তাঁর সংগীত গভীর অধ্যাত্মবাদ ও দর্শনচিন্তার স্বচ্ছ স্রোতে স্নাত। তিনি সংস্কৃত, ফারসি ও হিন্দি জানতেন, কৃষ্ণনগর রাজদরবার তাঁকে ‘কবিরঞ্জন’ উপাধি দান করে। তিনি অসংখ্য শাক্তসংগীত রচনা করলেও, মুখ্যত খ্যাত ‘বিদ্যাসুন্দর’ কাব্যের জন্য। এছাড়া তাঁর ‘কালীকীর্তন’, ‘শিবসংকীর্তন’ এবং ‘কৃষ্ণকীর্তন’ও সুর ও ছন্দের যাদুতে অতুলনীয়। রামপ্রসাদের অসাধারণ উচ্চারণ ‘এমন মানব জমিন রইল পতিত/আবাদ করলে ফলত সোনা’—চিরকালীন সত্যের দ্যুতিতে মানব মহিমা প্রকাশ করে যাবে। কবীর থেকে লালন ফকির হয়ে রবীন্দ্রনাথ সমস্ত মানব-প্রেমিক স্রষ্টার মনের কথা তাঁর কবিতায় জেগে উঠেছে। এডওয়ার্ড জে. থম্পসন এবং আর্থার মার্শম্যান স্পেনসার রামপ্রসাদের কবিতা এবং সংগীতের যে নির্বাচিত অংশের অনুবাদ প্রকাশ করেছেন তার ভূমিকায় তাঁরা বলেছেন: রামপ্রসাদ দেশের মাটি থেকে বৃক্ষের মতো শুষে নিয়েছিলেন জীবনরস এবং তাই পরিবেশন করেছেন কাব্যের ছন্দে, ‘from the soil and of the soil’, তাঁর বক্তব্য নিবিড় ভালোবাসা মাখানো, সাধারণের অন্তরে যা সহজেই স্থান করে নেয়। ‘He speaks directly to the heart’ তাই ‘Ramprasad may be regarded as a national poet.’—সাহিত্যকে মহিমান্বিত করেছেন রামপ্রসাদ।
বঙ্গে মুসলমানি শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর দেশজ জনগোষ্ঠীর ধর্মবিন্যাসে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে। রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও বিবিধ কারণে সুন্দরবন সন্নিহিত অঞ্চল থেকে হাসনাবাদ, বসিরহাট হয়ে বারাসাত পর্যন্ত বিশাল অঞ্চলের অন্ত্যজ ও অবহেলিত শ্রেণির মধ্যে ইসলাম ধর্ম গ্রহণের প্রবণতা দেখা দেয়। মক্তব, মাদ্রাসার মাধ্যমে ইসলামি শিক্ষার প্রবর্তন ঘটে।
উত্তর চব্বিশ পরগনায় তখনও পর্যন্ত অবশ্য ইসলামি শিক্ষার উৎকর্ষ প্রমাণের অবকাশ হয়নি। তবে প্রশাসনের কাজকর্মে ফারসির চলন ত্বরান্বিত হওয়ায় ফারসি শিক্ষার আগ্রহ তৈরি হয়। যাই হোক, ভাটপাড়া-কেন্দ্রিক সংস্কৃত শিক্ষা চর্চার সমতুল বা সমান্তরাল ইসলামি শিক্ষাকেন্দ্র এ জেলায় কোনওদিন গড়ে ওঠেনি। তবে মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে অধিকাংশই ধর্মান্তরিত-হিন্দু হওয়ার কারণে হিন্দুর লৌকিক দেবদেবতা, বনবিবি, ওলাইচণ্ডী, মনসা ইত্যাদি পির এবং গাজির গানে নববেশে অত্মপ্রকাশ করে। পির এবং গাজির গান বাংলার মাটি, জল, আকাশের আলোয় ভরা। সে সব গানেও মিলনের সুর, সমাজ সমন্বয়ের আকাঙ্ক্ষা ধ্বনিত। বাংলা সাহিত্যে পির-গাজির গান অমূল্য সংযাজন। ধর্মের কৃত্রিম বেড়াজাল ও নিষেধ অগ্রাহ্য করে মানবিকতা ও মনুষ্যত্বের সত্যমূল্য অন্বেষণে তারা ব্যাপৃত।
পলাশি বিজয় গোটা ভারতবর্ষের শাসনভার ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বণিকদের হাতে তুলে দেবে—এমন আশা তারা হয়তো করেনি। কিন্তু ইতিহাসের পরিহাস বণিককে মানদণ্ডের সঙ্গে রাজদণ্ডও ধরতে হলো। রাজ্যশাসনের জন্য অনুগত কর্মী দরকার, আরও দরকার ভাষা-সড়ক নির্মাণ, যাতে প্রাত্যহিক প্রশাসন পরিচালনা সহজ হয়। এদেশে সরকারি দৃষ্টিতে ইংরেজি শিক্ষার গোড়ার কথা এইটুকুই। মেকলে যথেষ্ট রূঢ়তার সঙ্গে বাস্তব সত্যটির ব্যাখ্যা দিয়েছেন—শিক্ষা বিষয়ক তাঁর ব্যবস্থা পত্রে। তবে, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে তার নিজস্ব বিলিতি কর্মচারীদের জন্যে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ তৈরি করলেও, ভারতীয়দের শিক্ষার জন্য ভাবনাটা খ্রিস্টীয় যাজক ও মিশনারি সম্প্রদায়ের হাতেই ছেড়ে দেয়। তারাও দূরদূরান্তে; অরণ্য, পর্বত, সমুদ্রের বাঁধা ডিঙিয়ে খ্রিস্টের নামপ্রচারে বেড়িয়ে পড়ে, সঙ্গে শিক্ষার কর্মসূচি। উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলায় ইংরেজি-আশ্রিত পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রবেশ ও প্রসার এইভাবেই হয়েছে। এর আগে পাঠশালা ও মক্তব-কেন্দ্রিক যে শিক্ষা ছিল—তার শোচনীয়তার চেহারা আমরা উইলিয়ম অ্যাডাম্স-এর ‘রিপোর্ট্স অন দ্যা স্টেট অব্ এডুকেশন ইন বেঙ্গল’ প্রতিবেদনে দেখেছি। কোনওরকমে অক্ষরজ্ঞান, নামসই, নামতা মুখস্থ, সরল যোগ-বিয়োগ ও চাণক্য শ্লোক আওড়ানোতেই সে শিক্ষার অবসান।
এম. এ. লেয়র্ড-এর ‘মিশনারিশ অ্যান্ড এডুকেশন ইন বেঙ্গল’ গ্রন্থটি অন্যান্য জেলার সঙ্গে তদানীন্তন চব্বিশ পরগনা জেলায়, পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রথম অভিসার পর্বের বিবরণ দিয়েছে। লেয়র্ড উল্লেখ করেছেন, ‘চার্চ মিশনারি সোসাইটি’র (CMS) অ্যাঙলিক্যান পাদরিরা কলকাতা, খিদিরপুর, বজবজের দিকে তো গিয়েইছিলেন, এছাড়াও দমদম থেকে বারাসাত পর্যন্ত এলাকায় তাঁরা মোট চারটি স্কুল স্থাপন করেন। তিনি এও বলেছেন, স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁদের উদ্যোগকে স্বাগত জানান এবং ইংরাজি শেখানোর জন্যে, পাদরিদের অনুরোধও করেন। ‘লন্ডন মিশনারি সোসাইটি’ ১৮২৩ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় কাজ শুরু করে চব্বিশ পরগনার উত্তর ও দক্ষিণ উভয় প্রান্তেই ছড়িয়ে পড়ে, বাদুড়িয়ায় তারা প্রাথমিক শিক্ষার একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে। ‘Society for Promoting Christian Knowledge’-এর কলকাতা শাখার বিশেষ অনুরোধে, গভর্নর জেনারেল মার্কুইস হেস্টিংস-এর স্ত্রী লেডি লাউডন, বারাকপুরের লাটবাগানের ভেতরে, ১৮১৫ খ্রিস্টাব্দে একটি বিদ্যালয় চালু করেন। প্রথাগত বিদ্যার বদলে, এখানে নীতি ও চরিত্র গঠনের শিক্ষার ওপর জোর দেওয়া হয়। ১৮১৬ খ্রিস্টাব্দে ‘চার্চ মিশনারি সোসাইটি’ বারাসাতে একটি বিদ্যালয়ের উদ্বোধন করে। ব্রাহ্মণ-প্রধান এই অঞ্চলে পাদরিদের স্কুলে বাড়ির ছেলেদের পড়তে পাঠানোর খুব একটা তাগিদ অবশ্য তখন ছিল না। ১৮৩৭ সালে বারাসাতে তারা আরও একটি স্কুল খোলে। স্কটিশ মিশনারিরা টাকি গ্রামে ওই বছরেই নতুন একটি স্কুল চালানোর পরিকল্পনা নেয়।
সেকালের চিন্তাশীল ও দেশানুরাগী মুষ্টিমেয় মানুষ খ্রিস্টীয় ধর্মযাজকদের বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উৎসাহের মধ্যে অন্য কোনও গোপন উদ্দেশ্য সাধনের আশঙ্কা করেন। তাঁরা মনে করেন, যাজকদের লক্ষ্য হচ্ছে খ্রিস্টধর্মের সম্প্রসারণ। হিন্দু ধর্ম নানা কুসংস্কার ও আচারবিচারে আচ্ছন্ন। এ ধর্মের সংস্কার যেমন দরকার, ঠিক তেমনি খ্রিস্টধর্মের আগ্রাসন থেকে তাকে রক্ষা করাও আমাদের কর্তব্য। রাজা রামমোহন রায় ও তাঁর অনুগামীরা এই মানসিকতা নিয়ে বিদ্যালয় স্থাপনে আগ্রহী হন। তাঁদের আরও একটি উদ্দেশ্য ছিল, পশ্চিমের আধুনিক শিক্ষার বিস্তার। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর যুক্তি ও বুদ্ধির মুক্ত চর্চার মাধ্যমে ঈশ্বরের স্বরূপ সন্ধানের উদ্দেশ্যে জোড়াসাঁকোর বাড়িতে ‘তত্ত্ববোধিনী সভা’ গঠন করেন। পরে পাদরিদের হাত থেকে বাংলার শিক্ষাকে বাঁচাবার বিকল্প হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হলো—তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা। কিন্তু কলকাতায় স্কুলটি ভালোভাবে চলল না বলে হুগলি জেলার বাঁশবেড়িয়ায় সেটিকে স্থানান্তরিত করা হয়। উত্তর চব্বিশ পরগনার পানিহাটিতেও একই উদ্দেশ্যে এইরকম আরেকটি স্কুল প্রতিষ্ঠিত হলো।
জেলায় সে সময় শিক্ষার তিনটি পৃথক-স্রোত বহমান। ভাটপাড়াকে কেন্দ্র করে টোল-চতুষ্পাঠী কেন্দ্রিক শিক্ষা, খ্রিস্টীয় ধর্মযাজকদের বিদ্যালয় এবং তত্ত্ববোধিনী ধাঁচের বিকল্প ধারার বিদ্যালয়। চতুর্থ ধারাটি, অর্থাৎ মক্তব-মাদ্রাসা কেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থা মুসলিম জনসংখ্যার আধিক্য সত্ত্বেও খুবই অপুষ্ট এবং ক্ষীণ ছিল।
ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ওপর নির্ভরশীল না থেকে, ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে এদেশীয়দের উদ্যোগে গরানহাটায়, ৩০৪ নং চিৎপুর রোডে, একটি ভাড়া বাড়িতে হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা হয়। ডেভিড হেয়ার, মি. হাইডের মতো জ্ঞান চর্চায় উৎসাহী ইংরেজরা এই উদ্যোগকে সবরকম সহায়তা দেন। হিন্দু কলেজ স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় যেন নতুন দিগন্ত খুলে গেল, সূচনা হলো নবযুগের, নব জাগরণের। ঘুম ভাঙল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিরও। ১৮২৩ খ্রিস্টাব্দের ৩১ জুলাই কোম্পানি একটি কমিটি গঠন করল—’General Committee of Public Instruction’ ১৮৩৫-এ মেকলে তার সভাপতি হলেন। ভারতবাসীদের সম্পর্কে অনেক রূঢ, কটু মন্তব্যসহ তিনি ইংরেজিকে বাহন করে পাশ্চাত্য শিক্ষার সুপারিশ করলে, গভর্নর জেনারেল বেন্টিঙ্ক তা গ্রহণ করলেন। মেকলে নব্যশিক্ষিত ভারতীয়দের নিয়ে একটি স্বতন্ত্র শ্রেণি তৈরির কথা ভেবেছিলেন—‘…a class of persons Indian in blood and colour, but English in tastes, opinions, in morals and in intellect.’—আর রাজা রামমোহনের রায়ের মতো উদারপন্থী ভারতীয়রা ভেবেছিলেন, ‘উচ্চস্তরের লোকেরা ইংরেজির মাধ্যমে লব্ধ জ্ঞান তাহাদের মাতৃভাষার মারফৎ সাধারণের মধ্যে ছড়াইয়া দিবে।’—একেই বলা হয়েছিল—‘ফিল্টারেশন থিয়োরি’।
ইতোমধ্যে, কলকাতায় নতুন নতুন স্কুল খোলার উদ্যোগ আয়োজন শুরু হয়ে গেছে। যে দীপশিখা ২০ জানুয়ারি হিন্দু কলেজ স্থাপনের মধ্য দিয়ে জ্বলে উঠেছে, তার থেকে শক্তি, সাহস ও তাপ সঞ্চয় করে বিন্দু বিন্দু নক্ষত্রের মতো আশপাশে স্কুল গড়ে উঠল। ‘চার্চ অব স্কটল্যান্ড মিশন’-এর সহায়তায়, কলকাতায় ডাফ্ সাহেব একটি স্কুলে খুললেন। রামমোহন নিজস্ব অর্থ ও আদর্শ সম্বল করে প্রতিষ্ঠা করলেন অ্যাংলো-হিন্দু স্কুল। ১৮২৭ এবং ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দে যথাক্রমে সংস্কৃত কলেজ ও কলকাতা মাদ্রাসায় ইংরেজি পঠনপাঠনের জন্য স্বতন্ত্র বিদ্যালয় খোলা হলো। ডেভিড হেয়ার তৈরি করলেন তাঁর নিজের স্কুল। প্রতিষ্ঠিত হলো জগমোহন বসু-র ইউনিয়ন স্কুল, গৌরমোহন আঢ্যর ওরিয়েন্টাল সেমিনারি, জেনারেল অ্যাসেম্বলিজ্ ইনস্টিটিউশন ইত্যাদি।
হিন্দু কলেজের প্রেরণার বাণী কলকাতার মধ্যেই শুধু সীমাবদ্ধ থাকল না। উত্তর চব্বিশ পরগনার জনজীবনেও সে-ই শিহরনের, শিক্ষার সংকেত পৌঁছে গেল, অনতিকালের মধ্যে। কলকাতার প্রতিষ্ঠিত মধ্যবিত্ত এবং বুদ্ধিজীবীরা প্রায় সকলেই আশপাশের জেলা থেকে আগত মানুষ। এঁরাই হিন্দু কলেজের বার্তা নিয়ে গেলেন—নিজ নিজ গ্রাম, জেলায়। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্য বিস্তার চলতে থাকল, তার সঙ্গেই নিঃশব্দে চলল বিদ্যা বিস্তারের দেশজ আয়োজন। দেশজ বলছি এই কারণে যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কোম্পানির কানাকড়ি সাহায্য না পেয়েও, নিজেদের উদ্যম এবং পরিশ্রম সম্বল করে আধুনিক শিক্ষার এক একটা চলনসই কাঠামো এঁরা তৈরি করলেন, জেলার নানা প্রান্তে।
ইংরেজি শিক্ষা প্রসারের জন্যে উত্তর চব্বিশ পরগনার প্রথম স্কুলটি স্থাপিত হয় টাকিতে, ১৮৩২ খ্রিস্টাব্দের ১৪ জুন। প্রতিষ্ঠাতা রাজা রামমোহন রায়ের একান্ত অনুরাগী ও অনুগামী জমিদার মুনশি কালীনাথ রায়চৌধুরী। কালীনাথকে স্বগ্রামে ইংরেজি স্কুল খোলার পরামর্শ দিয়েছিলেন রামমোহন, দ্বারকানাথ এবং আলেকজান্ডার ডাফ্। সতীশচন্দ্র রায়চৌধুরী ‘বঙ্গীয় সমাজ’ গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন, ‘টাকির ও তন্নিকটবর্তী গ্রামনিচয়ের বর্তমান সময়ের বহুতর ব্যক্তির পিতাপিতামহগণ কালীনাথ স্থাপিত সেই স্কুলে অধ্যয়নপূর্বক বিদ্যালাভ করিয়া বিত্ত সঞ্চয় করিয়া গিয়াছেন।’ সেকালের সংবাদপত্রগুলিতে কালীনাথের এই মহৎ প্রয়াস সমাদৃত হয়েছিল। ‘সমাচার দর্পন’, ৩০ জুন ১৮৩২ সংখ্যায় লেখে: ‘আমরা অত্যন্তাহ্লাদাপূর্বক পাঠক মহাশয়রদিগকে জ্ঞাপন করিতেছি যে কলকাতা নগর হইতে প্রায় বিংশতি ক্রোশ অন্ত সমৃদ্ধ টাকি স্থানে এতদ্দেশীয় বালকদের দ্বারা বিদ্যা শিক্ষার্থ এক বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে।’ স্কুলটি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার এক সপ্তাহের মধ্যে ৩৪০ জন ছাত্র ভর্তি হয়।
জেলার পরবর্তী বিদ্যালয়টি বারাকপুরে ১৮৩৭ খ্রিস্টাব্দে স্থাপিত হলো। বারাকপুরে গঙ্গার ধারে লাটসাহেবের বাগানবাড়ি। তিনি মাঝে মাঝে বারাকপুরে আসতেন বিশ্রাম নিতে। আমরা লর্ড অকল্যান্ডের কথা বলছি। তাঁরই নির্দেশে লাটবাগান সন্নিহিত অঞ্চলে বিদ্যালয়ের স্থাপনা হলো। লাটবাগানের কর্মচারীদের পুত্রকন্যার শিক্ষার এই আয়োজনকে সাধারণের মধ্যে সম্প্রসারিত করার জন্য বিনামূল্যে বই খাতা দেওয়া হতো। স্কুলে পড়বার জন্য বেতন লাগতো না। লাটবাহাদুরের নজর ছিল বলে, এই স্কুলের অনেক ছাত্র উচ্চতর শিক্ষার সুযোগ পেতো।
তৃতীয় বিদ্যালয়, ক্রাইস্ট চার্চ স্কুল পানিহাটির আগড়পাড়া অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৩৮ খ্রিস্টাব্দে। কৃশানু ভট্টাচার্য-র ‘পানিহাটি পরিক্রমা’ গ্রন্থ থেকে জানা যায় ১৮৩২-এর ৪ আগস্ট আকস্মিক প্লাবনে পানিহাটি বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। একটি অনাথ আশ্রমের ১৩০ জন বালককে নিয়ে ‘বঙ্গীয় খ্রিস্টধর্ম বিতরণকারী’ সম্প্রদায়ের মেরী অ্যান উইলস্ন তখন বিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনা করেন। বিদ্যালয়টি ১৮৫৪ সাল পর্যন্ত ছিল অবৈতনিক। তবে, ইতোমধ্যে ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে, রেললাইনের পূর্বদিকে, আমবাগানের মধ্যে, মুলি বাঁশের বেড়ায় ঘেরা একটি আটচালা ঘরে সোদপুর হাই স্কুলের প্রতিষ্ঠা হয়েছে, গ্রামের জমিদার ঈশ্বরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের তৎপরতায়। পানিহাটির জমিদার রায়চৌধুরীদের নাচঘরে একটি স্কুল ও সুখচরে তারকনাথ সেন প্রতিষ্ঠিত আরও একটি স্কুলের সন্ধান পাওয়া গেলেও, সে বিষয়ে বিশদ তথ্যের অভাব রয়েছে। ১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দে বরানগরে একটি স্কুল খোলেন রামরতন রায়, কালীনাথ রায়চৌধুরী ও প্রাণনাথ রায়চৌধুরী। টাকির রায়চৌধুরী বংশের কলকাতার বাসস্থান ছিল বরানগরে। টাকির রায়চৌধুরীরা তাই বরানগরেও শিক্ষা বিস্তারে উদ্যোগী হন।
জেলার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিদ্যালয়টি স্থাপিত হলো বারাসাতে। বারাসাত তখন কয়েক ঘর ব্রাহ্মণ অধ্যুষিত গণ্ডগ্রাম। ‘সমাচার দর্পণ’-এর ৫ শ্রাবণ ১২৪৬ বঙ্গাব্দ সংখ্যায় জানা যায়, ১৮৩৯ সালের জুলাই মাসে বারাসাতের কিছু বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি জমিদার প্রাণকৃষ্ণ মিত্রের বাড়িতে একটি সভা করে বারাসাতে উচ্চবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার তোড়জোড় শুরু করেন। অবশেষে জেলাশাসক চার্লস বিন্নি ট্রেভর-এর সহযোগিতায় একটি সরকারি স্কুল স্থাপিত হয় ১৮৪৬ সালের ১ জানুয়ারি। প্রথম প্রধান শিক্ষক, বিদ্যাসাগর-বান্ধব, প্যারীচরণ সরকার। স্কুলটি প্রথমে জেলখানার খানকয় ঘরে শুরু হয়। পরে প্যারীচরণের উদ্যোগে স্কুল বাড়ি নির্মিত হলো। বারাসাতেই প্রথম দূরবর্তী ছাত্রদের জন্য ছাত্রাবাস নির্মিত হয়। প্যারীচরণ বিদ্যালয়ের মধ্যেই উদ্যান ও কৃষি বিদ্যালয় চালু করেন। বৃত্তিমূলক শিক্ষারও প্রথম উন্মেষ বারাসাতেই। বিদ্যাসাগর ও প্যারীচরণ, দুই অভিন্ন হৃদয় বান্ধব একই সময়ে যথাক্রমে বাংলা ‘বর্ণপরিচয়’ ও ইংরেজি ‘First Book’ রচনায় হাত দেন। পরবর্তীকালে সমগ্র উপনিবেশের ইংরেজি শিক্ষার প্রারম্ভিক পুস্তকটির সঙ্গে বারাসাত স্কুলের স্মৃতি জড়িয়ে আছে। এই স্কুলের ছাত্রদের মধ্যেই বইটির প্রথম পাঠ শুরু হয়।
বারাসাত বিদ্যালয়ের ও প্রধান শিক্ষক প্যারীচরণের প্রশংসায় লেখা হয়—”…(Barasat School) soon attained a high position among the schools in Bengal. This early success was due to the able and preserving labours of Babu Peary Charan Sarkar.” (‘Report on Public Instruction’)—বারাসাতের স্কুলে রামতনু লাহিড়ী এবং মদনমোহন তর্কালঙ্কারও শিক্ষকতা করেছেন। উল্লেখ্য এই বিদ্যালয় থেকে এমন সব ছাত্র শিক্ষা সমাপ্তিতে নিজেদের জীবনে অন্যান্য কাজে ব্রতী হয়েছেন, যাঁরা দেশের সারস্বত ও অধ্যাত্মজীবনে তাঁদের প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। যেমন, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী শিবানন্দ-এর নাম স্মরণযোগ্য। সার্ধশতবর্ষে বিদ্যালয়টির নামের সঙ্গে প্রতিষ্ঠাতা প্রধান শিক্ষক প্যারীচরণ সরকারের নামটি সংযুক্ত হয়েছে।
এদেশীয়দের উদ্যোগে প্রথম বালিকা বিদ্যালয়টি উত্তর চব্বিশ পরগনার বারাসাতে প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৪৭ খ্রিস্টাব্দে। ইতোমধ্যে চুঁচুড়া, ব্যান্ডেল সহ কলকাতার নানা জায়গায় খ্রিস্টান যাজকেরা বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেও ছাত্রীর অভাবে তা চালাতে পারেনি। বারাসাতে, তিন বন্ধু: কালীকৃষ্ণ, প্যারীচরণ ও বিদ্যাসাগর বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনে সফল হলেন। এঁদের উদ্যোগকে আন্তরিক সহায়তা দেন তদানীন্তন ম্যাজিস্ট্রেট মি. চার্লস বিন্নি ট্রেভর। এঁরা কেউই বারাসাতের ভূমিপুত্র ছিলেন না। কিন্তু, বারাসাতের ভূমিতেই তাঁরা শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ ইতিহাস রচনা করে গেলেন। কালীকৃষ্ণের দাদা, নবীনকৃষ্ণ মিত্র, কলকাতা মেডিকেল কলেজের প্রথম ছাত্রদলের একজন। তাঁর কন্যা কুন্তীবালা এই বিদ্যালয়ের প্রথম দিনের একমাত্র ছাত্রী। বারাসাতের গোঁড়া ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায়ের একাংশ বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় সর্বনাশ হবে আশঙ্কা করে বিদ্যালয়টিকে অঙ্কুরেই বিনাশ করার তোড়জোড় শুরু করেন। প্যারীচরণ ও কালীকৃষ্ণের প্রাণনাশেরও চেষ্টা হয়। ‘সমাচার দর্পণ’-এর দর্পনে ধরা পড়েছে সে সময়কার নানা অত্যাচারের কথা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, লেয়ার্ড তাঁর গ্রন্থে বলেছেন—”charges of assault, suits of arrears of rent and complaints of all kinds and character were brought against the parents of those who sent their daughters to the school.”
এই অশুভ তৎপরতা বিদ্যালয়টির ক্ষতি করলেও, বিনাশ করতে পারল না। নারীশিক্ষা প্রসারে অন্যান্যদের উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে মদনমোহন তর্কালঙ্কার ‘স্ত্রীশিক্ষা’ শীর্ষক একটি প্রবন্ধে লেখেন—”এক বৎসর অধিককাল গত হইল কন্যাসম্তানদিগের শিক্ষা নিমিত্ত এই মহানগরীতে এবং বারাসাতে ও অন্যান্য কতিপয় স্থানে শিক্ষাস্থান সংস্থাপিত হইয়াছে। এই শ্রেয়স্কর বিষয় সর্বত্র প্রচারিত করিবার নিমিত্ত কএকজন, মহাত্মা প্রথমতঃ দৃষ্টান্ত স্বরূপ হইয়া আপন আপন কন্যাসন্তানদিগকে তত্তৎ পাঠস্থানে নিয়োজিত করিয়াছেন। ঐ ভদ্রমহাদয়েরা সর্বদাই মনের মধ্যে এইরূপ প্রত্যাশা করেন যে স্বদেশস্থ সমস্ত ভদ্র ব্যক্তিই তাঁহাদের দৃষ্টান্তের অনুবর্তী হইয়া স্ব স্ব কন্যাগণের অধ্যয়ন সম্পাদনের যত্নপূর্বক প্রবৃত্ত হন।” লেখাটি প্রকাশিত হয় ১৮৫১ খ্রিস্টাব্দে ‘সর্ব্বশুভকরী পত্রিকা’য়। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও মদনমোহন তর্কালঙ্কার সমাজ সংস্কারের হাতিয়ার হিসাবে পত্রিকাটির প্রকাশ শুরু করেন।
১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে বারাসাত পৌরসভা বিদ্যালয়টিকে স্বীকৃতি দেয়। কালীকৃষ্ণের মৃত্যুর পর বিদ্যালয়টি ‘কালীকৃষ্ণ বালিকা বিদ্যালয়’ নামে পরিচিত হলো। বারাসাত অ্যাসোসিয়েশন প্রদত্ত জমির ওপর নির্মিত বিদ্যালয়ের সুরম্য অট্টালিকার সামনে দাঁড়িয়ে আজ হয়তো অতীত সংগ্রামের সে-ই স্মৃতির কোনও আভাসই পাওয়া যাবে না। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর ‘মালঞ্চ’ নামক লেখাটিতে এই বালিকা বিদ্যালয়ের ইঙ্গিত দিয়েছেন। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ‘সেই সময়’ গ্রন্থে সমাজ পরিবর্তনের সংগ্রাম ও কালীকৃষ্ণ বালিকা বিদ্যালয়ের উদ্ভব নিয়ে আলোচনা করেছেন। তসলিমা নাসরিন, বাংলাদেশের পত্র-পত্রিকায় তাঁর নিজস্ব কলমে, নারীশিক্ষার প্রসার বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গেও উল্লেখ করেছেন কালীকৃষ্ণ বালিকা বিদ্যালয়ের।
প্রাপ্ত তথ্যমতে আমরা জানি, ১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দে, বারাসতের নিকটবর্তী নিবাধই গ্রামে কালীকৃষ্ণ দত্ত ও গ্রামস্থ অন্যান্য বিদ্বোৎসাহী ব্যক্তিদের প্রচেষ্টায় আর একটি বালিকা বিদ্যালয়ের যাত্রা শুরু হয়। যে বিরোধিতার বিবরণ বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনে ইতিপূর্বে ‘সমাচার দর্পণ’ পত্রিকা সহ অন্যান্য গ্রন্থে বিধৃত তার অনেকটাই প্রশমিত এক্ষেত্রে। বরং বলা যায় দত্তপুকুর গ্রাম সক্রিয় সহযোগিতায় বিদ্যালয় গড়ে তোলার কাজে এগিয়ে আসে। প্যারীচরণ সরকার এবং কালীকৃষ্ণ মিত্রের সূত্রে বিদ্যাসাগরের বারাসাত সংলগ্ন গ্রাম সমূহে যাতায়াত ছিল (প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়, উত্তর চব্বিশ পরগনাবাসীরা; বিশেষত বারাসাত, দত্তপুকুর, নিবাধই, বাদু-গুস্তিয়া গ্রামের অনেকে বিদ্যাসাগর প্রদত্ত বিধবা বিবাহের আবেদনপত্রে সই করেছিলেন)। নিবাধই গ্রামের কালীকৃষ্ণ দত্তের সঙ্গেও পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের পরিচয় ছিল। সংযোগ ছিল মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং বেথুন সাহেবের সঙ্গেও। তাঁদের ঐকান্তিক আগ্রহ ও সহযোগিতা কালীকৃষ্ণ দত্ত-র উদ্যোগকে দৃঢ় এবং ফলপ্রসূ করতে সহায়ক হয়।
‘আনন্দবাজার পত্রিকা’র ‘রবিবাসরীয়’ ক্রোড়পত্রে (৫ মার্চ ২০১৭) ‘সাবিত্রীর শিক্ষাব্রত’ শীর্ষক লেখায় স্বাতী ভট্টাচার্য যদিও মন্তব্য করেন, এদেশে ‘প্রথম’ বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে ১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দে। তাঁর এ মন্তব্যকে তথ্যভ্রান্তি বা ‘অজ্ঞতা’ কীরূপে বর্ণনা করা উচিত তা পাঠকের বিবেচনাধীন।
১৮৬৩ (মতান্তরে ১৮৬২) খ্রিস্টাব্দে জেলার পরবর্তী বালিকা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হলো বসিরহাটের অন্তর্গত টাকি গ্রামে। রক্ষণশীল পরিবারগুলি বিশেষ উৎসাহ না দেখালেও, টাকির রায়চৌধুরী বংশের ভূপেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে বিশেষ উৎসাহী হন এবং টাকির বিচক্ষণ ও বর্ধিষ্ণু ব্যক্তিদের নিয়ে এ কাজে এগিয়ে আসেন। টাকির লালমাধব রায়চৌধুরী ও ষষ্ঠীবর রায়চৌধুরী-র নাম এ বিদ্যালয়টির সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে ষষ্ঠীবর লালমাধব উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় নামে বর্তমানে পরিচিত।
আঠারো-উনিশ শতকে বাংলার সামগ্রিক শিক্ষাব্যবস্থার প্রায়-বিশ্বস্ত চিত্র পাওয়া যায় ১৮৭৫ সালে লন্ডন থেকে প্রকাশিত, W.W. Hunter লিখিত ‘A Statistical Account of Bengal’ গ্রন্থে। এই দুই শতকে বর্তমান উত্তর চব্বিশ পরগনার শিক্ষার ইতিহাস জানতে হলে হান্টারের বিবরণ প্রায় তথ্যের আকর-গ্রন্থের কাজ করে। হান্টার অবশ্য তদানীন্তন ‘ইনসপেক্টর অব্ স্কুল্স’ মি. উড্রো-র প্রতিবেদনটি গ্রাহ্য করেছেন এবং নিজের গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত করেছেন।
হান্টার, তাঁর প্রতিবেদনে ১৮৭১-৭২ সালে স্কুলের সংখ্যা ও ছাত্রছাত্রীর সংখ্যাও নির্দেশ করেছেন। যদিও সে পরিসংখ্যান উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার বিদ্যালয়গুলির মিলিত যুগ্মসংখ্যা। প্রণিধাণযোগ্য যে, হান্টার বলছেন, প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে সে সময় মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রায় পাঁচগুণ নিম্নবিত্ত পরিবারের ছেলেমেয়ে পড়ত। উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়ে যারা পড়ত তাদের প্রায় এক চতুর্থাংশই ছিল করণিক শ্রেণির বা কোম্পানি এবং অন্যান্য বণিক কুঠির কর্মচারীদের সন্তান-সন্ততি। হান্টারের মতে উনিশ শতকের অন্তিমকাল পর্যন্ত সময়ে জেলার শিক্ষিত মানুষের সংখ্যা ছিল শতকরা ১৩ জন।
বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। মধ্যবিত্তশ্রেণির মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষার আগ্রহ অনেকগুণ বাড়ে। এই সময়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য Raleigh-এর নেতৃত্বে শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়। এই কমিশনে, একমাত্র ভারতীয় সদস্য স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুপারিশগুলিকে কোনও মর্যাদাই দেওয়া হয়নি। গভর্নর জেনারেল কার্জ়ন শিক্ষার সংকোচনে বেশি আগ্রহী ছিলেন। Raleigh-এর পরামর্শ তাঁকে উৎসাহিত করে। ‘Carlyle’-এর বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে কার্জ়ন, বাংলার শিক্ষাব্যবস্থা যা ক্রমশ আরও পল্লবিত হওয়ার প্রয়াস নিয়েছিল, সে-ই সম্ভাবনার সর্বনাশ-যাত্রা শুরু করে দেন। কিন্তু সে প্রসঙ্গ এ প্রবন্ধের বিষয় নয়।