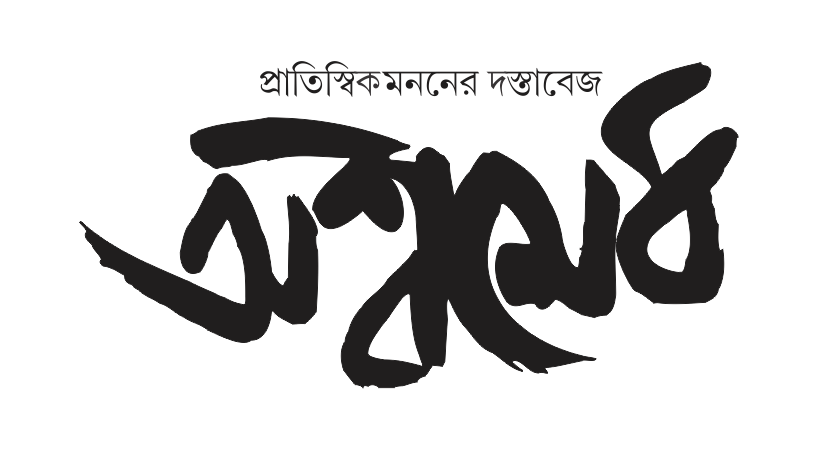নৈহাটির ‘মিডল টোন’ আয়োজিত ২০১৮ সালের সমরেশ বসু স্মারক বক্তৃতায় নির্দিষ্ট হয়েছিল শিরোনাম উল্লেখিত বিষয় এবং বক্তা হিসাবে এই নিবন্ধকার। যে বিষয় নিয়ে গোটা চার-পাঁচেক থিসিস লেখা যায়, বা যা নিয়ে অন্তত একটি বছরের পাঠদান পরিকল্পনাকেও সংক্ষিপ্ত মনে হয়, তেমনি একটি বিষয় নিয়ে একটি অতি স্বল্প সময়ের ভাষণ! এবং বক্তা হিসাবে এই নির্বাচন! সমরেশ বসু-র সাহিত্য জগৎ যেমন বিচিত্র তেমনি বিস্তৃত। তাকে ধরা যায় কীভাবে! ফলে সিলেবাস ছোট করা, করা হলো: ‘সমরেশ বসু-র ছোটগল্পের নাট্য সম্ভাবনা’—তার পরিধিও উপসাগর-সম! ফলে পথ কী! একটা উপায় এমন হতে পারে, প্রাথমিকভাবে বলা যেতে পারে নাটকীয়তা বিষয়টি কী! সাহিত্যের দু-একটি অন্য পরিসরে যেমন গান বা কবিতায় কীভাবে মুখ লুকিয়ে থাকে নাটকীয়তা, রসিক এবং আনুসন্ধিৎসুরা কীভাবে ওই কুঁড়ির সম্ভাবনাকে শনাক্ত করতে পারেন—খুব সাধারণভাবে সে-ই সম্পর্কে কিছু কথা বলা যেতে পারে। আর সমরেশ বসু-র ওই প্রায় দিকহীন আখ্যান-বিস্তারের পট থেকে নাটকীয়তার উজ্জ্বল আঁচড়গুলিকে ধরতাই হিসাবে আলোচনায় আনা, যাতে ছোটগল্পগুলো থেকে গল্পান্তরে যাওয়ার একটা পথ মেলে। এগোনো গেল সে-ই ভাবে। সে-ই প্রদত্ত ভাষণের এই লিখিত-রূপ। তবে এটাও সবারই জানা, কোনও সজীব সচল ভাষণে শ্রোতাদের প্রত্যক্ষ উপস্থিতি, তাঁদের ভাব-প্রতিক্রিয়া ইত্যাদি বক্তাকেও প্রভাবিত করে, নানা এ কথা সে-কথা যা তখন প্রাসঙ্গিক বলে মনে হয়েছিল, সে সব এই লেখায় নিয়ে আসা, বলা, পরিপ্রেক্ষিতহীন বলে মনে হতে পারে, ফলে, বাদ রাখা গেল সেগুলোকে।
২.
শ্রদ্ধেয় কুমার রায়ের প্রয়াণের পর ‘বহুরূপী’ নাট্যদল বাৎসরিক ‘কুমার রায় স্মারক বক্তৃতা‘র আয়োজন করে চলেছেন। ২০১৩ সালের সে-ই অনুষ্ঠানে প্রাবন্ধিক, অর্থনীতিবিদ শ্রী অশোক মিত্র মশাই ‘নাট্যমুহূর্ত: কিছু অগোছালো কথা’ এই শিরোনামে একটি অনবদ্য আলোচনা করেন। আমার বলা কথা-র ধরতাই হিসাবে উল্লেখ করা গেল সে-ই বক্তৃতার একটি অংশ: “আমি একটি বিশেষ চেতনা-স্তরে আছি। সেই চেতনা-স্তর থেকে যদি কোনওকিছু আমাকে হঠাৎ মস্ত ধাক্কা দিয়ে অতর্কিতে অন্য একটা চেতনা-স্তরে নিয়ে যেতে পারে, তবে এই প্রক্রিয়াটিকে বলবো নাটকীয়তা এবং সেই মুহূর্তটাকে বলবো নাট্যমুহূর্ত। আমি একটা বিশেষ উপলব্ধির স্তরে আছি। সেই স্তর থেকে হঠাৎ ধাক্কা মেরে আমাকে সম্পূর্ণ অন্য একটা স্তরে নিয়ে গেল, আমি হতচকিত! বিহ্বল! একেবারে ভেবে পাই না যে এটা কী করে হলো! কোনও একটা বিশেষ অভিজ্ঞতা-স্তর থেকে অন্য একটা অভিজ্ঞতা-স্তরে পৌঁছে গেলাম।”
এই যে চেতনার স্তর, অভিজ্ঞতার স্তরের একটা পরিবর্তনের অভিঘাত, এই নাটকীয়তা—প্রত্যেক শিল্পমাধ্যমেরই প্রধান বিবেচ্য বিষয়। কখনও যেটা প্রচ্ছন্ন, ধীর লয়ে চলতে থাকে, কখনও সেটা প্রকট, আকস্মিক। শ্রী অশোক মিত্র তাঁর, ওই বক্তৃতায় ছোটবেলায় দেখা রীতিমতো নাটক প্রযোজনার একটি অভিজ্ঞতার বর্ণনা করেছেন। টেনে এনেছেন ‘পুতুল নাচের ইতিকথা’ ‘পদ্মানদীর মাঝি’-র উদাহরণ, জীবনানন্দ দাশের ‘সেইসব শেয়ালেরা‘ কবিতার উল্লেখ, শেষে আবার এসেছে নাটক ‘রক্তকরবী’র উদাহরণ। এখন নাটকে, উপন্যাসে নাটকীয়তা থাকে, থাকবেই, আর সেইজন্য, ওই নতুন অভিজ্ঞতা উপলব্ধির কাছে পৌঁছবো বলেই আমাদের সাহিত্য পাঠ, নাট্যচর্চায় সক্রিয়ভাবে, আমরা বেশিরভাগই অপ্রত্যক্ষ সক্রিতায় দর্শক হিসাবে অংশ নিই। সুরের দোলায় ভেসে যেতে যেতে গানের ভেতরের নাটকীয়তার অভিঘাত কখনও কখনও মসৃণ হয়ে আমাদের কাছে সে-ই ভাবে পৌঁছয় না, সুরের আচ্ছন্নতার ঘোরে আমরা আবিষ্ট হয়ে যাই। কিন্তু গানের ভেতর দিয়ে যে নিবেদন, যে গাথা পরিবেশিত, একটু তলিয়ে ভাবলে, কিংবা যোগ্যজনরা যখন ধরিয়ে দেন, তখন বোঝা যায়, ওই আচ্ছন্নতার ভেতর দিয়ে চলতে চলতে কত কিছু অলক্ষ্য থেকে গেছে। ‘প্রেম এসেছিল নিঃশব্দ চরণে’ কিংবা ‘দূরদেশী সেই রাখাল ছেলে’—এগুলো তো একেবারে চিত্রনাট্য। এগুলো চট্ করে ধরা যায়। কিন্তু একটু গভীরতায় গেলেই ধরা পড়ে, প্রত্যেকটি গানের ভেতর ওই চেতনার স্তরকে ধাক্কা দেবার আয়োজন কত পরিপাটি, কী অমোঘ! আমরা অবচেতন ছিলাম বলেই সে-ই অমোঘতা অনির্দিষ্ট হয়ে গিয়েছিল। আর তখন শুধু আলোচকেরা নয়, যোগ্য গায়কেরা তাঁদের গায়নভঙ্গিতে, শব্দের মোচড়ে শ্বাসাঘাতে সে-ই নাটকীয়তাকে সুস্পষ্ট করেন। সে-ই নাটকীয়তার নির্মাণে দেবব্রত বিশ্বাস একরকম সুবিনয় রায় অন্যরকম। পীযুষকান্তি বা কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, সুচিত্রা মিত্র একেবারে স্বতন্ত্র। এমন উদাহরণ গানের, গায়কীর অসংখ্য অজস্র। সে নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার ক্ষেত্র এটা নয় ঠিকই, কিন্তু এই বিপুল সম্ভারের উল্লেখ না করাটা অপরাধ বলে মনে হচ্ছিল। আমাদের হাতে ধরা সময়, প্রতুল মুখোপাধ্যায়, কবীর সুমনের সৃষ্টিতে এই নাটকীয়তা যেমন অনায়াস তেমনই অনবদ্য। প্রতুল মুখোপাধ্যায়ের ‘ভালোবাসার মানুষ’ গানে হঠাৎ যখন ‘আমায় যাবার বেলায়’-এর মৃদু অথচ তীব্র একটা পরিবেশন, আমাদের মুহূর্ত আগের অবস্থানকে একেবারে ভেঙে ভাসিয়ে নিয়ে চলে যায়। বলা নিষ্প্রয়োজন প্রতুল মুখোপাধ্যায় বা কবীর সুমন-এর গীত রচনা আর পরিবেশনের মতো নাটকীয়তা—বহু শ্রম আর সময় ব্যয় করা নাটকেও গরহাজির। এই উদাহরণটিও যেন স্রোতের টানেই এসে পড়ল। সুভাষ মুখোপাধ্যায়, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতার হাত ধরে যে নাটকীয়তা স্থির-স্থিত হলো আমাদের এই নৈহাটি অঞ্চলের কবি মণিভূষণের কাব্যভূমিতে, তার প্রকাশ বিশেষত ‘গান্ধীনগরে এক রাত্রি’, ‘মানুষের অধিকার’, ‘দক্ষিণ সমুদ্রের গান’-এ ওই অনায়াস আর অব্যর্থ। উদাহরণ অজস্র। একটির উল্লেখ অপ্রতিরোধ্য—‘গান্ধীনগরে এক রাত্রি’—কবিতায় শুনছিলাম, গোকুলের গল্প। বিধবা মা’য়ের সামনে পুলিশ গুলি করে গোকুলকে, ঘনায়মান সন্ধ্যায়। আমরা বহুস্তরীয় সমাজের একেকজন প্রতিনিধি—একেকরকম প্রতিক্রিয়া জানাই, সময়ের, দেশের। কিন্তু সে-ই মা! সে-ই পরিবার! শেষ দুটো পঙ্ক্তি—’উনুন জ্বলেনি আর, বেড়ার ধারেই সেই ডানপিটের তেজী রক্তধারা,/গোধূলিগগনে মেঘে ঢেকেছিল তারা’—ওই শেষ পঙ্ক্তিতে সে-ই ধাক্কা, সে-ই অভিঘাত! রবীন্দ্রনাথের সে-ই গানকে কী অনায়াসে, যেন, ও হেনরি-র ছোটগল্পের মতো অভাবিত কবজির মোচড়ে একাবারে আলাদা, একেবারে হতচকিত করে দেওয়া। এই বিস্ময়ের, এই অনাস্বাদিত আনন্দের জন্যই শিল্পের কাছে আমাদের যাওয়া, পাশেই বয়ে চলা অথচ অদেখা সে-ই জীবনস্রোতকে চমকে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখা।
৩.
সমরেশ বসু সম্পর্কে লেখকের সুহৃদ, আমাদের শিক্ষক, সমালোচক শ্রী সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন—সমরেশ অস্তিত্বের প্রাণময়তায় বিশ্বাস করতেন।—বাইরের মানুষটা নয়, ভেতরের আশ্চর্য রহস্যময় মানুষটাকে দেখা, দেখানোর তীব্র আকাঙ্ক্ষা ছিল সমরেশ-এর। কোনও লেখকেরই সব গল্প সমান মাপের হয় না, মানেরও না। কিন্তু সমরেশ বসু-র প্রত্যেকটা গল্পে সে-ই রহস্য অনুসন্ধানের একটা প্রয়াস ছিল, যা প্রত্যেক মহৎ লেখকেরই শ্রম-আয়ত্ত আয়ুধ।
এইখানে আর একটি বিষয়, পার্শ্ববর্তী হলেও প্রাসঙ্গিক, সে-ই নিয়ে একটু আলোচনা করে নেওয়া যায়। যে-কোনো শিল্পমাধ্যমের গ্রহণযোগ্যতা, পাঠকের-দর্শকের কল্পনাশক্তির, নিজেকে সংলগ্ন দেখার অবকাশের উপর নির্ভর করে। স্রষ্টা যে ছবি তৈরি করেন, দ্রষ্টা, আমাদের ক্ষেত্রে পাঠক, সেটাকে নিজের মনের নাট্যমতে কতটা সচল, সজীব করে ধরতে পারছেন, গ্রহণযোগ্যতা নির্ভর করে তার ওপর। আমাদের থাকবন্দি এই সমাজে এইজন্যই সমস্ত সৃষ্টি সাধারণত সবার কাছে সমান গুরুত্ব পায় না। বুদ্ধদেব বসু-র ‘তপস্বী ও তরঙ্গিনী’ আবু সইয়দ আইয়ুব-এর কাছে, মনে হয়েছিল—বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টিগুলির একটি। অথচ এই গ্রহণের শংসাপত্র আলোচক অশোক মিত্র-কে ধাঁধায় ফেলে দেয়। এই প্রশংসার উচ্চারণে সহমত হতে পারেন না তিনি। ‘নিজেকে ভীষণ নিরক্ষর বলে মনে হয় আমার‘—চিনতে পারেন না তিনি, ওই সৃষ্টির অসামান্যতার অক্ষরমালা-কে। যে তারে এই বিতর্কের সুর বাঁধা, সে-ই সুরে শব্দ-সংযোজন আমাদের মতো সাধারণের পক্ষে দুঃসাধ্য। আমরা শুধু আমাদের বক্তব্যের স্বপক্ষে ওই দুই মাহিকানস্দের উদাহরণ উল্লেখ করলাম মাত্র।
‘সবচেয়ে দুর্গম যে মানুষ আপন অন্তরালে,/তার পূর্ণ পরিমাপ নাই বাহিরের দেশে কালে।/ সে অন্তরময়,/ অন্তর মিশালে তবে তার অন্তরের পরিচয়।’ (‘ঐকতান’)—সমরেশ বসু সম্ভবত তাঁর জীবন-নাট্যের একেবারে প্রথম অঙ্কেই ওই অন্তর মেশানোর সহজ-কঠিন ক্ষমতাটি অনায়াস রপ্ত করে ফেলতে পেরেছিলেন। আর তারপর ঐন্দ্রজালিকের মতো অত্যন্ত পরিমিত বিস্ময়কর সব শব্দবিন্যাসে সাজিয়ে দিয়েছেন তাঁর সৃষ্টির পশরা।
বুকে হিম ধরিয়ে দেবার মতো শব্দের ছবি তৈরি করেছেন তাঁর ‘পাড়ি’ গল্পে। গল্পটি পাঁচ লাইনে বলে দেওয়া যায়, যাঁদের নিয়ে গল্প তাঁরা আমাদের যুদ্ধর-প্রতিবেশী। সমরেশ যেভাবে বলেন,—’ওই নট সম্প্রদায়ের মাগি-মদ্দা এক হলে হেন কর্ম নেই যা করতে পারে না।’—জীবন বাজি রেখে জীবনযাপন তাঁদের। যেন মানবের আদিম সংগ্রামেরই একটি আধুনিক খণ্ডচিত্র এই গল্প। প্রবল দুর্যোগে পাড়ি দিতে হবে উত্তাল নদী, ওপারে পৌঁছে দিতে হবে শুয়োরের পাল, মালিকের কাছ থেকে তবেই মিলবে বাঁচার রসদ। যে গল্প লেখেন সমরেশ, যে বর্ণনা ওই পাড়ির যাত্রাপথের—সে ওই প্রতি মুহূর্তে ভয়ে-আশঙ্কায় দমবন্ধ করে পরের পঙ্ক্তিতে যাবার টান। মনে পড়ে যাওয়া সম্ভব, বাংলা সাহিত্যে ‘তিস্তাপারের বৃত্তান্ত’র ফরেস্টার চন্দ্র বাঘারু বর্মণ—যখন বিশাল মহিরুহকে আশ্রয় করে ভেসে আসে তিস্তা-র স্রোত বেয়ে, সে এক অসাধারণ বর্ণনা, পাঠকের অনুপম অভিজ্ঞতা। দেবেশ রায় লিখেছেন বিস্তারে, অগ্রজ সমরেশ লিখেছিলেন সাঁটে, কাব্যের পরিমিতিকে গদ্যে টেনে এনে। আর সেইজন্য রচনা হয় গহন, এক রহস্যময় টান বইতে থাকে ভেতরে ভেতরে। ‘পাড়ি’-কে উদাহরণ হিসাবে টেনে আনার উদ্দেশ্য এই যে, এই গল্পে চরম নাটকীয়তা সত্ত্বেও মাধ্যম হিসেবে নাটক কিন্তু এর কাছে আপন সীমাবদ্ধতায় বিস্ময়বালকের মতো নিঃশব্দে বসে থাকে। এই গল্পে চলচ্চিত্র হয়, হয়েওছে। নিজ-মাধ্যমের সমস্ত উপাদান সম্পৃক্ত হয়ে আছে ওই চলচ্চিত্রে। নাট্যে ওই পাড়ি-র যাত্রা বিধৃত করা অসম্ভব, অথচ চূড়ান্ত নাটকীয়তার শুরু গল্পের সূচনা থেকেই। ওই আখ্যান, আখ্যানই বলা সঠিক, যখন শেষ হয়, যখন নারী-পুরুষ দুটি প্রকৃত পারিশ্রমিকের থেকে অনেক কম পেয়েও, বলা বাহুল্য এতেই অভ্যস্ত তাঁরা, নিজেদের খিদে মেটান, ঘুমিয়ে পড়েন একসময়। আর আমরা পাঠকেরা জেগে উঠি। ‘গঙ্গার ধারে চটকলের বস্তিতে মাদি শুয়োরের ছানাপোনার সঙ্গে যেখানে হতবাক্ মানবশিশুরা কাতরাচ্ছে’ (‘কোনো এক কবি সম্মেলনে’, মণিভূষণ ভট্টাচার্য)—আমরা যেন এতদিনকার পাশে রয়ে যাওয়া সে-ই কমিউনিটিকেই নতুন করে চিনি! গঙ্গার ধারে ওই ‘নট-সম্প্রদায়ের মাগি মদ্দা’রা সম্ভ্রম আদায় করে নেয় আমাদের। এই গল্পে সংলাপের পর সংলাপ সাজিয়ে, ঘটনার আকস্মিক পরিবর্তনের ভেতর দিয়ে পাঠকের ঘাড় কামড়ে ধরার প্রক্রিয়া নেই কিন্তু অপরূপ নাটকীয়তা ওই বর্ণনায় ওই বিন্যাসে।
এইরকম অতি-নিকটে থাকা অপরিচিত, আরেকটি কমিউনিটির উদাহরণ ‘মানুষ রতন’ গল্পের ত্যাবড়া, ফোতে, মনা, পুনিয়া, জগা আর যমুনা। আর এদের অপনেন্ট গণেশ, ফটকে। নাটক কীভাবে তৈরি হয় সাহিত্যে, বিশেষত ছোটগল্পে, তার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ—‘মানুষ রতন’। কলেবরে একটু বড়, বিস্তারও অনেকটা। একটু খুঁটিয়ে লক্ষ করলে দেখা যায়, গল্প শুরু হয়: শুরুতেই রহস্যের আভাস। ত্যাবড়াদের দলের ইশারা এবং কাজে নেমে পড়া, গণেশদের সন্দেহ, এবং পাঠক হিসাবে আমাদেরও। একটা সময় একটা মড়া, একটা মৃতদেহ প্ল্যাটফর্মে শুইয়ে রেখে ত্যাবড়া ফোতে আদি রিকশাওয়ালাদের দান-সংগ্রহ এবং অবশ্যই, আমরা ভদ্রলোকেরা ধরে নিতে পারি গাপ্ করে দেবার মতলব, সেটা স্পষ্ট হয়। কিন্তু ততক্ষণে গুটিগুটি হাজির হয়ে গেছে আরেকটি আশঙ্কিত উপাদান—গণেশদের বিরোধিতা, প্রতিঘাত কতদূর যাবে? লেখক নাটকীয় উপাদান এবং তার বিন্যাস, একেবারে সুদক্ষ বাজিকরের মতো ঘটিয়ে চলেন একের পর এক। আর এর ভেতর দিয়েই কেবল কিছু আঁচড়ে স্পষ্টতর হতে থাকে চরিত্রগুলোর অতীত, বর্তমান, ইঙ্গিত থাকে অনির্দিষ্ট ভবিষ্যতের। সমাজ প্রশাসকরাও সময় মতো হাজির হন, আমরা মিলিয়ে নিই আমাদের শোনা অভিজ্ঞতাগুলোকে, আমাদের মতো কয়েক থাক উপরে থাকারা যে বাস্তবকে ‘সসম্মান’-এ এড়িয়ে চলি! গণেশদের দল-ও যে এইরকম মৃতদেহ শুইয়ে রেখে অর্থ সংগ্রহ করে, নিজেদের ‘ভোগ’-এ লাগায়, সে তথ্যও আসে অপ্রত্যক্ষে। দ্বিতীয় পর্ব যখন শেষ হচ্ছে, তখন দুই ছিনতাই পার্টির মারামারি, ত্যাবড়া ফোতোরা তুলনায় দুর্বল। আমরাও ততক্ষণে ওদের অনেকটা জায়গা দিয়ে ফেলেছি, আশঙ্কিত হচ্ছি, কী হচ্ছে? পুনিয়া যখন বলে, ‘যাক্, এসে গেছে।’—মানে পুলিশ, অর্থাৎ আপাতত এরা নিশ্চিন্ত। কিন্তু ততক্ষণে আরেকটা আশঙ্কা শ্মশানঘাটে কী হয়! এইখানে, একজন নাট্যকারকে যেন হাতে ধরে গল্পকার বলে দেন; এইখানে তুমি বিরতি দিতে পারো! পাঠক এবং দর্শকও জানেন না দ্বিতীয় বিস্তারে কী হবে! অনেকগুলো সম্ভাবনা কাজ করে, এবং অবশ্যই সে-ই সম্ভাবনাগুলো আমাদের চর্চিত জীবন থেকেই উঠে আসে। কিন্তু গল্পকার দেখছেন, ওই মানুষগুলোর অবস্থান থেকে, আর এবার তাঁর দৃষ্টি ওই চরিত্রগুলোর ভেতর-বাড়িতে। এই পর্বে একেবারে অন্য এক বিস্তার। যেন প্রথম পর্বের খরস্রোতা নদী এখন অনেক শান্ত, ওই উৎক্ষিপ্ত চরিত্রগুলি এবার নিজের নিজের দিকে তাকায়। তারা মদ খায়, শবদাহ করে। ত্যাবড়া বলে,—‘মানুষ যে কী, তা বুঝলাম না!’—যমুনা চিৎকার করে কাঁদে। যেন সবার পিতৃদাহ। ডোম চিতার দিকে এগোয়।
নাটক একেবারে সাজানো। এই নাটকের নাট্য-প্রচেষ্টাও হয়েছে। কিন্তু সমস্যা অন্য জায়গায়। যে সংলাপের ভেতর দিয়ে সিচুয়েশনকে এগিয়ে নিয়ে যাবার অপেক্ষা থাকে নাটক লেখার ক্ষেত্রে, তেমন শক্ত কলমের অভাব এই বাংলাদেশে ভয়ংকর। বহু বহু প্রকাশিত, এবং মঞ্চস্থ হওয়া নাটকেও দেখা যায়, চরিত্রগুলো যে কথা বলে, নাটককার যখন তা সাজান, তখন সে-ই শব্দ বাক্য সব নাটককারের নিজ সমাজ-অবস্থানগত জায়গা থেকে উঠে আসে, চরিত্রগুলোর অবস্থান থেকে নয়। ফলে নাটককারের ইচ্ছাপূরণ ঘটে। নাটক একটা অবাস্তব নড়বড়ে কাঠামোতে হাজির হয়। বরং সমরেশ বসু নিজেই এইসব প্রায়-নাটককে যদি নাটকের বিন্যাসে লিখে যেতেন! আমরা তো সে-ই মানুষ নই, যারা অন্তরের সঙ্গে অন্তর মিশিয়ে নিজেদের অভিজ্ঞতার ঝুলি সম্পূর্ণ করে সৃষ্টিতে নেমেছি! সে করেছেন সমরেশ! জীবনের একেবারে উৎসভূমিতে নিজেকে স্থিত রেখে প্রকাশ করেছেন সে-ই ওঠা-পড়াকে! ওই জন্য শুধু বিষয় নয়, সংলাপের ভেতরকার শব্দের বিচ্ছুরণই চিনিয়ে দেয় চরিত্রদের সমাজ-অর্থনৈতিক অবস্থান!
১৯৫৭ সালে নতুন সাহিত্য প্রকাশ করে ‘কিমলিশ’। পুস্তকাকারে ‘ফুলবর্ষিয়া এবং গল্পগ্রন্থ’। বইটির উৎসর্গ নৈহাটি-ভাটপাড়া অঞ্চলের বামপন্থী আন্দোলনের অবিংসবাদী নেতা শ্রী গোপাল বসু-কে। সমরেশ এবং ওই সময়কার বহু বামপন্থী কর্মীর মেন্টর তিনি। এই উৎসর্গপত্রের ভেতরেও একটি নাটকীয়তা আছে, সেটা এই আলোচনায় গৌণ হলেও উল্লেখের প্রয়োজন। এই ‘কিমলিশ’ বা পরবর্তীতে লেখা ‘শেকল ছেঁড়া হাতের খোঁজে’র ভেতর দিয়ে বামপন্থা এবং তার বাস্তবচর্চা সম্পর্কে সমরেশ তাঁর আপন উপলব্ধিই সম্ভবত তাঁর বা তাঁদের মেন্টরের কাছে পৌঁছে দিতে চেয়েছিলেন! গল্পের এই পশ্চাৎপটটিও নেহাৎ কম নাটকীয় নয়।
কারখানায় স্ট্রাইক করতে গিয়ে বেচনের জেল এবং গল্পের শুরু বেচনের ফিরে আসা থেকে। নাটকে আমরা যাকে ‘ফ্ল্যাশব্যাক’ হিসাবে উল্লেখ করি, লিখি, তা কোনও আলাদা ভাবনা-দৃশ্য না রেখেই গল্পের ভেতর পরতে পরতে খুলে যেতে থাকে। আধুনিক নাটকে কোনও দৃশ্য থামিয়ে দিয়ে, অতীত থেকে কোনও ঘটনার ভেতর দিয়ে ঘুরে আসা এড়িয়ে যাওয়াই হয়। বরং সংলাপের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম আঁচড়ে সে-ই অতীত-উন্মুক্ত করার ভেতর থাকে নাটকীয়তা এবং দর্শকের সক্রিয় অংশগ্রহণ—ওই আঁচড়ের টান-টোনগুলোকে সম্পূর্ণ করার ভেতর দিয়ে। ‘কিমলিশ’-এ সে-ই মুনশিয়ানা নাটক লিখিয়ে হিসাবে শিক্ষণীয়, প্রযোজনা বর্ণময় করে তুলতেও এই উপাদান মহার্ঘ্য। বেচন ফিরে এলেও, বাবা মা ভাই বোন স্ত্রী এবং পড়শি সবার কাছেই যেন অপরিচিত, সে নিয়ে আসে কিছু শহুরে-অভ্যাস, ব্রাশ-টুথপেস্টের ব্যবহার থেকে কিতাব পড়া… সব। বাড়িওয়ালা কালিকাপ্রসাদ থেকে স্ত্রী মুনিয়া—সবাই ওকে সন্দেহ করে। ওর বুলি-ও কেমন অচেনা ঠেকে পুরোনো সহকর্মী-মজদুরদের কাছেও। নিজেদের ভেতর, এবং বেচনের সঙ্গে কথোপকথনেও এই হঠাৎ কেমন নতুন হয়ে যাওয়া বিষয়টি সূত্র রাখে একসাথে হাস্যরসের এবং ঔৎসুক্যেরও। গোটা গল্পটি যেন একেবারে দৃশ্য ভাগ করে এখানেও সাজিয়ে রাখা আছে।
উল্লেখ করার মতো চরিত্র, খুব চলতি ভাষায় যদি বলা যায়, চরিত্রগুলোকে নিয়ে নাটকীয়ভাবে খেলবার উপাদান সমরেশ রেখে যান খুব সহজ কিন্তু সুগভীর ইঙ্গিতে। বাড়িওয়ালার সন্দেহ, বেচনের কাছে পড়বার বইপত্র সম্পর্কে পড়শিদের ঔৎসুক্য এবং ‘আচ্ছা কাল বাতায়েগা’ বলে বেচনের এড়িয়ে যাওয়া, বসতি-র পণ্ডিত যখন বলেন, ‘খবরদার, সমঝায়েগা তো আচ্ছা নেহি হোগা’, পার্টির নেতা নারায়ণবাবু যা বলেন, বেচন এখন বোঝে, তার চারভাগের একভাগও মজদুরদের মাথায় ঢোকে না! এই প্রত্যেকটি চরিত্র তাদের সমাজ-শ্রেণিগত অবস্থান থেকে যা সব বলে, ভেতরে রয়ে যায় আরও ন’ভাগ—যা তুলে এনে প্রকাশ করার অবকাশ এবং দায় থাকে নাটককারের। ‘দায়’ শব্দটি বলা এই কারণে, সমরেশ এই ছয়ের দশকেই যখন বুঝতে পারছিলেন, শ্রমিক শ্রেণির উন্নতিকল্পে উৎসর্গীকৃত সব নেতা-কর্মীরা যা বলেন, তা মজদুরদের তলে এসে দানা বাঁধতে পারে না, শব্দগুলি ভারী ভারী গোলা-র মতো নিক্ষিপ্ত হয়, মজুরের দল শোনেন, কেউ কেউ প্রতিধ্বনি করেন, তিনি ‘অগ্রবর্তী’—তখন এই ফাঁপা, শূন্য পরিস্থিতি আরও স্পষ্ট, প্রত্যক্ষ করার কাজটিকে নাটককার এড়িয়ে যেতে পারেন না। এবং গোড়ায় ওই উৎসর্গপত্রের যে নাটকীয়তা, নিজ-মেন্টরকে যে বারতা পৌঁছে দিতে চান সমরেশ, তা-ও নাটককার সাজাতে পারেন নিজের চিন্তা এবং লেখনীর মুনশিয়ানায়। একটি আপাত-সামান্য ঘটনা, যা ওই মজদুরদের কলোনিতে প্রায়শই ঘটে থাকে, তার সূত্র ধরেই বেচন আবার নিজের অবস্থান স্পষ্ট করে, মেহনতি মানুষদের কাছে গৃহীত, স্বীকৃত হয়।
নাটকীয় সব উপাদান একেবারে ধরে ধরে সাজানো, শুধু নির্দিষ্ট করে বিস্তারে যেতে হবে একজন নাটককারকে। খুবই সহজ সে-ই কাজ। এবং কঠিনও। কঠিন এ জন্য যে, এই বিস্তারে যেতে গেলেই ওই জীবনকে জানতে হবে, ঘোড়ার পিঠ থেকে জমি দেখার মতো না, একেবারে কাঁকুরে অমসৃণ মাটির ধুলোকাদা মেখে, যা করেছিলেন সমরেশ। সেইজন্য সাঁটে ছোটগল্পেও দিতে পারেন প্রায় মহাকাব্যের ইঙ্গিত।
খুবই কম আলোচিত, উদ্ধৃত একটি গল্প ‘সুবাসী’। নাটক এখানেও সাজানো—কথক একজন ‘নজরবন্দিবাবু’ এই গল্পের চরিত্ররাও জীবনের প্রায় প্রান্তসীমায়, কিন্তু ‘কিলমিশ’-এর কুলি-লাইনের লোক তারা নয়। নারকোল গাছ ঝুড়োয় গোপাল বাগদী, বিলে ঘরামি-র দিদিমা, দুধ দেন নজরবন্দিবাবুকে, পাশেই ব্রাহ্মণ ঘরের বিধবা যুবতী, অসহ্য জীবন থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য বাপের বাড়িতে চিঠি পাঠায় এবং যথারীতি আরও চিঠি পাঠানোর অবকাশ থেকেই যায়। দুলাল কারখানার মিস্ত্রি, বিপিন তার বন্ধু-সম অ্যাসিস্ট্যান্ট। সে-ই দুলাল বিয়ে করে নিয়ে আসে ষোলো-সতেরো বছরের কিশোরী সুবাসী-কে। হাসিখুশি দুলাল আর স্ত্রীর প্রেমের তরিকায় সারা বসতিতে ঢিঢি পড়ে। তারা সেজেগুজে সিনেমা দেখতে যায়, নজরবন্দিবাবু-র কাছে নতুন বউকে পরিচয় করাতে আনে দুলাল। আদবকায়দা অনেক আধুনিক যেন! সামান্য অসুখে মারা যায় দুলাল। সুবাসী অথই জলে। গঙ্গার ওপার থেকে সুবাসী-কে দেখভাল করার জন্য এক পিসি আসেন, তিনি নিজেই ‘অসতের শিরোমণি’! কিন্তু সুবাসী-কে দিয়ে তার মতলব সম্পূর্ণ হয় না, সুবাসী এখন ঠিকে ঝি, চার বাড়িতে কাজ করে, মাথায় ঘোমটা নেই, পুরো লড়িয়ে মানুষ। পট বদলে যায়। এবং নাটকের প্রথম পর্ব যেন শেষ হলো। এই লড়িয়ে মানুষটির কী হবে এইবার এই আখ্যানে?
সমরেশ বসু, আবারও বলা প্রয়োজন, এইসব ছোটগল্পে রেখে গেছেন মহৎ গভীর সব জীবন-চিত্র। ‘সুবাসী’-র গল্পের শেষ পর্ব যেখানে এসে থামে, পাঠকের, এবং যদি নাটক হয়, তবে দর্শকেরও সে-ই পরিণতি কল্পনাতীত। আর সেখানেই যেন অশোক মিত্র কথিত—একটি চেতনা-স্তর থেকে অন্য স্তরে যাওয়ার অভিঘাত! অফুরান নাট্যসম্ভার, এবং অভিনব। আর শুধু মুহুর্মুহু নাটকীয় অভিঘাতেই উচ্চকিত নয় সে সব, জীবনকে দেখার, জীবনচর্চার একটা অপ্রত্যক্ষ পাঠও যেন সযত্নে সাজিয়ে রাখেন। আর থাকে দর্শন। সমরেশ তাঁর কৈশোর-যৌবনের দর্শনকে, সমাজ বদলে দেবার বীক্ষাকে চর্চার একেবারে গভীরে গিয়ে আত্মস্থ করার চেষ্টা নিয়েছিলেন। আর বাদ সাধে সেখানেই। শোষিত মানুষদের জন্য নতুন ভোর এনে দেবার কাজে নিয়োজিত অগ্রবর্তী সৈনিকদের বেশিরভাগই প্রায় উদ্ধারকর্তার মন নিয়ে লড়াই-এর ময়দানে অবতীর্ণ। কিন্তু সমরেশ জানতেন, এই চর্চা, এই ভাবে প্র্যাকটিস ভুল, বিপজ্জনক। এইসব মেশায়াদের শেষ অবস্থান যে নেতৃত্বের সুখাসনে গিয়ে সমাপ্ত হবে, এই উচ্চারণ এদেশে ওদেশে বিদেশে সর্বত্র। কিন্তু কেউ এতে কান দেননি, দিলে যে নিজেদের ‘শ্রেণিচ্যুতি’ ঘটে। আর সমরেশ ওই সময়ে প্রায় একা কুম্ভের মতো আগলেছেন দর্শনের সে-ই অমোঘ অনিবার্য চর্চা-পথকে। যেখানেই সুযোগ পেয়েছেন, উচ্চারণ করেছেন সে-ই সাবধানবাণী। ‘সুবাসী’র মতো গল্পে নজরবন্দিবাবুকে যখন মোহমুগ্ধ কেউ ‘আপনি তো আমাদের জন্য লড়ছেন’ বলে বিহ্বল হয়ে যায়, সে-ই কথক নজরবন্দিবাবু বলেন: আমরা সবাই লড়ি নিজেদের জন্য। যে শুধু পরের জন্য লড়ে, আর লড়িয়ে হয়, তেমন বীরদের আমার বড় ভয়।—এই ভয় কথকের, সমরেশের। এবং বলা বাহুল্য, আজও, এখনও আমাদের।
৪.
অজস্র অসংখ্য ছোটগল্প সমরেশ বসু-র, অফুরান নাট্যসম্ভার নিয়েই তারা উপস্থিত। নামোল্লেখে নির্দিষ্ট করা বাতুলতা। প্রচুর, প্রচুর। বোম্বে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত বুদ্ধদেব বসু-র প্রবন্ধ ‘Tagore: Portrait of a Poet’ (প্রথম প্রকাশ: ১৯৬২)-এ রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে প্রাবন্ধিকের বক্তব্য: ‘জীবন ও কবিতা বিষয়ে যৌবন থেকে মৃত্যুকাল পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ একই ধারণা পোষণ করে গেছেন। আর তাঁর ক্ষেত্রে সেটাকেই হয়তো স্বাভাবিক বলা যেতে পারে।’ বুদ্ধদেব বসু যে বাক্যবন্ধটি ব্যবহার করেছিলেন তা হলো—’attitude to life’—শব্দগুলি কেমন প্রোজ্জ্বল হয়ে ওঠে! এমন উজ্জ্বল-সম্ভার থাকা সত্ত্বেও তাহলে বাংলার স্বর্ণপ্রসবিনী নাট্যমঞ্চে সমরেশ এত দূরবর্তী কেন! সেটা কী ওঁর গল্পে যে দর্শন, তার প্রতি আপাত নৈকট্য দেখানো সত্ত্বেও, ভেতর থেকে কোনও টান অনুভব করি না? নাকি ওই নজরবন্দিবাবুর কথামতো—যা ‘কিমলিশ’ বা ‘শেকল ছেঁড়া হাতের খোঁজে’ এবং আরও বহু গল্পে কোথাও স্পষ্ট প্রত্যক্ষ, কোথাও অপ্রত্যক্ষ ভাবে রয়েছে—‘লোকশিক্ষে’র পরম্পরায় ওইরকম ‘জনগণকে শিক্ষিত’ করার কাজেই নাটককেও ব্যবহার করি! নিজেরা নিজেদেরকে প্রশ্ন করতে, বিশ্লেষণ করতে ভয় পাই, গুটিয়ে আসি! এই দেশ এই সমাজের কাছে, শিক্ষকের ধুতি চাদরে পরিপাটি হয়ে দূরত্ব রেখে নিজ-আসন স্থির করে নিলে, ওইরকম উপদেশ চলে, মাটিতে নেমে সম্মিলিত যাত্রার সুর সাধা চলে না! সমরেশের সঙ্গে আমাদের সচেতন দূরত্ব রেখে চলা ওই জন্য। লীলা মজুমদার জিজ্ঞেস করেছিলেন সমরেশকে, ‘কেন লেখো’! সমরেশ বলেছিলেন ‘জানবার জন্য’। চারপাশের পরিসরের মাঝখানে নিজেকে রেখে দেখা, জানা। সমরেশ সে-ই অভিজ্ঞান অর্জন করেছিলেন! আমরা শুধু নাটকের লোক হিসেবেই নয়, মানুষ হিসেবেও সমরেশের সে-ই চর্চায় অনাগ্রহী। ফলত অভিজ্ঞান আমাদের দূরবর্তী হয়েই থাকে। ঐতিহ্যের বিস্তার ঘটে না। সমরেশ কেবল সংকলনে আটকা পড়ে থাকেন। নাটকের মতো এমন শক্তিশালী, ছড়িয়ে পড়ার এমন সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও ওই সম্ভার আমাদের দূরবর্তী। সমরেশ একলা হয়েই থাকেন।